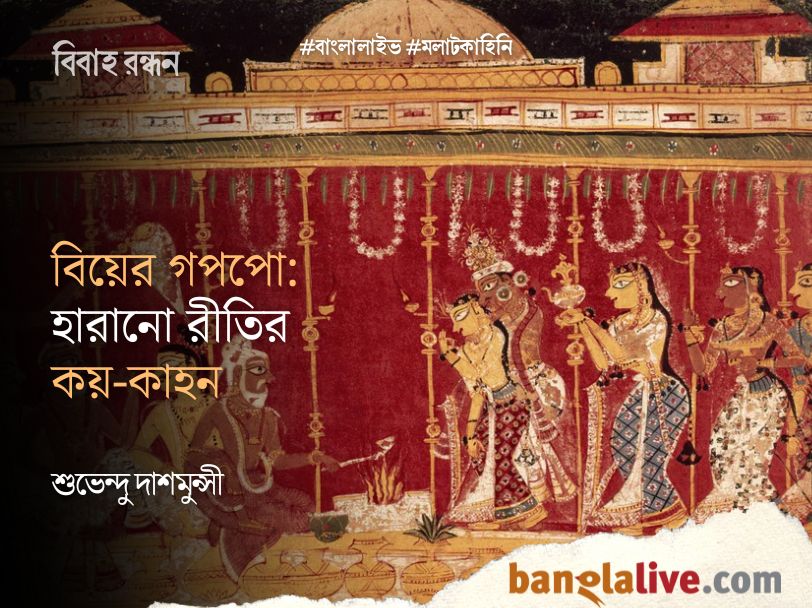Ancient Wedding
সে এক মজার গল্প। বিয়ের গল্প। তবে সে বিয়ে ঠিক আজকের বিয়ে নয়। ব্রিটিশরা এখানে আসারও আগের বিয়ের গল্প। ব্রিটিশরা আসেনি, তখন চলছে বাংলার সুলতানি পর্ব, সেই সময়ের বিয়ের কথা এটা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেকালের মঙ্গলকাব্যের অন্দরে। অন্দর-ই বটে, বিয়ের কাহিনি তো অন্দরের গল্পই। লোকবৃত্তের কথা। কত কিসিমের রীতি-রেয়াজ, কত ধরনের পর্ব তার। কালান্তরে তার অনেকটা হারিয়ে গিয়েছে, কতকটা নামে থাকলেও বদলে গিয়েছে তার ধরন আর কিছু তো একভাবেই বয়ে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, প্রজন্মের পর প্রজন্ম। (Ancient Wedding)
ব্রিটিশরা আসেনি, তখন চলছে বাংলার সুলতানি পর্ব, সেই সময়ের বিয়ের কথা এটা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেকালের মঙ্গলকাব্যের অন্দরে।
(Ancient Wedding) বিয়ে কেন করতে হবে আর কীভাবে তা সম্পন্ন হবে, তার এক লম্বা ফিরিস্তি ছড়িয়ে আছে সেকালের লেখাপত্তরে। তার অনেক কথাই আজ শুনতে ভারী অদ্ভুত আর অমানবিক মনে হবে, তবু তারা ছিল! যেমন ধরা যাক, বিয়ের দরকার কেন, সেটা বলতে গিয়ে, কৃত্তিবাস ওঝা লিখেছিলেন, “ইহকালে না হৈল আমার সন্ততি।/ পরকালে কী রূপে পাইব অব্যাহতি।/ সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।/ আমার মরণে বংশে নাহি একজন।” বাংলাতে একটি অপশব্দ সেকালে চালু ছিল, ‘আটকুঁড়ে’। সন্তানহীন পুরুষকে চিহ্নিত করা হত এই শব্দে। ওই কৃত্তিবাস-ই লিখেছিলেন মহারাজ দশরথের বেদনার কথা। দশরথ “অপুত্রক রাজা রাজ্য করে মনে দুখ/ প্রাতে নাহি দেখে লোকে অপুত্রকের মুখ।” ভাবুন কাণ্ড। খোদ মহারাজও যদি অপুত্রক হন, তাহলে লোকে তার মুখ দেখবে না!
রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে তিনি তো পষ্টাপষ্টিই বলে দিচ্ছেন, “আটকুঁড়া দরশনে মহাপাপ হয়”। বুঝতেই পারছেন সমস্যাটা কোথায়? ছিল ‘সন্ততি’ সেটা ক্রমশ হয়ে দাঁড়াল ‘পুত্র’। সেই যে বিবাহ মন্ত্রেই তো বলানো হয় যে, পুত্রার্থেই নাকি বিবাহ। (Ancient Wedding)
পাত্রী দেখা হত কীভাবে, কীভাবে হত তাদের লক্ষণবিচার তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন মনসামঙ্গলকাব্যের দুই কবি, নারায়ণদেব আর দ্বিজ বংশীদাস।
(Ancient Wedding) বিবাহের জন্য পাত্রী-নির্বাচন প্রক্রিয়াটিও আজকের চোখে ভারী বিসদৃশ। পাত্রী দেখা হত কীভাবে, কীভাবে হত তাদের লক্ষণবিচার তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন মনসামঙ্গলকাব্যের দুই কবি, নারায়ণদেব আর দ্বিজ বংশীদাস। নারায়ণদেব বলছেন: “পিঙ্গললোচন নহে, খঞ্জনেত্র আঁখি” হলে পাত্রী বাছাই করা চলবে না। আরো আছে এমন নিদান। বংশীদাস লিখছেন, “কপালেতে কালপূত জিহ্বা নীলরেখ। সেই কন্যা পুরুষের যম পরতেখ।” তার সঙ্গে যে মেয়ের ‘সর্পলেজ কেশ’ আর ‘শকুনের আঁখি’ সেও বাতিল। তারপরে, “অঙ্গুলি যাহার ছোটো, চঞ্চল কোমর” তার সঙ্গে নাকি ছেলের বিয়ে দিলে ছ-মাসে বরের ‘যমের নগর’ যাওয়া নিশ্চিত! অসবর্ণ বিবাহ তো নৈব নৈব চ। কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতে বলছেন “ক্ষত্রিয়ের যোগ্য নহে ব্রাহ্মণ নন্দিনী”। গোটা মধ্যযুগের কাব্যে বরপণের উল্লেখ নেই, আছে কন্যাপণের সাতকাহন। এ তো আর কোনও মজার গল্প নয়, এ তো রীতিমতো চিন্তার কথা। (Ancient Wedding)
আরও পড়ুন: বিবাহ রন্ধন: চিঠি কি এসব বোঝে! বেনারসি আসে যায় ওদের বিয়ের কথা হোক…
(Ancient Wedding) তবে এখন শোনা যাক দুই-তিনটি এমন প্রথার কথা, যা সেকালে ছিল, কিন্তু এখন আর নেই।
বিয়ের সব কথা পাকা হলে হত তখন ‘তুলসী-বদল’ আর ‘লগ্নপত্র’। অনেকটা ‘ফাইনাল এনগেজমেন্ট’ আর কী। লগ্নপত্রতে লিখিত থাকত এই পাকাকথার কথা। বিজয়গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গলকাব্যে লিখেছিলেন, লখিন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহ স্থির হলে বলা হল ‘এইবারে সদাগর লগ্নপত্র করো’। শুধু পার্থিব বিবাহে কেন, ভারতচন্দ্র তো দেবতার মানবায়ন ঘটিয়ে একেবারে শিব-দুর্গার বিয়েরও লগ্নপত্র তৈরি করিয়ে ফেলেছেন দেবর্ষি নারদকে দিয়ে। ভারতচন্দ্র লিখছেন: “হিমালয় মেনকা যেমনি দিল সায়।/ লগ্নপত্র তৈরি করে নারদমুনি যায়।” কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর মনসামঙ্গলকাব্যে লিখেছিলেন তুলসীবদল প্রথার কথা। (Ancient Wedding)
বিয়ের সব কথা পাকা হলে হত তখন ‘তুলসী-বদল’ আর ‘লগ্নপত্র’। অনেকটা ‘ফাইনাল এনগেজমেন্ট’ আর কী।
ঘটক জনার্দন বিয়ের কথা হওয়ামাত্র
“চতুর ঘটক ছিল জনার্দন সাথে।
তুলসী আনিয়া দিল দুজনের হাতে।।
তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয়।
লখিন্দরে বেহুলা দিব সায় বান্যা কয়।”
বিয়ের দিন সকালে জল সইতে যাওয়ার অনুষ্ঠান এখনও অনেক জায়গাতেই প্রচলিত। বাড়ির বধূরা একসঙ্গে গিয়ে কোনও কাছাকাছি জলাশয় থেকে জল আনেন, সেই জলেই চান করে বর গায়ে হলুদের পর। মূল বিষয়টা এক হলেও, মধ্যযুগের ইতিবৃত্তে দেখা যায় এই জল সইতে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল একেবারেই অন্য রকম। প্রথমে বাড়ির কুলবধূরা দল বেঁধে যান নিকটবর্তী মন্দিরে। সেখানে পুরোহিত তাদের কলসিতে ভরে দেন কিছুটা জল। তারপরে তাঁরা যাবেন পাড়াপড়শিদের দুয়ারে দুয়ারে। সেই সব বাড়ির বধূরা জল দেন আর এঁদের কাজ তাঁদের থেকে নব হবু দম্পতির জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা আর তাঁদের হাতে এরা তুলে দেন শুভেচ্ছার চিহ্ন পান-সুপারি। (Ancient Wedding)
(Ancient Wedding) সেই সংগৃহীত জল দিয়েই না বরের চান হবে। কৌম সমাজে সকল লোক-সাধারণের একদেশীভবনের কী চমৎকার এক আচার ছিল এটি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখাতে দেখি, “কাঁখেতে হেমঝারি মেনকা মিলি নারী, জল সহে ঘরে ঘরে। জতেক এয়ো মিলি করিয়া হুলাহুলি মঙ্গলসূত্র বাঁধে করে।” কেমন ভাবে, কেমন সাজে যাত্রা করত এই বধূর দল? সঙ্গে হেমঝারি, মানে সোনার কলসির কথা তো আছেই। তাদের “শিরে শোভে শিরি থালা/ গলে শোভে পুষ্পমালা/ আগে পিছে নানা বাদ্য বাজে।” এ এক রীতিমতো বর্ণময় শোভাযাত্রা যেন। (Ancient Wedding)
মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখছেন: “দুই দলে গালাগালি কোন্দন চুলাচুলি/ বরযাত্রী দেউটি না ছাড়ে।/ ধূলা খেলা ঢেলা বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি/ দুই দলে খুনাখুনি পাড়ে।”
(Ancient Wedding) সেকালের বিবাহ অনুষ্ঠানে মেয়ের বাড়িতে বর এলে তাকে বরণ করার দুটি রীতির কথা শোনা যেত। একটির নাম: ‘আঠারো বেকতা’, আরেকটির নাম ‘ঢেলাই চণ্ডী’। প্রথমটা আছে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গলকাব্যে আর পরেরটা আছে চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুথিতে। সেই পুথি প্রামাণ্য কী না, তা নিয়ে গবেষক মহলে সন্দেহ আছে। তা থাক। যেই লিখুন, আমাদের দরকার লেখা নিয়ে। কারণ, লেখা যখন হয়েছে, তখন বিষয়টি তো চালু ছিল আর সেটাই আসল কথা এখানে। আঠারো বেকতা হল বর যখন বিয়ে করতে প্রায় মেয়ের বাড়ি পৌঁছল, তখন কোত্থেকে হাজির হবে পাড়ার বাচ্চা ছেলের দল, ধাঁধা দিয়ে প্রশ্ন করবে, সেই উত্তর দিলে তবে খুলবে পথ। না পারলেও সমস্যা নেই, পান-সুপারি ধরে দিলেই হবে। কেতকাদাস লিখছেন: “কর প্রসারিয়া পথ আগুলিয়া/ আঠারো বেকতা পড়ে।” (Ancient Wedding)
আরও পড়ুন: বিবাহ রন্ধন: বিয়ের ছবির ভাগচাষ
(Ancient Wedding) অন্যদিকে ঢেলাই চণ্ডী হল, বর বিয়ে করতে এলে তাকে লক্ষ করে ছোটো ছোটো নুড়ি হালকা করে ছুড়বে মেয়ের বাড়ির লোক। সেটাই নাকি সেকেলে বরণ করার রীতি! মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখছেন: “দুই দলে গালাগালি কোন্দন চুলাচুলি/ বরযাত্রী দেউটি না ছাড়ে।/ ধূলা খেলা ঢেলা বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি/ দুই দলে খুনাখুনি পাড়ে।” বোঝাই যাচ্ছে, সামঞ্জস্যের অভাব বঙ্গজীবনের অঙ্গ বহুদিন ধরেই। (Ancient Wedding)
কৌম সমাজে সকল লোক-সাধারণের একদেশীভবনের কী চমৎকার এক আচার ছিল এটি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখাতে দেখি, “কাঁখেতে হেমঝারি মেনকা মিলি নারী, জল সহে ঘরে ঘরে।
(Ancient Wedding) তবু, এইসব মজার মজার আচার বিচার থেকে সরে আসতে আসতে এখন শুধু নিমিত্ততে ঠেকেছে আজকের বিয়ের অনুষ্ঠান। তার ভেতর যাদের বিয়ে হল, তাদের আনন্দ সংলগ্নতা আছে, ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে কৌমচেতনা, সকলের সঙ্গে মিলে, সকলকে নিয়ে আনন্দ উৎসবের আবহ। বুঝি সেটাই অনিবার্য, কিন্তু এই এত এত লোকাচারের ভেতর লুকিয়ে থাকা মানুষের জীবনপ্রবাহ যে ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি আমরা। তার বেলা? (Ancient Wedding)
শুভেন্দু দাশমুন্সী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্যর গুরুদাস মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক, সত্যজিৎ রায় বিশেষজ্ঞ। চিত্রনাট্যকার। গুপ্তধন সিরিজের সোনাদা চরিত্রের স্রষ্টা। গীতিকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সার্ধশতবার্ষিক রবীন্দ্র রচনাবলীর সম্পাদক।