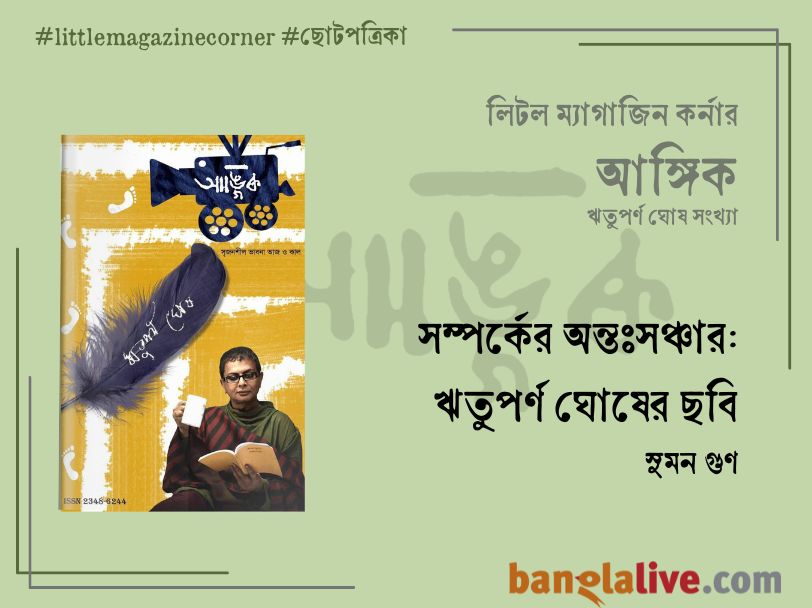বাংলা ফিল্মের ধারায় ঋতুপর্ণ ঘোষের অবস্থান খুব স্পষ্ট আর নিশ্চিত। তাঁর ছবির মতোই। বুদ্ধদেব অপর্ণা গৌতম-এর পরে ঋতুপর্ণ ঘোষের গল্প বলার দায়হীন আর কৌণিক ধরণটিই বাংলা ফিল্মের গ্রাহ্য প্রবণতা হয়ে উঠল নয়ের দশক থেকে। অথবা এমনও বলা যায়, ঋতুপর্ণর এই ধরণটি তাঁর সময়ই ঠিক করে দিয়েছিল। খেয়াল করলে দেখা যাবে, সাত-আটের দশকে সারা ভারতেই ফিল্মের ভাষায় যে দায়বোধের দাপট ছিল, কখনো কখনো আদর্শের প্রতি আস্থার যে স্বাভাবিক প্রকাশ ছিল, তা নয়ের দশক থেকে কমতে শুরু করে। আর্ট আর কমার্শিয়াল ফিল্ম নামে দুটো আলাদা ঘরানার মধ্যে লড়াইটা আটের দশক পর্যন্ত বেশ শোনা যেত, নয় থেকে যা নিঃশব্দে নিরর্থক হয়ে ওঠে। মনে আছে, বসন্ত শাঠে নামে একজন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী ছিলেন আটের দশকে, যিনি এই দুটি ঘরানা নস্যাৎ করে গম্ভীরভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি শুধু বোঝেন ছবি দু’রকম হয়— ভালো ফিল্ম আর খারাপ ফিল্ম। সেই কথা শুনে আমরা কী খেপে গিয়েছিলাম ! এর বিরুদ্ধে উৎপলেন্দু চক্রবর্তী খুব ধারালো একটা লেখা লিখেছিলেন ব্যঙ্গ করে, এখনো মনে আছে। (Little Magazine)
অবশ্য শুধু বাংলা বা ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীতেই নয়ের দশক থেকে এমন সব ছবি গুরুত্ব পেতে শুরু করল যা ফিল্মের ধ্রুপদী ভাষায় আর কথা বলে না। ‘পাল্প ফিকশন’, ‘ফরেস্ট গাম্প’, ‘ইউলিসিস গেজ’ জাতীয় ছবি সর্বস্তরে সমাদর পেল, আমরা দ্বিধায় পড়লাম— আমাদের এতদিনের যে কামনা ছিল ফিল্মের কাছে, তা এইসব ছবি দিতে পারল না, কিন্তু কান, ভেনিস, বার্লিন সর্বত্র এইসব ছবির গুরুত্ব বেড়েই চলল। ঋতুপর্ণ ঘোষ এই সময়ের সৃষ্টি। সত্যজিৎ মৃণাল ঋত্বিক ঘরানার পরে বাংলা ফিল্মে তখন পরের প্রজন্মের দহন অনেকটাই ধরে এসেছে। আটের দশকে বুদ্ধ দেব বা গৌতমের ছবিতে যে রাগ ছিল, রুক্ষতা ছিল, তা তখন নেই। বরং অপর্ণার ছবি শুরু থেকেই গল্প বলার শমিত বয়নটিকে আশ্রয় করে নিয়েছে, যার ভেতরে ভেতরে একটা ঘূর্ণি বজায় থাকে সবসময়। ঋতুপর্ণ এই ঘূর্ণির চোরাস্রোতেও বিশ্বাস রাখলেন না। ফিল্মের ভাষা কিন্তু তাঁর আয়ত্তে ছিল, সেই ভাষা তিনি ব্যবহার করলেন পরিচ্ছন্ন, আর্দ্র, ইশারাময় কিছু কাহিনি লেখার কাজে। আপাতত তাঁর নয়ের দশকের কয়েকটি ছবিতে এই বুননের কৌশলটি একটু বুঝে নিতে চাইছি।
ঋতুপর্ণর প্রথম ছবি ‘হীরের আংটি’ আমি দেখিনি। এর পরের ছবিটি থেকেই তাঁর উত্থান। ‘উনিশে এপ্রিল’ কলকাতায় প্রথম দেখার পরে, যতদূর মনে পড়ছে, দিল্লি ফিল্মোৎসবেও আরেকবার দেখেছিলাম। সেরার পুরস্কার নিতে ঋতুপর্ণ সেবার দিল্লি গিয়েছিলেন। সেবার কথা হয়নি, কিন্তু ছবিটি নিয়ে পরে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। নানা কথার সঙ্গে, সহাস্যে বলেছিলেন তিনি, ছবিটির নাম ‘বসে কাঁদো’ হলেই মনে হয় ভালো হত! ছবিতে কান্নাকাটির শট একটু বেশি আছে বলে মনে হয়েছিল তাঁর নিজেরই। যদিও, নিরাসক্তির একটা ধরনও এই ছবির ভাঁজে ভাঁজে রক্ষা করতে পেরেছিলেন তিনি। ছবির শুরুতেই একটি বিহ্বল মৃতদেহ দেখা যায়, যার শরীরে ক্রমশ স্তূপ হয়ে উঠছে মালা । পর্দায় ছোটো ছোটো শটে একই সঙ্গে ফুটে ওঠে ছবির পরিচয়লিপি, শোনা যায় অন্য ঘরে চা আর খাবারের নিরুদ্বেগ ব্যঞ্জনশব্দ। দৃশ্যটি তারপর দেখাও যায়, চা তৈরি, সঙ্গে কথাবার্তা : ‘বডি কি রেখে দেওয়া হবে?”, ‘চিনির কৌটোটা দে তো’, ‘ট্রেটা দে’, সৎকারের আগে খাবার ফেলে দেবার রীতি নিয়ে : ‘সে তো রান্না, চায়ে কোনো দোষ নেই’। পাশের ঘরের মৃত্যুর সঙ্গে যেন এই ঘরের এক স্বাভাবিক কিন্তু অস্বস্তিকর সম্পর্ক রয়েছে। এই নিরাসক্ত আর একই সঙ্গে স্বাভাবিক অথচ বিচলিত প্রবণতাই ছবিটির বৈশিষ্ট্য। ছবির আগাগোড়া এই ধরনটি বজায় রয়েছে। নৃত্যশিল্পী সরোজিনী গুপ্তের স্বামী মারা গেছেন, শিল্পী তখন মাদ্রাজে। তাঁর অলংকৃত ছবিটি থেকে, তাঁর সম্পর্কে নানাজনের কথা থেকে টের পাওয়া যায় তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা, এই দুটি সম্পর্কের মধ্যে যে গোপন আর উচ্চকিত টানাপোড়েন আছে, তাও ধরা পড়ে ৷ বাবা মারা যাবার দিন, শৈশবেই, মেয়ে মিঠুর সঙ্গে তার মা’র সম্পর্কের জটিলতা চেনা হয়ে যায় একটি কথাতেই—পরিচারিকা বয়াকে বলছে সে : ‘মা ডাকলে কিন্তু তুমি যাবে না।’ মা ও মেয়ের সম্পর্কের মধ্যে এই আচ্ছন্ন ও জটিল সম্পর্কের নানা পরম্পরাই ছবিটিতে দেখানো হয়েছে। দেখানোর যে ভঙ্গিটি নিয়েছিলেন ঋতুপর্ণ, তা বিশুদ্ধ ন্যারেটিভ, তবে কখনো কখনো তা ভেঙেও দিয়েছেন তিনি। এই ভাঙন প্রথমে বোঝা যায় না, আর এই না বোঝার ফলেই চমৎকার সয়েও যায় তা। যা জানাতে চান পরিচালক, তাঁর আঁচ পেতে পেতে ছবিটি দেখা শেষ হয়ে যায়।
মিঠুর শৈশব থেকে সরাসরি তার বিমূঢ় তারুণ্যে চলে আসে ক্যামেরা। মিঠুর সঙ্গে তার প্রেমিক সুদীপের সম্পর্কের মধ্যে যে অস্বচ্ছ বিষণ্ণতা আছে, তার ছায়া মিঠুর ব্যবহারে ছড়ানো থাকে। ট্রেনে তাকে বিদায় জানাতে সুদীপ আসে না, ট্রেনের কামরায় উদ্বিগ্ন-উৎসুক তার চঞ্চল অপেক্ষার দৃশ্যটি বারবার দেখানো হয় ছবিতে। যেন এই প্রস্তুত অথচ অচরিতার্থ অপেক্ষাই তার জীবন, তার মা ‘ডান্সার’ বলে সুদীপের তাকে বিয়ে করতে না-চাওয়াটাই যেন স্বাভবিক। যদিও তার একমাত্র নির্ভরতার জায়গাটাই এর ফলে ধসে যায়। বাবার সঙ্গে তার অসমাপ্ত সম্পর্কের পরে সুদীপের সঙ্গেই ঘন হয়ে উঠেছিল তার সবকিছু, তাও হারিয়ে যাওয়ায় খুব দ্রুত আর সংগত আবেগে আত্মহননের ট্যাবলেট কিনে আনায় সে।
এই সময়ে, একমাত্র মা-ই ফেরাতে পারত তাকে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তার সঙ্গে মা’র সম্পর্কের মধ্যে কোলাহলময় আর্তি ছাড়া আর কিছুই স্পষ্টভাবে তৈরি হয়নি। মা জাতীয় সম্মান পাওয়ায় তার নিরুপায় উদাসীনতা প্রায় ঈর্ষায় অনুবাদ হয়ে যায়। দুজনের সম্পর্কে কোনো সাচ্ছল্য না থাকায় তাদের সব বিনিময় মনে মনেই নষ্ট হয়। শুধু, মা’র হাঁটুতে ব্যথার খবরে তার সচকিত দুশ্চিন্তায়, ‘তোমার গলায় পাউডার লেগে আছে মা’ বলার আন্তরিকতায়— হয়তো তা আত্মহননের আগের আবেগে— মেয়ের বিয়ের লক্ষ্যে মা’র শাড়ি কিনে রাখা অভ্যাসে : ‘মা তো আমি আফটার অল, এবং আরো অনেক ছোটো বড়ো কৌণিকে মাঝে মাঝে তারা ঘন হয়ে এলেও সম্পর্ক কিছুতেই সহজ হয় না। এই দূরত্ব ভেঙে যাবার আগে কঠিন ঝড় ওঠে। অচেনা পাতা ও ধুলোয় ভরে ওঠে মেঝে। ঘরের সবকিছুই জায়গা বদল করে। ভেঙে যায় এতদিনের কাচ, বাইরের বাল্ব নিভে যায়। দুজনে, দুজনের দিকে মোমবাতির নিজস্ব আলোয় তাকায়, কথা বলে। বাবার সম্পর্কে মিঠুর যাবতীয় ধারণাকে অন্যরকম করে দেয় মা, ‘মনেপ্রাণে শিল্পী’ তার মা-র সঙ্গে ‘মিডিওকার’ বাবার সম্পর্কের নানা স্তর, ঈষৎ ফ্ল্যাশব্যাকসহ, ধরা পড়ে। ভাঁড়ার ঘরের দরজা ভিতরের দিকে খোলার ব্যর্থ কোলাহলের পর, অল্প চেষ্টাতেই বাইরের দিকে খুলে যায়। বাবার ছবি ধরে, তারপর, মিঠুর ভেঙে-পড়া কান্নায় তাই মিশে থাকে আকাঙ্ক্ষা আর অসহায়তা, যন্ত্রণা আর আত্মসমর্পণ। তার আত্মহননের সিদ্ধান্ত নেবার সময় কলে জল পড়ার যে অনবরত শব্দ হয়ে যায় মিঠুর নিরাসক্তির সমান্তরালে, তাও আর শোনা যায় না। দুজনের সম্পর্কের এই ঘনিষ্ঠ পরিণামেই শেষ হয় ছবি। সুদীপের আবার ফোন আসে। অনিচ্ছুক আর অভিমানী মিঠুকে ফোন ধরতে রাজি করায় মা, ‘দরকার পড়লে ডাকিস’— এই আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে মা দাঁড়িয়ে থাকে। ফোন হাতে সেদিকে তাকিয়ে উচ্চারিত হবার জন্য মুখ ফেরায় মিঠু।
ছবিটি সফল হয়েছিল প্রতিটি চরিত্রের স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্যও। মিঠুর জেদি ও বিশ্বাসী বিষণ্ণতা, পাশাপাশি তার মা-র নির্মম লাবণ্য ছবির দুটি আলাদা প্রবণতার মেজাজ ঠিকঠাক ধরে দিয়েছিল। নিছক ঘটনাকেই যে কতটা তাৎপর্য দেওয়া যায়, ‘উনিশে এপ্রিল’-এর পর ঋতুপর্ণ তা আবার প্রমাণ করেছিলেন ‘দহন’-এ। দুটি ছবিতেই আর্দ্রতার পরিপাটি আয়োজন এবং ‘উনিশে এপ্রিল’- এ অন্তত শেষের দিকে পরিচালকের সংযম টোল খায়নি একথা বলাও যাবে না। তবে ‘দহন’-এ, দেখা গেল, গোটা ছবিটিকে ধরে রাখার নিরভিমান প্রকরণ প্রায় করতলগত তাঁর।
ছবির শুরুতে রমিতার নবলব্ধ শ্বশুরবাড়ির আভাস ঈষৎ ধরা পড়ে নক্সাকাটা গ্রিলের সীমায়। তারপর, রমিতার বিপণিরঞ্জিত স্বামী পলাশের কথায় বোঝা যায়, বাড়িতে বাবা-মা’র পছন্দ-অপছন্দেই তাকে সাজতে হবে। দোকানে পলাশ একটি সুখী পুতুলের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সেই বিজ্ঞাপিত বসনে তাকে সাজাবার বাসনাও টের পায়।
রমিতাই নয় শুধু, নিজের বিয়ের ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকার নেই ঝিনুকেরও। ঝিনুকের, লেখক বাবা ও দর্পণপ্রবণ মা’র প্রথম কথোপকথনেই বুঝিয়ে দেওয়া হয় ঝিনুকের, এবং সাধারণভাবে এই সময়ের সব মেয়েরই পরিবারসম্মত পটভূমি। যে তিনটি মেয়ের কথা বড়ভাবে দেখানো হয়েছে এই ছবিতে, তাদের মধ্যে মিল শুধু সজল অসহায়তায় নয়, তারা তাদের পরিবারে একইরকম উহ্য, অতিরিক্ত। ঝিনুকের প্রচার আর পরিচিতি তাকে তার বাড়িতে যেমন বরণীয়া করেছে, তেমনি, ঘটনা অন্যদিকে ঘুরে যাবার পর পরিবারের বিরক্ত উষ্মাও বিঁধেছে তাকে। বিপন্ন ‘প্রেস্টিজ’ নিয়ে ঋতুর শ্বশুরালয় আগাগোড়া বিধ্বস্ত করেছে রমিতাকে, এবং শেষ পর্যন্ত বাধ্য করেছে তাকে নিজের প্রচারিত অপমান আরো বেশি অপমানের সঙ্গে আড়াল করতে। ‘শ্বশুরবাড়ি বলে’ যে একটা ব্যাপার আছে, আর মেয়েদের এই সর্বস্ব আশ্রয় তুচ্ছ কারণে নষ্ট না করার তাগিদেই যে রমিতাকে দ্বিতীয়বার অপমানিত হতে প্ররোচনা দিয়েছেন তার বাবা-মাও, একথা তো রমিতার বাবা নিজেই বিমর্ষ স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতে জানিয়েছেন ঝিনুককে। রমিতার লাঞ্ছনার গোটা প্রসঙ্গ টিকে তিনি যে-সারল্যে ‘তুচ্ছ’ উচ্চারণ করেন, তাতে তাঁর এই সচেতন ক্ষমাপ্রার্থীর ভূমিকাটি নিঃশেষে তুচ্ছ হয়ে যায়।
আর একটি মেয়ে তৃণা। ছবিতে অমনস্ক মনোরঞ্জনের টান (নাকি, দায় ? ) ঋতুপর্ণ এড়াতে পারতেন না মাঝে মাঝে, তাই তৃণার মা’কে অমন সারাক্ষণ অস্বাভাবিকভাবে রগড় করে যেতে হয়, কিন্তু মেয়ের প্রত্যাখ্যানকে তাঁর উড়িয়ে দেবার চলনটিই আসলে দেখানোর ছিল। বরং তৃণাকে তার বাবার বোঝানোর ছন্দটি অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকের সঙ্গে ধরেন ঋতুপর্ণ। বাবা বোঝান, তৃণার সঙ্গে পাত্রের ঘনিষ্ঠতা এতটাই বিদিত যে এই বিয়ে ভেঙে গেলে মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়া দুরূহ। অবশ্য, কন্যাদায়ের আগামী চিন্তায় বিচলিত পিতা এ আশ্বাসও দেন যে, অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি চাইবেন না একজন ‘ক্রিমিনাল’কে তার মেয়ে বিয়ে করুক। তবে, তৃণাকে নয় শুধু, নিজেকেও তিনি এই বলে নিশ্চিন্ত করেন যে, তাঁর মেয়ের জন্য নির্ধারিত পাত্রটিকে নির্দোষ প্রমাণ করার চক্র পুরোপুরি দুর্ভেদ্য।
শুধু এখানে নয়, গোটা ছবিতেই সংলাপের পুরো দাম চুকিয়ে দিতে চেয়েছেন পরিচালক। গতবয়সিনীর যে ভূমিকা সুচিত্রা মিত্র’র, তার তো কথাই সব। প্রজন্মের আর একটা স্তর আনার অঙ্কেই এই চরিত্র, কিন্তু তার সব সামর্থ্যই তো বোঝাতে হবে কথায়। দুই প্রজন্মের অন্তর্সম্পর্কটুকু তাঁর ভূমিকায় ছোঁয়া গেছে, তবে এ-ছবির অনেক চরিত্রের মতই তিনিও পুরোপুরি একমাত্রিক, একটু বেশিই তিনি, কারণ তাঁকে আবার একটা আদর্শের বয়স্ক চাদর গায়ে জড়িয়ে রাখতে হয়েছে সারাক্ষণ। ঝিনুক বা এক সৎ ট্যাক্সি ড্রাইভারের ভূমিকার স্বাভাবিকতা বোঝানোর চেষ্টায় তাঁকে আরো অস্বাভাবিক মনে হয়েছে।
অথচ, অভিনয়ে আপ্রাণ আড়ষ্টতা থাকলেও পলাশ এ-ছবির সবচেয়ে স্বাভাবিক দুটি চরিত্রের একটি। একই সঙ্গে দুর্বল অথচ উগ্র, নির্বোধ আর উত্তেজিত পলাশ, অপমানের জবাব দেবার বদলে লুকিয়ে রাখলেই যার প্রেস্টিজ অক্ষত থাকে, দোকানের মতোই একটি নির্বাক পুতুল যার শয্যাগৃহেও লক্ষণীয়, স্ত্রীর বিপন্ন ও বিপর্যস্ত কান্নার সামনে যে অশ্লীল নিরাসক্তির ধোঁয়া ছড়িয়ে সিগারেট খায় ৷
শুধু পলাশ কেন, ঝিনুকের বিদেশপ্রবণ বন্ধু তুণীরও, বিধ্বস্ত সঙ্গিনীকে আরও অস্পষ্ট অন্ধকারে রেখে এসে, নিরুপদ্রব সিগারেট জ্বালে। জি এই অনুদার আর অন্যমনস্ক প্রবণতা এ-ছবির নানা চরিত্রের, ঘটনারও। রমিতার লাঞ্ছনার সময় পলাশের সচকিত হবার মুহূর্তে একটি নির্মম ট্রাম তাদের মধ্যে আড়াল তুলে চলে যায়, আদালতে নিরুপায় রমিতার নাম ও পরিচয় যান্ত্রিক উচ্চারণ পায় টাইপরাইটারের নিরাবেগ প্রকরণে।
এই নির্লিপ্ত চলাচলের মাঝখানে দুটি বিপন্ন চরিত্র, রমিতা আর ঝিনুক । রমিতার স্বভাবে যে রম্য নম্রতা, ছবির শুরুতে পলাশের সঙ্গে চকিত কথায় যা বোঝা গেছে, তা বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে ছবিতে। অসংস্কৃত, ভীরু, ব্যক্তিত্বহীন মানুষ ও পরিবেশের নোংরা দাগ লেগেছে তার জীবনে। পলাশ আর রমিতাই এ-ছবির সবচেয়ে গ্রাহ্য চরিত্র। তবে অভিনয়ের শোচনীয় দারিদ্র্য পলাশকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিলেও রমিতা আগাগোড়া নিঁখুত, অক্ষুণ্ণ।
কিন্তু নিপাট গল্প বলার তো অনেক ঝুঁকি থাকে, কখন যে কী হেলে পড়বে কোথায়, ধরা যাবে না। ছবিতে তাই প্রতিবাদ করা ছাড়া ঝিনুকের আর কোনো ভূমিকা নেই, তৃণার মা সবসময়ই ওই রকম, ঝিনুকের ঠাম্মির ঘাড় ঘোরাতে অতক্ষণ লেগে যায়, ঝিনুককে বই দেবার সময় তার প্রগলভ ভাইয়ের চোখ মন্থর হয়ে ওঠে, পুজোর প্রসাদ নেবার সময় ঝিনুকের কপালে হাত ছোঁয়ানো জরুরি মনে হয়… এইরকম সব আর কি! হয়তো, এই ধরনের ছবিতে এইসব অগোচর অসতর্কতা না মাপাই বিধেয়। নব্বই-এর দশকে আরো তিনটি ছবি করেছিলেন ঋতুপর্ণ।
‘বাড়িওয়ালি’, ‘অসুখ’ এবং ‘উৎসব’। প্রথম দুটি ছবির তুলনায় ‘উৎসব’ অনেক বেশি সংহত। ‘বাড়িওয়ালি’ ছবিতে মনে হয় সম্পর্কের নানা স্তর দেখানোর একটা অস্পষ্ট তাগিদ ছিল পরিচালকের। কিন্তু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দৃশ্যের সুষমা ছাড়া এই ছবি থেকে পাওয়ার খুব কিছু একটা থাকে না । বনলতার ‘চোখের বালি’ পড়ার সময় বাসন্তী রঙের শাড়ি যেভাবে মেলা থাকে, তা আলাদাভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। জানলা দিয়ে বনলতার চলে যাওয়া গাড়ির দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকা বা তার স্বপ্নে সময়ের নানা স্তর একাকার হয়ে যাওয়ার দৃশ্যগুলি ঋতুপর্ণর জোর চিনিয়ে দিলেও ‘বাড়িওয়ালি’ তাঁর তৈরি ছবির তালিকায় একটি নিঃশব্দ সংযোজন বলেই মনে হয় আমার।
‘অসুখ’ও, বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মুহূর্তের উত্তেজনা ছাড়া এমন কিছুই দিতে পারে না, যা ঋতুপর্ণকে নতুন করে চেনাতে পারে। দেবশ্রীর রুক্ষতার মধ্যে যে সাবলীলতা আছে, ‘উনিশে এপ্রিল’-এর পরে এই ছবিতেও তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পরিচালক, কিন্তু গন্তব্য পুরোপুরি ঠিক না থাকার ফলে সেই চেষ্টা বারবার হোঁচট খেয়েছে। অনিরুদ্ধকে গোটা ছবিতে কেন অত কাতর করে রাখা হয়, বোঝা যায় না। তবে এটা বোঝা যায় যে, যুবক চরিত্রদের মুখে সারাক্ষণ সিগারেট গুঁজে দিয়ে তাদের সপ্রতিভতা বোঝানো একটা প্রিয় অভ্যেস ছিল ঋতুপর্ণর। আরো অনেক ছবির সঙ্গে ‘অসুখ’-এও এটা ঘটেছে। ছবিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে আসা আর একটা সচেতন প্রবণতা ছিল তাঁর। কখনো কখনো সেটা খারাপ লাগেনি, বিশেষ করে ‘বাড়িওয়ালি’তে ‘তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে’ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় নিরাসক্ত লাবণ্যের সঙ্গে যেভাবে গেয়ে যান, গোটা ছবিটির স্বরলিপি সেই ধরনে ধরা পড়ে। আর রবীন্দ্রসংগীতের আগ্রাসী আবেদনের বিপদ ঋতুপর্ণ বুঝতেন, তাই ছবির ভাষাকে ছাপিয়ে যাতে না যায় গান, সেটা খেয়াল রাখতেন। শরীরের স্বাভাবিক অসুখের পাশাপাশি মনের অসুস্থতার নানা পরত ‘অসুখ’-এ খুলে দেখাতে চেয়েছিলেন পরিচালক, এটা ছবিটি দেখে টের পাওয়া যায়। কবিতার উচ্চারণে ছবির নানা মুহূর্তকে ধরিয়ে দেবার প্রবণতা আরও অনেকের মতো ঋতুপর্ণরও ছিল, এই ছবিতে তার প্রয়োগ স্বাদু মনে হলেও অবধারিত ছিল কিনা, সে-প্রশ্ন ওঠা অবান্তর নয়৷
‘উৎসব’ তুলনায় অনেক পরিপাটি ছবি। অনেক নির্মেদ। সত্যজিৎ-এর ‘শাখাপ্রশাখা’র ধরন আছে এই ছবিতে, আর অপর্ণা সেনের ভঙ্গিটি তিনি বলেকয়েই মেনে নিয়েছেন। তৎপর সম্পাদনার গুণে ছবিটি ঝরঝরে হয়ে উঠতে পেরেছে। সম্পর্কের চোরা চলাচলগুলির দিকে নজর রাখতে পছন্দ করতেন ঋতুপর্ণ, এই ছবিতে সেই প্রবণতা বিছিয়ে ব্যবহার করেছেন তিনি। মমতাশঙ্কর আর দীপঙ্কর দে’র সম্পর্কের বুননে যে রহস্যের অসহায়তা, তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারা কম সামর্থ্যের কথা নয়। ছবির শেষে সব সম্পর্কই সমে ফেরে, শুধু এইটি ছাড়া। এমনকি বিকল হয়ে পড়ে থাকা টেলিফোনটিও ঠিক হয়ে যায়। এমন সব মেলানোর ছকে টোল দিয়ে ওই সম্পর্কটি ছবিটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই ছবিতেও রবীন্দ্রনাথের ‘অমল ধবল পালে লেগেছে…’ গানটি মোক্ষমভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন ঋতুপর্ণ। সিনেমার ভাষা কতটা করতলগত ছিল তাঁর, সেটা এই ছবিরও বেশ কয়েকটি মুহূর্ত দেখে বোঝা যায়। অরুণ চলে যাবার পর কেয়া তাকিয়ে থাকে যে জানলা দিয়ে, তার একটি বন্ধ পাল্লার স্তব্ধতা গোটা দৃশ্যটির বেদনাকে ধারণ করে থাকে।
সম্পর্কের অন্তঃসঞ্চারে সমাজ আর সময়ের নানা চলাচল ছবিতে ধরে দিতে চেয়েছিলেন ঋতুপর্ণ। নব্বই নয় শুধু, পরের পর্বের ছবিগুলিতেও।
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।