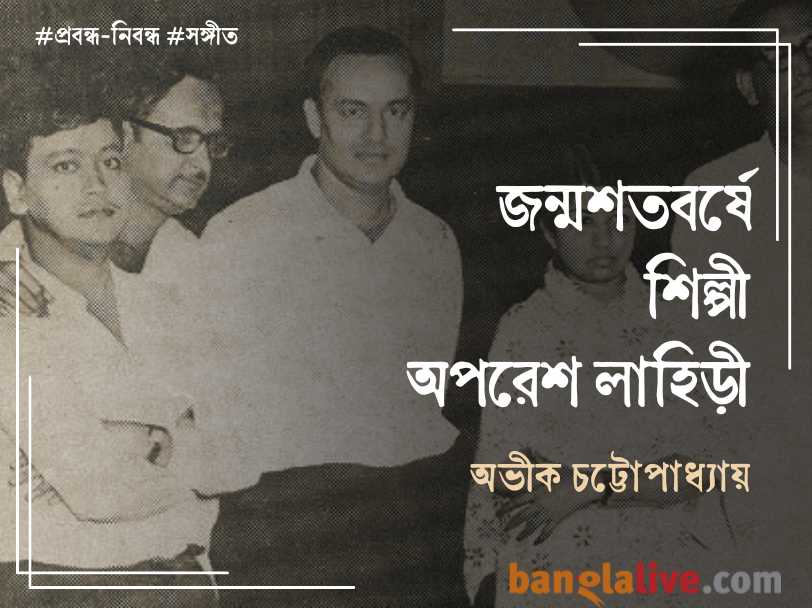বাংলা গান, নানা পথ পেরিয়ে, ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছে জন্ম দিল “আধুনিক বাংলা গান”-এর। শুরুতে একে ‘কাব্যগীতি’-ও বলা হত। এতদিন গান পরিবেশনে ছিল অতিরিক্ত সুরের কায়দা ও কালোয়াতি নির্ভরতা। এবার কিছু সংগীতকার নজর দিলেন, সহজ সাবলীল মেলডি নির্ভর বাংলা গান নির্মাণের ব্যাপারে। রবীন্দ্রনাথের ভাবধর্মী সংগীত-মতাদর্শের অনুসারী হিসেবেই এই সংগীতধারার উন্মেষ ঘটল আধুনিক বাংলা গানে। কাব্যধর্মী বাণী, মনকাড়া সুর ও অন্তর-ছোঁয়া পরিবেশনে আধুনিক গান ছড়িয়ে পড়তে লাগল বাংলার আকাশে বাতাসে। অচিরেই যা আপামর বাঙালির হৃদয় জয় করে নিল। কণ্ঠশিল্পীদের অধিকাংশই শাস্ত্রীয় সংগীত-শিক্ষার শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেও গান পরিবেশনে নিয়ে এলেন ভাবের প্রাধান্য। এই ধারারই অন্যতম শিল্পী অপরেশ লাহিড়ী(Aparesh Lahiri)। যিনি আধুনিক বাংলা গানের দুনিয়ায় পা রাখলেন ১৯৪০-এর দশকে। এ বছর এই শিল্পীর জন্মশতবর্ষ। স্ত্রী ও পুত্র হলেন যথাক্রমে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী বাঁশরী লাহিড়ী ও ভারতবিখ্যাত সংগীত পরিচালক বাপী লাহিড়ী। এক কথায় সুরময় পরিবার।
১৯২৪ সালের ৮ আগস্ট বাংলাদেশের রংপুর জেলার ডোমার গ্রামে জন্ম অপরেশ লাহিড়ীর। বাবা সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী ও মা ভবতারিণী দেবী ছিলেন সংগীতে অনুরক্ত। ফলে, তিন ছেলের মধ্যেও তা বর্তাল। ছোটো ছেলে অপরেশের প্রথম গান শেখা তাঁর দুই দাদা ভবেশ ও অমরেশের কাছে।
১৯২৪ সালের ৮ আগস্ট বাংলাদেশের রংপুর জেলার ডোমার গ্রামে জন্ম অপরেশ লাহিড়ীর। বাবা সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী ও মা ভবতারিণী দেবী ছিলেন সংগীতে অনুরক্ত। ফলে, তিন ছেলের মধ্যেও তা বর্তাল। ছোটো ছেলে অপরেশের প্রথম গান শেখা তাঁর দুই দাদা ভবেশ ও অমরেশের কাছে। কিছুদিন ওপার বাংলায় কাটিয়ে চলে আসতে হয় এপারে। এখানে সম্ভবত বাঁকুড়ায় এসে, সেখানকার কোনও স্কুলে ভর্তি হন অপরেশ। কারণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার তিনি বলেছিলেন, “বাঁকুড়াতে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমি হেমন্তদার গানের ভক্ত ছিলাম। রেকর্ড কেনার খুব বাতিক ছিল আমার। আমি প্রথম যে রেকর্ডটা কিনি সেটা হল, ‘জানিতে যদি গো তুমি/পাষাণে কি ব্যথা আছে…’।” প্রসঙ্গত এটাই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম রেকর্ড, যার রেকর্ডিং ১৯৩৭ সালে হলেও রেকর্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮-এ। অপরেশের বয়স তখন ১৪।
সেকালের ভোট ও দাদাঠাকুরের রঙ্গব্যঙ্গ : অভীক চট্টোপাধ্যায়
১৯৪১ সালে রেডিয়োয় গাইলেন অপরেশ লাহিড়ী। সেই ছিল তাঁর প্রথম সাংগীতিক আত্মপ্রকাশ। আর ঐ বছরই “আহুতি” ছবিতে সমবেত সংগীতে অংশ নিয়ে পা রাখলেন প্লেব্যাক ও রেকর্ডের দুনিয়ায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন হরিপ্রসন্ন দাস। এঁরই সাহচর্যে তখন অপরেশ।
শুরুতে কে. এল. সায়গলের প্রভাব পুরোপুরি ছিল অপরেশের গায়নভঙ্গিতে। যা স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৯৪২ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত একককণ্ঠে গাওয়া তাঁর প্রথম রেকর্ডের দুটি গানে― “গহন তিমিরতলে…”(কথা― দেবেশ বাগচী, সুর― বীরেন ভট্টাচার্য) এবং “মধুরাতি ফিরে গেল…”(কথা― প্রফুল্ল মিত্র, সুর― অপরেশ লাহিড়ী)। এখানে লক্ষ্যণীয়, শুরু থেকেই গায়কের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে সুরকার অপরেশকে। দ্বিতীয় রেকর্ড বেরোল রিগ্যাল কোম্পানি থেকে ১৯৪৩-এ। ১৯৪৬ সালে পায়োনীয়র কোম্পানির রেকর্ডে ব্যোমকেশ লাহিড়ীর কথায় গাওয়া “তুমি নাই চাঁদও নাই…” অপরেশকে প্রথম জনপ্রিয়তার স্বাদ দিল। গানটি এতটাই ভাল হয়েছিল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চিঠি লিখে প্রশংসা করেছিলেন। এর পর থেকে নিয়মিত রেকর্ড বেরোনোর শুরু।

বীরেন ভট্টাচার্য, হরিপ্রসন্ন দাস, ঊষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী, সুধীরলাল চক্রবর্তী প্রমুখ সংগীতগুণীর কাছে সংগীতশিক্ষা নিয়েছিলেন অপরেশ লাহিড়ী। ১৯৪৮ সালে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় ও সুধীরলাল চক্রবর্তীর সুরে দুটি গান, শিল্পী হিসেবে তাঁকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিল― “ভালবাসা যদি অপরাধ হয়/আমি অপরাধী তবে…” এবং “সেই মালা দেয়া নেয়া…”। প্রথম গানটি নিয়ে একটা ঘটনা আছে। এর কয়েক বছর আগে, পরাধীনতার সময়ে, দেশপ্রিয় পার্কে চলা একটি জনসভায় অপরেশ শোনেন এক দেশনেতা বলছেন, “দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি অপরাধী”। কথাটা মনে দারুণ দাগ কেটেছিল তাঁর। রেকর্ড করার সময় ওই কথাগুলো মাথায় রেখে গান লেখালেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে দিয়ে। সুপার হিট হল “ভালবাসা যদি অপরাধ হয়…”। লোকের মুখে মুখে ফিরল।
হেমন্ত-র স্বর্ণকণ্ঠ : কিছু ভাবনা : অভীক চট্টোপাধ্যায়
১৯৫০-এ অরূপ ভট্টাচার্যের কথায়, দুর্গা সেনের সুরে “এ জীবনে ভালবেসে…”, ১৯৫২ সালে “চাঁপা কেঁদে বলে…”(কথা― সুবোধ পুরকায়স্থ, সুর― শৈলেশ দত্তগুপ্ত) ইত্যাদি গানে রোমান্টিকতায় ভরা মেলডিপূর্ণ সংগীত পরিবেশনে নিজেকে মেলে ধরলেন অপরেশ লাহিড়ী। সায়গলের প্রভাব থেকে বেরিয়ে তিনি ততদিনে এনে ফেলেছেন নিজস্ব গায়কীর ধাঁচ। কণ্ঠে মিষ্টতা ছিল। সঙ্গে নাটকীয়তার প্রাধান্য। ফলে, গানগুলি অর্থবহ হয়ে উঠত শ্রোতাদের কাছে। এর পর ক্রমশ প্রেম-বিষয়ক ধরন বদলে, অপরেশের গান থেকে ফুটে উঠতে লাগলো চারপাশের সামাজিক অবস্থা নিয়ে তৈরি এক বিশেষ ধরনের সংগীত-চিত্র। মূলত এই ধরনের গানগুলিই আজও কিছু মানুষের মনে গায়ক অপরেশ লাহিড়ীকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় শুধুমাত্র বাপী লাহিড়ীর বাবা হিসেবে নয়।
অপরেশের স্ত্রী বাঁশরী লাহিড়ীও ছিলেন বাংলা গানের এক বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁর জন্ম ১৯৩২ সালে বর্তমান বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ শহরে। বাবা ডা. অন্নদা গোবিন্দ চক্রবর্তীর কাছে প্রথম গান শেখা। ১৯৪৭ সালে মেগাফোন কোম্পানি থেকে বেরোয় তাঁর প্রথম রেকর্ড।
অপরেশের স্ত্রী বাঁশরী লাহিড়ীও ছিলেন বাংলা গানের এক বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁর জন্ম ১৯৩২ সালে বর্তমান বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ শহরে। বাবা ডা. অন্নদা গোবিন্দ চক্রবর্তীর কাছে প্রথম গান শেখা। ১৯৪৭ সালে মেগাফোন কোম্পানি থেকে বেরোয় তাঁর প্রথম রেকর্ড। গানদুটির গীতিকার ও সুরকার ছিলেন যথাক্রমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও অপরেশ লাহিড়ী। এরপর, ধীরে ধীরে গানের জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে লাগলেন বাঁশরী। যে ব্যাপারে মেগাফোন কোম্পানি ও অপরেশ লাহিড়ীর সক্রিয় ও আন্তরিক ভূমিকা ছিল। মেগাফোনের মালিক মেগা ঘোষের খুবই স্নেহধন্য ছিলেন অপরেশ-বাঁশরী। এই রেকর্ড কোম্পানিতেই তাঁদের পরিচয়। সেখান থেকে ঘনিষ্ঠতার ধাপ পেরিয়ে অবশেষে পরিণয়। শিল্পী-দম্পতির বিয়ে নিজে উদ্যোগী হয়ে দিয়েছিলেন মেগা ঘোষ। অপরেশ তো বটেই, বাঁশরীরও অনেক জনপ্রিয় গানের রেকর্ড আছে মেগাফোন থেকে। বেসিক গানের পাশাপাশি বাংলা ও হিন্দিতে বেশকিছু প্লেব্যাকও করেছেন বাঁশরী লাহিড়ী। অপরেশ লাহিড়ী ছাড়াও গেয়েছেন অন্যান্য সুরকারের সুরে, যার মধ্যে অন্যতম তাঁর পুত্র বাপী। পরের দিকে বাঁশরী লাহিড়ী রাগপ্রধান ও শাস্ত্রীয় সংগীতের দিকে চলে যান।
চেনা মহানায়কের অন্তরালে অন্য উত্তম : অভীক চট্টোপাধ্যায়
রেডিয়োর সঙ্গে অপরেশ লাহিড়ীর সংযোগ ১৯৪১-এ শুরু হয়, সক্রিয়ভাবে বজায় ছিল ১৯৭২ অবধি। এই দীর্ঘ সময় জুড়ে গান গাওয়ার পাশাপাশি সুরকার হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন বেতারে। চিরবিখ্যাত “মহিষাসুরমর্দিনী”-তে বেশ কয়েক বছর অংশ নিয়েছেন অপরেশ। সেখানে শুধু গানই করেননি, সংগীত আয়োজনে পঙ্কজ মল্লিককে সহায়তাও করেছেন। বাঁশরী লাহিড়ীও বেশ কয়েকবার গেয়েছেন এই সংগীত-আলেখ্যে। ১৯৭২-এ পুত্র বাপীকে নিয়ে মুম্বাই পাড়ি দেওয়ার পর থেকে অপরেশের শিল্পীজীবনে ছেদ পড়ে।
১৯৫০ দশকের সময় থেকে অপরেশ লাহিড়ীর গানগুলির ধরন অন্যদিকে বাঁক নিতে থাকে। হয়ে ওঠে অনেক বেশি সমাজমুখী। এর কারণ, অপরেশের রাজনৈতিক বোধ। তিনি কলকাতায় অধিকাংশ সময় থেকেছেন বাঁশদ্রোণী অঞ্চলে। সেখানে “ক্রান্তি শিল্পী সংঘ” তৈরিতে অপরেশের উদ্যোগী ভূমিকা ছিল। সংগঠনটি ছিল “ভারতীয় গণনাট্য সংঘ”-র সমান্তরাল একটি সংস্থা। এখানেই অপরেশ লাহিড়ী নিয়ে আসেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁকে সংগঠনের উপযোগী গান লিখতে বলেন। শিবদাস তখন অল্পবিস্তর কবিতা লেখেন। গান লেখার ধারেকাছেও নেই। কিন্তু অপরেশ নাছোড়। অবশেষে গান লিখলেন শিবদাস। জন্ম হল আধুনিক বাংলা গানের অন্যতম এক বিশিষ্ট গীতিকারের। যার পিছনে অপরেশ লাহিড়ীর ষোলো আনা অবদান। যে সমাজচেতনামূলক নতুন ধরনের আঙ্গিকে তৈরি আধুনিক গানগুলি অপরেশ লাহিড়ীকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গেল, তার প্রায় সবগুলিই শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা― “খবর এসেছে টক্কা টরে…”, “আমি জন্মে শুধু কান্না নিলাম…”, “এই দুনিয়া চিড়িয়াখানা…”, “আমি যদি কালো হলাম…” এবং “লাইন লাগাও…”। প্রত্যেকটা গানের সুরকার ভি. বালসারা। বেশিরভাগ গানের বাণীতে শ্লেষের যে ছোঁয়া রয়েছে, গায়কীতেও একেবারে নিজস্ব ঢঙে তা এনেছেন অপরেশ। আর বালসারাজির সুর ও মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টও সেই পথে হেঁটেছে। ফলে, এইসব গান বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা পেল। তখনকার জলসায় হরদম দেখা যেত অপরেশ লাহিড়ীকে এবং সেখানে গাইতেই হত এসব গান। “লাইন লাগাও/লাইন লাগাও…” গানে ১৯৫০/৬০ দশকের কলকাতার বিপর্যস্ত জীবনের ছবি ফুটে উঠত। শ্রোতারা যা গ্রহণ করেছিলেন মনেপ্রাণে। এছাড়াও, তাঁর গাওয়া “এই পৃথিবী ভরা সাহেব বিবি…”, “আশ্চর্যপ্রদীপটা জ্বালো আলাদিন…”(কথা― পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর― অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়), “জলের জাহাজ…”, “থাক থাক পিছু ডাক…”(কথা―পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর― ভূপেন হাজারিকা), “ঐ দোল দুল দোলে…” ও “এক বৈশাখে ঐ শাখে…”(কথা― গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর― শ্যামল মিত্র) ইত্যাদি গানও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়। সবমিলিয়ে দেখলে বলা যায়, ১৯৫০ দশক থেকে অপরেশ লাহিড়ীর গাওয়া অধিকাংশ আধুনিক গানগুলি বাণী, সুর ও গায়নভঙ্গির দিক থেকে বেশ অভিনব ধরনের। ১৯৪০/৫০ দশকে কাহিনিভিত্তিক গানের একটা চল হয়েছিল। অনেক শিল্পী গেয়েছিলেন এই ধরনের গান। যার মধ্যে কিছু কালজয়ী হয়ে আছে। অপরেশ লাহিড়ীও ১৯৫১ সালে অরূপ ভট্টাচার্যের কথায় ও চিত্ত রায়ের সুরে রেকর্ডের দুপিঠ জুড়ে গেয়েছিলেন, “একটি কুঁড়েঘরের কাহিনী(১ম ও ২য়)”। তবে সেরকম জনপ্রিয়তা পায়নি গানটি।
শিল্পী-দম্পতির পুত্র হয়ে বাপী লাহিড়ীর মধ্যে ছিল জন্মগত সংগীতপ্রতিভা। বাচ্চা বয়স থেকে তবলা, হারমোনিয়াম বাজানোয় দারুণ দক্ষতা ছিল। গান তো গাইতে পারতেনই। যে জন্য পরে হিন্দিজগতে আলোড়ন তুললেন, বাপীর সেই সুরকার-সত্ত্বারও প্রকাশ ঘটেছিল ছোটো থেকে।
শিল্পী-দম্পতির পুত্র হয়ে বাপী লাহিড়ীর মধ্যে ছিল জন্মগত সংগীতপ্রতিভা। বাচ্চা বয়স থেকে তবলা, হারমোনিয়াম বাজানোয় দারুণ দক্ষতা ছিল। গান তো গাইতে পারতেনই। যে জন্য পরে হিন্দিজগতে আলোড়ন তুললেন, বাপীর সেই সুরকার-সত্ত্বারও প্রকাশ ঘটেছিল ছোটো থেকে। ১৯৬৪ সালে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা যে দুটো গান অপরেশ লাহিড়ীর গলায় জনপ্রিয়তা পায়, সেই “সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো এ জীবন…” এবং “ঘুড়ি লাল নীল…”-এর সুরকার ছিলেন ১২ বছরের বাপী লাহিড়ী। এ বাদেও, ১৯৭২ সালে বাপী সুরারোপিত “জনতার আদালত” ছবিতে তাঁর বাবা-মা, দুজনেই গেয়েছিলেন।
এবার আসা যাক সিনেমাজগতে। এখানেও গায়ক ও সংগীত পরিচালক অপরেশ লাহিড়ীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। বাংলা গানে তাঁর আসাই তো ১৯৪১ সালে “আহুতি” ছবিতে সমবেতভাবে নেপথ্যকণ্ঠে গলা দিয়ে। এর পর, “শ্রীতুলসীদাস”(১৯৫০), “ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”(১৯৫৩), “দানের মর্যাদা”(১৯৫৬), “দিল্লী থেকে কলকাতা”(১৯৬১), “জনতার আদালত”(১৯৭২) ইত্যাদি ছবিতে গেয়েছেন অপরেশ লাহিড়ী। শেষের দুটি ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে বাঁশরী লাহিড়ী ও বাপী লাহিড়ী। এছাড়াও, নিজের সুরারোপিত ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটিতেও তিনি প্লেব্যাক করেছেন। মোট পাঁচটি বাংলা ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেন অপরেশ লাহিড়ী― ১৯৫২ সালে “নতুন পাঠশালা”(বীরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যৌথ সংগীত পরিচালনা), “ও আমার দেশের মাটি”(১৯৫৮), “অজানা কাহিনী”(১৯৬০), “আজ কাল পরশু”(১৯৬১) ও “সুভাষচন্দ্র”(১৯৬৬)। বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি জাতীয় লোকসংগীতে অপরেশ লাহিড়ীর যথেষ্ট দখল ছিল, যার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত তিনি রেখেছিলেন “ও আমার দেশের মাটি” ছবির সংগীত পরিচালনায়। রত্নখচিত কণ্ঠশিল্পী সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন অপরেশ এই ছবিতে― শচীন দেব বর্মন, আব্বাসউদ্দিন, এ.টি.কানন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, ড.গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, বাঁশরী লাহিড়ী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অমর পাল, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সঙ্গে নিজে তো ছিলেনই। আর ছিলেন লতা মঙ্গেশকর। তাঁকে দিয়ে প্রায় কোনও মিউজিক ছাড়া “ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে…”-র মতো একটি প্রচলিত পল্লীগীতি গাইয়ে যেন নতুন এক লতাকে সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন সংগীত পরিচালক। এছাড়া, এ ছবিতে মান্না দে-র গাওয়া “এল যে চৈতন্যের গাড়ি…” গানটিও অসাধারণ।
প্লেব্যাক থেকে অভিনয়: বহুমুখী অনুভার দীপ্তি : অভীক চট্টোপাধ্যায়
এর পর, ‘সুভাষচন্দ্র’ ছবির সংগীত পরিচালনায় আবারও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন অপরেশ লাহিড়ী। শুধুমাত্র একটি দোতারা সহযোগে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে গাওয়ালেন চিরস্মরণীয়―”একবার বিদায় দে মা…”। এছাড়া আরও কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী গেয়েছেন এই ছবিতে। ব্যবহার করা হয়েছে কিছু দেশাত্মবোধক গান, যার প্রত্যেকটাই সুপ্রযুক্ত। অপরেশ নিজে গাইলেন সুভাষচন্দ্রের অন্যতম প্রিয় গান― “নাহি জ্যোতি নাহি সূর্য…” (স্বামী বিবেকানন্দের লেখা ধ্রুপদাঙ্গের একটি কালজয়ী গান)। ছবির একটি অসাধারণ দৃশ্যে মান্না দে-র গাওয়া রজনীকান্তের “তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী…” গানটি ভোলা যায় না। গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেইসব গানকেই বাছা হয়েছে, যার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ ছিল। মনগড়া নয়। অর্থাৎ, এগুলোর কোনওটা গেয়েছিলেন বা শুনেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। প্রসঙ্গত, ছবিটি হিন্দিতেও হয়েছিল। তবে নতুনভাবে তৈরি করে, ডাবিং নয়। এরও সংগীত পরিচালনা করেছিলেন অপরেশ লাহিড়ী। নেপথ্যশিল্পী ছিলেন মহম্মদ রফি, মুকেশ, হেমন্তকুমার প্রমুখ। হিন্দি ছবিটির নির্মাণ ১৯৬৮/৬৯ সালে শেষ হয়ে গেলেও সেন্সরশিপ্-এর ছাড়পত্র পেতে অপেক্ষা করতে হয় প্রায় ৯ বছর। অবশেষে ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৮ সালে।

অপরেশ লাহিড়ী হিন্দি গানও গেয়েছেন বেশকিছু। বিমল রায় পরিচালিত নিউ থিয়েটার্স-এর “পহেলা আদমি”(১৯৫০) ছবিতে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে অপরেশ গেয়েছিলেন, “হাম চলে নয়া দুনিয়া রাখনে…” এবং “তারোঁ কি রোশনি…”(গীতিকার― প্রকাশ)। ১৯৫৪ সালে “বাদশা” ছবিতে হসরত জয়পুরীর লেখা ও শঙ্কর জয়কিষেণের সুরে অপরেশ লাহিড়ীর গাওয়া “জাগে মেরা দিল/শোয়ে জমানা…” অসম্ভব জনপ্রিয় হয়। এ বাদেও আরও কিছু হিন্দি ছবিতে তাঁর গান আছে। শুধু ছবিতেই নয়, ১৯৫০/৬০ দশকে কয়েকটি নন-ফিল্ম হিন্দি গানের রেকর্ডও আছে অপরেশ লাহিড়ীর। তার মধ্যে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে “ইয়ে কৌন আ রহা হ্যায়…”, নিজের সুরে “ইস্ চাঁদনি…”, গোবিন্দ মুনিসের কথায় ও নিজের সুরে “দিয়ে দিয়ে যা…”, “তেরা ভি সবেরা…” ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
তখনকার দিনের বাংলা গানের শিল্পীদের মধ্যে ভার্সন গান রেকর্ড করার একটা চল ছিল। তার মানে হল, সেই সময়ের হিন্দি ছবিতে থাকা বিভিন্ন শিল্পীর জনপ্রিয় গানগুলি নতুন করে রেকর্ডে গাওয়া। অপরেশ লাহিড়ীও “হাম্ মাতওয়ালে নওজোয়ান” ও “মডার্ন গার্ল” ছবিদুটিতে মুকেশের গাওয়া যথাক্রমে “সাথী হ্যায় আলবেলা…” ও “কভি ইনকার করতে হো…” বা “পাতালপুরী” ছবির রফির গাওয়া “অ্যায় জানে যাঁহা…” ও “আল্লা হ্যায় নিগেবান…” ইত্যাদি কিছু গান ভার্সন গান হিসেবে রেকর্ডে গেয়েছিলেন।
শিল্পী অপরেশ লাহিড়ীর কর্মকাণ্ড কতটা বৈচিত্র্যে ভরা ছিল, এতক্ষণের আলোচনায় তা কিছুটা হয়তো পরিষ্কার। এরকম একজন সংগীতব্যক্তিত্ব ১৯৭২ সালে গানের জগৎ থেকে সরে এলেন নিজের ছেলের কথা ভেবে। এই বছরই তিনি বাপীকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে মুম্বাই চলে যান।
শিল্পী অপরেশ লাহিড়ীর কর্মকাণ্ড কতটা বৈচিত্র্যে ভরা ছিল, এতক্ষণের আলোচনায় তা কিছুটা হয়তো পরিষ্কার। এরকম একজন সংগীতব্যক্তিত্ব ১৯৭২ সালে গানের জগৎ থেকে সরে এলেন নিজের ছেলের কথা ভেবে। এই বছরই তিনি বাপীকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে মুম্বাই চলে যান। তখন থেকে শুরু হয় তাঁর নিজের পুত্রকে মুম্বাইয়ের সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। সবসময় ছিলেন ছেলের পাশে এবং শেষে সাফল্যও যে এসেছিল দারুণভাবে, তা তো বলাই বাহুল্য। অবশ্যই এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল বাপী লাহিড়ীর সাংগীতিক প্রতিভা। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর পিতার ভূমিকাকেও নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে, যিনি তাঁর নিজের শিল্পীসত্ত্বাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বাপী লাহিড়ীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সংগীতদুনিয়ায়।
অল্প কয়েক বছরের সংগীতজীবন অপরেশ লাহিড়ীর। তার মধ্যেই গায়ক ও সংগীত পরিচালক হিসেবে তিনি তাঁর বিশিষ্টতা প্রমাণ করেছেন। নানারকম গান তিনি গেয়েছেন, সুর করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ ধরনের সমাজচেতনামূলক গান ও নিজস্বতায় ভরা পল্লীসংগীতের প্রয়োগ― এই দুটি দিক থেকে বোধহয় শতবর্ষী শিল্পী অপরেশ লাহিড়ী গানের দুনিয়ায় এক পৃথক অবস্থানে থেকে যান।
তথ্যঋণ :
১) প্রসাদ পত্রিকা, সংগীত সংখ্যা
২) কথায় কথায় রাত হয়ে যায়― পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
৩) জীবনপুরের পথিক হেমন্ত( সংকলন ও সম্পাদনা : ধীরাজ সাহা)
৪) সা রে গা পত্রিকা
৫) বিভিন্ন সিনেমার বুকলেট
কৃতজ্ঞতা : সঞ্জয় সেনগুপ্ত
জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।