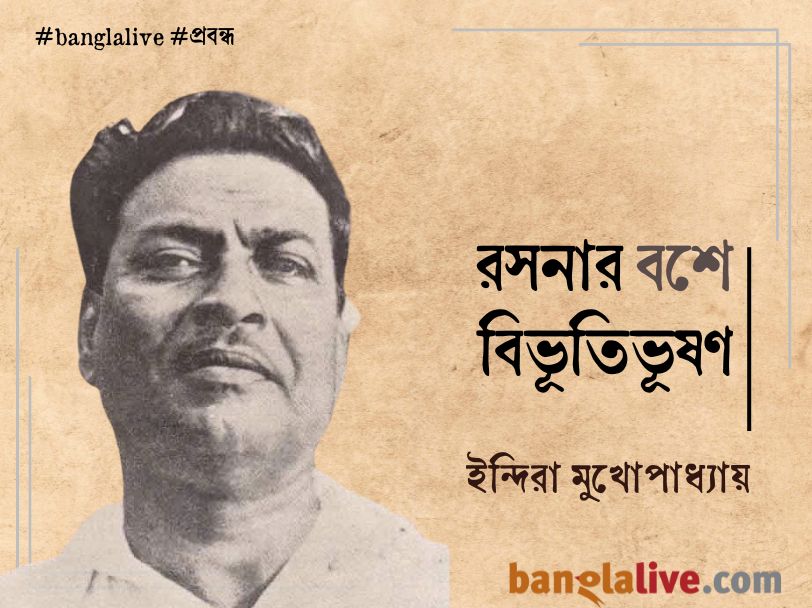হাজারি ঠাকুরের হাত ধরে যে পাইস হোটেলের সংস্কৃতি ফুটে উঠেছিল বিভূতিভূষণের “আদর্শ হিন্দু হোটেল” বিখ্যাত গল্পে তা পড়ে মনে হয় লেখক হয়তো মনেপ্রাণেই চেয়েছিলেন তেমনি এক পাইস হোটেলের মালিক হতে যেখানে মানুষ এসে দুদণ্ড জিরিয়ে নিতে নিতে আড্ডা দেবে আর খাওয়াদাওয়া করবে। কারণ হাজারি ঠাকুর শুধু একজন সামান্য পাচকই নন, রান্না তাঁর কাছে এক পূর্ণ শিল্প। সহকারী পদ্ম আর তাঁর হাতের অভিনব কেরামতিতে রান্না যেমন সুস্বাদু হয় তেমনই উঠে আসে নিপুণভাবে মফস্বলী জীবনের খুঁটিনাটি। আর তাঁর স্বপ্নের এই বাঙালি হোটেলটি তাই বুঝি আজও অক্ষত আছে। রাণাঘাট স্টেশন থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ে। বিভূতিভূষণের মনের কোণে সুপ্ত ছিল সেই স্বপ্নের হেঁশেলের কারিগর হওয়ার বাসনা। আরও কিছুদিন বাঁচলে হাজারি ঠাকুরের মতোই সুস্বাদু পদ তৈরি করে মানুষের পেট ভরানোর লক্ষ্যে তিনিও অবিচল থাকতেন। আর তখনই মনে ঢেউ তোলে সেই দ্বন্দ। তুখোড় খাইয়ে হলেই ভাল পাচক হওয়া যায় নাকি দক্ষ রাঁধিয়ে হলেই ভোজনরসিক হওয়া যায়? (Bibhutibhusan Bandyopadhyay)
সেই মেয়ে একাই মায়ের হাতে পিঠে খেত পেট ভরে। পৌষসংক্রান্তিতে অন্নপূর্ণা যখন পিঠে বানাতে বসেন তখন বাকি মেয়েদের চোখ পড়ে সেই পুঁইমাচার ওপর আর ক্ষেন্তির কথায় অন্নপূর্ণার মাতৃ হৃদয়ের হাহাকার ফুটে ওঠে। তবে সবের অনুষঙ্গে সেই পুঁইশাক।
আবার এই বিভূতিভূষণই চূড়ান্ত অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে জীবনসরণি পেরোতে গিয়ে লালন করেছিলেন দারিদ্র্যকে। আর তাই পথের পাঁচালীর সর্বজয়ার কাছে অপুর মোহনভোগের বায়না মনে পড়লে চোখ ফেটে জল আসে। ছেলের আবদারে মা বানিয়ে দেন পুলটিসের মতো গুড়ে ফোটানো সুজি। তাই ছিল ছেলের মুখে অমৃতসম।
অথবা “পুঁইমাচা” গল্পে খাইতুড়কে ক্ষেন্তির রায়েদের বাড়ির পাকা পুঁইশাক গোগ্রাসে গেলার জন্য অন্নপূর্ণার ভর্ৎসনা যেমন জুটেছিল তেমনি পরিত্যক্ত এক পুঁইডাঁটা নিজের ঘরের উঠোনের লাগোয়া জমিতে লাগিয়ে সে গাছ যখন লকলক করে মাচায় বেড়ে উঠেছিল তখন আর ক্ষেন্তি ইহলোকে নেই। সেই মেয়ে একাই মায়ের হাতে পিঠে খেত পেট ভরে। পৌষসংক্রান্তিতে অন্নপূর্ণা যখন পিঠে বানাতে বসেন তখন বাকি মেয়েদের চোখ পড়ে সেই পুঁইমাচার ওপর আর ক্ষেন্তির কথায় অন্নপূর্ণার মাতৃ হৃদয়ের হাহাকার ফুটে ওঠে। তবে সবের অনুষঙ্গে সেই পুঁইশাক।
হতদরিদ্র চাট্টুজ্যে পরিবারের সামর্থ্য ছিল না মেয়েদের ভাল খাইয়ে ভরিয়ে দেওয়ার। তার মাঝেও ক্ষেন্তির পুঁইশাক প্রীতি দেখে তার মা “মেয়েছেলের এত নোলা কিসের” বলতেও কসুর করেনি। আর সেই পুঁইশাক একদিন জিতিয়ে দিয়েছিল মৃত ক্ষেন্তিকে। একটা গোটা গল্প যেখানে খাদ্যাখাদ্যের প্রাসঙ্গিকতায় ভরপুর হয়ে ওঠে সেখানে লেখকের চিন্তায় ভাবনায় খাদ্যের যে ভূমিকা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক।
এই যে দারিদ্র্যের সঙ্গে অক্লান্ত ওঠা-বসা যে লেখকের তিনিও তো একসময় শুধু মুঠো মুঠো তেঁতুলপাতা খেয়ে পেট ভরিয়েছেন তাই বা ভুলি কেমন করে আমরা? তাঁর পুত্রবধূ শ্রীমতী মিত্রা বন্দ্যোপাধায়ের লেখাতেই পেলাম শ্বশুরমশাইয়ের স্মৃতিচারণায়।
তাঁর শ্বশুরমশাইকে নিয়ে একটা রটনা ছিল। তিনি নাকি প্রচুর খেতেন। সে কথায় খুব দুঃখ পেতেন বিভূতিবাবুর দ্বিতীয়া পত্নী কল্যাণী ওরফে রমা দেবী। তিনি বলতেন, আমি তো নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছি তাঁকে। আমি জানি তিনি কতটা খেতেন। খাদ্যরসিক ছিলেন কিন্তু খেতেন খুব কম পরিমাণে। যদিও ছোটবেলায় খিদের জ্বালাও সয়েছেন প্রচুর।
১৯১৪ সালে বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতেই নিজের চেষ্টায় কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হলেন। তখন বিভূতিভূষণের আর্থিক কষ্ট এতটাই প্রবল যে রোজ ভাত জুটত না। খুঁজে পেতে অনেক কষ্টে দু’পয়সা বের করে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের সিঁড়িতে বসে তালফুলুরি আর কলের জল খেয়ে পেট ভরাতেন।
গ্রামের মানুষদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। গ্রামে কারোর জামাই হয়তো এসে পড়েছে হঠাৎ করেই। তাঁকে কী খেতে দেবেন কল্যাণী দেবী? একবার পঙক্তি ভোজে বসে বিভূতিভূষণের পাতের সামনে থেকে মাছের বাটি তুলে নিয়ে সেই জামাইকে খেতে দিয়েছেন কল্যাণী। জামাইয়ের সামনে গ্রামের মান সম্মান রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের দুজনেরই।
এই কল্যাণীকে নিয়েই আবার ঘাটশিলায় গিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হেঁটেই চলেছেন তিনি। খিদে তেষ্টা সব ভুলে। এদিকে কল্যাণীর খিদে পেয়েছে দেখে গাছের তলায় পড়ে থাকা বুনো আমলকী খেয়েই পেট ভরাতে আদেশ দেন বিভূতভূষণ। ওদিকে ভোর গড়িয়ে সন্ধে উপস্থিত। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে রত বিভূতিভূষণের হুঁশ নেই খাওয়াদাওয়ায়।
১৯১৪ সালে বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতেই নিজের চেষ্টায় কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হলেন। তখন বিভূতিভূষণের আর্থিক কষ্ট এতটাই প্রবল যে রোজ ভাত জুটত না। খুঁজে পেতে অনেক কষ্টে দু’পয়সা বের করে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের সিঁড়িতে বসে তালফুলুরি আর কলের জল খেয়ে পেট ভরাতেন। তবুও পরজন্মে যেন দরিদ্র হয়েই জন্ম হয় এমনই ছিল তাঁর প্রার্থনা। মাঝেমধ্যে শুধু নুন-ভাত খেতেন সেইকারণেই। স্ত্রী কে বলতেন, “সবরকম অভ্যেস থাকা ভাল, বুঝলে কল্যাণী?” কল্যাণী সুস্বাদু সব পদ রান্না করে সাজিয়ে দিয়েছেন হয়তো। বিভূতিভূষণ বললেন সেসব সরিয়ে নিতে। কল্যাণী বললেন “নিজের হাতে বাজার করে এত সুন্দর মাছ আনলে আর তুমিই খাবে না?” তিনি বলতেন “আজকেই তো বেশি করে সম্বরণ করতে হবে। কোন দারিদ্রের অতল থেকে সংগ্রাম করে উঠে এসেছি সেটা যেন ভুলে না যাই কখনও”!
দুগ্ধজাত খাবার ছিল তাঁর খুব প্রিয়। কলকাতায় এলেই নানারকম সন্দেশ কিনে আনতেন। তাছাড়াও তাঁর গ্রামবাংলার প্রিয় সুখাদ্য চালভাজা, ডালভাজা, কাঁঠালবীচিভাজা এসবের জোগান দিতেন কল্যাণী। চায়ের সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা পাউরুটি, কাঁচা চিঁড়ে দিয়ে নারকোল… এসবও ছিল পছন্দের।
এই বিভূতিভূষণকেই দেখা যায় ময়দানের লর্ড রবার্টসের মূর্তির পাদদেশে দিকপাল সব জ্ঞানীগুণীর আদেশ মতো সেই সমাবেশে পান, মশলামুড়ি আর ধূমপানের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হতে। দ্বিতীয় বিয়ের পর বিভূতিভূষণ একবার শ্যালিকাদের বললেন, “তোরা তো কিছুই রান্না জানিস না দেখছি। এই যে ধনেপাতা দিয়ে কত সুন্দর রান্না হয়, তোরা তো জানিসই না”
“এই যে আপনি বললেন ধনেপাতা খান। আমরা ডালে ধনেপাতা দিয়েছি তো”
আসলে বন্ধুমহলে বিভূতিভূষণ শুনে এসেছেন ধনেপাতা দিয়ে রান্নার কথা, অথচ নিজে তা কোনওদিনই খেয়ে দেখেননি। সেযাত্রায় অবিশ্যি খেয়ে নিয়েছিলেন সেই ধনেপাতা দেওয়া ডাল।
শ্যালিকারা অবাক হয়ে বলল, “আপনি ধনেপাতা খান জামাইবাবু? আচ্ছা আপনাকে রান্না করে খাওয়াব”
সেইদিনই তাঁকে দুপুরে খেতে দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই ডালের সঙ্গে ভাত মেখে মুখে দিয়ে বললেন, “অ্যাই তোরা ডালে ছারপোকা দিয়েছিস? এরকম গন্ধ কেন?”
শ্যালিকারা তখন বলল, “এই যে আপনি বললেন ধনেপাতা খান। আমরা ডালে ধনেপাতা দিয়েছি তো”
আসলে বন্ধুমহলে বিভূতিভূষণ শুনে এসেছেন ধনেপাতা দিয়ে রান্নার কথা, অথচ নিজে তা কোনওদিনই খেয়ে দেখেননি। সেযাত্রায় অবিশ্যি খেয়ে নিয়েছিলেন সেই ধনেপাতা দেওয়া ডাল।
ল্যাঙড়া আম নিয়ে তাঁর জীবনের অলৌকিক ঘটনা সর্বজনবিদিত। একবার শীতের সময় সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের অনুরোধে পুরী বেড়াতে গেছেন। গজেনবাবুর পরিচিত পাণ্ডা মধুসূদন সিঙার এর তত্ত্বাবধানে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়া হল। রাতে প্রসাদ আসবে। বিভূতিভূষণ গজেনবাবুকে বললেন, “জগন্নাথদেবের প্রতি তোমার এত ভক্তি শ্রদ্ধা, উনি কি যা চাইব তাই দেবেন?” গজেনবাবু বললেন, “যদি ভক্তি সহকারে চাইতে পারেন, তবে তা ঠিক পাবেন। একবার চেয়েই দেখুন না”
বিভূতিভূষণ বললেন, “এখন তো শীতকাল, আমি যদি তোমার জগন্নাথের কাছে ল্যাঙড়া আম খেতে চাই?”
এদিকে রাতে সহকারীকে দিয়ে প্রসাদ পাঠিয়েছেন পাণ্ডা মধুসূদন সিঙার। প্রসাদের ঝোলা রেখে সে বলল, “আজ এক মজার ঘটনা ঘটেছে। এক ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মনোবাসনা পূর্ণ হলে জগন্নাথকে আম খাওয়াবেন। সেই আশা পূর্ণ হওয়ায় নিউমার্কেট থেকে পুজো দেওয়ার জন্য এক ঝুড়ি ল্যাঙড়া আম এনেছেন সঙ্গে। সেই পুজোর প্রসাদী ল্যাঙড়া আম কিছুটা আপনাদের পাঠালেন বাবু”
গজেনবাবু ও বিভূতিভূষণ একে অপরের দিকে শুধু চেয়ে রইলেন।
বিভূতিভূষণের সাহিত্য সৃষ্টিতেও খাবারের কথা ছত্রে ছত্রে। বিখ্যাত গল্প “হিঙের কচুরি”র সেই কুসুম? যার লম্বা চুল, বেশ মোটাসোটা বাবু কিনা পাতার ঠোঙায় মুড়ে হাতে একটা বড়ো ঠোঙায় কী খাবার নিয়ে আসত। বিভূতিভূষণ বলছেন “কলকাতার দোকানে খাবার কিনতে গেলে ওইরকম পাতার ঠোঙায় খাবার দেয়। আমাদের দেশে ও পাতা নেই, সেখানে হরি ময়রার দোকানে মুড়কি কী জিলিপি কিনলে পদ্মপাতায় জড়িয়ে দেয়।” আর কুসুম যখন তাঁকে সেই ঠোঙার মধ্যে থেকে একখানা বড়ো কচুরি দিয়ে বলে “এই নাও, খেতে খেতে বাড়ি যাও” তখন কি পাঠকের মনে হয় না? যে সেই ছেলেটিই স্বয়ং লেখক। এই গল্পের সংলাপ তেমনই বলে আমাদের।
আর এই কলের সামনের বাড়ির ভাড়াটে বামুন ছেলেটির মধ্যেই লুকিয়ে হিঙের কচুরী অন্তপ্রাণ লেখক। নয়তো হিঙের কচুরির লোভে সে রোজ বাঁধা নিয়মে কুসুমের বাবু আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়? আর রোজই কি সকলের আগে কুসুম তার হাতে দু-খানা কচুরি তুলে দিয়ে বলবে- “যাও খোকা, এইবার খেতে খেতে বাড়ি চলে যাও”।
“এককামড় দিয়ে আমার ভারি ভাল লাগল। এমন কচুরি কখনও খাইনি। আমাদের গ্রামের হরি ময়রা যে কচুরি করে, সে তেলে-ভাজা কচুরি, এমন চমৎকার খেতে নয়।
উচ্ছ্বসিত সুরে বললাম, বাঃ! কীসের গন্ধ আবার!
কুসুম বললে, হিঙের কচুরি, হিঙের গন্ধ। ওকে বলে হিঙের কচুরি—এইবার বাড়ি যাও।
কুসুমের বাবু বললে, কে?
—কলের সামনের বাড়ির ভাড়াটেদের ছেলে। বামুন।
কুসুমের বাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, যাও খোকা, এইবার বাড়ি যাও”
আর এই কলের সামনের বাড়ির ভাড়াটে বামুন ছেলেটির মধ্যেই লুকিয়ে হিঙের কচুরী অন্তপ্রাণ লেখক। নয়তো হিঙের কচুরির লোভে সে রোজ বাঁধা নিয়মে কুসুমের বাবু আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়? আর রোজই কি সকলের আগে কুসুম তার হাতে দু-খানা কচুরি তুলে দিয়ে বলবে- “যাও খোকা, এইবার খেতে খেতে বাড়ি চলে যাও”। সেখানেই শেষ নয় সারাটা গল্পের চলন এই হিঙের কচুরীর মধ্যে দিয়েই। বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে সে গল্প করে সুস্বাদু হিঙের কচুরির। শুধু তাই নয়, খাস্তা গজা, কুলের আচার, চালতার অম্বল এসব খাদ্যানুষঙ্গ পেরোতে থাকে গল্পের সরণী আর আষাঢ়ের শেষে তাল প্রসঙ্গ এসে পড়ে হঠাৎ করেই। আর গল্প শেষ হয় মাঝবয়সী কুসুমের আনা শালপাতার ঠোঙায় মোড়া হিঙের কচুরি দিয়েই। তিরিশ বছর পরেও সেখানে কুসুম ভোলেনি সেই লোভী কচুরিপ্রেমী ছেলেটিকে।
তাঁর কালজয়ী গল্প তালনবমীতে এক অনুন্নত সরল-সাধারণ গ্রাম্য জীবনের প্রেক্ষাপটে, পবিত্র দুই শিশুমনের নির্মল আনন্দ, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া- নাপাওয়ার এক বাস্তব গল্প উঠে আসে। কিন্তু সেখানেও জটিপিসিমার তালনবমীকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ কাহিনির চলন সুস্বাদু তাল ফলটিকে কেন্দ্র করেই। সেইসঙ্গে তালনবমীর নেমন্তন্নে ওপার বাংলার সব পদ মানে কাঁকুড়ের ডালনা, তিল পিটুলি ভাজাও কিন্তু পাঠকের চোখ এড়ায় না। সঙ্গে গুড়ের গন্ধে ম ম করা পায়েস, তালের বড়া তো আছেই। এসব পড়তে পড়তে মনে হয় রন্ধন কৌশল জানা না থাকলেও তাল যে তিনি খেতে ভালোবাসতেন তা কিন্তু দিব্য বোঝা যায়।
কলকাতার সাহিত্যিক মহলে নাকি তাঁর নাম ছিল নামকরা খাইয়ে হিসেবে। যে কোনও আড্ডায় খাওয়ার কথা উঠলেই সতীর্থ সাহিত্যিকরা এক বাক্যে বলে উঠতেন ‘হ্যাঁ, খেতে পারতেন বটে বিভূতিবাবু’ যদিও তাঁর স্ত্রী রমাদেবী তা মানতে রাজী নন। তা বেশিই খান বা কম তাঁর ভোজন বিলাস নিয়ে নানারকম গল্প চলত সে সব আড্ডায়।
একবার কলকাতা থেকে সাহিত্যিকদের একটি দল মেদিনীপুরের সাহিত্যবাসরে গেছেন যার দলপতি বিভূতিভূষণ।
উদ্যোক্তারা খড়গপুর স্টেশনে এসেছেন তাঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। দলপতি বিভূতির পিছন পিছন চলেছেন বাকিরা। হঠাৎ দেখা গেল এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কী যেন আলোচনা চলছে। বাকিরা ভাবল অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা চলছে বোধহয়। কিন্তু জানা গেল, সেদিন দুপুরের মেনু কী সেই নিয়েই চলছিল গম্ভীর কথাবার্তা।
রাতে এক বড় হলঘরে শুয়েছেন সবাই। হঠাৎ কানে এলো খড়খড় আওয়াজ। ইঁদুর জামাকাপড় কেটে নষ্ট করবে না তো?এসব আলোচনা যখন চলছে বিভূতিভূষণ তন্দ্রা জড়ানো গলায় পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, ‘তোরা বড় বকর বকর করিস, ঘুমোতে দে’
সেদিন দুপুরের খাওয়া খেতে খেতে হঠাৎই জানালেন, ‘মেদিনীপুরের কাঁকড়ার ঝোল নাকি খুব ভাল খেতে’
দুম করে উদ্যোক্তাদের বললেন, ‘কাল তো রবিবার, কাল দুপুরে আপনারা কাঁকড়ার ঝোল খাওয়াতে পারেন?’
উদ্যোক্তারা প্রস্তুত ছিলেন না এমন আবদারের জন্য। তাঁরা জানালেন, ‘আগে খবর পেলে লোক লাগিয়ে ভাল জাতের কাঁকড়া সংগ্রহ করে রাখতাম’
কিন্তু পিছপা হলেন না তাঁরা। অতিথিদের কাঁকড়ার ঝোলের বরাত ছিল বলেই হয়তো।
রাতে এক বড় হলঘরে শুয়েছেন সবাই। হঠাৎ কানে এলো খড়খড় আওয়াজ। ইঁদুর জামাকাপড় কেটে নষ্ট করবে না তো?এসব আলোচনা যখন চলছে বিভূতিভূষণ তন্দ্রা জড়ানো গলায় পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, ‘তোরা বড় বকর বকর করিস, ঘুমোতে দে’
তবুও বাকীদের সেই আলোচনাটা চলতেই থাকল।
মাঝরাত্তিরে ঘুমের মাঝে গলার হইহল্লায় বিরক্ত বিভূতিভূষণ বললেন, ‘তোরা শহরে থেকে অমানুষ হয়ে গেছিস, ওটা ইঁদুরের নয়, কাঁকড়ার আওয়াজ’।
গোটা হলঘর হইহই করে উঠল! ‘বিছে নয় তো?’
এবার উঠে বসলেন। বালিশের তলা থেকে টর্চখানা বের করে বললেন, ‘শহরে থেকে থেকে তোদের আর বুদ্ধিশুদ্ধি হল না। কাঁকড়াবিছের আবার ওরকম খড়খড় আওয়াজ হয় নাকি? ওটা কাঁকড়ার ঝোলের কাঁকড়া।’
হলে গুদাম করে রাখা বস্তার গায়ে টর্চ ফেলতেই দেখা গেল ভিতরের জীবগুলো খড়খড় করে নড়ছে।
খড়খড়ানির শব্দ কেন আসছে সে রহস্য ভেদ হতে বেশ নিশ্চিন্তি নেমে এল ঘরের ভিতর। কেবল একজন গোয়েন্দা কৌতূহলে প্রশ্ন করলেন, ‘এক বস্তা কাঁকড়া কেন বিভূতিদা, তাছাড়া, আমাদের শোবার ঘরেই বা কেন এনে রাখল?
ঘুমধরা গলার উত্তর কানে এল, ‘সারারাত ধরে আমাদের জানান দিতে যে আমাদের জন্য কাঁকড়া সংগ্রহ করা হয়েছে’
এক বস্তা কাঁকড়া কেন?
পরের দিন দুপুরে রান্না করা হবে অর্ধেক আর বাকি অর্ধেক তুলে দেওয়া হবে কলকাতার ট্রেনে।
সে রোববারের দুপুরে ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’-এর কাহিনিকার দেখিয়েছিলেন কাঁকড়া খাওয়া কাকে বলে! একেবারে তাক লাগানো ব্যাপার।
বাটি থেকে বিভূতিভূষণ একটা-একটা করে কাঁকড়া তুলছেন। দাঁড়াটা মড়মড় করে ভেঙ্গে চুষিকাঠির মতো চুষে নিয়ে দাঁত দিয়ে টুক করে কামড় দিয়ে ভেতরের শাঁস কুরে কুরে খেতে ব্যস্ত। কোনও দিকে তাকাবার অবসর তাঁর নেই।
পাত সাজিয়ে ভাত আর নানারকম ভাজাভুজি। পাশে বড় জামবাটির এক বাটি লাল টকটকে কাঁকড়ার ঝোল। বাটি দেখেই ঝলমলে হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা। তরিতরকারী সব একধারে সরিয়ে রেখে কাছে টেনে নিলেন বাটিটা।
কিছুক্ষণের মধেই সে বাটি খালি। ফের টইটুম্বুর করে দিলেন গৃহকর্ত্রী।
বাটি থেকে বিভূতিভূষণ একটা-একটা করে কাঁকড়া তুলছেন। দাঁড়াটা মড়মড় করে ভেঙ্গে চুষিকাঠির মতো চুষে নিয়ে দাঁত দিয়ে টুক করে কামড় দিয়ে ভেতরের শাঁস কুরে কুরে খেতে ব্যস্ত। কোনও দিকে তাকাবার অবসর তাঁর নেই।
বাকিদের খাওয়া শেষ। কিন্তু তাঁরা উঠতে পারছেন না। দলপতির খাওয়া দেখছেন। খাওয়া তো নয়, যেন আর্ট।
একইভাবে ভর্তি হল বাটি। ফের খালি। তিন-তিনবার।
এবার পাত থেকে ওঠার অনুমতী চাইলেন সঙ্গী-সাথীরা। তিনি তাঁদের বললেন, ‘তোরা ওঠ। আমার একটু দেরীই হবে। ভাল জিনিস রেখে-চেখে না খেলে আমি তৃপ্তি পাইনে’।
তাঁরা উঠেই পড়লেন। তবে রহস্য কিন্তু থেকেই গিয়েছিল। রান্না না হওয়া আধবস্তা কাঁকড়া আদৌ ট্রেনে উঠেছিল কী না, ধাঁধাটা কাটেনি।
বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীসাথীদের দেখা হয়েছিল ফের দু’মাস পর।
সেদিনের কাঁকড়া খাওয়ার বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে জানা গিয়েছিল, মেদিনীপুর থেকে ফেরার পর নাকি তিনদিন উঠতে পারেননি বিছানা থেকে।
তবে তাঁর দোষ নেই। সব দোষ নাকি ধানক্ষেতের কাঁকড়ার।
তথ্যসূত্র
বিভূতিভূষণ রচনাবলী
“পিতা নোহসি” (দীপ প্রকাশন) – তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
“সম্পাদকের বৈঠকে” (আনন্দ পাবলিশার্স) – সাগরময় ঘোষ
রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।