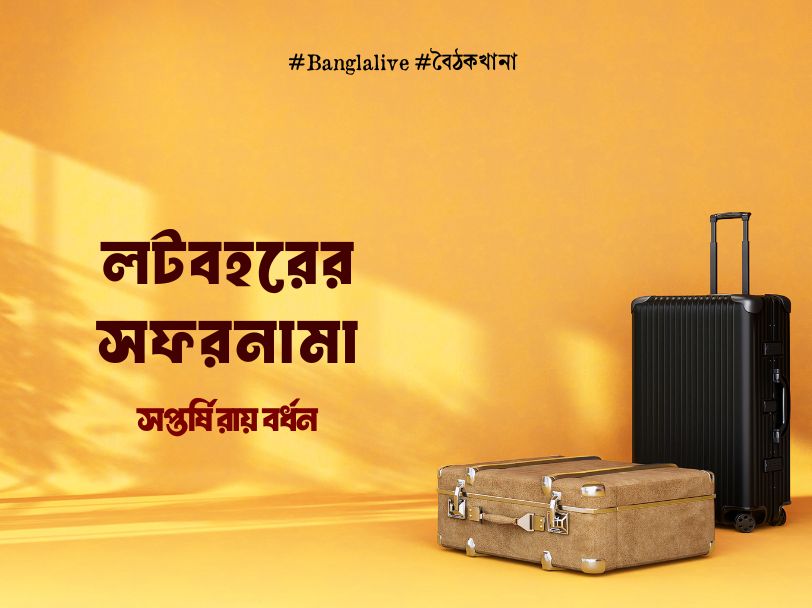বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘রেলরঙ্গ’ বই থেকে খানিক উধৃতি দিয়ে শুরু করা যাক। ‘এ ভিন্ন তিনখানা তোরঙ্গ; একটা নূতন, একটা পুরাতন সুটকেস, একটা হারমোনিয়ামের বাক্স, একটা গ্রামোফোন। আউধ-ত্রিহুত রেলওয়ের ছোট গাড়ি– মাঝের খালি জায়গাটা, দুইটা বাঙ্ক এবং তিনখানা বেঞ্চের এক খানা বেঞ্চ পর্যন্ত ভরিয়া গিয়া কামরাটা থৈ থৈ করিতে লাগিল।’
একটা সময়ে রেলকামরার এরকম ছবি নিতান্তই অস্বাভাবিক ছিল না। সেসময়ে ওই ছিল দস্তুর। কালের নিয়মে সে ছবির পরিবর্তন হয়েছে। ভ্রমণবিলাসী বাঙালি জীবনে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দায় অবশ্যই বর্তায় তার ভ্রমণসঙ্গী লটবহরের চেহারা বদলের ওপরে। আমাদের শৈশবে যে সমস্ত ভারিক্কি বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে যাত্রাপথ পেরুনোর রীতি ছিল, সে কাছেই হোক বা দূরে, তা আজকের অনুপাতে বৃহৎ, আপাতদৃষ্টিতে বেখাপ্পা। সে সময়ে রেলে করে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে ছিল একধরণের উত্তেজনা। সফরসূচি চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ত সেই উত্তেজনার পারদ। আর টিকিট কাটা হয়ে গেলে সফরসঙ্গী জিনিসপত্র গোছগাছের তোরজোড় শুরু হয়ে যেত। শুধু রেলযাত্রার সময়টুকু নয়, “বাহিরে যাত্রা”–র সবটুকুকে মাথায় রাখতে হত জিনিসপত্র গোছানোর সময়। পোশাক আশাক তো বটেই, তার সঙ্গে যোগ দিত বিছানা বালিশ, তৈজসপত্র, চটজলদি খাবার দাবার, ওষুধপত্র, ছোটখাটো বাসন কোসন, ছাতা, বরষাতি, দু’একজোড়া জুতো, বইপত্র এবং অবশ্যই একখানা লুডো বা একটা তাসের প্যাকেট। পাহাড়ি ভ্রমণে পোশাক আশাক খানিক পর্বতপ্রমাণ হত শীতের আশঙ্কায়। আসলে সুখী গৃহকোণ ছেড়ে ভ্রমণবিলাসী বাঙালি বেড়াতে যাওয়ার মধ্যেও ধরে রাখতে চায় তার স্বগৃহের নিশ্চিন্ত আরামটুকুকে। আর সেই জন্যই ‘অধিকন্তু ন দোষায়’– ঝামেলা এড়ানোর তাগিদে খানিক বেশি জিনিসপত্র নিয়েই আমরা, বলা ভাল আমাদের অভিভাবকরা, চলাফেরা করতে ভালবাসতেন। কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক আইনের ধারায় বুঝি বা লেখা ছিল সাড়ে বত্রিশ খানা মালপত্র ছাড়া সফর নৈব নৈব চ। এত কিছু করেও একেবার ঝামেলাহীন হয়েছে কোনও সফর এমনটা মনে পড়ে না। (Luggage)
যাত্রা শুরুর আগে অব্দি, বাড়িতে একটা সাজ সাজ রব, যুদ্ধকালীন তৎপরতা। ঘরের মেঝেতে হাঁ করে খোলা একটা কালো ট্রাঙ্ক, দু-একটা চামড়ার সুটকেস, চার পাঁচখানা ব্যাগ আর অবশ্যই বেরসিক দর্শন, তাঁবু কাপড়ের তৈরি একটা হোল্ডঅল। এদের বেশিরভাগ এসেছে উত্তরাধিকার কিংবা বৈবাহিক সূত্রে। ট্রাঙ্কের উপরে এবং সামনে লেখা মালিকের নাম। কফিনের মতো এই বস্তুটি সেই সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছিল আমার মাতামহের অনুগত সঙ্গী হয়ে। দেশভাগ ভাঙতে পারেনি এই নৈকট্য। এ দেশের জলবায়ুতেও তার চেহারা এতটুকু টসকায়নি। কালো রঙের ওপরে খানিক মরচের আলপনা আঁকা হলেও সে সুস্থ সবল। সে সময়ে চামড়ার সুটকেস নতুন আঙ্গিকে এসেছে বাজারে– “লুজ টপ” অর্থাৎ খানিক বেশি জিনিসপত্র ভরলেও বাধা না দিয়ে বাধ্য ছেলের মতো সে ধারণ করবে তাদের। সব কিছুর ভেতর থেকেই ন্যপ্থালীন মাখা পুরনো সময়ের গন্ধ উঠে আসে, হরেক কিসিমের জিনিসপত্র সেঁধিয়ে যায় তাদের গহ্বরে।
ইতিহাস বলে হোল্ডঅলের পূর্বসূরি duffel bag– বেলজিয়াম থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রান্তরে হেঁটে যা পৌঁছে গিয়েছিল নানা দেশে। মার্কিনরা তার গায়ে “holdall” নামের তকমা লাগিয়ে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বাঙালির ভারি সুবিধে করে দিয়েছিল।
হোল্ডঅলের ব্যাপারটা একটু আলাদা করে বলা দরকার। ইতিহাস বলে হোল্ডঅলের পূর্বসূরি duffel bag– বেলজিয়াম থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রান্তরে হেঁটে যা পৌঁছে গিয়েছিল নানা দেশে। মার্কিনরা তার গায়ে “holdall” নামের তকমা লাগিয়ে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বাঙালির ভারি সুবিধে করে দিয়েছিল। শতরঞ্চি, পাতলা তোশক, চাদর, লেপ, কম্বল, বালিশ আর শেষ মুহূর্তে মনে পড়া নানা ধরণের অত্যাবশ্যকীয় টুকিটাকি অনায়াসে ঢুকিয়ে নেওয়া যেত হোল্ডঅলের জঠরে। বিনা প্রতিবাদে সে স্ফীতদেশ নিয়ে চলত যাত্রাসঙ্গী হয়ে। ট্রেন যাত্রার সুবাদে সিনেমা জুড়ে হোল্ডঅলের আসা যাওয়া। ট্রেনের বাঙ্ক, মেঝে, রেলের প্ল্যাটফর্ম– দিনের পর দিন সে পেতে দিয়েছে এক নিশ্চিন্ত আরাম সজ্জা। মোটামুটি নব্বই দশকের শেষ অবধি হোল্ডঅল নামক এই পেল্লায় জঠর বস্তুটি ভ্রমণের সুখ স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আমাদের।
একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইঙ্গিত যখন সবে মিলতে চলেছে– লালজামা কুলি হাত পাতে “মেরা পইসা”? এবার আরেক প্রস্থ উষ্ণ দেওয়া নেওয়ার সূত্রপাত।
অবশেষে যাত্রার দিন আসন্ন। ঠাকুর প্রণাম সেরে, দইয়ের ফোঁটা কপালে লাগিয়ে ব্যাগব্যাগচি গুণে বুঝে ট্যাক্সি চড়ে ষ্টেশন পৌঁছে আবার এক দফা গিণতি। ডাক পড়ল লাল জামা কুলির। ষ্টেশনের অন্ধিসন্ধি সে চেনে নিজের মতো করে। মালপত্তর ঘাড়ে মাথায় নিয়ে সে দৌড়য় আগে আগে– কর্তা বাবু আর গিন্নিমা টেঁপি বাপির হাত ধরে তখন নেমেছেন এক অসম প্রতিযোগিতায়। ট্রেনে সেঁধিয়ে আরেক প্রস্থ ঝামেলা। বাক্স তোরঙ্গ হোল্ডঅল নিয়ে বেঁধে গেছে প্রবল হইহট্টগোল ও বচসা সহযাত্রীদের মধ্যে। সবাই চায় নিজের মাল নিজের কাছে রাখতে। একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইঙ্গিত যখন সবে মিলতে চলেছে– লালজামা কুলি হাত পাতে “মেরা পইসা”? এবার আরেক প্রস্থ উষ্ণ দেওয়া নেওয়ার সূত্রপাত। সবাই তো আর লালমোহন গাঙ্গুলি নন যে পাঁচ সিকে ঠেকিয়ে “তঙ্গ মাত করো” করে নিশ্চিন্তে হাত ঝেড়ে ফেলবেন!
মদিরা ও সত্যজিতের ফিল্মি চরিত্ররা
প্লাস্টিক মোলডেড লাগেজ এসে যাত্রাপথের এই সাবেকি চেহারায় প্রথম আঘাত হানল। রঙ বেরঙের চেহারা, হালকা আধুনিক ডিজাইনের সঙ্গে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন দু- জোড়া চাকা। যত ভারীই হোক না কেন সুটকেস, একজন তা অনায়াসে, অক্লেশে বহন করে নিয়ে যেতে পারে, এটা একটা বড় উপলব্ধি। সভ্যতার সেই কোন ঊষাকালে চাকার আবিষ্কার যেমনভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিল জীবনযাপনের মোড়, আপাতদৃষ্টিতে এই নিরীহ উদ্ভাবন ভ্রমণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিবর্তনে একটি বড় ভূমিকা পালন করল। চাকায় ভর করে শুরু হল এবার বিশ্বজয়। রেল পরিষেবায় যাত্রী স্বাচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখে ট্রেনের গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, যাত্রার সময় হ্রাস পেতে থাকে ক্রমশ। সুতরাং কিছু ক্ষেত্রে পথিমধ্যে বিছানা, চাদর, বালিশ, কম্বলের প্রয়োজন গেল কমে। আর্থসামাজিক পরিবর্তনের কারণে যাত্রীদের একটা বড় অংশ রেলের মধ্যশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণী এবং বিমান ভ্রমণে উন্নিত হতে থাকে। সময়ের সঙ্গে আধুনিকতার মিশেলে পর্যটনের রূপরেখা বদলে যায়। সব মিলিয়ে যাদের কাছে তখনও ‘ঘর হতে আঙিনা বিদেশ’, এবার তাদের মনেও কোথাও উঁকি দিল travelling light এর আলো। রঙ বাহারি সুটকেসের মন্ত্রই হল হালকা চালে হালকা চলন- ‘take travel lightly’র বার্তা। নিজের লট বহরের ভার এবার নিজের উপরেই ন্যস্ত। বিমানযাত্রায় প্লেনের ভিতরে স্যুটকেস নিয়ে যাতে নিশ্চিন্তে ভ্রমণ করা যায়, তার জন্য মোল্ডেড স্যুটকেসের আকার আকৃতিতে পরিবর্তন তো এলই, সঙ্গে এল আরও নানা ধরণের সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য। এক হিসেবে মোলডেড লাগেজের আগমন ছিল ভ্রমণের আধুনিক হয়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ। রঙিন, হালকা, চাকায় ভর করা সুটকেস ভ্রমণকে যেমন দিয়েছিল সুবিধে, তেমনই এক ঝকঝকে চেহারা। পুরনো আমলের ধাতব ট্রাঙ্ক, তোরঙ্গ, হোল্ডল একদিন তাদের প্রয়োজনীয়তার শেষ লগ্নে এসে হারিয়ে গেল সফরের লিস্টি থেকে।
জার্মানদের কাছে ঐ ধরণের ব্যাগের নাম “রুকস্যাক” বা “হ্যাভারস্যাক”। চার দশকের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া দুই বিশ্বযুদ্ধের ময়দানে সৈন্যসামন্তর পিঠে চেপে সে প্রমাণ করে দেয় তার উপযোগিতা।
২০০০ সালের পরবর্তী সময়ে বাজারে এসে আবার আরেক ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটাল সফট লাগেজ অর্থাৎ ক্যানভাস, নাইলন, পলিয়েস্টার কাপড়ে তৈরি ব্যাগ আর সুটকেস যার নবতম রূপ হল ব্যাকপ্যাক। উনিশ শতকের প্রথম দিকে মার্কিন দেশে “ব্যাকপ্যাক” কথাটির প্রচলন হয়– অর্থাৎ, পিঠে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এমন ব্যাগ। জার্মানদের কাছে ঐ ধরণের ব্যাগের নাম “রুকস্যাক” বা “হ্যাভারস্যাক”। চার দশকের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া দুই বিশ্বযুদ্ধের ময়দানে সৈন্যসামন্তর পিঠে চেপে সে প্রমাণ করে দেয় তার উপযোগিতা। ভারী লটবহর পিঠে বয়ে নিয়ে গেলে দুই হাত খালি থাকে; তাদের লাগানো যায় শত্রুকে নিশানা ও নিধনের কাজে। অ্যাডভেঞ্চারের সফরসঙ্গী হয় হ্যাভারস্যাক। কিন্তু সেখানেও সে থেমে থাকে না। একসময়ে অ্যাডভেঞ্চারের আনুষঙ্গিক হিসাবে ব্যবহৃত জিনিসটি ক্রমশ হয়ে ওঠে নিত্যযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। ল্যাপটপ এবং অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র বহন করার সহজ উপায় হিসাবে কর্মক্ষেত্রে তার প্রবেশ ঘটে। ব্রিফকেস থেকে ব্যাকপ্যাকে উত্তরণ আসলে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। কর্মক্ষেত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণীবিন্যাসকে সবার অলক্ষ্যে সে মুছে দেয়। উঁচুতলার কর্তা থেকে বড়বাবু হয়ে নীচের তলার প্রান্তিক মানুষটি– সবাই ব্যাকপ্যাককে পিঠে তুলে নেন নমনীয় অথচ টেকসই সফরসঙ্গী হিসেবে! জেনারেশন এক্স হাতে পেয়ে যায় একজোড়া জিন্স এবং টি-শার্টে, ব্যাকপ্যাকার টুরিস্টের সাদামাটা সফর ও যাপনের আস্বাদ।
আমাদের সফরনামায় এভাবেই বাক্স, তোরঙ্গের আকার প্রকার বদলে গেছে সময়ের হাত ধরে। জীবনের চাহিদা মেনেই হয়েছে তা। বেড়ানোর তাগিদ এবং যাত্রাপথের আনন্দ, আরাম, উচ্ছাস, উত্তেজনা সব কিছুর মিশেলে এর উদ্ভাবন তাই অনস্বীকার্য।
সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।