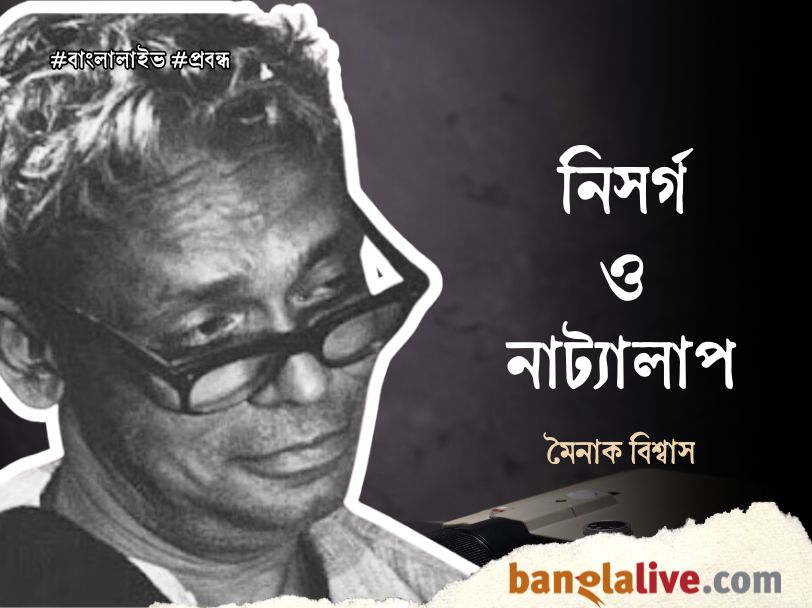এমন ছবি এ দেশে এর আগে কেউ দেখেনি। আর দেখার জন্য যে কেউ তৈরি ছিল না সেটা ছবির প্রদর্শনের মর্মন্তুদ ইতিহাস থেকে আমরা জানি। এ জাতের সৃষ্টিকে নানা সময়ে নানা দৃষ্টিতে দেখার তাগিদ তৈরি হয়। টুকরো করে দেখার প্রয়োজন সমগ্রকে বোঝবার মতোই হয়তো জরুরি হয়ে ওঠে। সেই রকম একটা টুকরো নিয়ে কথা বলব এখানে।
ঋত্বিক ঘটকের কোমল গান্ধার-এ (১৯৬১) যে নানা স্তরে নানা স্বর, অনেক বস্তু ধরা আছে সে কথা ঋত্বিক (Ritwik Ghatak) নিজেই জানিয়েছেন (দ্রষ্টব্য, ওঁর প্রবন্ধ “কোমল গান্ধার প্রসঙ্গে”, ১৯৬১)। এমন ছবি এ দেশে এর আগে কেউ দেখেনি। আর দেখার জন্য যে কেউ তৈরি ছিল না সেটা ছবির প্রদর্শনের মর্মন্তুদ ইতিহাস থেকে আমরা জানি। এ জাতের সৃষ্টিকে নানা সময়ে নানা দৃষ্টিতে দেখার তাগিদ তৈরি হয়। টুকরো করে দেখার প্রয়োজন সমগ্রকে বোঝবার মতোই হয়তো জরুরি হয়ে ওঠে। সেই রকম একটা টুকরো নিয়ে কথা বলব এখানে।
বাবার গল্প – মৈনাক বিশ্বাস
[পর্ব ১], [পর্ব ২], [পর্ব ৩], [পর্ব ৪], [পর্ব ৫]
ছবির ভিতরকার দেশান্তরের কথা ভাবা যেতে পারে। এ নাগরিক ছবি; কিন্তু মাঝে মাঝে শহর কলকাতা থেকে দূরে চলে যায় কুশীলবেরা – লালগোলা, কার্শিয়ং, বোলপুর, বজবজ। যতিচিহ্নের মতো কাহিনির কাঠামোয় এই সব বেরিয়ে-পড়া রাখা আছে। এর আভাস ছিল একেবারে প্রথমে, জানলা দিয়ে অনসূয়ার বৃষ্টি দেখার দৃশ্যে। নাগরিক –এ (১৯৫৩) ছিল ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডার থেকে দূরের হাতছানি। মেঘে ঢাকা তারা-য় (১৯৬০) নীতার ঘরে রাখা ছেলেবেলায় পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার ছবির কথা মনে করা যেতে পারে। তার পুনর্বার পাহাড়ে যাওয়ার সাধ পূরণ হয়েছিল নিসর্গের বুকে তার শেষ নিঃশ্বাস মিশে যাওয়ায়। সুবর্ণরেখা-য় (১৯৬২) এসে এই যতি বা পাংচুয়েশনের নিয়মকে রীতিমতো চিন্তার হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন ঋত্বিক। কোমল গান্ধার-এ গল্পের মূল স্রোতে যতির টানে একটা দূরে বেরিয়ে পড়ার নিয়ম গল্পের কাঠামোতে বুনে দেওয়া আছে।

এ ছবিতে ভ্রমণ এসেছে গানের অবসর হিসেবে। লালগোলায় হরেক গানের মেলা; কার্শিয়ং, বোলপুর, বজবজে রবীন্দ্রনাথের গান। সন্দেহ হয় যেন গানের অবকাশ খুঁজতেই শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে অনসূয়া ভৃগুদের দল। গানের অবকাশ ব্যাপারটা ভারতীয় ছবির বাণিজ্যিক বদ অভ্যাস শুধু নয়, গানের জন্যে কাহিনির সোজা পথ থেকে একটু সরে জায়গা করে-দেওয়া বেনিয়মী ছবিতেও ঢুকে পড়তে পারে – এ কথাটা ঋত্বিকের ছবি দেখে আমরা টের পেয়েছি। কোমল গান্ধার-এ ওই অবকাশের নানা রকম ভূমিকা আছে। লালগোলা দৃশ্যে এক সুতোর ওপর অন্য সুতো, এক টানের ওপর আরেক টান চাপিয়ে গানের অজুহাতে যে অবিশ্বাস্য সুন্দর ও জটিল নকশা গড়া হয়েছে সেটা ছবির সামগ্রিক গড়নের এক ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব। এই দৃশ্যের কথা কিছুটা বলতে চাই এই লেখায়, সেই সঙ্গে বলতে চাইব গান থেকে বাচনে, উচ্চারণে পৌঁছনোর কথা। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গান থেকে ঋত্বিক বিষয়টি শিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান যে কোমল গান্ধার-এর আকাশ ভরে থাকবে তাতে আশ্চর্য কী।

২
শহর ছেড়ে প্রথম যাত্রা লালগোলায়, পদ্মার পাড়ে। ভৃগুদের দলবল নাটকের প্রপ, লাইট নিয়ে বাসে চড়ে রওয়ানা দেয়, কণ্ঠে সমবেত গান ‘এসো মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার’, এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের রচনা। ওঁর ‘নবজীবনের গান’ থেকেও নানা অংশ ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে। গন্তব্যে পৌঁছনো মাত্র একের পর এক গানের পালা শুরু হয়। এরা যে নাটকটার অভিনয় করতে এসেছে তার কথা আমরা জানতে পারি না, কিন্তু দৃশ্য জুড়ে একরকম পারফরমেন্স বিস্তার লাভ করে, যেন নিসর্গ এক মঞ্চ, সেখানে ক্যামেরা, চরিত্র সবাই হঠাৎ মুক্তির স্পর্শে শিহরিত। শট গ্রহণ আর সম্পাদনার গতি ছন্দ সব বদলে যায় এখানে এসে, ছড়ানো জটিল এক নকশা তৈরি করতে থাকে। সেই নকশার জমি বোনা হয় গানের ওপর।
দুজনের হাত এক করার জন্যে বিয়ের গান গেয়ে গেয়ে ওই কোরাস অপেক্ষা করে ছবির শেষ অবধি – দুই বাঙলার, দ্বিখণ্ডিত নাট্য আন্দোলনের, আর দুই নরনারীর মিলনের জন্যে এক সুরে প্রার্থনা করে চলে।
পদ্মার হাওয়া ছুঁয়ে যাওয়া মাত্র উত্তেজনায় অনসূয়া ভৃগুর হাত স্পর্শ করে। ‘এসো মুক্ত কর’ থেকে ছবির থিম সঙ্গীতে পৌঁছে যাই তৎক্ষনাৎ, শোনা যায় – ‘আইজ হইব সীতার বিয়া’ গানের পঙক্তি: ‘আমের তলায় জামুর জুমুর কলাতলায় বিয়া/আইলেন গো সোন্দরীর জামাই মটুক মাথায় দিয়া’। সঙ্গতে উলুধ্বনি। দুজনের হাত এক করার জন্যে বিয়ের গান গেয়ে গেয়ে ওই কোরাস অপেক্ষা করে ছবির শেষ অবধি – দুই বাঙলার, দ্বিখণ্ডিত নাট্য আন্দোলনের, আর দুই নরনারীর মিলনের জন্যে এক সুরে প্রার্থনা করে চলে। একেবারে শেষে যখন সে প্রার্থনা পূরণ হতে চলে, বজবজে আরেক রেল লাইনের ওপর এরা দুজনে হাত ধরে দাঁড়ায় (যে রেল লাইন আর লালগোলার মতো ‘বিয়োগ চিহ্ন’ নয়)। তখন বিয়ের গান থেকে পৌঁছে যাব দেশের কথায়, শুনব ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’।

এর কয়েক মুহূর্ত পরেই আসে সারি গান, নদীর বুকে নৌকো চড়ে হই হই করে গায় দলের ছেলেরা। সেই গানের ধুয়ো ‘দোহাই আলি’ এক সময় কোরাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেপথ্যে চলে যাবে, বিলাপ করবে। ‘দোহাই’ কথাটার মাত্রা বদলে যাবে, এক যৌথ স্বর যন্ত্রণা থেকে রেহাই চাইবে। কিন্তু সে আরও পরের কথা। তার আগে আলোয় ভরানো আকাশকে গানে ভরিয়ে দেওয়া হয়। তিনটে দলে এদের ভাগ করে, এক থেকে অন্য দলে যাতায়াত করে চারপাশের মানচিত্র আর এদের নিজেদের গল্প পাশাপাশি সাজানো হয়। গগন আর বংশী গিয়ে বসে জাগনার চরে; ঋষি, শিবু, জয়া আর অন্যরা যায় নৌকা বাইতে; নিরিবিলি একটা জায়গায় আলাদা থাকে অনসূয়া আর ভৃগু।
সারি গানের রেশ মিলিয়ে যেতেই শুনি গগনের গাওয়া ভাটিয়ালি, ‘এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মইধ্যে জাগনার চর’। জাগনা নামক চরে বসেই গাইছে সে; ছবির মধ্যেই ছবির হদিশ ধরিয়ে দেওয়ার যে অভ্যাস পরিচালকের ছিল, আইজেনস্টাইন আর ব্রেশটের থেকে যে অভ্যাস উনি রপ্ত করেছিলেন, সেটা ওঁর সব ছবিরই শব্দপথে ধরা পড়ে। সেখানে কেউ গান করে, মন্ত্র পড়ে, বিলাপ করে, ‘হো হো’ শব্দ পায়ে চলার সঙ্গত করে। এইসব কণ্ঠ চরিত্রের নয়, এরা গল্পের কেউ নয়, এপিক আঙ্গিকের কথকের মতো এদের সংস্থান। গগনের গানে শুধু জাগনার চরের কথা আছে তা নয়, সুর আর কণ্ঠেও আত্মদর্শন আছে। গানটিতে সুর লাগাবার সময় গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে ঋত্বিক অনুরোধ করেছিলেন কোমল গান্ধার স্বরটি লাগাতে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস কণ্ঠ দিয়েছেন গগনের ভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্যকে। এই ছবি যে নিজের কথা বলছে, গণনাট্য আন্দোলনের কথা বলছে, সেটা এইরকম নানা উপায়ে নির্দেশ করা আছে।
গগন দু’হাত ঝাঁকিয়ে ওদের উৎসাহ দেয়। তারপর আবার ফিরে যাই ভৃগু অনসূয়ার কাছে, আবার শুনি বিয়ের গান। ওরা বলে সামনে বয়ে যাওয়া পদ্মার অন্য পারে ওদের ফেলে আসা ঘরের কথা। ওদের যে উৎস একটাই সেটা এবারে জানিয়ে দেওয়া হয়। একই ঘর, একই শৈশব থেকে যেন ওরা এসেছে।
আবার শাঁখের আওয়াজ, উলুধ্বনি, ঘণ্টা। ভৃগু আর অনসূয়া দাঁড়িয়ে আছে রেললাইনের শেষ প্রান্তে। সেই বিয়ের গান শোনা যায়, ‘আমের তলায় জামুর জুমুর’। সংক্ষিপ্ত সংলাপ শুনি এদের মধ্যে। তারপর চলে যাই নদীর বুকে নৌকা-বাওয়া ছেলেদের কাছে। ওরা হই হই করে, ‘দোহাই আলি’। গগন দু’হাত ঝাঁকিয়ে ওদের উৎসাহ দেয়। তারপর আবার ফিরে যাই ভৃগু অনসূয়ার কাছে, আবার শুনি বিয়ের গান। ওরা বলে সামনে বয়ে যাওয়া পদ্মার অন্য পারে ওদের ফেলে আসা ঘরের কথা। ওদের যে উৎস একটাই সেটা এবারে জানিয়ে দেওয়া হয়। একই ঘর, একই শৈশব থেকে যেন ওরা এসেছে। এটা পরিচালকের সব ছবিতে বয়ে যাওয়া গভীর, প্রায় না-বলা এক সূত্র। ওঁর ছবিতে রোমান্টিক যুগল প্রায় কখনোই কাহিনির কেন্দ্রে থাকে না, সে রকম যুগল সহজে তৈরি হয়ে উঠতে পারে না। তার জায়গায় থাকে ভাই-বোনের জুটি। এ নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি।
(দ্রষ্টব্য, http://www.rouge.com.au/3/ghatak.html) ঋত্বিকের ছবিতে ভৃগু-অনসূয়া একমাত্র সার্থক প্রেমিক জুটি। কিন্তু মনে করে দেখুন, পরে বোলপুরে একদিন অনসূয়া ভৃগুকে বলবে, ‘তুমি আমার মায়ের ছেলে’। সেই কথাটা বিয়ের গানের সঙ্গেই এখানে নিঃশব্দে বলা আছে – এরা একই মায়ের সন্তান।
আমরা পারফরমেন্সের কথা বলছিলাম। দৃশ্য-রচনায়, সম্পাদনায়, শব্দে এতটা গতি আর সঙ্গীতময়তা আমদানি করার একটা দার্শনিক যুক্তি ঋত্বিকের মনোযোগী দর্শকের কাছে হয়তো ধরা পড়বে। মনস্তত্ত্ব-নির্ভর রচনায় ওঁর আস্থা ছিল না, সামূহিক মন আর নিসর্গ-জোড়া চৈতন্যের কোনও এক সংযোগের ওপর ভর করে উনি কাহিনির বিস্তার ঘটাতেন। সেজন্যেই অযান্ত্রিক থেকে ওঁর কম্পোজিশনে নিয়মিত একটি রীতি দেখা যায়: কোনও সংকট বা উত্তরণের মুহূর্তে চরিত্ররা আক্ষরিক অর্থে ফ্রেমে গৌণ হয়ে পড়ে, একেবারে সীমানায় ঠেলে দেওয়া হয় তাদের, তাদের শরীরের একটা টুকরো দৃশ্যে রেখে বাকিটা জুড়ে বসানো থাকে নিসর্গ। লালগোলা দৃশ্যে পারফরমেন্স অনুভূতি জিনিসটাকে একের থেকে অন্যে, ভিতর থেকে বাইরে দেওয়া-নেওয়া করার কাজটা সম্পাদন করে।

অতীতের ভূমিকা ঋত্বিকের ছবিতে যন্ত্রণাদায়ক। ব্যাপারটা এমন নয় যে অতীতের হাত ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনও সহজ পথ ঠিক করা আছে, এবং শেষ পর্যন্ত সেই এগিয়ে যাওয়ার কাহিনি সবাইকে বলতে হবে। অতীতের গভীর বহমানতা ঋত্বিকের ছবিতে ক্ষতচিহ্ন হিসেবে যেমন আসে, তেমনই আসে সুশ্রুষা হিসেবে, এবং যা আমাদের হাতে বর্তমান হিসেবে বর্তেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে। গোটা ছবি জুড়ে গানের পর গান যে গাঁথা হচ্ছে তার মধ্যে মেয়েলি বিয়ের গানটির ভূমিকা লক্ষ করলে করলে দেখব ওটাই মূল ধুয়ো। এই দৃশ্যেও তাই। অ-বৈদিক প্রাকৃত মেয়েলি আচার থেকে ধার করা ঐ গানটাই সুদূর কোনও অতীতকে বহমান রেখেছে, তাকে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে নকশা বুনছে পরের সৃষ্টি – গণনাট্যের আধুনিক গান, রবীন্দ্রনাথের গান।
মেঘে ঢাকা তারায় নীতার শেষ কথা চরাচরে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল, সুবর্ণরেখা-য় শালবনে সীতা আর অভিরামের প্রথম প্রেমের উচ্চারণ ফিসফিস করে হাওয়ার শব্দের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। শব্দ আর কথার এই রকম ভিতর থেকে বাইরে খুলে যাওয়া, ব্যক্তির কথা বিশ্বে রটে যাওয়ার এই রীতি অন্য রূপ ধরে অযান্ত্রিক-এ।
দিনের আলো পড়ে আসে, নৌকা তীরে ফিরে আসে, মন্থর হয়ে আসে গান। জাগনার চরে ফিরে যাই। গগনের বিষণ্ণ মুখ, মৃদু স্বরে ভেসে আসে রণেন রায় চৌধুরীর কণ্ঠে আরেক ভাটিয়ালি। গানটা ভৃগু অনসূয়ার ওপর এসে পড়ে, ওদের শেষ দৃশ্যে, এবং বেজে চলে। ওদের প্রেমের উচ্চারণের মুহূর্তে শিবু এসে পড়ে কাছাকাছি। প্রেমের একান্ত উচ্চারণ ঋত্বিকের ছবিতে কখনও সাক্ষী না রেখে ঘটে না। এখানে সাক্ষী শুধু শিবু নয়, গোটা প্রান্তরটাই। সেইজন্যে সংলাপ ফিসফিস করে শোনা যায়। মেঘে ঢাকা তারায় নীতার শেষ কথা চরাচরে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল, সুবর্ণরেখা-য় শালবনে সীতা আর অভিরামের প্রথম প্রেমের উচ্চারণ ফিসফিস করে হাওয়ার শব্দের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। শব্দ আর কথার এই রকম ভিতর থেকে বাইরে খুলে যাওয়া, ব্যক্তির কথা বিশ্বে রটে যাওয়ার এই রীতি অন্য রূপ ধরে অযান্ত্রিক-এ। সেখানে জগদ্দলের হর্নের আওয়াজ মোটিফ হয়ে ফিরে ফিরে আসে। আর যখনই তা বাজে তার সঙ্গে মিশে যায় ওরাঁও শিঙার ধ্বনি। মেঘে ঢাকা তারা-য় নীতার শেষ চিৎকার মিশে যায় পাহাড়ের গায়ে। ভিতর আর বাইরের জায়গা বদল, একের অন্যের মধ্যে উন্মুক্ত হওয়ার এ আরেক পন্থা। নদীর বুক থেকে ভেসে আসা ভাটিয়ালি যখন শেষ বিকেলের হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তখন অনসূয়াদের কথাও অস্ফূট হয়ে ওঠে।

সেই অস্ফূট ধ্বনি কোরাসে মিশে যায়। শিবু শুনেছিল ওদের কথা, পরিবেশ শুনেছিল। আরেক সাক্ষী এই কোরাস, যে সবকিছুর সাক্ষী, ভিতর বাইরের মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে। ‘দোহাই আলি’র ধুয়ো কাতর মিনতির মতো বেজে ওঠে। ঠিক এইখানে নাটক প্রবেশ করবে ছবিতে। কোরাসের ওই ব্যবহার মডার্নিস্ট শিল্প তো নাটকের থেকেই শিখেছে। ভৃগু, যেন কাহিনি থেকে মুখ ঘুরিয়ে, সোজা তাকিয়ে দাঁড়ায়। তার ফ্রন্টাল শট থেকে ক্যামেরা প্যান করে ঘুরে যায় হাওয়ায় দুলতে থাকা ঝোপের ওপর দিয়ে। তারপর দৌড়ে এগিয়ে যায় রেললাইনের ওপর দিয়ে, যে রেললাইন, ভৃগুর কথায়, এক বিয়োগচিহ্নে পরিণত হয়েছে। কোরাস প্রায় চিৎকারে পৌঁছে যায়, ক্যামেরা আছড়ে পড়ে বাফারের গায়ে। এরপরে প্রায় এগারো সেকেন্ড কালো পর্দার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে কোমল গান্ধার। এর আগে কোনও ছবিতে এতটা সময়ব্যাপী কালো ফ্রেমের ব্যবহার দেখা গেছে বলে আমার জানা নেই। আঘাত বা বিস্ফোরণের সাক্ষাৎ উপমান হিসেবে এই অন্ধকার এসেছে নিশ্চয়ই, যতিচিহ্ন হিসেবেও এসেছে। কিন্তু নাটকের প্রতিমা সৃষ্টি করতে গিয়েও এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে; দৃশ্যের ওপর যবনিকার মতো অন্ধকারের পর্দা নেমে এসেছে, পারফরমেন্সে বিরতি টানতে।
আঘাত বা বিস্ফোরণের সাক্ষাৎ উপমান হিসেবে এই অন্ধকার এসেছে নিশ্চয়ই, যতিচিহ্ন হিসেবেও এসেছে। কিন্তু নাটকের প্রতিমা সৃষ্টি করতে গিয়েও এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে; দৃশ্যের ওপর যবনিকার মতো অন্ধকারের পর্দা নেমে এসেছে, পারফরমেন্সে বিরতি টানতে।
ঋত্বিকের ছবির নাটকীয়তা নিয়ে নানা কথা, বেশির ভাগ সময়ে অস্বস্তির কথা, আমরা শুনেছি। কিন্তু নাটক আঙ্গিকের যে সম্পূর্ণ আরেক প্রয়োগ ছবির ভিতরে রয়েছে, উপাদানগুলোর সজ্জায়, কথনের বিন্যাসে – তা তেমন খেয়াল করিনি। করলে দেখা যাবে শুধু যে প্রকাশভঙ্গি কোথাও উচ্চগ্রামে বাঁধা আছে (যেমন এখানে শেষ শটে) তা নয়, কথা, সুর, গান সবকিছুই বাচনের শিল্প হয়ে উঠতে চাইছে ওঁর ছবিতে। এটা নাটকের ব্যাপার, নাটকীয়তার নয়।
(প্রথম প্রকাশ চিত্রভাষ, ‘ঋত্বিক ঘটক ও কোমল গান্ধার বিশেষ সংখ্যা’, ২০১৩। ঈষৎ পরিমার্জিত)
মৈনাক বিশ্বাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং মিডিয়া ল্যাব পরিচালনা করেন। চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ওঁর নানা প্রকাশনা রয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বই 'উজান গাঙ বাইয়া' (১৯৮৯, ২০১৮) ও 'গানের বাহিরানা' (১৯৯৮) সম্পাদনা করেছেন।