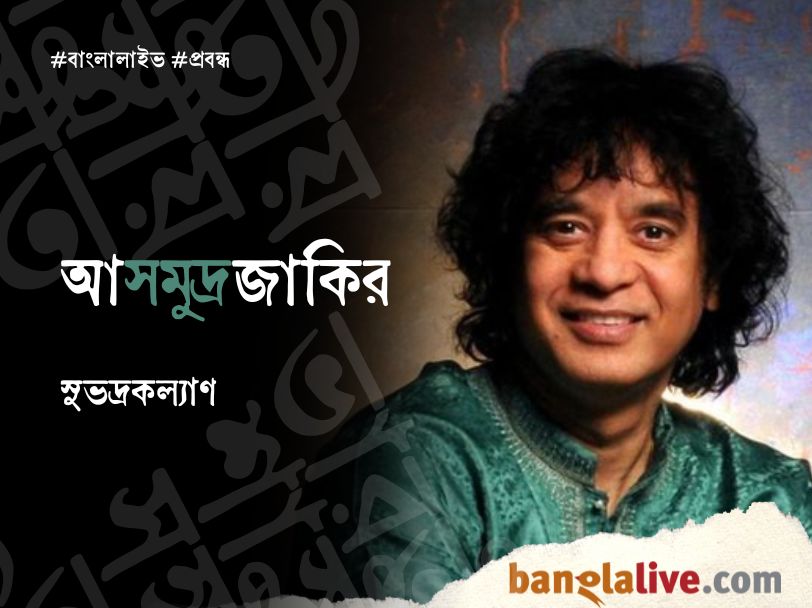উস্তাদ জাকির হুসেন চলে গেছেন, এই আশঙ্কাতে যে অদ্ভুত, অব্যাখ্যাত শূন্যতার সৃষ্টি হল মনে, তা আগে কখনও হয়নি!
এই শূন্যতা-বোধ শুধু শিল্পীসত্ত্বাকে নয়, জাতিগত ভাবে যে গভীর জাকির-প্রভাবে আমরা এতদিন ডুবে আছি, তাকে আঘাত করে। ‘জাকির’ কি সত্যিই এক সংস্কৃতির নাম নয়? ছেলেবেলার কথাই ধরা যাক। তবলা শেখা সবে শুরু হয়েছে। বাড়ি ব্যতীত অন্য কোথাও তবলার প্রসঙ্গ উঠলে অল্প সময়ের মধ্যেই অবধারিতভাবে চলে আসত জাকির হুসেনের নাম। তারপর কথা এমনভাবে এগোত, যেন ‘তবলা’ এবং ‘জাকির’ সমার্থক। কথাটি ঠিক, কিন্তু যাঁরা সেই কথা বলছেন, তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গে তবলার ন্যূনতম আত্মীয়তা নেই। তবে তাঁরা জানলেন কীভাবে, যে তবলা মানেই উস্তাদ জাকির হুসেন? (Zakir Hussain)

আমাদের নব্বইয়ের দশকের গীতিকাররা যখন তাঁদের ব্যাঙ্গ-গীতরচনার প্রচেষ্টায় সাংস্কৃতিক উপাদান হাতড়েছেন, তখনও ‘জাকির’ ছাড়া তাঁদের চলেছে কি? ‘জাকির হোসেন পায়রা পোষেন – ভুল করে ফেলে তালে’ ইত্যাদি পঙক্তি শুনে তো তা মনে হয় না। অথচ, এটা ভেবে দেখাও প্রয়োজন, কীভাবে সম্ভব হল এই বিস্তার? জাকির হুসেন একজন তবলিয়া– তিনি তবলা বাজাতেন। কিন্তু, তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম তবলিয়া নন। তাঁর সমসময়ে তিনিই একমাত্র তবলিয়া, তাও তো নয়। তা সত্ত্বেও তবলা, এবং পরবর্তী সময়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তথা বিশ্বসঙ্গীতের প্রধানতম মুখ জাকির হুসেন কেন? তাঁর আগে-পরে অন্যান্যজন অবশ্যই পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ। এর কারণ নিশ্চয়ই কেবল তাঁর প্রচার নয়– যা তিনি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে, এমনকি তাঁর আত্মজীবনীতেও বলেছেন– যে, তিনি জনপ্রিয়, কারণ জনমাধ্যম বারবার তাঁকে জনতার সামনে এনেছে।
এবার একটু ইতিহাসের দিকে তাকানো দরকার। ভারতবর্ষে তবলার যে ঘরানাগুলি প্রচলিত, তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্বতন্ত্র পঞ্জাব ঘরানা।
এবার একটু ইতিহাসের দিকে তাকানো দরকার। ভারতবর্ষে তবলার যে ঘরানাগুলি প্রচলিত, তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্বতন্ত্র পঞ্জাব ঘরানা। পঞ্জাবের বাজ সম্পূর্ণত পাখোয়াজের শৈলী ভেঙে সৃষ্ট। পঞ্জাবের দিকপাল তবলাগুরু, মতান্তরে পঞ্জাবের তবলা-ঘরের সূচক, উস্তাদ মিঞা কাদের বক্শ শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন পঞ্জাবের পাখোয়াজি, ভবানীপ্রসাদ সিংহের কাছে। পরবর্তী সময়ে মিঞা কাদের বক্শের কাছে তবলার তালিম পান উস্তাদ আল্লারাখা এবং উস্তাদ শৌকৎ হুসেন খাঁ। আল্লারাখারই পুত্র জাকির হুসেন। শৌকৎ হুসেন খাঁর প্রধান শিষ্য উস্তাদ তারী খাঁ। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর আল্লারাখার প্রসার হয় হিন্দুস্তানে, বা ভারতে। শৌকৎ হুসেন খাঁ রয়ে যান পাকিস্তানে। পঞ্জাব ঘরানার পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে জাকির হুসেন এবং তারী খাঁ হিন্দুস্তান-পাকিস্তান দুই দেশেরই পঞ্জাবের বাজকে সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেন। তারী খাঁ পাকিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। একমাত্র পঞ্জাব ঘরানার বাজেই তবলার আদি ঘরানার, অর্থাৎ দিল্লী ঘরানার, কোনওরকম প্রভাব প্রায় পড়েনি, এমনই কথিত আছে। যদিও তা কতখানি গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। বিশেষত তারী খাঁর বাজনায় দিল্লীর ‘তেরেকেটে’ বা ‘তেটে’ অঙ্গের বাণীর বহুলতা অনেকেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন।
আর, জাকির হুসেন? তাঁর রাস্তা ছিল সম্পূর্ণ আধুনিকতার। কোনওভাবেই কোনও ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে, বা ঘরানার মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখেননি তিনি। বরং, তাঁর বাজনা শুনলে বারবার মনে আসে টি.এস.এলিয়টের ‘ট্র্যাডিশন অ্যান্ড দি ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট’ শীর্ষক সেই প্রবন্ধের কথা, যেখানে এলিয়ট লিখেছেন কেমন করে একজন আধুনিকের লেখার সার্থকতা নির্মিত হয় তাঁর লেখায় তাঁর পূর্বজরা কী লিখে গেছেন তার পাঠের পরিচয়ের উপস্থিতির ভিত্তিতে। এই পাঠ যে সবসময় গ্রহণেই প্রতিফলিত হবে, বা হয়েছে, তা কিন্তু নয়।

তবলার শিক্ষার্থী হিসেবে আমার কাছে জাকির হুসেনের বাজনা নিয়ে আগ্রহের বা উত্তেজনার কারণ অবশ্যই তাঁর স্বতন্ত্রতাই, কারণ যা তিনি বাজাতেন, তার অনেক কিছুই যেহেতু তাঁর অগ্রজেরা, এমনকি আল্লারাখাও, বাজিয়েছেন, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেখা, কীভাবে সেই একই রচনা তাঁর হাতে একদম সকলের থেকে ভিন্ন হয়ে ওঠে। তবলা লহরার বিলম্বিত অংশে যে কায়দাগুলি তিনি বাজাতেন, তার সবই যে পঞ্জাবের নিজস্ব বন্দিশ, তা নয়। তার মধ্যে কিছু এমনও ছিল, যা আল্লারাখার ভাবনা-অনুযায়ী পঞ্জাবের রচনা, যেমন ‘ধেনে-ধেনে’ অঙ্গের বাণী। ‘তেটে’ ও ‘তেরেকেটে’র ওপর জাকির হুসেনের বিশেষ দখলের কথা আমার বলার কোনও প্রয়োজনই নেই। বিশেষত, ‘তেরেকেটে’র প্রসঙ্গে বলি, অনেক ক্ষেত্রে আমাকে আমার গুরুই বলেছেন, “জাকির জি’র তেরেকেটে’র ওজন লক্ষ্য কর।” কিন্তু, ‘তেটে’ বা ‘তেরেকেটে’ দুইই দিল্লীতে চর্চিত হয়। পঞ্জাবের কেন, পাখোয়াজের কোনও ঘরানাতেই এই দুইয়ের চর্চা নেই।
লক্ষ্ণৌ-এর প্রভাবও তাঁর বাজনায় ছিল। তিনি প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই খলীফা ওয়াজিদ হুসেন খাঁর নাম নিয়ে তাঁর একটি রচনা বাজাতেন। আজরাড়া ঘরের ‘নাড়াঘেনে-ধাড়াঘেনে’ও তাঁর বাজনায় ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি উস্তাদ হাবিবুদ্দিন খাঁর কথা বলতেন
লক্ষ্ণৌ-এর প্রভাবও তাঁর বাজনায় ছিল। তিনি প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই খলীফা ওয়াজিদ হুসেন খাঁর নাম নিয়ে তাঁর একটি রচনা বাজাতেন। আজরাড়া ঘরের ‘নাড়াঘেনে-ধাড়াঘেনে’ও তাঁর বাজনায় ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি উস্তাদ হাবিবুদ্দিন খাঁর কথা বলতেন, এবং তাঁর বিখ্যাত রচনা, ‘ঘেতগ ঘেতগ ধেনেনাড়াঘেনে’ বাজাতেন। এই ‘ঘেতগ’তে বাঁয়ার যে ঘসীট, তাঁর মাধ্যমেই পায়রা-ডাকের শব্দের অনুকরণ করতেন তিনি, যেমন করতেন হাবিবুদ্দিন খাঁ। ফারুখাবাদের প্রভাব কোনও তবলিয়ার ক্ষেত্রেই অস্বীকার করে চলা সম্ভব নয়। উস্তাদ আহমেদজান থিরাকুয়ার প্রভাবের কথাও জাকির হুসেন বহুবার স্বীকার করেছেন, এবং তাঁর বাজনার মূল বিন্যাস যে ফারুখাবাদের ধাঁচেই, একথাও কারুর অজানা নয়।
এতকিছুর পরও কিন্তু কিছুতেই জাকির হুসেনকে পঞ্জাব ঘরানা থেকে আলাদা করে দেখার প্রশ্ন ওঠে না। পঞ্জাবের পারম্পরিক রচনা তিনি বিলক্ষণ বাজাতেন, এমনকি প্রয়োজনে তার ইতিহাসও বলতেন। আবার তিনি যে শুধু পঞ্জাবেরই তাও নয়। এতজনের এতরকম প্রভাব নিজের বাজনার মধ্যে আসার পরও, কোথাও কখনও জাকির হুসেনকে তো তাঁদেরই একটা বাড়তি অংশ হিসেবে মনে হয়নি? এইজন্যই বোধহয় তিনি আধুনিক।

তাঁর বাজনা ওয়াজিদ হুসেন খাঁ, হাবিবুদ্দিন খাঁ, আহমেদজান থিরাকুয়া, এঁদের সবার পরিচয় বহন করত, কিন্তু স্বাক্ষর নয়। একই সঙ্গে তাঁর নিজের পারম্পরিক পরিচয়ও তিনি বর্জন করেননি, বরং সারাজীবন করে গেছেন তার পরিবর্ধন। মজার বিষয়, এই পঞ্জাব এবং অ-পঞ্জাব তার বাজনায় কখনও কোনও বিরোধ সৃষ্টি করেনি। কিছুটা যেন আমাদের এই দেশটার মতোই নানান রকমের নানান কিছুর একটা সহাবস্থান থাকত তাঁর বাজনায়। পঞ্জাব যেন সেই নানান কিছুর মধ্যেই রয়েছে, অথচ, এমনভাবে রয়েছে, যাতে তাঁকে পঞ্জাব বলে চেনাও যায়, বাকিদেরও অ-পঞ্জাব মনে না হয় তাঁর আশেপাশে। জাকির হুসেন যেন এক দীর্ঘ পর্বতের মতো এই সামঞ্জস্য রক্ষা করতেন, যা দেখেই হয়তো শ্রীজাত লেখেন, ‘…এই ভারতবর্ষ আসমুদ্রজাকির।’
জাকির হুসেনের ঠিক আগেই তবলা সঙ্গতে যে ধারা প্রচলিত ছিল, যা শুরু হয় ফারুখাবাদে উস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ, পণ্ডিত কানাই দত্ত এবং পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের হাতে, এবং বেনারসে পণ্ডিত কিষাণ মহারাজ এবং পণ্ডিত শান্তা প্রসাদের হাতে, তার অনেক কিছুই জাকির হুসেনের বাজনায় আমরা পেতাম না।
পূর্বজদের কী কী তিনি গ্রহণ করেছেন, তাই নিয়ে যেমন আলোচনা করলাম তাঁর একক বাদনের প্রসঙ্গে, সঙ্গতের ক্ষেত্রে আলোচনা করব, কী কী তিনি গ্রহণ করেননি, বা সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। জাকির হুসেনের ঠিক আগেই তবলা সঙ্গতে যে ধারা প্রচলিত ছিল, যা শুরু হয় ফারুখাবাদে উস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ, পণ্ডিত কানাই দত্ত এবং পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের হাতে, এবং বেনারসে পণ্ডিত কিষাণ মহারাজ এবং পণ্ডিত শান্তা প্রসাদের হাতে, তার অনেক কিছুই জাকির হুসেনের বাজনায় আমরা পেতাম না। বিশেষ করে যদি শঙ্কর ঘোষের তবলা-সঙ্গত শুনি, দেখব, তবলা যে কোনও সাঙ্গীতিক উপস্থাপনায় আসে নিজস্ব এক পরিচয় নিয়ে যা তারযন্ত্রীর বাজনার যেমন পরিপূরক, অপরদিকে কিছুটা জবাবীও। জাকির হুসেন বাজনার শুরুতে কিন্তু শঙ্কর ঘোষের তিন-দরজার উঠান নিলেন না, বরং, তাঁকে ভেঙে ঠায় লয়ে পেশকার-অঙ্গে নিয়ে এলেন। বাজনার মাঝে কায়দার ব্যবহারের পরিবর্তে নিয়ে এলেন উপজের প্রচলন। সেই উপজও জবাবী নয়, পেশকার-অঙ্গেরই। দ্রুত লয়ে পারম্পরিক রচনার ব্যবহার তেমনভাবে করেননি তিনি, যেমনটা তাঁর আগে প্রায় সকলেই করেছেন। ঝালার ঠেকা বাজানোতেও পরিবর্তন এল। একটানা খাড়া ঠেকা বাজানোর বদলে সমানে তারযন্ত্রীর সঙ্গে লয়ের খুনসুটিই যেন হয়ে উঠল রীতি। ভাবার বিষয়, এও কি আধুনিকতা নয়? যেখানে প্রভাব অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব, সেখানে প্রায় নিজস্ব এক ধারার প্রবর্তনও তো বহন করে শিল্পীর, বা এলিয়টের মতে কবির, পাঠের পরিচয়!
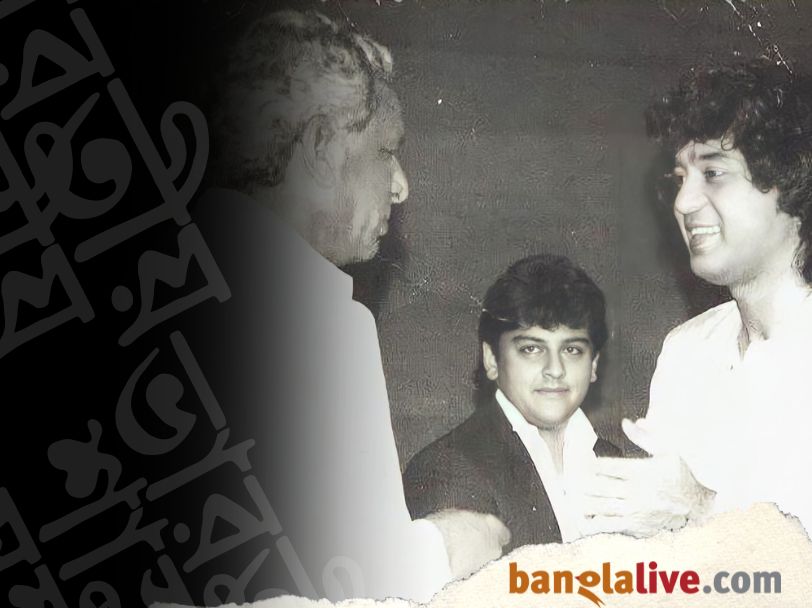
জাকির হুসেন কতিপয় কয়েকজন তবলাবাদকের একজন, যিনি তবলার শব্দ উৎপাদন নিয়ে ভেবেছিলেন। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁর হাতের জাদু– যা লুকিয়ে ছিল তাঁর হাতের ওজনে, বাঁয়ার মীড়ে, এবং বিভিন্ন বাণীর বৈচিত্রে, সমতায় – এবং তাঁর চিন্তা, মনন একসঙ্গে মনোগ্রাহী করে তুলেছিল তাঁর তবলার শব্দকে। এর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছিল তাঁর বাজনার আখ্যানধর্মীতা, যা শেষ পর্যন্ত তাঁর বাজনাকে করে তোলে বিশ্বসংস্কৃতির এক অংশ। আমি অন্তত যে পনেরো থেকে কুড়িখানা একক তবলাবাদন শুনেছি তাঁর, লক্ষ্য করেছি, পেশকার থেকেই যেন তাঁর বক্তব্যের সূচনা হত।
বিলম্বিত লয়ের পেশকারের চঞ্চল গতি, বন্ধুর পথ নির্ধারণ করত তাঁর বাজনার চলন। পাঁচ মাত্রা ব্যাপী একটি ধা যখন বাঁয়ার মীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, তখন যেন বাজনা আপনা থেকেই চলতে শুরু করত দ্রুত লয়ের সেই বন্দিশগুলির দিকে, যার সঙ্গে স্পষ্টতই কোনও না কোনও গল্প জুড়ে দিতেন জাকির হুসেন।
বিলম্বিত লয়ের পেশকারের চঞ্চল গতি, বন্ধুর পথ নির্ধারণ করত তাঁর বাজনার চলন। পাঁচ মাত্রা ব্যাপী একটি ধা যখন বাঁয়ার মীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, তখন যেন বাজনা আপনা থেকেই চলতে শুরু করত দ্রুত লয়ের সেই বন্দিশগুলির দিকে, যার সঙ্গে স্পষ্টতই কোনও না কোনও গল্প জুড়ে দিতেন জাকির হুসেন। সেই গল্পগুলি কখনও রাধা-কৃষ্ণের ব্রজলীলা, কখনও বা কলকাতার রাস্তা নিয়ে। এমন বাজনা সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের যেমন ভালো লাগবে, তেমনই সাধারণ মানুষেরও মন জয় করবে, এতে আর আশ্চর্যের কী থাকতে পারে? সংস্কৃতির বৃহত্তর বৃত্তে তো আমরা সকলেই পড়ি।
ডিসেম্বর মাসের পনেরো তারিখ। সন্ধে নাগাদ সমাজমাধ্যমে খবর ছড়ায়, প্রয়াত হয়েছেন উস্তাদ জাকির হুসেন। সেই সময় আমি এবং আমার এক বন্ধু উপস্থিত ছিলাম শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি আসরে। তিনি বললেন, “জাকির হুসেন প্রয়াত– শব্দগুলো পাশাপাশি ভাবতেই তো অসুবিধে হচ্ছে।” ঠিকই। এ বছর অনেককেই হারিয়েছি আমরা, যেমন উস্তাদ রাশিদ খাঁ, বিদুষী প্রভা আত্রে, উস্তাদ আশিস খাঁ। আমরা সঙ্গীতশিল্পী, সুতরাং এঁদের প্রত্যেকের মৃত্যুতেই বেদনাদায়ক আমাদের কাছে। রাশিদ খাঁর মৃত্যু ছিল অবিশ্বাস্য, কিন্তু সেই ধাক্কা অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছিত হলেও আকস্মিকতার আলোড়ন কিছুটা কেটেছিল তাঁর দীর্ঘ অসুস্থতার কথা শুনে।
সেদিন রাত্রে একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখেছিলাম আমরা সবাই। চেয়েছিলাম খবরটি মিথ্যা হোক, কিন্তু পরের দিন সকালে উস্তাদ জাকির হুসেন সত্যিই আমাদের ছেড়ে চলে যান।
সেদিন রাত্রে একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখেছিলাম আমরা সবাই। চেয়েছিলাম খবরটি মিথ্যা হোক, কিন্তু পরের দিন সকালে উস্তাদ জাকির হুসেন সত্যিই আমাদের ছেড়ে চলে যান। বিশ্বাস করা কঠিন হলেও, বিশ্বাস করতে হবে। উপায়ন্তর নেই।
তাহলে কেন এতদিন পর এই লেখা? কারণ আমি চেয়েছিলাম সময় নিতে। চেয়েছিলাম, বড়দের সবার বলা হলে আমি বলব। এবং চেয়েছিলাম, যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করে লিখতে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে লিখতে হবে, সত্যিই তো ভাবিনি কোনওদিন, তাই এই লেখা সম্মাননা হিসেবে কতখানি যথাযথ, তাই নিয়েও আমার মনে প্রশ্ন রয়ে যায়।
আমাদের মনে রাখা উচিৎ, তবলা, ইতিহাসে যে বিতর্কিত জায়গায় অবস্থান করত, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করার যে কজন কাণ্ডারি, তাঁদের মধ্যে জাকির হুসেন অন্যতম।
জাকির হুসেনের আন্তর্জাতিক কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ থাকলেও, আমি মূলত তাঁর শাস্ত্রীয় তবলাবাদন নিয়েই বললাম, কারণ তাই আমার প্রাথমিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমাদের মনে রাখা উচিৎ, তবলা, ইতিহাসে যে বিতর্কিত জায়গায় অবস্থান করত, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করার যে কজন কাণ্ডারি, তাঁদের মধ্যে জাকির হুসেন অন্যতম। তাঁর বাজনা, তাঁর চিন্তা শত শত মানুষের মন ছুঁয়েছে বলেই আজ সারা বিশ্বে তবলা বাজে। কয়েক দশক আগেও যে তবলার স্থান ছিল পর্দার পিছনে, সেই তবলা বাজিয়ে যে কোনও শিল্পী সসম্মানে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, সেই স্বপ্নও দেখিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী জাকির হুসেন।
(পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ এবং পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ আমার গুরু, তা সত্ত্বেও আমি এই লেখায় তাঁদের আমার ‘গুরু’ বলে উল্লেখ করিনি, লেখাটির নিরপেক্ষতা বজায় রাখার তাগিদেই।)
সুভদ্রকল্যাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর। বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর করছেন। স্তরের ছাত্র। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখা সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বহু বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিও প্রকাশিত ও সমাদৃত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত ইংরাজি ভাষায় কবিতা লেখেন সুভদ্রকল্যাণ। তাঁর আরেকটি পরিচয় রাগসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। সংগীতশিক্ষা করেছেন আচার্য শঙ্কর ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকর, ডঃ রাজিব চক্রবর্তী প্রমুখ গুরুর কাছে। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা।