আগের পর্বের লিংক: [১]
বিগত দশকগুলির মধ্যে সত্তরের দশক সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিল। রাজনীতি থেকে সংস্কৃতি, সমস্ত দিক থেকেই একটা দশক আন্তর্জাতিক তথা আধুনিক হতে চেয়েছিল। আর, এই দশকের যে ক’জন ব্যক্তিত্ব নিজের জীবন ও কাজে ধারণ করেছিলেন সময়ের গর্জন, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। নব্বইয়ের দশক ও তার পরের বাংলা গানে সময়ের থাবা নিয়ে দ্বিতীয় এই কিস্তিতে গৌতম ও তাঁর ব্যান্ড ‘মহীনের ঘোড়াগুলি’ তাই অনিবার্য একটি নাম।
গৌতম চট্টোপাধ্যায় মহীনের ঘোড়াগুলির ছদ্মবেশে চেয়েছিলেন এ শহরের ছোটছোট চৌকোচ্যাপ্টা সাদাসাদা দেওয়ালগুলো ভাঙতে। মিশে যেতে ও মিশিয়ে দিতে ভয়ানক সংক্রমণের মতো ভালোবাসা। সদর দফতরে এক রকম কামানই দেগেছিলেন তিনি বন্ধুত্ব দিয়ে, দল গড়ে, বসন্তের মাতাল সমীরণে। যা রাজনীতিতে পারেননি, তাই শিল্পে খুঁজেছিলেন গৌতম। বড় শিল্পীরা আসলে এভাবেই একটা ঘোর তৈরি করেন, তৈরি করেন একটা দিগন্তিকা বা স্কেপ, যা স্পর্শ করলেই আপনি আর আপনি থাকেন না। বদলে যান। গৌতমের জীবনও আসলে তেমনই এক নোটেশান, যা বেজে উঠলেই বেজে ওঠে সেই সময়, সেই শহর, যা ম্যাজিক রিয়েল, যা আন্তর্জাতিক বলেই স্থানীয়, ভীষণ ইতিহাসসচেতন বলেই বাউণ্ডুলে। তিনি যেন নিয়ম ভাঙবেন বলেই নিয়মটা রক্তমজ্জায় ঢুকিয়ে ফেলেছেন হাজার হাজার বছর আগে, যখন ঘোড়ার ফসিল পাওয়া গিয়েছিল আলতামিরায়…

আশির দশকে যেমন পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটার করত ছেলেমেয়েরা, নব্বই তেমনি পেল ব্যান্ড, যা মহীনের ঘোড়ারা আগেই শুরু করেছিলেন। পিঙ্ক ফ্লয়েডের মতোই শহুরে সভ্যতার সাইকেডেলিক অভিজ্ঞতার গল্প, নৈরাশ্য ও অর্থহীনতার গল্প সেই বিকল্প রক সাউন্ড ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছিল গলিগলতায়। নবারুণ একবার লিখেছিলেন, রেবেলদের ভাগ্য এরকমই। তাঁর মতে, ঋত্বিকের পর সবচেয়ে মননশীল ও জটিল চলচ্চিত্রের নাম ‘সময়’ যা গৌতমের পরিচালনা।
গৌতমের কলকাতায় কমলকুমার থেকে বারীন সাহা, ধরণী ঘোষ, দীপক মজুমদার ছিল রোজনামচা। মৃণাল সেন বা সত্যজিৎ সে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বই পড়তেন। আবার কান, বার্লিন গিয়ে পুরস্কার নিয়েও আসতেন। আর, পার্ক স্ট্রিটে মধ্যরাতে বোতল ভাঙতেন গৌতমরা। সেখানে ট্রিঙ্কাস, ব্লু ফক্সে প্রতি সন্ধায় বিলিতি সুর ভেসে বেড়াত। ভাসতে ভাসত গৌতম, বুলা, তাপসরাও চলে যেতেন সদর স্ট্রিটের বেস গিটারের ডেরা থেকে চিত্রবাণী ঘুরে কেঁদুলির বাউল আখড়ায়। প্রবীণ কৃত্তিবাসী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তারপর বলতেন, আমাদের গানের সংকলনটা শুনুন সুনীলদা… রাসবিহারী মোড়ের সুতৃপ্তি কাফেতে বসে তারপর গান বাঁধতেন তাঁরা, কাঁপে কাঁপে আমার প্রিয়া কাফে…। সে গানে ধরা পড়ত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সদর স্ট্রিটও…
নাকতলায় থাকতেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। সেই নাকতলাকে আমরা ডাকতাম ‘মেটাল পল্লি’ নামে। মহীনের ‘সম্পাদিত বাংলা গান’ শব্দবন্ধটা আমাকে কৈশোরে খুব ভাবাত। যেমন ঋত্বিক ঘটক ‘প্রণীত’ চলচ্চিত্র লেখা থাকত টাইটেল কার্ডে। সাহিত্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কের কথাই মনে করায় এই প্রয়োগ। মনে করায়, তাঁদের ‘মেরুন সন্ধ্যালোক’-এ কি ভীষণ জীবনানন্দ বা ‘অঘ্রাণের অনুভূতিমালায়’ কী ভীষণ বিনয় মজুমদার! মনে করায়, গৌতম সক্রিয় রাজনীতি করতেন। নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যান, অত্যাচারিত হন। ভিনরাজ্যে অন্য পেশা নিয়ে থাকতে বাধ্য হন দীর্ঘদিন।
কত ভাবে ফ্রেম ভাঙতে চেয়েছিলেন আদ্যন্ত আন্তর্জাতিক এই মানুষটি! গান যে আসলে তানসেনের কোলে বসে না বরং আর পাঁচটা শিল্পক্রিয়ার মতই স্বাভাবিক উচ্চারণ, বংশকৌলীন্যর বদলে তাই রকস্টার হওয়া বেশি সম্মানের মনে করেছিলেন গৌতম। আধুনিক, আধুনিক এবং আধুনিক– এই প্রজন্ম আর তাঁদের কলকাতার কথা মনে পড়লে আমার এটাই মনে হয়। অঞ্জন দত্ত গৌতমকে নিয়ে লেখা গানে লিখেছিলেন, ‘তাঁকে পোষ মানানো যায়নি, যায়নি শেখাতে/ এই কলকাতা শহরে বেঁচে থাকার হিসেব..’
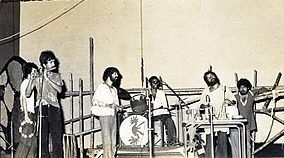
সময়টার কথা বলতে গিয়ে দিনকয়েক আগে চিত্রপরিচালক শেখর দাশ বলছিলেন,
‘আমার পরিচালনায় বিসর্জন অভিনীত হচ্ছে সে সময়। দীপকদা রঘুপতি করছেন, আমি জয়সিংহ করছি। সুনেত্রা ঘটকও অভিনয় করেছিলেন। হাবিব তনবিরের সঙ্গে পাঁচের দশকে কাজ করেছিলেন দীপকদা। আমায়, হিরণদাকে আর গৌতমকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ওঁর মতো ব্যক্তিত্ব সত্যিই বিরল। অনেক গড়িমসির পর রাজি হলেন কাজ করতে নাটকে। সেই সূত্রেই হিরণদার সঙ্গে পরিচয়। গৌতম মিউজিক করেছিল। আমরা সেই নাটকের রিহার্সাল করতাম সদর স্ট্রিটের গির্জার উঠোনে। সেখানে আবার সন্দীপনদা (চট্টোপাধ্যায়) আসতেন।’
এই সময়েরই আর এক অনিবার্য ভাষ্যকার তথা লেখক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। দেশপ্রিয় পার্কের লা ক্যাফে বা রাসবিহারীর অমৃতায়নে আড্ডা জমাতেন অনন্য রায়, নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তিনিও। অদূরেই হয়তো দাঁড়ানো গৌতমবাবু ও তাঁর দলবল। বাড়ি ফেরার পথে সকলেই দেখতেন, চন্দ্রকুমার স্টোর্সের সামনে ফুটপাতে শুয়ে আছেন আকণ্ঠ মদ্যপান করে দেবদূত ঋত্বিককুমার ঘটক।
ঋত্বিকের পরম্পরাতেই গৌতমকেও সুকৌশলে মিথ বানানো গেল। আজ কলকাতা বড়লোকের। প্রিভিলেজড মধ্যবিত্তের। তাঁদের এসব অলীক আর রূপকথা মনে হয়। মনে হয় সানকিসড নস্টালজিয়া। তাই ক্যাফের নাম হয় সত্তরের বিপ্লবের নামে। চায়ের দোকান উঠিয়ে গজিয়ে ওঠে দগদগে স্পা। বন্দুকের মুখে উঠে যায় শপিংমল। তবু তো ঘোর থেকে যায়।

তবু আজও যখন ‘রাত্রিবেলা সবাই যখন ঘুমে অচেতন’ শুনি, আমার প্রেমিকার মধ্যবিত্ত পাড়াটা মনে পড়ে যা একমাত্র ধরা রয়েছে মৃণাল সেনের কলকাতা-৭১ এ। সে কলকাতাও আজ বিগত। সরু গলি দিয়ে ছুটে যায় না আর কোনও প্রতিবাদ, মৌলালি মোড়ে থিয়েটার করেন না বাদল সরকারও, কোনও বোকারা আর স্বপ্নও দেখে না খোলাবাজারের হাওয়ায় দুনিয়াটা বদলানোর, আমার তবু গানমালার ‘বিন্তু’ কে মনে পড়ে, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় বিনীতা কেমন আছে? মহৎ প্রেমিকরা কি আজও ন্যাকা সাজে?
মাঘের অন্তরঙ্গ দুপুরে কেওকার্পিনের গন্ধমাখা দক্ষিণ খোলা জানলা মনে পড়ে, মনে পড়ে গানটির মাঝে বেজে ওঠা অসামান্য ফিউশান, ফুটপাথ ঘেঁষা বেলুনগাড়ির দাউদাউ ইমেজ, টেলিফোন গানের মাঝে বেজে চলা অসামান্য ডিসটরশন গিটার, প্রিয়া কাফে-র জ্যাজ়-জীবনানন্দ-পিকাসো-বুনুয়েল-দান্তে-বিটলস-ডিলান আর বেঠোফেন বেজে চলে আমার নাগরিক পথ হাঁটায়, আমার একলা পথ হাঁটায়, আমার ভেঙেচুরে দিতে চাওয়া বাসনায় ও মধ্যবিত্ত আপসে… রক্তচলাচলে… স্নায়ুবিনিময়ে…
শহুরে গল্প ডালপালা মেলছিল এভাবেই। শহর ও আধুনিকতাকে ঘিরে চালচিত্র বেড়ে উঠছিল। সেখানে গ্রাম্যতা ছিল না, ছিল স্মার্টনেস। কান্ট্রি ও প্রগ্রেসিভ রকে গল্প বলছিল যৌবন, বলছিল আশা-হতাশা, পারা-না-পারা। আমরা সে অর্থে বাংলা ব্যান্ড প্রজন্ম। বছর কুড়ি পরে ফিরে এসে মহীনের ঘোড়ারা আবার বিশ্বাস করাচ্ছিলেন সময়ের চেয়ে অনেকটাই এগিয়েছিলেন তাঁরা। বিশ্বাস করছিলাম আমরাও পারব আমাদের গল্প বলতে একদিন ঠিক। গলিতে গলিতে ব্যান্ডের দল গজাচ্ছিল তারপর। আমরা বিশ্বাস করছিলাম, গানে বা সিনেমাতে একদিন ঠিক আমাদের গল্প বলে ফেলতে পারব আমরা। আবার কলকাতা শাসন করবে যৌবন। আমরা, নিশ্চয়ই পারব…
*ছবি সৌজন্য: NYT, loopnews.com, Wikipedia, TOI
*ভিডিও সৌজন্য: Youtube
পেশা মূলত, লেখা-সাংবাদিকতা। তা ছাড়াও, গান লেখেন-ছবি বানান। শখ, মানুষ দেখা। শেল্ফ থেকে পুরনো বই খুঁজে বের করা। কলকাতার রাস্তা ধরে বিকেলে ঘুরে বেড়ানো।



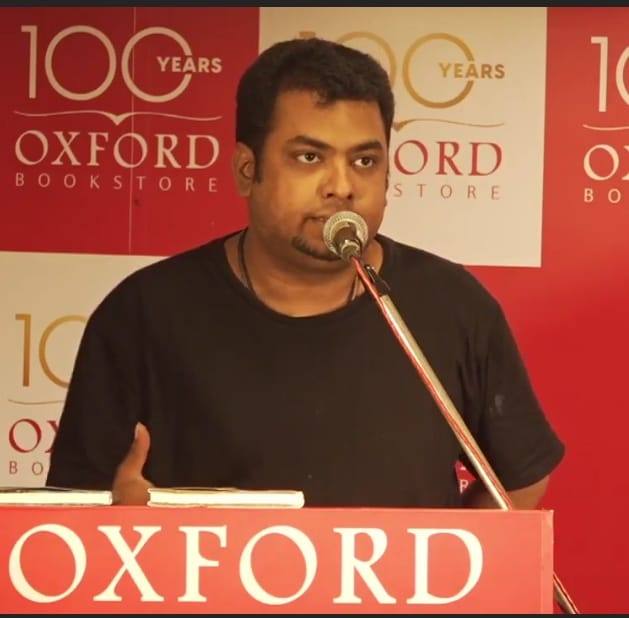






















One Response
দূর্দান্ত প্রতিবেদন ,সেই সময় বদলের প্রতিচ্ছবি