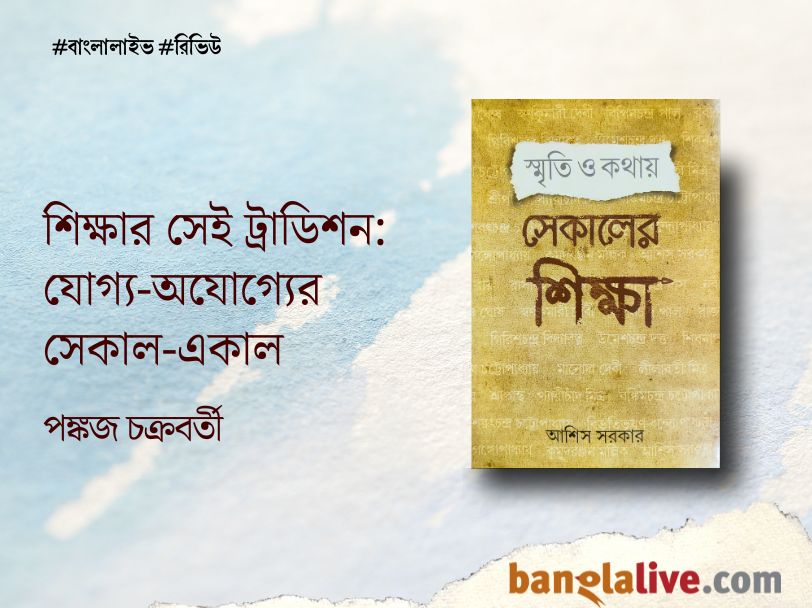(Book Review)
বইয়ের নাম: স্মৃতি ও কথায় সেকালের শিক্ষা
লেখক: আশিস সরকার (সম্পাদিত)
প্রকাশক: নান্দনিক
প্রচ্ছদ: চঞ্চল গুঁইন
বিনিময় মূল্য: ৬৫০ টাকা
যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষক নিয়ে আজ যখন তুমুল তর্কবিতর্ক চলছে, তখন কয়েকটি জরুরি কথা একটি বইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলে নেওয়া যাক। জানি যোগ্যতার প্রশ্নে আপনাদের নৈতিক সমর্থন সেকালের পক্ষে। আমরা জানি আপনার আমলে সেই সব মাস্টাররা ছিলেন। যাঁরা দেবতুল্য আদর্শবান, মহৎ হৃদয়। আজ তাঁদেরই দেখা মেলা ভার। যেন ডুমুরের ফুল। সৎ ও যোগ্য শিক্ষক আজ আর মেলেই না। আমরা যারা বিশ্বাস করি আপনাকে এবং ফিরতে চাই সেকালের দিনগুলিতে তখন কার্যত আশ্চর্য হই। (Book Review)
আরও পড়ুন: রাহুল পুরকায়স্থ: সময়, শূন্যতা ও দেহপাঠাগার
আসুন প্রথমেই আপনাদের নিয়ে যাই প্রায় ১০০ বছর আগের একটি স্কুলে। ভারতী ইনস্টিটিউশন। পুজোর ছুটি পড়বে। ছাত্ররা সবাই মিলে প্রত্যেক ক্লাস টিচারের জন্য চাঁদা তুলে উপহারের আয়োজন করেছে। তাই নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে চলছে রেষারেষি। শিক্ষক পতাকীচরণ বাবু, থার্ড বি ক্লাসে গিয়ে বলেন- ডি সেকশনে ধুমধাড়াক্কা ব্যাপার। এক টাকা করে দিচ্ছে প্রত্যেকে। কেউ বাদ নেই। ওরা অনন্তবাবুকে সিল্কের চাদর দেবে। আবার অনন্তবাবু ঘোষণা করেছেন বি সেকশন নাকি দারুণ আয়োজন করেছে। প্রতিটি ক্লাসেই ছেলেমেয়েদের, লোভের জন্য লড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষকেরা। এরপর ঠিক কী হয় আমরা উপন্যাস থেকে দেখে নেব: (Book Review)
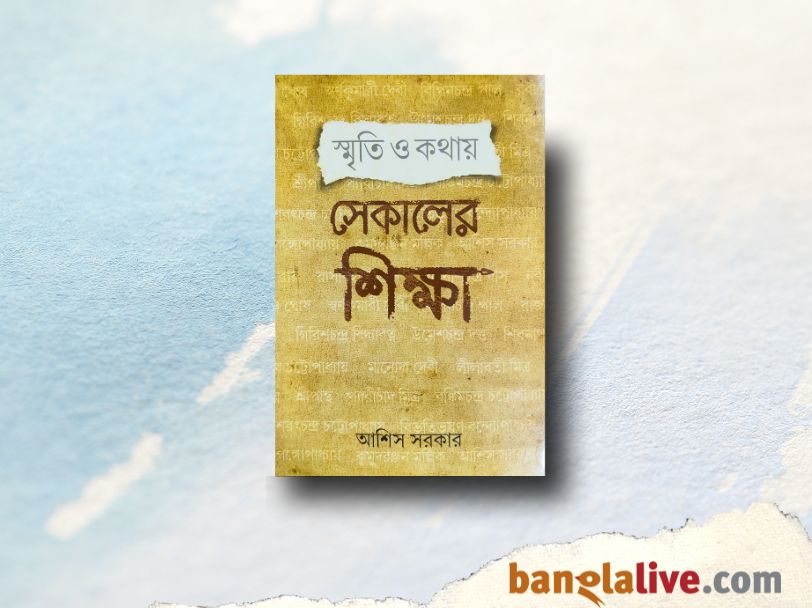
“রামকিঙ্করের নিচু ক্লাস-এইটথ্-এ। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, পয়সা কে তাদের হাতে দেবে? চাঁদা উঠেছে অতি সামান্য, পুরোপুরি পাঁচ টাকাও নয়। রামকিঙ্কর বেজার মুখে বলেছেন, ছি ছি, এত খেটেখুটে এই মাত্তর হল? লোকসমাজে কহতব্য নয়। তা ওই উনিশ সিকে কিসে খরচ হবে, ঠিকঠাক করলি কিছু? (Book Review)
নাইনথ ক্লাস থেকে ফার্স্ট হয়ে উঠেছে সেই ছেলেটা বলে, গোড়ের মালা আসবে একটা স্যার। আর জলখাবার।
“বই কি হবে রে? পাহাড় প্রমাণ বই-টই পড়ে তবে তো শিক্ষক হয়েছি। বই বয়েই জনম কাটল-কোন্ বইটা না পড়া? বই দিতে যাস্ না, ওতে লাভ নেই!”
রামকিঙ্কর বলেন, পুজোর মুখে মিষ্টিমুখ-সেটা খুব ভাল। দিস্ জলখাবার যেমন তোদের খুশি। সন্দেশ দিস্, লেডিকেনি দিস্। চপ-কাটলেট দিলেও খাব। ক’দিন আর খেতে পারব বল। যা তোরা হাতে করে দিবি, চেটেপুটে খেয়ে নেব। (Book Review)
আবার বলেন, কিন্তু মালার বুদ্ধি কে দিয়েছে শুনি? গুচ্চের জঙ্গল কিনে আনবি পয়সা দিয়ে। গোড়ের মালা ঝুলিয়ে নৃত্য করে বেড়াব নাকি? এক ঘণ্টা তো পরমায়ু- শুকিয়ে তার পরে আমসির মতো হয়ে যাবে। মফস্বল হলে পোষা গরু-ছাগলের মুখে দেওয়া যেত, কলকাতা শহরে তা-ও তো নেই।
ছেলেটা বলে, জলখাবার হয়ে যা বাঁচে, তাই দিয়ে তবে বই কিনে দেব স্যার। যে বই আপনি বলবেন। (Book Review)
রামকিঙ্কর বলেন, এই দেখ। ছেলেমানুষ তবে আর বলি কেন। বই কি হবে রে? পাহাড় প্রমাণ বই-টই পড়ে তবে তো শিক্ষক হয়েছি। বই বয়েই জনম কাটল-কোন্ বইটা না পড়া? বই দিতে যাস্ না, ওতে লাভ নেই!
ছাত্রেরা মুখ তাকাতাকি করে: তবে কি দেব স্যার? (Book Review)
“এরই আরেকটি ছবি দেখতে পাই বিভূতিভূষণের ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসে। শিক্ষকের উঞ্ছবৃত্তি কী পরিমান তা দেখলে তাজ্জব হতে হয়। আপনার হয়তো ভাবছেন উপন্যাস যখন তখন সবটাই কল্পনা।”
কি দিবি? তাই তো, ঝট করে কি বলি এখন তোদের! এক কাজ করিস্, টাকা-পয়সা যা বাঁচে নগদ ধরে দিস্ আমায়। আমি কিনে নেব। ভেবে দেখতে হবে কিনা, কোন জিনিস হলে আমার কাজে আসবে। (Book Review)
নগদ টাকা দেওয়া-সেটা কি রকম। মালা হলে গলায় পরিয়ে দিত, বই হলে ফিতে বেঁধে নাম লিখে টেবিলের ওপর রাখা চলত। তা নয়- টাকা দিলাম আর রামকিঙ্কর স্যার পকেটে ফেললেন, কাকপক্ষী কেউ টের পাবে না। তবু ক্লাসটিচারের কথার ওপর আপত্তি চলে না। ঘাড় নাড়তে হল মনমরা ভাবে।” (Book Review)
এতক্ষণ যা পড়লেন তা মনোজ বসুর ‘মানুষ গড়ার কারিগর’ উপন্যাসের অংশ। এখানেই দেখা মিলবে কয়েকজন শিক্ষকের যারা ফাঁকিবাজ, লোভী, ছাত্রদের ব্যাপারে উদাসীন। সারাদিন প্রাইভেট টিউশন করে যাঁরা স্কুলে শুধুমাত্র বিশ্রাম নিতেন। তাই খাতা দেখা থেকে পড়াশোনা সবেতেই নানা ফাঁকিবাজির অজস্র কৌশল। এই ঘটনা মোটামুটি শতবর্ষ আগের। এরই আরেকটি ছবি দেখতে পাই বিভূতিভূষণের ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসে। শিক্ষকের উঞ্ছবৃত্তি কী পরিমান তা দেখলে তাজ্জব হতে হয়। আপনার হয়তো ভাবছেন উপন্যাস যখন তখন সবটাই কল্পনা। তা বাস্তবের ব্যস্তানুপাতিক হয়তো। (Book Review)
“সেকালের শিক্ষা সম্পর্কিত এই গ্রন্থটির তিনটি অংশ। প্রথম ভাগে স্মৃতিকথা, দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষক সম্পর্কিত কথাসাহিত্যের অংশ। তৃতীয় ভাগে রয়েছে পরিশিষ্ট, সরকারি নানা নথি ও রিপোর্ট, পরিসংখ্যান।”
কিন্তু এই ভুল ভেঙে যায় যখন হাতে নিই আশিস সরকার সম্পাদিত ‘স্মৃতি ও কথায় সেকালের শিক্ষা’ গ্রন্থটি।
সেকালের শিক্ষা সম্পর্কিত এই গ্রন্থটির তিনটি অংশ। প্রথম ভাগে স্মৃতিকথা, দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষক সম্পর্কিত কথাসাহিত্যের অংশ। তৃতীয় ভাগে রয়েছে পরিশিষ্ট, সরকারি নানা নথি ও রিপোর্ট, পরিসংখ্যান। সবমিলিয়ে সেকালের শিক্ষার বিশ্বস্ত দলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এর বিস্তার। সেকালের পাঠশালা, সেকালের শিক্ষকতা, বিদ্যাশুরুর দিন, মেয়েদের শিক্ষার হার সবকিছুই উঠে এসেছে এই গ্রন্থে। দীনেন্দ্র কুমার রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মনোমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র সেন, রাসসুন্দরী দেবী, মানকুমারী বসু, মানোদা দেবী, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু থেকে শ্রীপান্থ পর্যন্ত বিস্তারিত লেখক তালিকা। (Book Review)
এতক্ষণ যাকে কাল্পনিক বলে ভাবছিলেন এবার সেই বাস্তবের দিকে একটু তাকাই। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘পল্লীচিত্র’ গ্রন্থ থেকে একটি অংশ তুলে দিই সেকালের পাঠশালার শিক্ষকদের আচার-আচরণ সম্পর্কে। (Book Review)
“চক্রবর্তীদের দক্ষিণদ্বারী চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালা সংস্থাপিত ছিল। দোল, রাস বা ঝুলনের সময় চক্রবর্তীদের গৃহবিগ্রহ রাধাকান্তদেব সিংহাসনে চড়িয়া এই গৃহে উৎসব করিতে আসিতেন, উৎসবান্তে তিনি তাঁহার অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। উৎসবের কয়দিন পাঠশালা বন্ধ থাকিত, কিন্তু তাই বলিয়া চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণে উৎসবমত্ত ছেলের দলের অভাব হইত না; গুরুমহাশয়ও এ কয়দিন ছেলেদের সঙ্গে বড় ভাল ব্যবহার করিতেন, কারণ, কোন একটা উৎসব বা পার্ব্বণ উপস্থিত হইলেই পড়ুয়াদের কাছে গুরুমহাশয়ের দক্ষিণা বরাদ্দ ছিল-এক বারকোশ সিধা ও চারিটী পয়সা। (Book Review)
“সেকালে দিনে দু’বার পাঠশালা বসত। সকালে পাঠশালার নিকটের পুষ্করিণী থেকে স্নান করে নামতা পড়ে ছুটি। তারপর আবার বিকেলে পাঠশালা খুলত। পুজোয় এবং বর্ষায় পাঠশালা বন্ধ থাকত।”
এ বিষয়ে কোন পড়োর বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হইবার যো ছিল না; ‘আমি গরীব,’ কি ‘মা মাপের হাতের পয়সা নাই’, এরূপ কৈফিয়ৎ তাঁহার নিকট টিকিত না; তিনি এরূপ কৈফিয়ৎ অবাধ্যতার লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতেন, এবং উৎসবের পর পাঠশালা খুলিলেই, অপরাধী ছাত্রকে সম্মুখে ডাকিয়া, তাঁহার হস্তস্থিত সুদৃঢ় বেত্রদণ্ড পুনঃ পুনঃ আস্ফালন পূর্ব্বক চক্ষু পাকাইয়া বলিতেন, “পয়সা নেই ত আমি কি জানি! পয়সা নেই বলে কি আমি আমার ন্যায্যগণ্ডা ছেড়ে দেব? পয়সা নেই ত পাঠশালায় মরতে এসেছিস্ কেন? যা গরু চরাগে। ভাল চাস্ ত যেখানে পাস, সেখান থেকে সিধে আর পয়সা জুটিয়ে আনিস্; হাত পা আছে, চুরি করতে পারিসনে? ফাঁকি দিয়ে বিদ্যে শিখবি, আমি তেমন গুরুমশায় নই।”- দেখিলাম, বড় কঠিন স্থান, পূজা মানত করিয়া কালীঠাকুরাণীকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিতে গেলে হাতে হাতে ফল ভোগ করিতে হয়। সেকালের এ দেবতাগুলি এমনি জাগ্রত ছিল!” (Book Review)
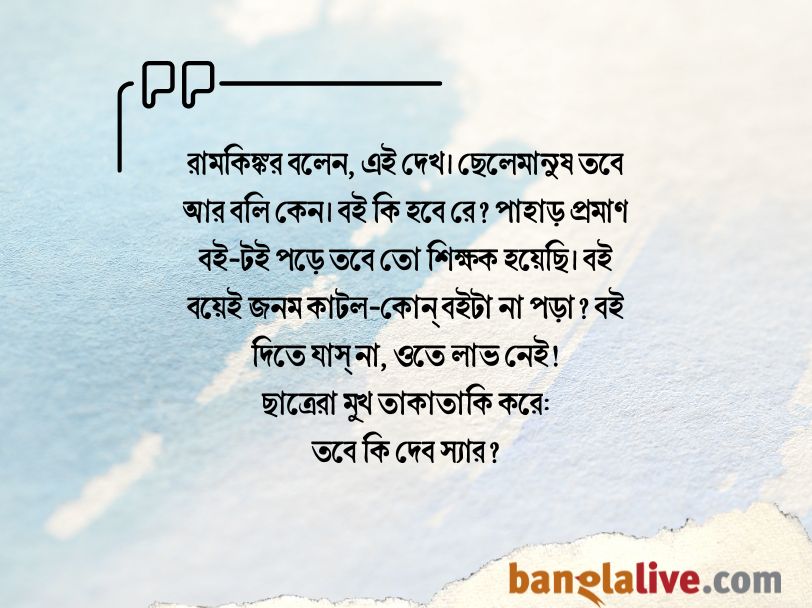
আশা করি ইদানীং স্কুলের শিক্ষক এবং গৃহ শিক্ষককে বা একই দেহে যিনি দুই রূপ তাঁকে কসাই বলার আগে, ‘প্রফেশনাল’ কথাটি ভুল অর্থে প্রয়োগের আগে এই চিত্রটি আমাদের স্মরণে থাকবে। আজকের শিক্ষকই শুধু ফাঁকিবাজ, একএকটি অর্থপিশাচ একথা বলবার আগে এই উত্তরাধিকার যেন বিস্মৃত না হই। (Book Review)
সেকালে দিনে দু’বার পাঠশালা বসত। সকালে পাঠশালার নিকটের পুষ্করিণী থেকে স্নান করে নামতা পড়ে ছুটি। তারপর আবার বিকেলে পাঠশালা খুলত। পুজোয় এবং বর্ষায় পাঠশালা বন্ধ থাকত। প্রথমেই কাগজে লেখার অধিকার ছিল না। আগে মাটিতে আঁক কাটা, তারপর তালপাতায় লেখা, এরপর কলাপাতায় লেখা। তারপর উপযুক্ত সিধার বিনিময়ে কাগজে লেখার সুযোগ মিলত। অনেকেই কালি বাড়িতে প্রস্তুত করত। হরতুকি বহেড়া, তার সঙ্গে বাবলার ছাল জলে ভিজিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে কালো করে নিতে হত। (Book Review)
আরও পড়ুন: যেভাবে রচিত, ব্যর্থতার এলাহি আয়োজন
লোহার কড়াইতে জল দিয়ে সেগুলি ফুটিয়ে হীরাকষ চূর্ণ ঘুটিয়ে কালি প্রস্তুত করা হত। একে অনেকেই বলত ইংরেজি কালি। এছাড়াও কলাপাতায় লেখার জন্য ছিল ঝিউনীর কালি। হাঁড়ির নীচের কালি কাঠখোলায় ভেজে সম্পূর্ণ পুড়ে গেলে একটি নেকড়ায় বেঁধে বড় পাথরের বাটিতে রাখতে হত ভিজিয়ে। তারপর তাতে বাবলার আঠা ও কলাগাছের রস দিয়ে কালি প্রস্তুত করা হত। কলাপাতা বা তালপাতা ধুয়ে নিয়ে অনেকবার ব্যবহার করা যেত। আগেই বলেছি গুরুমশাইদের লোভ ছিল সীমাহীন। দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখছেন পাঠশালায় গোবিন্দ আসেনি বলে গুরুদেব তাকে উত্তম প্রহারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তার উত্তরে গোবিন্দ যখন বলে, ‘আমি তো ইচ্ছে করে দেরি করিনি, আপনি কাল বাবার মশলা দেওয়া ভাল অম্বুরী তামাক চুরি করে আনতে বলেছিলেন, তা বাবা কাছারি না বেরুলে ত তা আনতে পারিনে, সেই জন্যে একটু দেরি হয়ে গেল।’ এই এক উৎকোচেই শাস্তি মুকুব। (Book Review)
আজ প্রায়শই একটা কথা ওঠে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও অধ্যাপকের অধীনে গবেষণা করেন তাঁদের অনেক রকম তোষামোদ করতে হয়। টাকা দিতে হয়, গয়না কিনে দিতে হয়, এমনকি বাড়ির বাজার করে দিতে হয়। গুপ্তচর হয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। সেকালেও পণ্ডিতদের একাধিক চর ছিল তবে তা প্রকাশ্যে। আজ পরিস্থিতি বদলেছে। যিনি যত অক্ষম ও অনুৎপাদক তাঁর গুপ্তচর তত বেশি। তিনি সহজেই ছাত্রী, ইদানীং ছাত্রকেও যৌন নির্যাতন করেন। ক্ষমতা তার প্রধান অস্ত্র। শিক্ষক সংগঠন তাঁর মুখোশের হাতিয়ার। ছাত্রছাত্রীর হৃদয়ে তিনি বিছানাবল্লভ হয়ে স্মরণীয় আসন পাতেন। (Book Review)
আজ থেকে এক দেড়শ বছর আগের এক চিত্র ‘দাসী’ পত্রিকা থেকে তুলে দিই। দেখবেন সেই একই ঐতিহ্য ও পরম্পরা “আমাদের গুরুমহাশয় পাঠশালায় আসিবার সময় বাজার খরচা সঙ্গে লইয়া আসিতেন। অবশ্য সকালকার পাঠশালার অধিবেশনেই এরূপ করিতেন। প্রায়ই স্কুলের নিকটবর্তী পথ দিয়া বাজারে মৎস্য, তরকারী, ইত্যাদি যাইতেছে দেখা যাইত, অমনি গুরুমহাশয় আমাদিগকে নামতা পড়িতে হুকুম দিতেন। নামতা পড়া শেষ হইলেই আমাদের ছুটি হইত। (Book Review)
“আজ যে দুর্নীতি নিয়ে কথা উঠছে, অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কথা উঠছে সে আমলেও তাহলে, তা ছিল। শুধুমাত্র তোষামোদের বলে অযোগ্যদেরই অধিকার ছিল বোধহয় সবচেয়ে বেশি।”
আমাদের মধ্য হইতে পর্যায়ক্রমে ২/৩ জনকে প্রত্যহ গুরুমহাশয়ের সহিত বাজারে যাইতে হইত এবং তাঁহার ক্রীত জিনিষাদি তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইত। ২/৩ জন বাদ্যকরের ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। গুরুমহাশয়ের বাড়ীতে কোন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেই ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে যাইয়া বিনা পয়সায় গুরুমহাশয়ের বাড়ীতে বাজাইয়া দিয়া আসিতে হইত। জন কয়েক ঘরামির ছেলেও আমাদের সঙ্গে পড়িত। বর্ষাকালে গুরুমহাশয়ের ঘরের খড় উড়িয়া গেলে ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে যাইয়া ঐ ঘর মেরামত করিয়া দিয়া আসিতে হইত। এইরূপে ধোপাকে বিনা পয়সায় কাপড় কাচিতে হইত, নাপিতকে কামাইতে হইত- ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের সুবিধা আমাদের গুরুমহাশয়ের ছিল। (Book Review)
(দাসী /অক্টোবর,১৮৯৫/শ্রী রাসবিহারী সেন)
আজ যে দুর্নীতি নিয়ে কথা উঠছে, অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কথা উঠছে সে আমলেও তাহলে, তা ছিল। শুধুমাত্র তোষামোদের বলে অযোগ্যদেরই অধিকার ছিল বোধহয় সবচেয়ে বেশি। তাই বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন সেইসময়ের বিভিন্ন লেখক তাঁদের স্মৃতিকথায় ও রিপোর্টে: (Book Review)
“এডেড্ স্কুলের মাষ্টারীতে বড় আঁটা আঁটী নাই, মাষ্টার হলেই হল। কালেজ, হাইস্কুলে প্রায় মেকী চলে না, বড় আঁটুনী, বিএ এমের ভাগ বেশী, আইবুড়োর কলকে পাওয়া ভার। পূর্ব্বেই বলেছি এর অবারিত দ্বার, সম্পাদক খুড়ো হর্তা কর্তা বিধাতা, যা মনে করেন তাই করতে পারেন। বাঙ্গালী ভায়ারা ভারী খোশামোদের বশ, এডেড্ স্কুলের মাষ্টারী করতে হলে, একাযে বিশেষ প্রফিসিয়েনসী চাই, তা নৈলে প্রায় ঘটে না। মেম্বর মহাশয়দের খোশামোদ বারামোদ করে একবার ঢুক্তে পারলে অটুট্ চাকরী। এখানকার মাষ্টার পণ্ডিত প্রায় ম্যানেজারদিগের আপনার লোক, সুতরাং যেমন তেমন হউক না কেন কোন কথাই নাই। কথায় বলে “ভগ্নিপোত মুচ্ছুদ্দি হলে শালা আগে ক্যাশিয়ার হয়”, এ নজিরে অনেকে এডেড্ স্কুলের মাষ্টারী পদ পেয়েছেন দেখা যায়। এদিগে ভাল বটে, কিন্তু খোশামোদ করতে করতে প্রাণ যায়।… (Book Review)
“সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হয়ে চলেছে পড়াশোনার মানের মেধায়। অথচ আজ এই বিষয়গত মেধার দুর্নীতি নিয়ে কোনও কথা নেই। যা আর্থিক দুর্নীতির থেকেও ভয়াবহ।”
মাষ্টারী কায গোঁজায় মেলে না, এতে বিদ্যা চাই, পেটে কিছু না থাকলে একায নির্ব্বাহ করা কঠিন, সুদু চালাকীতে চলে না। অনেক পড়া শুনার আবশ্যক, “মাছী মারা” কপিয়িৎ ক্লার্ক নয় যে যা দেখলাম তাই লিখে দিয়ে খালাস। ছেলে পড়াতে হলে মাষ্টারপণ্ডিতের উচিত, বিদ্যালয়ে যা পড়াবেন বাড়ীতে সেটা দেখে আসা। পচা আদার ঝাল ভারী, কেবলা মাষ্টারের অভিমান পেট পোর, পাছে ছেলের কাছে মান যায়, কিন্তু (There are ups and downs if life) কেউ কেউ অল্প দিন বাঁচে, কেউ অধিক দিন বাঁচে, পড়িয়ে মানের গোড়ায় ছাই দিচ্ছেন তা জানেন না। এডেড্ স্কুলে এরূপ কেবলা মাষ্টার অনেক। বাবাজীদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রায় “লীলাবতীর নদের চাঁদের মত,” কাঁচা পাকায় বিলক্ষণ পটু, পরবে সরবে “মামার বাড়ী” যেতেও ছাড়েন না। রাগও তেমনি, বদ্দিনাথের এঁড়ের মত দক্ষিণ পা তুলে মধ্যে মধ্যে ছেলেদের আশীর্ব্বাদ করতেও দেখা গিয়াছে। নিতান্ত খোশামোদের বশ হয়ে এরূপ মাষ্টার পণ্ডিতের হাতে অধ্যাপনা কার্য্য সমর্পণ করা নিতান্ত গর্হিত কায কেনা স্বীকার করবেন? এতে বিদ্যালয় দেশ ও বিদ্যার দুর্নাম মাত্র।… (Book Review)
বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদন যাঁদের হাতে, তাঁদের দেখে শুনে মাষ্টার পণ্ডিত নিযুক্ত করা উচিত, খোশামোদের বশ হয়ে বা সুপারিশের অনুরোধে যাকে তাকে মাষ্টারী কার্য্যে নিযুক্ত করিলে সমাজের উন্নতি বর্দ্ধন করা হয় না, বরং তাতে সমূহ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। (Book Review)
(হক্ কথা/ প্রথম কোপ/ এডেড্ স্কুল/ হালিসহর পত্রিকা/ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ)
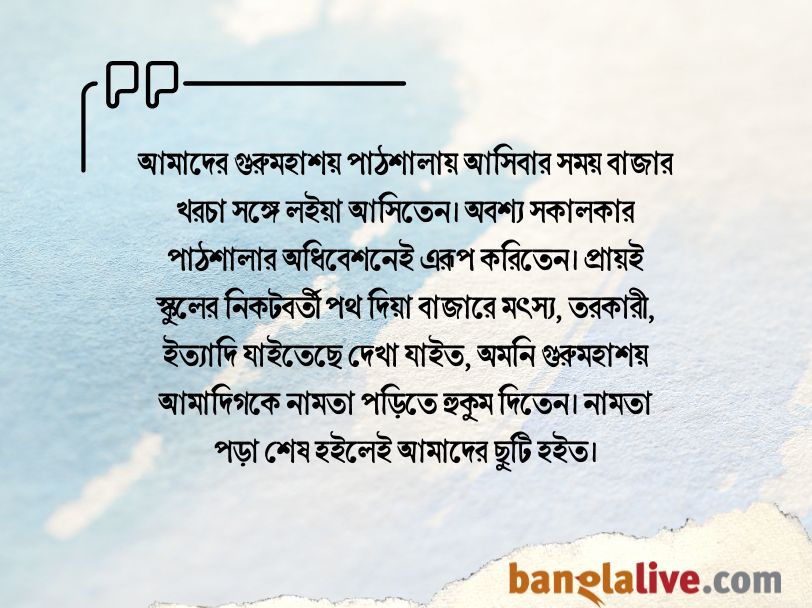
এইমুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি শতাংশ শিক্ষক অনুৎপাদক সম্পদ। মৌলিক কোনও চিন্তা ছাড়াই দিন গুজরান করছেন। সবচেয়ে বড় দুর্নীতি হয়ে চলেছে পড়াশোনার মানের মেধায়। অথচ আজ এই বিষয়গত মেধার দুর্নীতি নিয়ে কোনও কথা নেই। যা আর্থিক দুর্নীতির থেকেও ভয়াবহ। যা সমূলে শিকড় উপড়ে নিচ্ছে, শিক্ষার মেরুদণ্ডে আঘাত হানছে গত চল্লিশ বছর। আজ একজন শিক্ষক ক্লাসে যান কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই। (Book Review)
“আন্তর্জাতিক সেমিনারের নামে গরু পাচার চক্র চলেছে। এপারের গরু ওপারে যায়, ওপারের গরু এপারে এসে বক্তৃতা দেয়। শুধু খাওয়া দাওয়া আর মোচ্ছব। আর সার্টিফিকেট নিয়ে প্রোমোশন বৈতরণী পার। এখন তাঁর সমস্ত সক্রিয়তা গৃহশিক্ষকের উদবৃত্ত অর্থে।”
মধ্যমমানের বা নিম্নমানের লেকচার দেন। সেই দুর্নীতির বিচার করবে কে? দীর্ঘ পচিশ বছর কলেজ এবং বিদ্যালয়ের স্টাফরুমগুলোতে দেখেছি শিক্ষকদের আলোচনার পরিসরটি। সেখানে ছাত্র ব্রাত্য, পড়াশোনা ব্রাত্য। এইমুহূর্তে অধিকাংশ শিক্ষক শেয়ার বাজার, ফ্ল্যাটের দাম, বর্ধমানের বালি, নলহাটির পাথর, চালানি মাছের বিষ ইলেকট্রনিক গ্যাজেট, মাচার পটল-জমির পটল, বাড়ির বাস্তুবিচার-সব বিষয়ে আপ টু ডেট। শুধু নিজের সাবজেক্টে ডিগ্রি লাভের পর আর নতুন কিছুই জানেন না। নতুন বই কেনার নাম নেই। একই সিলেবাসকে নতুন দৃষ্টিতে পড়ানোর ভাবনা নেই। (ও তো সবই জানা আছে, একই সিলেবাস)। অতিরিক্ত পড়াশোনায়, নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবনায় আগ্রহ নেই। বেশির ভাগ শিক্ষকের বাড়িতে একটি সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত লাইব্রেরি নেই। (Book Review)
সিলেবাস বদলালে বাজারে রেফারেন্স বই না আসা পর্যন্ত তাঁরা কার্যত অচল। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাদল সরকারের ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকটি পাঠ্য হয়েছিল। শুধুমাত্র রেফারেন্স বইয়ের অভাবে শিক্ষকরা পড়াতে পারছেন না বলে তা সিলেবাস থেকে বাদ দিতে হয়েছিল। অতি সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শঙ্খ ঘোষের ‘শব্দ আর সত্য’ বাদ গেল। শুধুমাত্র হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে কয়েকশো শিক্ষকের ন্যূনতম ধারণা নেই বলে। অথচ এভাবেই চলছে। এভাবেই চলবে। শুধু কুড়ি শতাংশ শিক্ষকের অসামান্য মেধা আর দায়িত্ববোধে টিকে আছে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা। না হলে ছাত্রের যেকোনো প্রশ্ন তাঁদের কাছে ঔদ্ধত্যের সমার্থক। সম্প্রতি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের প্রোমোশনের জন্য যুক্ত হয়েছে অহেতুক সেমিনার। (Book Review)
আন্তর্জাতিক সেমিনারের নামে গরু পাচার চক্র চলেছে। এপারের গরু ওপারে যায়, ওপারের গরু এপারে এসে বক্তৃতা দেয়। শুধু খাওয়া দাওয়া আর মোচ্ছব। আর সার্টিফিকেট নিয়ে প্রোমোশন বৈতরণী পার। এখন তাঁর সমস্ত সক্রিয়তা গৃহশিক্ষকের উদবৃত্ত অর্থে। (Book Review)
“‘পথের পাঁচালী’ পাঠশালায় অপু অংশটি রয়েছে অথচ ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসের কোনও চিহ্ন নেই। একই কথা বলা চলে, মনোজ বসুর ‘মানুষ গড়ার কারিগর’ উপন্যাস সম্পর্কেও।”
বইটির দ্বিতীয় অংশে আছে কয়েকটি ছোটগল্প এবং উপন্যাসের প্রয়োজনীয় অংশ। প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত তার বিস্তার। হয়তো আয়তনের কারণেই এই অংশটি সংক্ষিপ্ত। না হলে আরও অজস্র গুরুত্বপূর্ণ লেখার কথা বলাই যেত। ‘পথের পাঁচালী’ পাঠশালায় অপু অংশটি রয়েছে অথচ ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসের কোনও চিহ্ন নেই। একই কথা বলা চলে, মনোজ বসুর ‘মানুষ গড়ার কারিগর’ উপন্যাস সম্পর্কেও। আর তৃতীয় ভাগটি নানা পরিসংখ্যান এবং শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট নিয়ে তৈরি। সেখানে বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা থেকে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের অনুপাত এবং শিক্ষকদের বেতন সবই আছে। এই প্রসঙ্গে সেকালের পাঠশালার শিক্ষকদের বেতনের একটি ছোট্ট পরিচয় উদ্ধৃত করি। (Book Review)
“পাঠশালার গুরুমশাইদের বেতন ছিল খুবই অল্প। স্থায়ী বেতন বলতে তাঁরা কিছুই পেতেন না। যে সকল উৎস থেকে তাঁরা আয় করতেন তা হোল
(ক) জমিদার, জোতদার বা মহাজনদের অনুদান বা মাসিক ভাতা।
(খ) ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব থেকে সম্মানীয় উপহার।
(গ) জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্ত্যিক উপহার।
(ঘ) ছাত্রদের কাছ থেকে সংগৃহীত বেতন।
(ঙ) গুরুমহাশয়দের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ প্রদত্ত ‘সিধা’।
(চ) গুরুমহাশয় ধর্মীয় উপাসনার ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকলে একসঙ্গে দুই ক্ষেত্র থেকে আয়।
(ছ) গুরুমহাশয়দের একইসঙ্গে শিক্ষকতা ও অন্যান্য ব্যবসাতে লিপ্ত থাকায় আয়।
[‘পথের পাঁচলি’তে প্রসন্ন গুরুমশায়] (Book Review)
আরও পড়ুন: দেশভাগ আর কৈশোরক স্মৃতির আখ্যান
এই হল আমাদের শিক্ষকের যোগ্য ও অযোগ্যের পরম্পরা। ঐতিহ্য ও বিস্তার। তাই কথায় কথায় আমাদের সময় মাস্টারমশাইরা, আমাদের সময়ের পাঠকেরা, নিজের দিকে ঝোল টানার আগে এই চিত্রটি যেন মনে থাকে। যেন মনে থাকে আধুনিককালে একইরকম কৌশলে মেধার দুর্নীতি হয়ে চলেছে বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলিতে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘তেঁতুল পাতার ঝোল’ উপন্যাসটি হয়তো তার সাক্ষ্য দেবে। বাকি সাক্ষ্য রয়েছে ট্রেনে- বাসে, ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের কথোপকথনে। (Book Review)
স্কুলে এবং কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছে। ছাত্রছাত্রীদের অভাবে অজস্র স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে। সেকালে লোভে পড়ে দরিদ্র পন্ডিতমশাই ছাত্রদের চৌর্যবৃত্তিতে উৎসাহ দিতেন। আজকের শিক্ষক চৌর্যবৃত্তির সমস্ত অধিকার নিজের হাতে রেখেছেন তফাৎ শুধু এটুকুই। আজ তিনি ‘কঠোর বিকল্পের কোনো পরিশ্রম নেই’ একথা জেনেই স্টাফরুমে ভাতঘুমটি সেরে নিচ্ছেন। (Book Review)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
জন্ম ১৯৭৭। লেখা শুরু নব্বইয়ের দশকে। পঞ্চাশের বাংলা কবিতার আতিশয্যর বিরুদ্ধে এযাবৎ কিছু কথা বলেছেন। ভ্রমণে তীব্র অনীহা। কিংবদন্তি কবির বৈঠকখানা এড়িয়ে চলেন। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - বিষণ্ণ দূরের মাঠ চার ফর্মার সামান্য জীবন, উদাসীন পাঠকের ঘর, লালার বিগ্রহ, নিরক্ষর ছায়ার পেনসিল, নাবালক খিদের প্রতিভা। গদ্যের বই- নিজের ছায়ার দিকে, মধ্যম পুরুষের ঠোঁট। মঞ্চ সফলতা কিংবা নির্জন সাধনাকে সন্দেহ করার মতো নাবালক আজও।