ফেসবুক আর হোয়াটস্যাপ আসার পর দুনিয়াটা আর আগের মতো নেই৷ গত কুড়ি বছরে বদলে গেছে সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের রসায়ন তথা শিল্পমাধ্যমগুলির হালচাল। ‘বাংলা গানে সময়ের থাবা‘ নামের এই ধারাবাহিকের আগের পর্বে (পর্ব ৩) বাংলা ব্যান্ড প্রজন্মের কথা লিখেছলাম। সে প্রজন্ম পেরিয়ে আমরা ঢুকে পড়ব এবারে ডিজিটাল প্রজন্মের গানবাজনায়।
ডিজিটাল যুগান্তরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ প্রজন্মে যেমন বদলেছে গানের বিষয়, তেমনই বদলেছে উপস্থাপনার অভিনবত্ব। ব্যান্ডের জন্য অনিবার্য ছিল মঞ্চের পারফরম্যান্স, এখন তা বদলে হয়েছে ইউটিউবের পর্দা। সে পর্দায় সাবক্রাইব করলে শুনে ফেলা যাবে বড়-মেজো-ছোট সমস্ত শিল্পীদের গান এবং ‘ভিউজ‘ যে শিল্পীর যত বেশি ততই মিডিয়া কভারেজ বাড়বে তাঁর। অবশ্য এই বদল শুধু এতেই থামল না, গান ছড়িয়ে পড়ল র্যাপের তির্যকতা থেকে স্ট্রিট হকিং হয়ে রুফটপেও। গোলপার্কের মোড়ে গিটার হাতে গান করে খাবার বিক্রি হোক বা বাড়ির ছাতের পরিসরে রীতিমতো পাকাপোক্ত অনুষ্ঠান– দুনিয়াকে টেক্কা দিয়ে কলকাতা যথারীতি আবার বলে উঠল, বিশ্বসঙ্গীত আন্দোলনের নিরিখে কোনওভাবেই পিছিয়ে নেই আমরা…
বারবারই নতুন শিল্পমাধ্যমকে দু’হাত বাড়িয়ে আপন করেছে কলকাতা। বাঙালি পকেটের পয়সা খরচ করে দেখেছে নতুন সিনেমা বা ছবির প্রদর্শনী, শুনেছে নতুন গান। নতুন প্রজন্মের হাত ধরেই এসেছে নতুন নতুন মাধ্যমও। নব্বইয়ের বিশ্বায়নের পর থেকে ক্রমশই একটা ডিজিটাল প্রজন্মও তৈরি হয়েছে। এই প্রজন্ম সিনেমা দেখে নেটফ্লিক্সে, গাড়ি ডাকে উবর বা ওলাতে, আড্ডা দেয় ফেসবুকে আর খাবার আনায় সুইগিতে। এদের প্রকাশের ভাষা তো আলাদা হবেই! এমনই মনে করছেন সমাজতাত্ত্বিকেরাও। তবে মজা এটাই, তিনশো বছরের এই শহরে, প্রকাশ আলাদা হলেও একেবারে ছিন্নমূল না তারা। শেকড় ধরেই বেড়ে উঠছে এ প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়েই…
গোলপার্কের দেওয়ালের গ্রাফিতিগুলি পেরিয়ে কিছুদূর এগোলেই আপনি দেখতে পাবেন হাতে গিটার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কয়েকজন যুবক। সামনের সাইকেলে স্যান্ডউইচ ঝুলছে। গান গেয়ে সেগুলি বিক্রি করছেন তাঁরা। স্ট্রিট মিউজিক এভাবেই ছড়াচ্ছে তাঁদের হাত ধরে কলকাতায়। লেক হোক বা নন্দন চত্বর বা পার্ক স্ট্রিট- এমনই অনেক যুবককেই আপনি দেখবেন প্রতিদিন। তাঁদের ঘিরে রয়েছে আগ্রহী জনতা। ‘মিউজিকাল স্যান্ডউইচ‘ নামের এমনই এক অভিনব উদ্যোগের পুরোধা নীলাঞ্জন সাহা। জানালেন, লেকের সামনে তাঁরা প্রতিদিন বিক্রি করছেন খাবার। মাঝে কিছুদিন লকডাউনে বন্ধ ছিল যদিও। লেকে আসা যুগল হোক বা রামকৃষ্ণ মিশনে আসা প্রৌঢ়, সকলেই হাঁটাচলার পথে থমকে দাঁড়িয়েছেন কিছুটা সময় তাঁদের গান শুনে। কথা বলেছেন। মিলিয়েছেন গলাও। প্যাশান আর পেশা মেলাতে গিয়েই এমন উদ্যোগের কথা মাথায় এসেছিল নীলাঞ্জনের। বিদেশে বহুকাল ধরে প্রচলিত এই ফর্ম। তা হলে কলকাতায় কেন হবে না? পার্ক স্ট্রিট এলাকায় শুভ্রজ্যোতি ও তাঁর বন্ধুও ভায়োলিন বাজিয়ে চলছিলেন রাস্তায়। দীর্ঘদিন ধরেই তো ট্রেনে-বাসে গান করেন বাউলরা। শহরে যদি সেই ফর্মকেই নিয়ে আসা যায়? আর তার সঙ্গে আসে কিছুটা হাতখরচও?– সতর্ক প্রশ্ন নীলাঞ্জনের।
কথা হচ্ছিল খ্যাতনামা ব্যান্ড চন্দ্রবিন্দুর সদস্য উপল সেনগুপ্তের সঙ্গে। বাংলা ব্যান্ড ফরম্যাটে বুদ্ধিদীপ্ত লিরিক এবং হিউমরকে বাঙালির সামনে এনে জনপ্রিয় করেছিলেন তাঁরা। এই নতুন ফর্মকেও স্বাগত জানালেন উপল। কিছুদিন আগে রুফটপ কনসার্ট প্রথম কলকাতায় জনপ্রিয়তা পেয়েছে তাঁর হাত ধরেই। “আমাদের ছাতে” নামের সেই কনসার্ট থেকে উঠে এসেছেন একাধিক শিল্পী।
“কীভাবে এল এই আইডিয়া?” উপলদার জবাব, “ছাতে গানবাজনা করার রেওয়াজ তো নতুন কিছু না। যে কোনও অনুষ্ঠানেই এই হুল্লোড় চলে বাঙালির। প্যান্ডেল বাঁধা হয়। আমার বাড়িতেও সবসময়েই চলে আড্ডা-হুল্লোড়। তো, একদিন এভাবেই কথা হচ্ছিল নতুন মিউজিশিয়ানদের নিয়ে। এখন তাঁদের আর তেমন প্রমোট করছে না এফএম চ্যানেলগুলো। তাহলে তাঁরা কোথায় প্ল্যাটফর্ম পাবেন? কীভাবে নিজেদের গান শোনাবেন? ভাবতে ভাবতেই আইডিয়াটা এল।”
পর পর বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল রুফটপে গানবাজনার। হালফিল শহরতলিতেও হচ্ছে এ ধরনের ইনফরমাল অনুষ্ঠান। সে নৈহাটিই হোক বা চুঁচুড়া। অনু্ষ্ঠানের ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে মুহূর্তে। ছাতের এই অভিনব আয়োজনে পরিচিতি পেয়েছেন দেবদীপ। হেসে জানালেন, “যার কেউ নেই তার রুফটপ আর ইউটিউব আছে।” একই কথা বললেন আর এক শিল্পী সুলগ্নাও। জানালেন, যখন ছাতে ঘিরে থাকেন বন্ধু-পরিচিতরা, জ্বলে ওঠে একে একে টুনি হলুদ-সবুজ, তখন একটা আলাদা আনন্দ হয় গাইতে। এই সমবেত অনুভবে আত্মবিশ্বাসটাই অন্য মাত্রায় চলে যায়।

ফেসবুক ও ইউটিউবেও প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে নতুন শিল্পীদের গান। কখনও পুরোনো জনপ্রিয় গানকে তাঁরা ফিরিয়ে আনছেন আবার কখনও গাইছেন নিজেদের রচনাও। তারপর নিজেরাই আপলোড করে দিচ্ছেন। এরা কেউই গান গেয়ে বিখ্যাত হতে চান না। নেহাত ভালোলাগা থেকে গান আপলোড করেন ফেসবুকে। কখনও ইউটিউবেও। ইউটিউব থেকে রোজগার করা গেলেও, তাঁরা অনেকেই তা চান না তেমন। শুধু চান গানগুলি ছড়িয়ে যাক।
যেমন ধরা যাক লিমন আর মিমির কথা। একসঙ্গে ক’দিন আগে গাইছিলেন ‘অলিরও কথা শুনে বকুল হাসে..‘ গাইতে গাইতে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সে চাহনি দেখে মানুষ থমকে যান। কারণ, সুরের মতোই সেই তাকানোয় ছিল পবিত্রতা, ভালোবাসা। গাইছিলেন ‘আকাশ পারের ওই অনেক দূরে/ যেমন করে মেঘ যায় গো উড়ে..‘। অর্চন আর মৈত্রীর একসঙ্গে গাওয়া গানগুলিও মূলত এ প্রজন্মের নানা ভাষাকে ধরেই বানানো। শুধু একটা গিটার বা কখনও একটা পিয়ানোয় গান বাঁধছেন তাঁরা। পেছনে থাক করে রাখা বই। একতালে গান গেয়ে যাচ্ছেন। বন্যপ্রেমের মতো সপাট অথচ সুরের ঔচিত্যে সুনিপুণ। ঝোঁকগুলো ঠিক ঠিক পড়ে এই বেতালা সময়েও। গানগুলি বাঁধেন অর্চন। কিছুটা হিউমার থাকে কখনও, কখনও থাকে পরিহাস। থাকে এ শহরের প্রতি দুর্মর ভালোবাসাও। ফিমেল ভোকালে হারমনি করেন মৈত্রী। বড় সুন্দর লাগে দুজনের সুরের এই বিন্যাস..
বাংলা গান তথা রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা ও উপস্থাপনা করে চলেছেন রাহুল মিত্র। পাশাপাশি সমকালের গান নিয়ে বরাবরই উৎসাহী তিনি। কেমন লাগছে তরুণদের উদ্যোগ? জানালেন, ‘গান মানুষের আবহমান প্রকাশের উপায়। এই প্রকাশ যেমন নিয়মিত অনুশীলন করে ধ্রুপদী সংগীতে করা যেতে পারে, তেমনি আনন্দের মধ্যে দিয়ে তারুণ্যের স্বাধীন স্বরের প্রকাশও গান। এই দ্বিতীয় ধারায় প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার প্রকাশও ঘটেছে চিরকাল প্রগতির লক্ষ্যে। তবে কার কতটা প্রস্তুতি সেটাও প্রশ্ন। নব্বইয়ের দশকে সুমন চট্টোপাধ্যায় (পরে কবীর সুমন) তাঁর সংগীতে মেধার ছাপ রাখলেন সলিল চৌধুরীর পর। পরবর্তীতে ব্যান্ডের মধ্যে দোহারের কাজ ভালো লেগেছে৷ ভালো লেগেছে চন্দ্রবিন্দুকেও। মহীনের ঘোড়ারা তো আছেনই। কিন্তু বেশিরভাগ ব্যান্ড অচিরেই ভাঙছে। তাই প্রশ্ন উঠছে, শিল্পে নিজেদের কতটা নিয়োজিত করেছেন তাঁরা? যৌথতার যৌক্তিকতাই বা কেমন ছিল? শিল্পের কার্যকারণ আছে কি? আজকের তরুণরা আবার ডিজিটালে প্রকাশ খুঁজছে। ‘তালপাতার সেপাই‘দের গান যেমন আমার ভালো লেগেছে। যে কোনও সৎ প্রচেষ্টা হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও এগোবে বলেই মনে করি। অন্তরের অনন্ত সন্ধানে নিয়োজিত থাকলে যে কোনও ধারার গান আবহমান হয়ে এসেছে চিরকাল…‘
ফেসবুক ও ইউটিউবেও প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে নতুন শিল্পীদের গান। কখনও পুরোনো জনপ্রিয় গানকে তাঁরা ফিরিয়ে আনছেন আবার কখনও গাইছেন নিজেদের রচনাও। তারপর নিজেরাই আপলোড করে দিচ্ছেন। এরা কেউই গান গেয়ে বিখ্যাত হতে চান না। নেহাত ভালোলাগা থেকে গান আপলোড করেন ফেসবুকে। কখনও ইউটিউবেও। ইউটিউব থেকে রোজগার করা গেলেও, তাঁরা অনেকেই তা চান না তেমন। শুধু চান গানগুলি ছড়িয়ে যাক।
দেবদীপ আর তমালিকা নানা পুরোনো গান নিজেদের মতো করে গেয়ে থাকেন তাঁদের চ্যানেলে। যেমন, ক’দিন আগে শুনছিলাম তাঁরা গাইছেন কবীর সুমনের ‘আমি তো ছিলাম বেশ নিজের ছন্দে‘ গানটি…। নিজেদের মতো করে যত্নে সুর বজায় রেখেই গাইছিলেন। গানের একটা পর্যায়ে আসে ‘কোথাও ছিলে না তুমি কেন তুমি এলে/ কেন গান এনে দিলে? কেন এনে দিলে?’ এ লাইনটি যখন তাঁরা গাইছিলেন, অপার জাদু তৈরি হচ্ছিল। মাঝেমাঝেই ইংরেজি গান গিটার নিয়ে গেয়ে একইভবে চমকে দেন সঞ্চারী ভট্টাচার্য। উপল সেনগুপ্তের গাওয়া নীলাঞ্জনের ‘তোমার প্রিয়‘ গানটি গাওয়ার সময় তাঁর কন্ঠে যেমন অপার প্রেম ছিল, তেমনই ছিল তাল। বড় মায়াবি তাঁর গায়ন…
এ ছাড়াও দুটি দল তাঁদের গান নিজেদের মতো করে গেয়ে চলেছেন। ‘এই সময়ের গান‘ নমের জোরালো এক রাজনৈতিক উচ্চারণ শুনলাম ক’দিন আগে ‘নো ভোট টু বিজেপি‘র ব্যানারে। র্যাপ আজকাল অনেকেই করেন। কিন্তু এ গানের গায়করা তার সঙ্গে মিউজিক আর ভিডিও-র মন্তাজে যে আশ্চর্য শক্তি বের করে আনলেন, তা বলার নয়। একইভাবে আবিষ্ট হয়েছিলাম ‘তালপাতার সেপাই’দের হ্যারি বেলাফন্টের সুর ধার করে বানানো ‘ফেয়ারওয়েল কলকাতা’ গানটি শুনে। দুই বন্ধু ঘুরতে গিয়ে নিজেদের মতো বানান এই গানের ভিডিওগুলি, তারপর সামাজিক পরিসরে ছেড়ে দেন। এত মায়াবি ওদের এই গানের সুর, বেগ পেতে হয়েছে এ গান থেকে বেরতেও।
আনকোরা এই শিল্পীদের গানে আজ সোনা ঝিকমিক আগামী। সে দিন বেশি দূরে নেই যখন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টেই গোটা শিল্পজগত ঢুকে পড়বে… আলাদা করে গান/কবিতা/সিনেমা/রাজনীতি থাকবে না। তার খারাপ দিক নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ভালো দিকটা বেশি চোখে পড়ে বরাবর। আর সেটা হল, বাধাহীনভাবে প্রতিশ্রুতিমান শিল্পীরা সরাসরি নিজেদের শিল্প তুলে দেবে আন্তর্জালে এবং তা থেকেই সময় খুঁজে পাবে তার বাতায়ন, তার নন্দন… যে জানলা হাত দিয়ে নয়, সুর দিয়েই একমাত্র খোলা যায়। আর এভাবেই বাংলা গানে আগামীর অনিবার্যতায় আত্মপরিচয় খুঁজে নেবে ভাবীকালের বাংলা। বারবার..
*ছবি সৌজন্য ফেসবুক ও টুইটার
পেশা মূলত, লেখা-সাংবাদিকতা। তা ছাড়াও, গান লেখেন-ছবি বানান। শখ, মানুষ দেখা। শেল্ফ থেকে পুরনো বই খুঁজে বের করা। কলকাতার রাস্তা ধরে বিকেলে ঘুরে বেড়ানো।



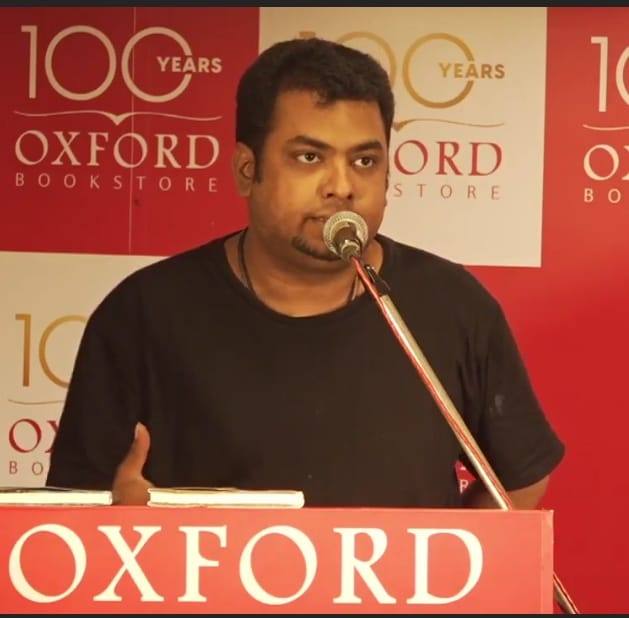






















One Response
বাহ! বেশ সুন্দর লেখা।