নব্বই দশক বললেই অজান্তে ভেসে ওঠে ক’জন মাঝবয়সীর মুখ যাঁদের একগাল দাড়ি আর হাতে একটা গিটার। স্বচ্ছন্দে ওঁরা লেখক বা সাংবাদিক হতে পারতেন, হতে পারতেন অ্যাকটিভিস্ট। বদলে ওঁরা গাইলেন গান। গান না বলে যদি বলা যায় তাঁরা কিছু কথা বলছেন, গানের মতো করে, কবিয়ালরা যেমন বলতেন, তাতে হয়তো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যাবে তাঁদের। বোঝাই যাচ্ছে, তীব্র রাগ আর শ্লেষ দিয়ে বিদ্ধ করছেন তাঁরা সমকালকে। আমাদের অবাক কৈশোর জানছে, ওঁদের পরিচয় ‘সংরাইটার’।
যে কলকাতার ফুটপাথে সারা দুনিয়ার বই পাওয়া যেত, বাদল সরকার মৌলালি মোড়ে নেমে আসতেন থিয়েটার করতে, উৎপল দত্ত অবলীলায় মঞ্চ থেকে এনকাউন্টার করতেন দর্শককে, মৃণাল সেন রেড রোডে শুয়ে ক্যামেরা ধরতেন, সেই আন্তর্জাতিক কলকাতার গল্পই বলছিলেন তাঁরা। সুমন তো তাঁর গানকে বলেইছিলেন, ‘বাংলা গানের গ্রুপ থিয়েটার’। কেন গ্রুপ থিয়েটার? কারণ, এই পারফরমেন্স স্রেফ ফাটকা বিনোদন নয়। বরং সিরিয়াস ‘লোকশিক্ষা’, ঠাস-ঠাস করে যা সুবিধেবাদের গালে থাপ্পড় কষাতে পারে। আবার ছাই ঘেঁটে দেখলে দেখা যাবে কোথাও একতিল মিথ্যে নেই…।
সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণালের সিনেমা ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিকতার যে পরম্পরা, তা ক্রমেই শুকনো নদীর মতোই মজে আসছিল। গণচেতনা যখন নেমে আসে তখন শিল্পী এসে সুতোটা ধরে তুলে দেন। সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স উইবারের এই কথাটাই যেন-বা প্রমাণ করলেন সুমন, নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় তাঁর আধুনিক বাংলা গানের অভ্যুত্থানে। প্রচলিত সমস্ত চিহ্নকে পরীক্ষা করতে থাকলেন তিনি ধারাবাহিকভাবে। মূলধারার বাজারে হঠাৎই বিকল্প আন্তর্জাতিক পরিসরের স্রোত এসে লণ্ডভণ্ড করল যা কিছু সুগোল, তাকেই। আশির দশক আপাতভাবে শূন্যতা ও রুগণতায় আক্রান্ত ছিল ঠিকই। সেভাবে ‘বড়’ ঘটনার অভাব। যদিও সমান্তরালভাবে সে মহীনের ঘোড়াগুলি তথা লিটল ম্যাগাজিন ও গ্রুপ থিয়েটারের দুনিয়ায় স্বতন্ত্র স্বর খুঁজে চলেছিল। সেখানে যেমন অনন্য রায়-দীপক মজুমদারের মতো লেখক-চিন্তকরা ছিলেন, তেমনই ছিলেন হিরণ মিত্র বা গৌতম চট্টোপাধ্যায়র মতো মাল্টি-ডিসিপ্লিনের শিল্পী।

ঋত্বিক ঘটকের আভাঁ-গার্দ পন্থায় সুললিত অর্ডারে গল্প বলার বদলে তাঁরা ভাঙচুরকেই শিল্প করে তুলছিলেন। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের ধারায় প্রতুল মুখোপাধ্যায় রাস্তাকেই করে তুললেন তাঁর মঞ্চ। সত্তর থেকেই আন্তর্জাতিক থিয়েটারের পরিসর প্রসারিত করছিলেন অঞ্জন দত্ত, নবারুণ ভট্টাচার্যরা। অঞ্জনের গানের চরিত্র মালা-বেলা-জয়িতা বা মেরিয়ান আর স্যামসনদেরও আজও আপনি দেখতে পাবেন ভোরের ফুলঘাটে। কিম্বা বো-ব্যরাকের বড়দিনে, যারা শনিবার দুপুরে এলআইসি করাতে আপনার দরজায় আসত। যারা ছিল আপনার ছেলেবেলার চ্যাপ্টা গোলাপ ফুল।
অঞ্জনবাবু যেন-বা ওদের ডকুমেন্ট করতেই এসেছিলেন। নিজের জীবন আর ওদের জীবনের গল্প বললেন জীবনভর। কোনও চিৎকার ছিল না এই ঘোষণায়। ছিল আপনমনে ভোরের কুয়াশায় লিটল রাসেল স্ট্রিটে ঘুরে বেড়ানো। আর, কখন যেন অজান্তেই এভাবে তিনি গেঁথে রাখলেন বিগত কয়েক দশকের কলকাতা। বিকল্প কলকাতা। এদের কথা বাঙালি পড়ত ফেলুদার গপ্পে। ফেলুদা দেখত এদের কারো বাড়ির দরজায় লেখা, কুকুর হইতে সাবধান। ফেলুদা তোপসেকে বলত, লেখা উচিত ছিল কুকুরের মালিক হইতে সাবধান।
এদের পাওয়া যেত সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। রোগগ্রস্ত অ্যাংলো মেয়ের সঙ্গে প্রণয়ের সময়। ঘোলাটে বিকেলে তিন মাসব্যাপী গোপন যোগাযোগ পার্ক স্ট্রিট সিমেট্রিতে। তারও আগে অবশ্য ওদের কথা লিখেছেন দীপেন্দ্রনাথ। অশ্বমেধের ঘোড়া-য়। সারারাত ঘর না পেয়ে এক বিবাহিত যুগলের স্ট্রাগলের গল্প, চল্লিশের কলকাতায়। সমর সেনের কবিতাতেও ভিড় করে এরা। বিনয় ঘোষের গদ্যেও। কবীরের ভাষায়, এঁদের, “গোপনীয়তার নেই মালিকানা”।
বস্তুত, বিশ শতক থেকেই দক্ষিণ কলকাতার আনাচকানাচ, বিশেষত রাসবিহারী মোড়-হাজরা মোড় সরগরম থাকত সদর্থে আন্তজার্তিক মননের বাঙালি আড্ডায়। ফ্রান্স বা রাশিয়ায় মেঘ করলে, ঝড়জল জমত দক্ষিণ কলকাতায়। এ বাঙালির পয়সা ছিল না। কিন্তু ভাবনায় তাঁরা ছিলেন আন্তর্জাতিক । সে কলকাতায় রেস্তোরাঁর নাম ছিল, বনফুল-সাঙ্গুভ্যালে-অমৃতায়ন-অলিম্পিয়া। বুদ্ধিজীবীর নাম ছিল অরুণ মিত্র-সমর সেন-বিনয় ঘোষ-রাধাপ্রসাদ গুপ্ত-সুবীর রায়চৌধুরী-বুদ্ধদেব বসু-নীহাররঞ্জন রায়-নীরদ চৌধুরী। অন্যদিকে, ঋত্বিক-বিজন-দেবব্রত-হেমাঙ্গ বিশ্বাসরা ভবানীপুর-কালীঘাট-রাসবিহারীজুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জোড়া গির্জায় বই বিক্রি করতেন নির্মলকুমার। সেসব পুরনো বই কিনতে হাজির হতেন সত্যজিৎ, শাঁটুলবাবু, কমলকুমার মজুমদার। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে খোঁচা মারতে ভোর ভোর তাঁর বাড়ি হাজির হয়ে জানাতেন, “সুনীল তোমায় কে বেশি গালি দেয়? আমি না শ্যামল গাঙ্গুলী?”
আজকের মতো ছেলেমেয়েরা খোলামেলা মিশতে পারত না সে কলকাতায়। বিয়ের আগে বাইরে একরাত্রি কাটানো ছিল বিপ্লব। অসম্ভব। ঠিক এর পরের দশকের মালা-বেলা-দেবলীনারা একরাত বাড়ি না ফিরলেও একইরকম চিন্তায় পড়তেন অভিভাবকরা। তাই নিয়ে সিনেমা করতেন মৃণাল সেন। নিশ্চয়তার অভাবে এই সব যুবতীরা বিয়ে করে মিসেস মুখার্জি হতেন। আর তাঁদের বেকার প্রেমিকদের নিয়ে অঞ্জন লিখতেন ‘প্রিয় বন্ধু।’ গৃহযুদ্ধ ছবিতে এইসব যুবকরা আবার চাকরি পেয়ে পয়সা কামালেও তাকে অস্বীকার করতেন মমতাশংকরের মতো চরিত্রেরা। কারণ সেই হিপি বা নকশাল আর এই কর্পোরেট এক নয়। তারপর রাস্তা পার হতেন মমতা একাই।

সেসব পেরিয়ে নব্বইয়ে এসে খবর কাগজের হেডলাইন থেকে গান পেড়ে আনতে লাগলেন সুমন। পলাশদা, বিশ্বরূপদা, ভবানীপুরের পাগল, রাস্তার বাঁশুরিয়া, বয়স্ক মধ্যবিত্ত বাবা, পাড়ার বন্ধু টুকাই, কানোরিয়া জুটমিলের শ্রমিকরা, কবি অরুণ মিত্র-সবকিছু, এই সবকিছুই আসলে গান তৈরির কাঁচামাল সুমনের। যে সমাজে সব ছেড়ে বারবার ফিরে এসেছেন তিনি। সুমনের একাধিক ব্যক্তিপ্রেমের গানও সেই সময়কে ঘিরেই, সমাজকে নিয়েই। সেগুলি আদপেই ব্যক্তিপ্রেমের না। শ্রোতারাও হলেন সুমনের গানের এক্সটেনশান। এবং এই আদান-প্রদান স্বাস্থ্যকর বাংলা গানের জন্য, বহুদিন যা ছিল না। কথাটা সুধীর চক্রবর্তীর।
আর, সুমনের গান আর সুমনও আদতে এক। কাজেই, শ্রোতা-সঙ্গীতকার-সমাজ কোথাও এক সুতোয় বাঁধা। তাই, তোমাকে চাই প্রকাশের এত বছর পরও, সময়ের সেই শিরা ধরে বসে থাকেন গানওলা। আমাদের ফিরে আসতে হয় এ সব গানের কাছে, আমরা খুঁজে পাই, “পরিযায়ী” শ্রমিকদের ভিড়ে “সঞ্জীব পুরোহিতকে”, আমরা শুনতে পাই পলাশদার ভয়ার্ত টেলিফোন আসন্ন দাঙ্গার পদধ্বনি শুনে, “সুমনদা, আমিনুলের কী হবে সুমনদা..” আর তারপর সুমন তা থেকে গান পেড়ে আনবেন, “পলাশের বাড়ি দত্তপুকুর…”
এ সব গান ঘিরে কত কত ছেলেমেয়ে পত্রিকা প্রকাশ করল, স্লোগান লিখল, কত কত প্রেম হল ও ভেঙে গেল, বদলে গেল কবিতার ভাষা-খবর কাগজের হোর্ডিং। একটা যুগ নিজেকে খুঁজে পেল ক্রমশ এরপর। আশির দশক থেকেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়র গান বারবারই মানবাধিকার তথা নাগরিক ও প্রান্তিক আন্দোলনের মুখপত্র হয়ে উঠছিল। সুরের ক্ষেত্রে বারবার তিনি সন্ধান চালালেন দেশ ও বিদেশের নানাবিধ ধ্রুপদী তথা লোকায়ত আঙ্গিকের দিকে।
মৌসুমী ভৌমিকের গান হল নাগরিক নারীর অন্তর্লোকের এক মার্জিত আধুনিক প্রকাশ। কাজি কামাল নাসেরও সুমনের ধারাকেই অনুসরণ করলেন। নচিকেতা তাঁর মতো করে হতাশ যুবকের রোজনামচার কথা শোনালেন। গজলে অনুরক্ত ছিলেন তিনি। দীক্ষিত ছিলেন ধ্রুপদী সঙ্গীতেও। তবু নাগরিক পড়ালেখা জানা মধ্যবিত্তকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করল সুমনের গান ও তাঁর উপস্থাপনা। বাংলা সংস্কৃতির মরা গাংয়ে এক রকম জোয়ারই এল সুমন-নচি-অঞ্জন-মৌসুমীদের সমাবেশে।
তবে, ‘সংরাইটার’ তকমাটা, যেখানে একজন মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ এসে মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে গিটার নিয়ে মানুষের কথাই বলছেন, তা কোথায় যেন হারিয়ে গেল ক্রমশ। সুমন বা অঞ্জনের যে নাগরিক পড়ালেখা জানা আন্তর্জাতিক মনন, তা আবার অনাধুনিক হয়ে পিছতে থাকল ক্রমশ। আসলে কবিরা তো দলবেঁধে আসেন না, কেউ কেউ আসে মাঝেমাঝে। অথচ বাজার বড় বালাই! আর, সুমন একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসে ঢুকে পড়েছিলেন বাংলাবাজারে। তাঁকে তাই আগেই ‘আউটসাইডার’ বলেছিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। সেই ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করতে গিয়েই হল সমস্যা। নিজের স্বকীয়তার বদলে বেশিরভাগ গায়ক তথা সংগীতকাররা সুমনকে অনুকরণ করতে শুরু করলেন।
কিন্তু সত্যজিৎ-ঋত্বিক নিজে স্ক্রিপ্ট লিখেছেন মানেই ফিল্মমেকার মাত্রেই নিজের চিত্রনাট্য নিজে লিখবেন, এটাই রেওয়াজ নয়। তেমনই সঙ্গীতের শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে কয়েকটি কর্ড বাজালেই যে তা আধুনিক বাংলা গান হবে না, একথা বুঝতে সময় লাগল অনেকের। কাজেই নব্বই-পরবর্তীতে সঙ্গীতের থেকে খানিকটা সরে মেধার জায়গাটা প্রতিস্থাপিত হল বাংলা থিয়েটারে। ব্রাত্য বসু-সুমন মুখোপাধ্যায়-কৌশিক সেনরা ধারাবাহিক ঘাত-প্রতিঘাতে আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্বকে তুলে আনতে লাগলেন বাংলা থিয়েটারে। ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ বা ‘তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত’ হয়ে উঠল সেই আধার।

অন্যদিকে, যৌবন নিজের মতো করে একটা স্পেস খুঁজে নিল বাংলা ব্যান্ডে। এল ‘চন্দ্রবিন্দু’, ‘ক্যাকটাস’, ‘ফসিলস’। আশির দশকে পাড়ায় পাড়ায় যেভাবে থিয়েটার হত, সেভাবেই নতুন শতকে বাংলা ব্যান্ড হয়ে উঠল যৌবনের আগুন। গান লেখা হল, ‘তুমিও বোঝো, আমিও বুঝি/ বুঝেও বুঝি না’ বা ‘স্নানের জলে লিখেছি ডাকনাম’। এবং এই গোটা আন্দোলনের পুরোধা, বলা বাহুল্য, তবু না বললেই নয়, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ব্যান্ড ‘মহীনের ঘোড়াগুলি।’
ফিনিক্স পাখির মতোই বিশ্বায়নের দাপটের মাঝে সত্তরের দশকের আগুন আরও একবার বেঁচে উঠল সময়ের প্রয়োজনেই। শহুরে আধুনিকতার রোজনামচা সিগারেটের কাউন্টার বদলের মতোই কাঁধ ঝাঁকিয়ে গেয়ে ফেলল যৌবন, কিছুটা বেসুরেই। তা ততটা গান হল না হয়তো, হয়ে উঠল ‘না-গান’। আর ঠিক সেই অ্যাটিটিউডই খুঁজে চলেছিল আমাদের প্রজন্ম, আজ থেকে দশ বছর আগে।
*ছবি সৌজন্য: Facebook, Indiatimes, Premiumbeat
*ভিডিও সৌজন্য: Youtube
পেশা মূলত, লেখা-সাংবাদিকতা। তা ছাড়াও, গান লেখেন-ছবি বানান। শখ, মানুষ দেখা। শেল্ফ থেকে পুরনো বই খুঁজে বের করা। কলকাতার রাস্তা ধরে বিকেলে ঘুরে বেড়ানো।











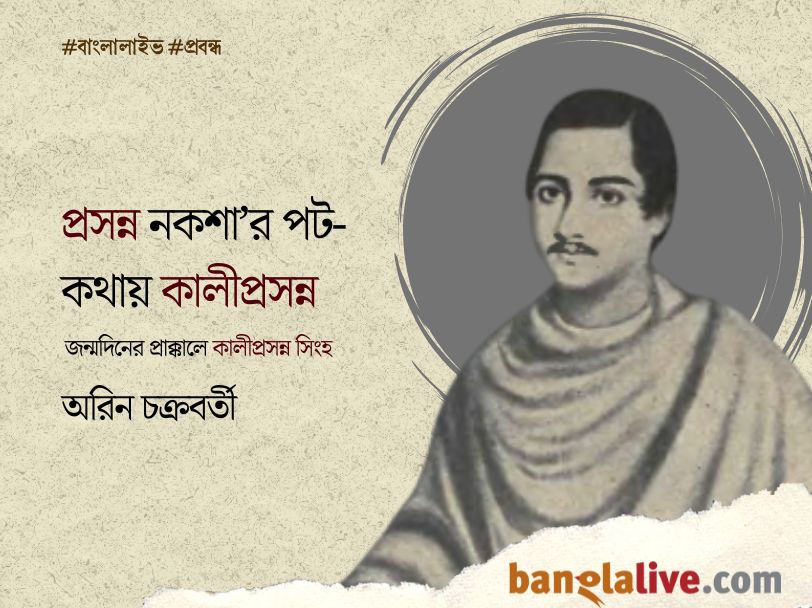








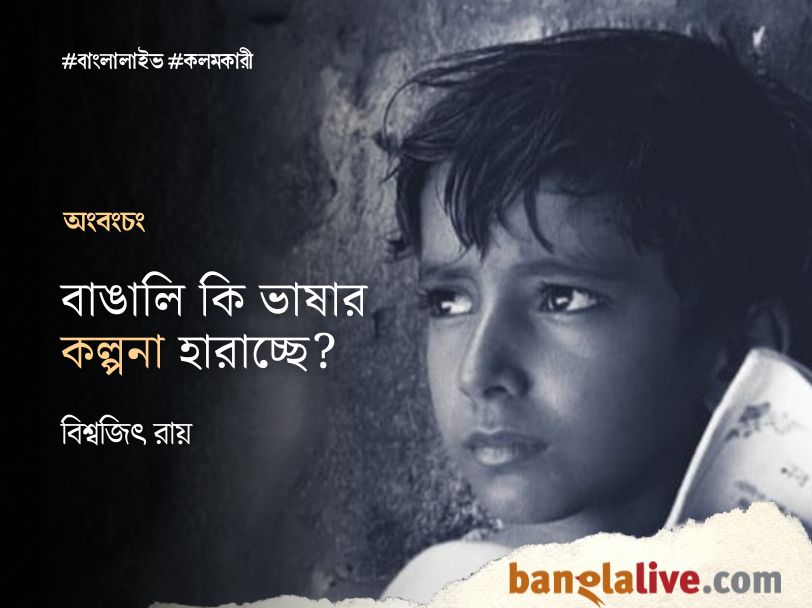





One Response
সুমনের গান মানেই হঠাৎ করে নিজের চিন্তা গুলোকে গান হয়ে উঠতে দেখা। রাস্তার পাগলও যে গানের বিষয় হয়ে উঠতে পারে তা সুমন দেখালেন। ছাপোষা মধ্যবিত্ত সমাজের ভণ্ডামি বারবার তাঁর গানের মাধ্যমে আমাদের গালে থাপ্পড় মেরেছে। আর বাঙালির রোমান্টিসিজম যে জাগিয়ে তুলেছেন অঞ্জন দত্ত। নচিকেতা সেই যুগের তরুণ তরুণীদের প্রেম এবং হতাশার জলজ্যান্ত ছবি এঁকেছেন গান দিয়ে। নব্বুইয়ের গান তাই শুধু গান নয়, হাতিয়ার আমাদের হাতের, স্বপ্ন দেখার নতুন চোখ ও বটে।