বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অরণ্যের বা প্রকৃতির যোগাযোগ সংবেদনশীল পাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু যে প্রশ্ন মনে আসে, তা হল, আজকের দিনেও, প্রায় এক শতাব্দী কেটে যাওয়ার পরে, বর্তমান পাঠকের নিরিখে বিভূতিভূষণের এই চেতনা কেন প্রাসঙ্গিক? বিভূতিভূষণের পৃথিবীর সঙ্গে বর্তমান জগতের বিস্তর অমিল। শতাব্দী পিছিয়ে দেখতে হবে না, প্রযুক্তিকেন্দ্রিক প্রগতির জেরে আমাদেরই ছোটবেলার পৃথিবীর সঙ্গেই এই পৃথিবী আর মেলে না। সকলেই অল্পবিস্তর সম্পন্ন হলেও, প্রকৃতপক্ষে পণ্যভোগী সমাজ প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে।
দুঃস্বপ্নলোকের মতো এক জগতে আমরা দ্রুত প্রবেশ করছি, যেখানে সব হিসাব উল্টেপাল্টে যায়: হিমবাহ গলে যায়, মেরুপ্রদেশে বরফ কমে আসে, অকালে অতিবৃষ্টিতে ভেসে যায় পথঘাট। তবু মানুষ এইসব দেখেও দেখে না, মুঠোফোনে চোখ রেখে ক্রমাগত বিনোদনে ভুলিয়ে রাখে নিজেকে। ভুলে যায় যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তাও এত দূষিত, যে তাকে পরিশ্রুত করে আনতে হয় যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। সমাজের নিয়ন্ত্রণ যখন পুরোই বাজারের হাতে, আর সমস্ত যন্ত্রনার উপশম হয়ে দাঁড়িয়েছে পণ্য, সেই উন্মত্ত ছুটে চলার যুগে বিভূতিভূষণের একশো বছর আগেকার প্রকৃতিচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়?
‘তৃণাঙ্কুর’ দিনলিপিতে লিখছেন বিভূতিভূষণ,
‘প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে…অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে। জ্যোৎস্নাভরা মাঠে, আকন্দ ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনা শুকনা সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী— মৃত, মূর্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।’
আধুনিক যুগের চেতনা যেখানে আরও মৃত ও মুর্ছিত হয়ে মুক্তি খোঁজে পণ্যের মধ্যে, আরও তলিয়ে যেতে যেতে, সেখানে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচিন্তা কি কোনও পথ দেখায় সাধারণ মানুষকে, ভাসিয়ে রাখতে পারে ডুবতে না দিয়ে?
বিভূতিভূষণ আগামীকে নিয়ে কি ভাবছেন দেখা যাক, ১৯২৫ সালে পিছিয়ে গিয়ে। ভাগলপুরে জঙ্গলমহলের কাছারিতে বসে এই সময়ে ‘পথের পাঁচালী’ লিখছেন তিনি। সকলের অলক্ষে বাংলা ভাষার অন্যতম কালজয়ী উপন্যাসটি রচিত হচ্ছে। কিন্তু বইটির প্রকাশে এবং বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের উজ্জ্বল নতুন জ্যোতিষ্ক হিসাবে বহিঃপ্রকাশের তখনও বছর তিন-চার বাকি। অনেক পরে এই পটভূমি নিয়েই তিনি আবার ‘আরণ্যক’ লিখবেন, তার পরিকল্পনাও করছেন এখনই। কিন্তু সে সবই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে। এখনও বিভূতিভূষণ প্রধান পরিচয় জমিদার জঙ্গলমহলে খেলাতচন্দ্র ঘোষের বিস্তীর্ণ এস্টেটের করণিক হিসাবে। গুটিকয়েক গল্প শুধুমাত্র প্রকাশিত হয়েছে পত্রপত্রিকায়। প্রশংসাও পেয়েছেন, কিন্তু অভিজ্ঞ লেখক এখনও তিনি নন।

এর সঙ্গে সঙ্গেই দিনলিপিও লিখে চলেছেন নিয়মিত, যেখানে সাহিত্যের বাইরেও তাঁর দৈনন্দিন চিন্তার আভাস পাওয়া যায়, আর তার সঙ্গেই আনুষঙ্গিক চিন্তার পরিচয়। ইতিমধ্যেই সাহিত্যের উপযোগিতার দিকটির সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে সচেতন, এবং সমাজের প্রতি সাহিত্যিকের দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে সতর্ক। তাঁর এই সময়কার দিনলিপি পড়লে যার উদাহরণ মেলে ছত্রে ছত্রে। অবশ্যই, বিভূতিভূষণ মনে মনে যাই ভাবুন না কেন, লেখাকে নীতিগর্ভ করে তোলেননি। যেই কারণে অনেকেই অনেক সময়ে ঈঙ্গিতও করেছেন যে তাঁর লেখা অবচেতন থেকে উঠে আসা চেতনাপ্রবাহ। সেখানে বুদ্ধির কৌশল কম। অর্থাৎ বিভূতিভূষণ আয়না, যেখানে বিশ্বজগৎ প্রতিফলিত হয়। তাঁর নিজস্ব মননের প্রতিফলন তাঁর লেখায় কম। আয়না কি সজ্ঞান হয়? কিন্তু দিনলিপিগুলিতে বারবার দেখা যায়, বিভূতিভূষণ শুধুমাত্র শিল্পী হিসাবে সতর্ক নন, শিল্পের সামাজিক প্রভাবের বিষয়েও অত্যন্ত সজাগ। নীতিবোধকে লেখায় এনে তাকে নিজের বিশ্বাসের ইস্তেহার করে পাঠকের ওপর চাপিয়ে দিলে সাহিত্যরস লঘু হয়। শুধুমাত্র সাহিত্যের দ্বারাই যে সমাজে সঠিক জীবনের বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব, সেই বিশ্বাস নবীন লেখকের কাছে প্রশ্নাতীত।
‘স্মৃতির রেখা’ দিনলিপি বিভূতিভূষণের এই সময়কার রচনা, ভাগলপুরের কাছারিতে বসে লেখা। সেখানে তিনি তাঁর ভূমিকার বিষয়ে কী লিখছেন দেখা যাক:
‘আজ বসে বসে অনাগত দূর ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে… আমার সেই সব অনাগত শিশু প্রপৌত্র, বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রদের জন্যে কি রেখে যাব তাই ভাবছি।’
আর এক জায়গায় লিখছেন:
‘একশত বৎসর পরে আমার নাম দশ বৎসর আগেকার পাতা মাকড়সার জালের মত কোথায় কালসাগরে মিলিয়ে যাবে— তবে কি রেখে যাবো আমার দুঃখের মত দুঃখী ঐ সব অনাগত কচি কচি শিশু মনগুলির খোরাকের জন্যে? কি রেখে যাবো? কি সম্পত্তি, কি heritage তাদের জন্যে দেবো?’
ভেবে অবাক লাগে যে, আমাদের কথাই ভাবছেন বিভূতিভূষণ। আমাদের— তাঁর বহুদূর ভবিষ্যতের প্রজন্মে প্রতি তাঁর অঙ্গীকারও তাঁর সাহিত্যরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। বিভূতিভূষণের লেখায়, দিনলিপিতে বারেবারে এই আগামীর মানুষদের কথা ঘুরেফিরে আসে। আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁর এই দায়বদ্ধতার কথা আমার মনে হয় খুবই জরুরি। আমরা যেই যুগে দাঁড়িয়ে আছি, বিশেষ করে তার নিরিখে, যখন প্রাকৃতিক সম্পদকে অবিলম্বে ভোগ করে ফেলার এক আশ্চর্য প্রতিযোগিতা চলছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের একটি স্বাভাবিক জীবন পাওয়ার যে মৌলিক অধিকার, সে সবের কথা সম্পূর্ণ ভুলে।
ভাগলপুরে জঙ্গলমহলের কাছারিতে বসে এই সময়ে ‘পথের পাঁচালী’ লিখছেন তিনি। সকলের অলক্ষে বাংলা ভাষার অন্যতম কালজয়ী উপন্যাসটি রচিত হচ্ছে। কিন্তু বইটির প্রকাশে এবং বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের উজ্জ্বল নতুন জ্যোতিষ্ক হিসাবে বহিঃপ্রকাশের তখনও বছর তিন-চার বাকি। অনেক পরে এই পটভূমি নিয়েই তিনি আবার ‘আরণ্যক’ লিখবেন, তার পরিকল্পনাও করছেন এখনই। কিন্তু সে সবই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে।
বিভূতিভূষণকে অনেকেই পলায়নবাদী মনে করেছেন। তিনি কি তাই? দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি দেন কম? যেমন মনে করা হয়েছে তিনি স্বভাবকবি, তাঁর লেখার সাবলীল ছন্দ নৈর্বক্তিক কোনও দৈব আকর থেকে উৎসারিত চেতনার স্রোত? অথচ, তিনি যে শিল্প রচনা করছেন, তার পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত কারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, নিজেই বলছেন। আসলে, সমষ্টিগত রাজনীতিক অবস্থান থেকে নয়, গভীর মানবদরদ থেকে আসে বিভূতিভূষণের রচনা। তাঁর শীল্প নিতান্তই অভিপ্রেত, আকস্মিক কোনও সমাপতন নয়। ‘তৃণাঙ্কুর’ ডায়েরির শুরুতে, উপন্যাসটি প্রকাশের দিন তিনি লিখছেনও যে, পথের পাঁচালীর আর্ট সবাই ধরতে পারেন না। বস্তুত, পথের পাঁচালী উপন্যাসের খসড়ায় ক্রমাগত রদবদল দেখলে বোঝা যায় যে কতবার লেখককে ফিরে ফিরে এসে সংশোধন করতে হয়েছিল পাণ্ডলিপির বিভিন্ন অংশ। অবচেতনের স্রোতে অত সংশোধনের প্রয়োজন হয় না।

বিভূতিভূষণের অগাধ পড়াশুনো নিয়ে অনেকেই বলেছেন। বিশেষ করে নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, এই ধরনের পড়াশুনোর বিস্তার তিনি কলকাতা শহরে আর কারওর মধ্যে দেখেননি। ভূগোলের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে উদ্ভিদজগতের সম্বন্ধে খানিক বৈজ্ঞানিক পাঠ, প্রাগৈতিহাস থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের খবর, সমস্ত বিষয়ে যেমন তাঁর পড়াশোনা ছিল গভীর, তেমনই এই সমস্ত বিজ্ঞানসম্মত সত্যসমূহের পশ্চাদপটে যে এক সমন্বয়সাধনকারী সার্বিক অস্তিত্ব রয়েছে, সে ব্যাপারে তাঁর এক নিজস্ব দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ধর্মবিশ্বাস নয়, বরং আধ্যাত্মিকতা বলা চলে। বিভূতিভূষণ নিজেই একজায়গায় লিখছেন, তিলতুলসির পূজায় তাঁর বিশ্বাস নেই। এই আধ্যাত্মিকতা, এই সমসাময়িক এবং ভবিষ্যতের মানুষের প্রতি গভীর মমতার বোধ, সমস্ত মিলিয়ে বিভূতিভূষণের চিন্তাজগত। তাঁর প্রকৃতিচিন্তা এই বৃহত্তর জগতের, অরণ্যের, মানুষের, গতির, সারল্যের সঙ্গমে তৈরি এক সার্বিক ভাবজগত। অরণ্য তথা প্রকৃতি এক চিরন্তন সত্যের এবং আনন্দের প্রতীক, যার খোঁজে মানুষ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু পায় না। সংসারের গ্লানির সম্পূর্ণ প্রতিকার না থাকলেও, প্রকৃতির ক্রোড়ে সেই বিষাদের থেকে বিশ্রাম পাওয়া সম্ভব।
আগের প্রসঙ্গে ফিরি এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে। ‘স্মৃতির রেখা’ দিনলিপির বিভিন্ন দিনের টুকরো টুকরো লেখার অংশ যদি এক সূত্রে গাঁথা যায়, তা হলে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই আন্দাজ পাওয়া যায়। কী রেখে যাবেন ভাবছেন বিভূতিভূষণ আগামী দিনের মানুষের জন্য এবং কেন? কী তাঁর দায়? এর উত্তর একটি ছোট লেখায় পাওয়া যাচ্ছে এইভাবে:
‘জীবনটা ছেলেখেলার জিনিস নয়। এটা একটা serious জিনিস। যারা হেসে খেলে তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ স্ফুর্ত্তি করে কাটালে তাদের কথা ধরি না, কিন্তু যারা জীবনটারে serious ভাবে নিতে যায়, নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের সুখ না দেখে, তাদের উচিত এই উত্তরকালের শিশু, বৃদ্ধপৌত্র, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রগণের জন্য কিছু সঞ্চয় করে যাওয়া।’
খানিক পরে আবার বলছেন,
‘জনসেবার জন্যে sacrifice করবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে এও এক জনসেবা, এর জন্যেও বিরাট স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন আছে। এ সাময়িক হুজুগের জনসেবা নয়। ধীর, শান্ত সমাহিত ভাবে উত্তরকালীন অনাগত জনগণের সেবা।’
জনসেবা বলতে বিভূতিভূষণ অবশ্যই এখানে সাহিত্যরচনাকেই বুঝিয়েছেন। যদি সংক্ষেপ করে দেখি, বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যরচনার মূল কারণ হিসাবে দেখছেন আগামী প্রজন্মের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাকে, জনসেবার আঙ্গিক থেকে। এই জনসেবার পথ দুর্গম এবং তাৎক্ষণিক কোনও পরিতৃপ্তির— যাকে ইংরাজিতে বলে instant gratification— সুযোগ এই পথে নেই, তাও তিনি অনুমান করছেন।
বিভূতিভূষণের লেখায়, দিনলিপিতে বারেবারে এই আগামীর মানুষদের কথা ঘুরেফিরে আসে। আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁর এই দায়বদ্ধতার কথা আমার মনে হয় খুবই জরুরি। আমরা যেই যুগে দাঁড়িয়ে আছি, বিশেষ করে তার নিরিখে, যখন প্রাকৃতিক সম্পদকে অবিলম্বে ভোগ করে ফেলার এক আশ্চর্য প্রতিযোগিতা চলছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের একটি স্বাভাবিক জীবন পাওয়ার যে মৌলিক অধিকার, সে সবের কথা সম্পূর্ণ ভুলে।
এইখানে আমার মনে হয়, বুদ্ধের বাণীর যেন খানিকটা ছায়া পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের চিন্তায়। অস্বাভাবিক নয়। বৌদ্ধ চিন্তার দ্বারা বিভূতিভূষণ যে বারবার উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তা তাঁর বিভিন্ন গল্পে দেখা যায়। ব্যক্তিগত জীবনও বিভূতিভূষণ দারিদ্র্য-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন জীবনের লম্বা সময়। তাঁর চিন্তায় বৌদ্ধ চিন্তার ছায়া পাওয়া সঙ্গত। জগতে দুঃখ, তার কারণ, তার অবশেষ এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে। আবহমানকাল ধরে মানুষ চক্রবত এই সংসারের থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে এসেছে। সংসার দুঃখের আকর, সংসারের চরিত্রগত বৈশিষ্টই হল দুঃখ, সংসারে আটকে থাকলে দুঃখ থাকবেই।
বিভূতিভূষণ অবশ্য এরপর কিঞ্চিত অন্য মার্গে চলেন। যেখানে বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় আটটি পথের ক্রমাগত অনুশীলন বলে দর্শানো হয়েছে, বিভূতিভূষণ সেই দুরূহ পথের প্রতিস্থাপন করেন প্রকৃতিকে দিয়ে। আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গটিকে বোঝা যাক। বিভূতিভূষণ লিখছেন,
‘জগতের অসংখ্য আনন্দের ভান্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না রাত্রি, অস্ত সূর্য্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময় উদার শূন্য… এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল, অবক্তব্য আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে, সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান পৌঁছয় না।… সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্ত্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া… তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা।’
সংসার যদি দুঃখের সাগর হয়, তা হলে তার প্রতিকার, এই অসীম আনন্দের চাবি তিনি তুলে দিলেন প্রকৃতির হাতে। আর সাহিত্যিকের কী ভূমিকা? সাহিত্যিক হলেন যাজক। তিনি প্রকৃতি আর বিস্মৃত সাধারণ মানুষদের যোগস্হাপন করেন, মার্গপ্রদর্শক। অসীম আনন্দের আকরের সন্ধান দেওয়া তাঁর কাজ। আশ্চর্যের বিষয়, স্বভাববিনীত বিভূতিভূষণের প্রত্যয় এই ব্যাপারে বেশ দৃঢ়, বিশ্বের প্রেক্ষিতে তাঁর ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর কোনও দ্বিধা নেই।
একটা কথা এখানে বলা হয়তো প্রয়োজন। দুঃখের অনুভুতিকে বিভূতিভূষণ অবাঞ্ছিত রূপে দেখেননি, বরং জীবনের প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হিসাবে দেখেছেন। ‘তৃণাঙ্কুর’ দিনলিপির শুরুর দিকের একটি বহুল-পঠিত অংশ দেখা যাক, অন্য কথায় যাওয়ার আগে:
‘দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ; দৈন্য বড় সম্পদ; শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ। যে জীবন শুধু ধনে মানে সার্থকতায়, সাফল্যে, সুখে-সম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্যের, বিলাসের মেলা— যে জীবন অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, যে জীবনে শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্নায় বহুদিন-হারা মেয়ের মুখ ভাববার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র দুধ খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা করতে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ-ধনসম্পদ-ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।’
২৮ অগাস্ট, ১৯২৫-এ যদি আবার ফিরে যাই, ‘স্মৃতির রেখা’ দিনলিপিতে তিনি বলছেন:
‘…Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ- Sadness ভিন্ন জীবনে profundity আসে না- যেমন গাঢ় অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশী হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশে সত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও জ্যোতিষ্মান হয়ে প্রকাশ পায়। তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তারা চিরকালই অপ্রকাশ থেকে যেত।’
দিনলিপিতে এক জায়গায় বিভূতিভূষণ লিখছেন, যীশুকে যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা হল বা অশোক যেদিন রাজা হলেন, সেদিনও সামনের পাহাড়টা অমনি দাঁড়িয়েছিল— তখনকার লোক অমনি জঙ্গলে কাঠ কাটতো। কে খবর রাখতো সুদূর খাইবার গিরিবর্ত্ম দিয়ে কোনও নতুন বিজেতার দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করল কি না? সুবর্ণরেখা তখনও এমনি নিঃসঙ্গ নির্বিকারভাবে বেয়ে চলত— এইসব পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। আসলে বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি এবং তার মধ্যের অরণ্যবাসী মানুষগুলির জীবনযাত্রা এক অজর অমর সত্যের রূপ। তাঁর কাছে তুচ্ছ, ব্রাত্য, অবহেলিত, নিপীড়িতের মধ্যেও সেই একই রূপের প্রকাশ। আর তিনি চান তাঁর পাঠকেরাও সেই সত্যের সান্নিধ্য লাভ করুক। শুধুমাত্র উদ্ভিদের প্রতি ভালোবাসা বা নান্দনিক সৌন্দর্য্যবোধ থেকে নয়, বরং কোনও পরমতর সত্যের রূপক হিসাবেও বিভূতিভূষণ অরণ্যকে আর অরণ্যচারী মানুষদের দেখেন। আত্মার আত্মীয়তার সূত্রে।
আরণ্যক উপন্যাসের শেষে সত্যচরণ যখন সিংভূমের জঙ্গলজমি সমস্তটাই ইজারা দিয়ে বসতি বসিয়ে কলকাতা ফিরে আসছে, তার জবানিতে লেখক ক্ষমা চান, ‘হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!…’ এই আর্তি কেবল সত্যচরণের নয়, যুগে যুগে সকলেরই। আরও বিশেষ করে আমাদের, এই বর্তমান নিরর্থক প্রাচুর্যে ভরা পৃথিবীর অধিবাসীদের, যেখানে প্রতি মুহূর্তে চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি, আমাদের আসল সম্পদ, আমাদেরই আকাঙ্খার জেরে। অগোচরে কী ঘটে গেল, আমাদের কারণে হলেও, তা নিয়ে আমরা কমই ভাবি। নিজের হাতে না মারলে তার দায়ভার মানুষ নেয় না। চোখের অগোচরে যতই গর্হিত কিছু হোক না কেন, না দেখলে তার দোষ তো আর আমাদের নয়।

কাঠের এই যে টেবিলের ওপর এই লেখাটা লিখছি, এই কাঠ যে এক দিন মহীরুহ শিশুগাছ ছিল, তা নিয়ে কি ভাবার অবকাশ আছে? এই যে দূরত্ব, হত এবং হন্তার মাঝখানে, যা বাজারের বিমূর্ততায় নিয়ত হারিয়ে যেতে থাকে, সেখানে আমাদের নিজস্ব দায় বোঝা প্রয়োজন, কিন্তু সহজ নয়। সত্যচরণ সেখানে হয়তো যুগযুগ ধরে আমাদের প্রতিনিধি, যে নিজের হাতে জঙ্গল সাফ করিয়ে বসতি স্থাপন করে আমাদের দায় আমাদেরই বোঝায়। বিভূতিভূষণের ভাষায় এই গভীর বিষন্নতা পাঠককে ছুঁয়ে যায়।
‘নাঢ়া-বইহার ও লবটুলিয়ার সমুদয় জঙ্গলমহাল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোথাও পূর্বের মতো বন নাই। প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়োঝাঁকার নিভৃত লতাবিতান, কত স্বপ্নভূমি— জনমজুরেরা নির্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল এক দিনে। এখন কোথাও আর সে রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নাই, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত, মহিষের দেবতা দয়ালু টাঁড়বারো হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া বন্য মহিষদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত।’
‘নাড়া-বইহার নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তি মাত্র। যে দিকে চোখ যায়, শুধু চালে চালে লাগানো অপকৃষ্ট খোলার ঘর। কোথাও বা কাশের ঘর। ঘন ঘিঞ্জি বসতি— টোলায় টোলায় ভাগ করা— ফাঁকা জায়গায় শুধুই ফসলের ক্ষেত। এতটুকু ক্ষেতের চারিদিকে ফনিমনসার বেড়া। ধরণীর মুক্তরূপ ইহারা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে।’
আবার কিছু পরে লেখক বলছেন আমাদের যুগের পূর্বানুমানে,
‘এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষে অরণ্য দেখিতে পাইবে না— শুধুই চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুন্ন থাকুক।’
অবশিষ্ট অরণ্যও আর কতদিন অক্ষুন্ন থাকবে বলা মুশকিল। আক্ষেপ এই, যদি আমরাও বুঝতে পারতাম, পণ্যের সূচকে নয়, আসল সম্পদ রয়েছে অন্য কোথাও, তা হলে হয়তো সব সমাধানের চাবি আমাদের সামনেই সাজানো বলে দেখা যেত, সব দরজা সহজেই খুলে নেওয়া যেত।
দিল্লির বাসিন্দা তৃণাংকুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৮০ সালে। আদি বাড়ি ব্যারাকপুরে। পেশা এবং নেশায় শিল্পী তথা গ্রাফিক ডিজাইনার তৃণাঙ্কুর একটি পারিবারিক সাহিত্যিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন নিজের নামের সঙ্গে। তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। এই ঐতিহ্য এবং স্মৃতিরক্ষায় সক্রিয় তৃণাংকুর একাধিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে একসময় কাজ করেছেন কলকাতা ও দিল্লির একাধিক নামী সংবাদপত্রে। বর্তমানে স্বাধীনভাবে কাজ করেন। নেশা বই পড়া ও দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ানো।



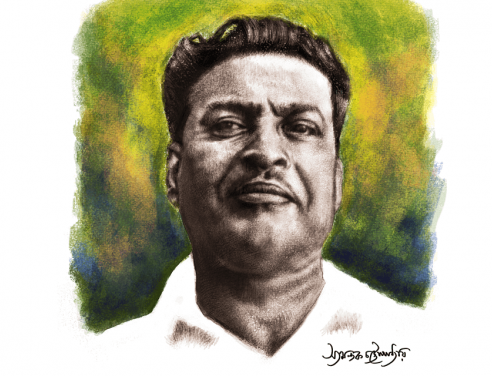





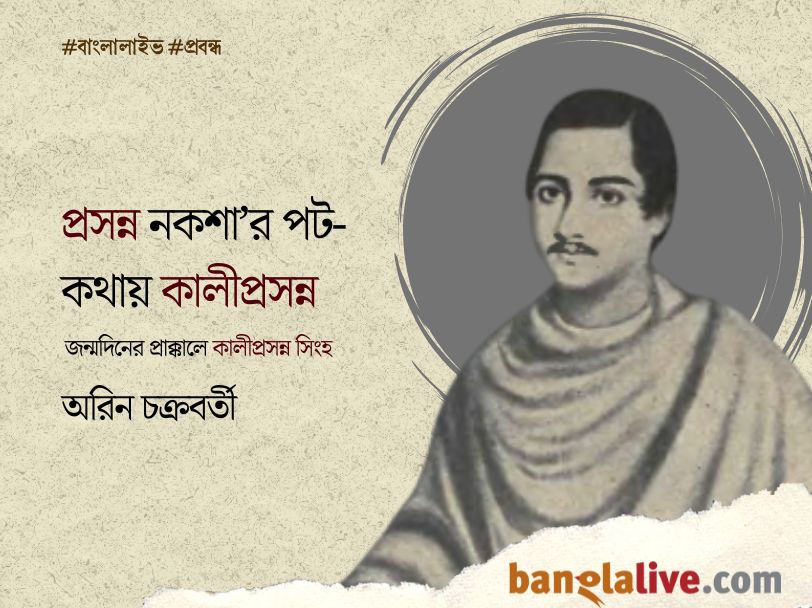














4 Responses
Apne bhagyaban.mahamanaber native apne.
আমি পড়তে পারছি না কেন?
অসাধারণ স্মরণ- বিভূতিভূষণ, তাঁর বাণী দিয়ে তাঁকেই দেখা, পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিয়ে তাঁর ভাবনা নিয়ে আমাদের ভাবানো এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আজ সারা ভারত জুড়ে জল জঙ্গল জমিকে ইজারা দেওয়ার যে অবিচ্ছন্ন প্রয়াস চলছে,প্রকৃতির কোল খালি করে দেবার যে প্রয়াস চলছে তা মনে করিয়ে দিল। আজকের প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্ম সাক্ষী রইল।
উফফ কি অসাধারণ লেখা। খুব ভালো লাগলো এই কারণে,যে কয়েক দিন আগেই জঙ্গল ঘুরে এলাম,ওখানে প্রতি মুহূর্ত আমার লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর কথা বার বার মনে পড়েছে।উনি আমার ভীষন প্রিয় একজন লেখক। আর তারপর এই লেখাটা যেনো হতে স্বর্গ পেলাম 🙏💐