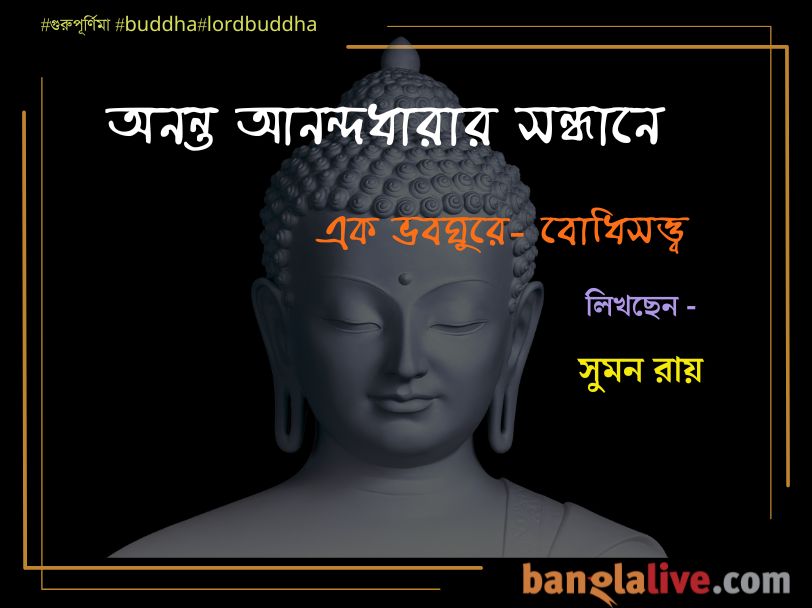সে এক শান্তির রাত। বাইরে মৃদুমন্দ বাতাস। জানলার নীল রেশম পর্দা দুলছে সেই বাতাসে। সিদ্ধার্থর (Bodhisattva) মন যেন আজ একটু বেশিই শান্ত। সন্ধ্যায় পুজোর ঘর থেকে ভেসে আসছিল গান। কোন এক নারীকণ্ঠ গাইছিল, ‘বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব, জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা, একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে, পরম-এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে।’ সিদ্ধার্থর মনে তখন থেকেই বাঁধভাঙা আনন্দ। কেন বইছে এই নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা? উত্তর আজানা সিদ্ধার্থের। সে সিদ্ধান্ত নেয়, আজই সেই রাত। আজই বেরিয়ে পড়তে হবে।
এই লেখার বিষয়বস্তু হিসাবে সম্পাদক বলেছিলেন, গৌতম বুদ্ধের ভবঘুরে প্রবৃত্তি। লেখাটা শুরু করতেই অনেক দেরি হয়ে গেল। মাঝে এক কাকভোরে খবর এল, বারো বছর স্কুলজীবনের সহপাঠী মারা গিয়েছে। জীবদ্দশায় যাঁর বাড়ি কোনও দিন যাওয়ার সুযোগ হয়নি, সেখানেই যাওয়ার সুযোগ এনে দিল মৃত্যু। সেটাও সন্ধ্যা। শান্ত সন্ধ্যা। প্রাক গ্রীষ্মের গরম হাওয়া তখনও নাভিশ্বাস তুলে দেয়নি। হাজির হই ছাদে। মেঝেয় রঙিন আলপনা। চার পাশে অসংখ্য গাছ। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সকালেও এই ছাদ নিজে হাতে ধুয়ে দিয়েছিল আমার সেই সহপাঠী। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে বলেছিল, শীত করছে। ৩৯ বছর বয়সের শীত। প্রাক গ্রীষ্মের শীত। যে শীত আর কমেনি।
আরও পড়ুন: যে ঠিকানা লেখা যায় না, সেই ঘরে যাদের বাস! পর্দার ভবঘুরেরা
হঠাৎ মনে পড়ে এই লেখার কথা। বুদ্ধ সম্পর্কে আমি কী জানি? ইতিহাসের যে সব অধ্যায় আবছা কালিতে লেখা, যার পাতা হলুদ হয়ে গিয়েছে, সে সম্পর্কে জানবই বা কোথা থেকে! ৩৯ বছরের এক মানুষের শীতকাতুরে অসুস্থ সন্ধ্যা বারবার ফিরে আসে মাথায়, তার চেয়ে দশ বছরের ছোট এক মানুষের গৃহত্যাগের অনুভূতি পিছনের বেঞ্চে বসে থাকে। সব গুলিয়ে যায়।
সিদ্ধার্থ। শহরের সবচেয়ে নামজাদা মানুষের ছেলে। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে। বউ-বাচ্চা আছে। এসব ছেড়ে চলে যাওয়া যায় নাকি? সিদ্ধার্থ তো ভোগী। সবচেয়ে বড় ভোগী। জীবনকে পুরোপুরি ভোগ করতে চায় সে। নিজের গাড়িতে কিছু দিন আগেই ঘুরতে বেরিয়েছিল সিদ্ধার্থ। কপাল এমন, প্রথমেই এক বৃদ্ধকে দেখে সে, খুঁড়িয়ে হাঁটছে, যে কোনও মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়বে! আর কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে এক অ্যাম্বুলেন্স। ভিতরে মুমূর্ষু কেউ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে পাশে বসা মহিলা। কিছুটা এগোতেই শববাহী গাড়ি। ভয়, তীব্র ভয়! এই যে এত কিছু, আর দেখা হবে না! মরে যেতে হবে? শরীরে জোর থাকবে না? কোথাও যাওয়া হয় না সিদ্ধার্থর। ড্রাইভারকে বলে, গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে। গেটে ঢোকার মুখে দেখে এক মাঝবয়সি ভিখারি। ছেঁড়া-ফাটা জামা, মুখ ভর্তি দাড়ি, গেয়ে চলেছে খোলা গলায় গান। কে ও? ওর ভয় নেই কোনও?

সিদ্ধার্থ রোগে ভুগতে চায় না। সিদ্ধার্থ বুড়ো হতে চায় না। সিদ্ধার্থ মরতে চায় না। এই ছয় ফুটের পাঁচিল, যশোধরার ঘাড়ের কাছে আঁচিল, মার্গারিটার গ্লাস, অস্তিনের তাস, উড়ন্ত অ্যালবাট্রাস, টাইগার বাম, ছোড়দার ঘাম— সব কিছু অনুভব করতে চায় সে। ছেড়ে দিতে চায় না কোনও কিছু। দেখতে চায় দুনিয়া। দু’চোখ ভরে। সব কি এক জীবনে পাওয়া সম্ভব? যদি এমন হত, জীবনের যা কিছু খুশির, যা কিছু পাওয়ার, যা কিছু নেওয়ার, যা কিছু দেওয়ার— সব ছোট্ট করে এক জায়গায় পাওয়া যেত? এই হাতের মধ্যে? সিদ্ধার্থ সিদ্ধান্ত নেয়, সেটিকেই সে ধরবে। সব কিছু একসঙ্গে। যা যা ভোগের, যা যা পাওয়ার। সব একসঙ্গে হাতের মধ্যে, চোখের মধ্যে, কানের মধ্যে। ‘একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে, পরম-এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে’র কাছে যাবে সে, বিশ্ব চরণে বিনত হবে সে।
সেই শান্ত রাতেই ঘর ছাড়ে সিদ্ধার্থ। শহরের সবচেয়ে নামজাদা মানুষের ছেলে বেছে নেয় ভিক্ষুকের জীবন। ভবঘুরের জীবন। চার দেওয়ালের মধ্যে যা কিছু, শুধু সেটুকুতে যে তার সাধ মিটবে না, এ বহু আগেই বুঝেছিল সে। সিদ্ধার্থ বিস্তৃত করে তার দুনিয়া। সে হাত বাড়ায়। বিশ্বের সঙ্গে মিলনে তার ‘সকলি যায় খুলে, বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।’ ন্যাড়া মাথা, গায়ে চাদর, হাতে ভিক্ষার পাত্র। শান্তির রাতে পথে নামে সিদ্ধার্থ। পরবর্তীতে যাকে আমরা ডাকব বোধিসত্ত্ব নামে।
হঠাৎ মনে পড়ে এই লেখার কথা। বুদ্ধ সম্পর্কে আমি কী জানি? ইতিহাসের যে সব অধ্যায় আবছা কালিতে লেখা, যার পাতা হলুদ হয়ে গিয়েছে, সে সম্পর্কে জানবই বা কোথা থেকে! ৩৯ বছরের এক মানুষের শীতকাতুরে অসুস্থ সন্ধ্যা বারবার ফিরে আসে মাথায়, তার চেয়ে দশ বছরের ছোট এক মানুষের গৃহত্যাগের অনুভূতি পিছনের বেঞ্চে বসে থাকে। সব গুলিয়ে যায়।
নতুন জীবনের প্রথম পর্যায়ে বোধিসত্ত্বর শিক্ষাগ্রহণ শুরু হয় অলরা কলমার কাছে। কে এই অলরা কলমা? এক অন্য ভোগবাদের গুরু। মনকে বশ করার সব তরিকা যাঁর নাকি জানা। মহাশূন্যের মধ্যে তিনি নাকি পেয়েছেন তাঁর সূত্র। পোষালো না বোধিসত্ত্বর। অতএব, দ্বিতীয় গুরু। রামপুত্র। তিনি দেখালেন নতুন পথ। মনকে জয় করার জন্য জানা না-জানার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পথ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘জানা না-জানার মধ্যসেতু, নিত্য পার হতেছিল কিছু তার না বুঝিয়া হেতু’। বোধিসত্ত্বরও হল তাই। সে টের পায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সে যে ভোগের পথ দেখাতে চায়, যে অমরত্বের পথে সে হাঁটতে চায়— এসব দিয়ে তার হবে না। আবার কোনও রাতে বেরিয়ে পড়ে সে।
জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে বোধিসত্ত্ব। কঠোর তপস্যার সময়কাল। শরীর এবং শরীরের চাহিদাগুলি তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভোগের পথের বাধা। বোধিসত্ত্ব থামতে চায় না, সীমার মধ্যে আটকে থাকতে চায় না। অদৃশ্য পদার্থের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করতে চায় সে। একসঙ্গে দু’টি-তিনটি-পাঁচটি-দশটি জায়গায় উপস্থিত থাকতে চায় সে। ভবিষ্যৎ দেখতে চায়, বর্তমান দেখতে চায়, অতীত দেখতে চায়। উড়তে চায় আকাশে। সব রোগ সারাতে চায় নিজে নিজে। সব চায়। সব চাই তার। তাই তো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসা। এবার আর একটা সীমা ভাঙতে হবে তাকে। শরীরের সীমা। বোধিসত্ত্ব শুরু করে কঠোর তপস্যা। ছয় বছর কোনও খাবার খাবে না সে। একা নয়, জুটে যায় আরও পাঁচ দোসর। সবে মিলে করি কাজ… শরীর থেকে মুক্তির পথে হাঁটে সে। সেও এক ভবঘুরের যাত্রা। ভবঘুরে আত্মার যাত্রা।

কিন্তু এভাবে কত দিন? অধিকাংশ দিন দানা নেই, পানি নেই। কোনও দিন খুব খিদে পেলে একটা ধান বা একটা তিল। এই খেয়ে চলে? দেখতে দেখতে শরীর শুকিয়ে যায় তার। গায়ে ঘা, ত্বক শুকনো চটের মতো, গোটা শরীরটা যেন একটা দড়ি। কিন্তু ছয় বছর এভাবে কাটিয়েও তো পাওয়া গেল না মুক্তির সন্ধান। পাওয়া গেল না সব কিছুকে ভোগের রাস্তা। তাই ছয় বছর পরে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধান্ত নিল, আর নয়। থামল তপস্যা। ত্যাগের মধ্যে যে ভোগ নেই তা ষোলো আনা টের পায় সে। আবার নতুন করে ভিক্ষার পালা শুরু। আবার অন্ন-জল-বাসস্থানের সন্ধান শুরু।
বহু পরে নির্বাণের কাছে পৌঁছোতে পারে বোধিসত্ত্ব। সে কাহিনি অন্য। তার যাত্রাপথ অন্য। তার সঙ্গে মিল নেই প্রাণপাত করে তপস্যার। সম্পর্ক নেই আত্মাকে শরীর মুক্ত করার, ভোগকে সংজ্ঞামুক্ত করার। সংসারের কাছে ফিরে আসে বোধিসত্ত্ব। তবে এ সংসার ফেলে আসা সেই বাড়িঘর নয়। এই ‘সংসার’ হল চিরস্থায়ী এক ভবঘুরপনা। রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করা, আবর্তনের দিকে যাওয়া, লক্ষ্যহীন এক ভ্রমণ। কৈবল্য। মু্ক্তির সন্ধানে ভাবজগতে ভবঘুরে হয়ে যায় বোধিসত্ত্ব। তবু তার ‘যাওয়া তো নয় যাওয়া, ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া’।
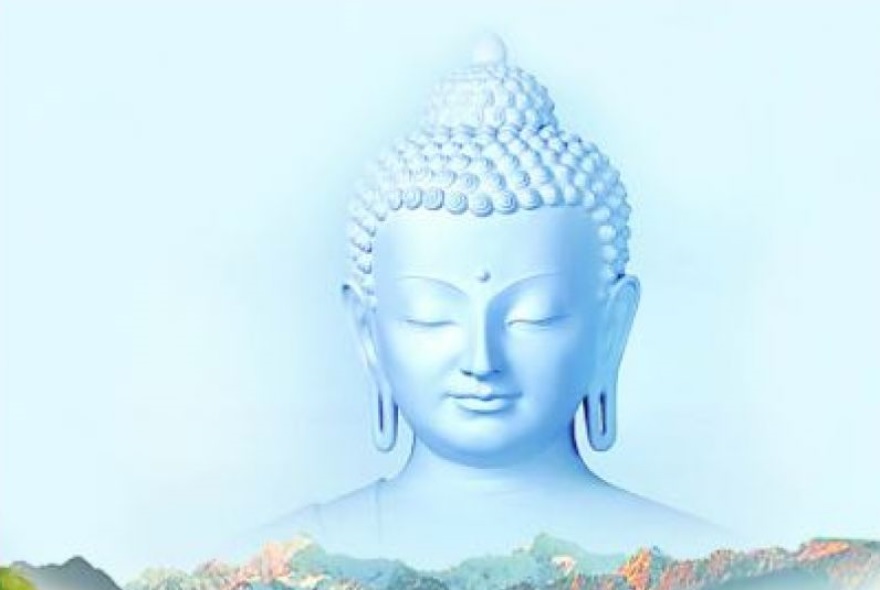
সেই হাওয়া। যে হাওয়া একদিন এসে জানলার নীল রেশম পর্দা দুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, যে হাওয়ায় সিদ্ধার্থ নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারার সন্ধানে রওনা দিয়েছিল চার দেওয়ালের গণ্ডি ভেঙে, যে হাওয়া জন্ম দিয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ভোগী মানুষটার, যে হাওয়া তৈরি করেছিল অসীম নভোমাঝে অনাদি রবের উৎস সন্ধানি এক ভবঘুরের, সে হাওয়া বয়ে যেতে যেতে শুকিয়ে দেয় কোনও এক ভেজা ছাদের রঙিন আলপনা, টবের মাটি, সে হওয়ায় হঠাৎ শীত করে ৩৯-এর এক আঁকিয়ের।
তার পরে সে হাওয়া শহরের রাস্তায় রাস্তায়, গ্রামের আল পথে ধরে শত-সহস্র ঘূর্ণির মতো এলোমেলো ছড়িয়ে যায় এর-ওর-তার পায়ের কাছে। সে হাওয়ার ছোঁয়া লাগলেই মনে জাগে লোভ। সব কিছু পাওয়ার লোভ, সব কিছু ভোগের লোভ, অনন্তকে ছোঁয়ার লোভ। রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণাদের জীবিত করে যে হাওয়া আবার জন্ম দেয় বহু সিদ্ধার্থের, বহু বোধিসত্ত্বের, বহু ভবঘুরের। কেউ যাদের ভুলিবে না, কভু ভুলিবে না।
ছবি সৌজন্য: Swadestimes, jonogonotontro
সুমন রায় খুব সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন মানুষ। দু’বেলা দু’মুঠোর তাগিদে বর্তমানে হিন্দুস্তান টাইমসের বাংলা ডিজিটাল মাধ্যমে কর্মরত। এর আগে আনন্দবাজারের ডিজিটাল মাধ্যম এবং ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে খুবই সাধারণ পদে কাজ করেছেন। প্রায় কোনও বিষয়েই সুমন রায়ের কোনও জ্ঞান নেই বলে, তা আহরণের চেষ্টা করেন। সে জন্য বই পড়া, সিনেমা দেখা, গান শোনা এবং অজানা জায়গায় গিয়ে দিনযাপনের চেষ্টা করেন।প্রিয় ঋতু গ্রীষ্ম। প্রিয় খাদ্য দই-খই। ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে টুপি পরতে পছন্দ করলেও প্রিয় পোশাক মুখোশ। প্রয়োজনে স্নান করেন এবং অবসরে ভজন-কীর্তন। এভাবেই বছর চল্লিশেক কাটিয়ে ফেলেছেন। এর পরেও আক্কেল হয়নি। তা কবে হবে, তা নিয়ে চিন্তায় আছেন।