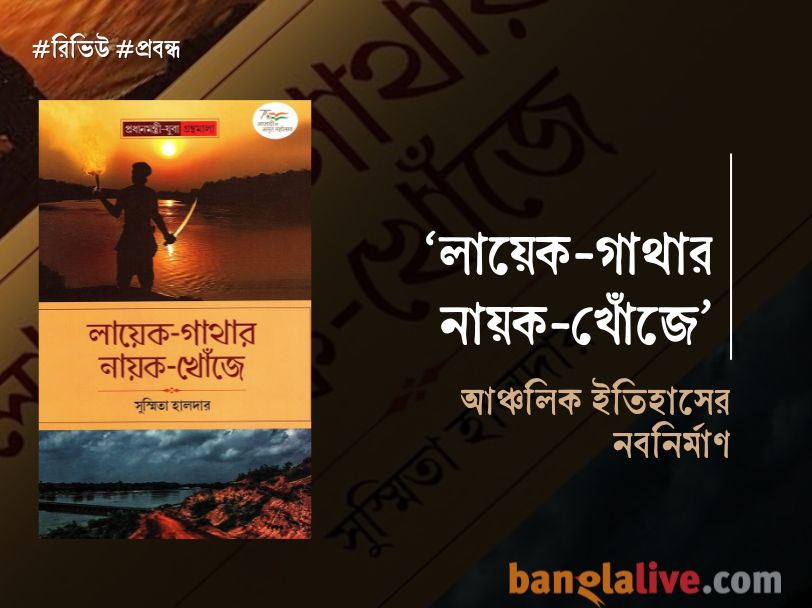বইয়ের নাম : লায়েক-গাথার নায়ক-খোঁজে
লেখক : সুস্মিতা হালদার
প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট
প্রথম প্রকাশ : ২০২৩
বিনিময় মূল্য : ১৯০/-
আঠারো শতকের কথা। দেশ তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে। জমি, খাজনা, দেশীয় রীতিনীতি, সংস্কৃতি, স্থানীয় রাজা-জমিদার আর সাধারণ প্রজাদের সম্পর্ক– সবকিছুর ওপরেই তাদের নজর। বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে ক্রমেই জমে উঠছে ক্ষোভ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ, উপজাতি বিদ্রোহ, আঞ্চলিক স্তরে একের পর এক গণ অভ্যুত্থান এরই ফলশ্রুতি। তৎকালীন মেদিনীপুরের বগড়ী পরগণা জুড়ে জ্বলে উঠেছিল এমনই এক বিদ্রোহের আগুন, যা ‘নায়েক’ বা ‘লায়েক’ বিদ্রোহ নামে পরিচিত। চুলচেরা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের নিরিখে বলা যায়— এ হল চুয়াড় বিদ্রোহেরই তৃতীয় পর্যায়, যা প্রায় দাবানলের আকার ধারণ করেছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন স্থানীয় রাজার ‘পাইক’ বা লেঠেল-সৈন্যসামন্তরা। ‘পাইক’ বা ‘নায়েক’ বা স্থানীয় উচ্চারণে ‘লায়েক’ (Layek Movement)— যে পরিচয়েই এঁদের অভিহিত করা হোক না কেন, দুঃখজনকভাবে এঁরা ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের প্রান্তিক চরিত্র হয়েই রয়ে গেছেন। মূলধারার ইতিহাসে এঁদের বিদ্রোহের কথা স্থান পায় হয়তো দু-চার লাইন। আঞ্চলিক স্তরের ইতিহাস-গবেষকরা এই নিয়ে কিছু লেখালিখি করলেও, তাঁদের কাজ সেভাবে উঠে আসে না সর্বভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস-চর্চায়। সেই অনাদৃত বিদ্রোহীদের মরণপণ সংগ্রামের স্বল্প-আলোচিত কাহিনি, জাতীয় স্তরের ইতিহাসে তুলে আনার উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন সুস্মিতা হালদার। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত ‘লায়েক-গাথার নায়ক-খোঁজে’ বইটিতে ধরা পড়েছে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের মানচিত্র।
পেশায় আইনের অধ্যাপিকা হলেও সুস্মিতা লেখালেখির সূত্রে জড়িয়ে পড়েছেন আঞ্চলিক ইতিহাসের অলিখিত কাহিনির মায়ায়। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রকল্পে নির্বাচিত লেখক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে, বর্তমান গড়বেতা (যা সেসময় ছিল বগড়ী পরগণার অন্তর্গত) অঞ্চলের নানা জায়গায় ঘুরেছেন, কথা বলেছেন স্থানীয় মানুষজন এবং রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। আর্কাইভে গিয়ে খতিয়ে দেখেছেন ব্রিটিশ আমলের সরকারি নথি। লৌকিক গাথা, স্থানীয় আবেগ, গল্প-উপন্যাস-ঐতিহাসিক নাটক-লোকগান ঘিরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিচেতনা আর ইতিহাস-অনুসন্ধানীর তথ্যনিষ্ঠা একত্র করে লিখেছেন ‘লায়েক-গাথার নায়ক-খোঁজে’।
বইটি আখ্যানধর্মী। গড়বেতা অঞ্চলের ইতিহাস, সেখানকার রাজবংশের কাহিনি, রাজাদের সঙ্গে পাইক- প্রজাদের সম্পর্কের কথা লেখক বলেছেন গল্প কথনের ভঙ্গিতে। তারপর প্রবেশ করেছেন বিদ্রোহের কথায়। বইটির কথক এক স্থানীয় যুবক, দূরশিক্ষণের কোর্সে ইতিহাস নিয়ে স্নাতকোত্তর, শিক্ষকতার ইচ্ছে থাকলেও চাকরি মেলেনি।অগত্যা ছেলেটি বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের ‘গাইড’ হিসাবে কাজ করেন, আর সেই কাজের সূত্রেই নিজের জায়গার এক অজানা ইতিহাস ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় তাঁর চোখে। এই বিষয়ে দু-একজন অধ্যাপকের কাছে প্রাথমিক পরামর্শ নিলেও, ছেলেটি উচ্চতর গবেষণার ‘অ্যাকাডেমিক’ রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন।
কিন্তু যেভাবে সাধারণ পর্যটকদের তিনি ইতিহাসের গল্প শোনান, সেভাবেই লিখে চলেন ‘লায়েক-গাথা’র এক-একটি অধ্যায়। নিয়মমাফিক গবেষণার বাইরে, এক ‘হাটুরে’ ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসুর যাত্রাপথ ধরে অন্য ধরনের ভাবনা পাঠকের সামনে উপস্থিত করে এই বই। লেখক নিজের অধ্যাপক-পরিচয়কে সামনে আসতে দেননি, সহজ-সরল আন্তরিক কথনের ভঙ্গিতে জীবন্ত করে তুলেছেন শখের গবেষক চরিত্রটিকে। ভাষার ব্যবহারেও কথক-চরিত্রের স্বাভাবিক বাকরীতি সচেতন ভাবেই বজায় রেখেছেন তিনি। একটু উদাহরণ দেওয়া যাক— “… আপনি গড়বেতা যাবেন, জিজ্ঞাসা করবেন, ‘রাজবাড়িটা কোথায়’? সবাই ওই গড় মঙ্গলাপোতা মৌজার রাজবাড়িটার কথাই বলবে। গড়বেতা মৌজার মধ্যে যে রাজবাড়ি ছিল তা এককথায় কেউ জানেই না। …ছোট থেকে আমিও এটাই শুনে এসেছি। অথচ আমি বইতে পড়েছি বগড়ীর রাজাদের রাজধানী গড়বেতা। তবে রাজবাড়িটা কোথায় গেল? খুঁজতে খুঁজতে পেলাম গৌরীপদ স্যারের বইতে। এই তথ্যটি একমাত্র ওই বইটাতেই রয়েছে।”
এই ব্যক্তিগত উদ্যোগে শখের গবেষকের মনের কথা লেখার ভঙ্গিই আকর্ষণ করে পাঠককে। অভিনবত্বের দাবি রাখে। সুস্মিতা শুধু কথকের মাধ্যমে নিজের গবেষণার কথাই বলেননি, দীর্ঘদিনের বিস্মৃতি ঘুচিয়ে সামনে এনেছেন আরও অনেক স্থানীয় ইতিহাস-লেখকের কথা, যাঁদের নাম মূলধারার ইতিহাস-আলোচনায় গুরুত্ব পায় না। এ বই তাঁদের কাজের প্রতিও এক ধরনের ‘ট্রিবিউট’।
সুস্মিতা তুলে এনেছেন আরও অনেক প্রশ্ন— যা জনশ্রুতির সঙ্গে মিশে যাওয়া আসল ইতিহাসকে খুঁজে আনার ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয়। আজকের প্রজন্মের কাছে প্রায়-ভুলে যাওয়া স্থানীয় বিদ্রোহী নেতা অচল সিংহ– যাঁর আসল পরিচয় পর্যন্ত ইংরেজরা উদ্ধার করতে পারেনি, যাঁর শেষ পরিণতির প্রমাণও ঠিকঠাক পাওয়া যায় না, তাঁকে আঞ্চলিক বিদ্রোহের সীমানা ছাড়িয়ে জাতীয় ক্ষেত্রেও নায়কের আসনে বসানোর উদ্যোগ, পাশাপাশি যুগল-কিশোর-ভোঁন্দা বিশার মতো অন্যান্য নেতার কথাও আলোয় নিয়ে আসার জন্য লেখকের সাধুবাদ প্রাপ্য।
ছবি, আর্কাইভের নথি, গ্রন্থপঞ্জি সহ এত বড় একটি কাজকে লেখক বেঁধে রেখেছেন ১১৩ পাতার একটি বইয়ের মধ্যে। শেষে কথকের মাধ্যমেই জানিয়েছেন– তাঁর কাজ এখনও শেষ হয়নি। “লায়েক-গাথার নায়কদের খোঁজের এই তো সবে শুরু। খোঁজার এখনও অনেক বাকি। অন্তত আমার কাছে তো তা-ই। চলমান এক ‘অচল ইতিহাস’।” হয়তো সে ইতিহাসের কথা তিনি লিখবেন গবেষণার পরবর্তী পর্যায়ে।
উপসংহারে আরও একটি মূল্যবান প্রশ্ন তুলেছেন সুস্মিতা। এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে, গবেষণা চলাকালীন। কোম্পানি আমলের ছোটখাটো আঞ্চলিক অভ্যুত্থানকে কি আদৌ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়ে ফেলা যায়? সে তো স্থানীয় স্বার্থের সংঘাত মাত্র। তখন তো জাতীয়তাবাদ বা ‘দেশ’-এর বৃহত্তর ধারণাই ছিল না। কিন্তু তথাকথিত ‘অসভ্য’, ‘বুনো’, ‘চোয়াড়’ বা ‘লায়েক’রা ‘দেশ’ বলতে বুঝেছিল তাদের বগড়ী পরগণাকেই। এই আঞ্চলিক ‘দেশ’-এর মাটি, সেখানকার পুরনো রাজবংশের অধিকার রক্ষার জন্যই তারা যুদ্ধে নেমেছিল। তাদের জ্বলন্ত আবেগ, তীর-ধনুক-বর্শার সঙ্গে এঁটে উঠতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল ইংরেজদের। শেষরক্ষা হয়নি, অনেকের মতে ইংরেজরা লায়েকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল তাদেরই রাজাকে। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন—রাজা ছত্র সিংহ কি সত্যি বিশ্বাসঘাতক, না কি তিনিও বিদ্রোহীদের পক্ষেই ছিলেন? ইংরেজের চক্রান্তে ‘বিশ্বাসঘাতক’ তকমা লেগেছিল তাঁর গায়ে? আসলে ক্ষমতা যখন কোনওকিছু আত্মসাৎ করতে চায়, তখন এভাবেই করে। আর ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যারা নিজেদের অধিকারের লড়াই করে প্রাণপণ, তারা শেষ পর্যন্ত জিতুক বা হারুক—সংগ্রামের ইতিহাসে তারাই নায়ক। সে যুদ্ধ, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে হোক বা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে, তার তাৎপর্য বা গুরুত্বকে খাটো করে দেখা চলে না। ‘লায়েক-গাথা’র নায়ক-খোঁজের প্রক্রিয়ায় উঠে আসতেই পারে তথাকথিত প্রান্তিক ইতিহাসের এমন অনেক অনালোচিত দিক, যা মূলধারার ইতিহাসে জায়গা করে নেওয়ার দাবি জানাবে সোচ্চারে।
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।