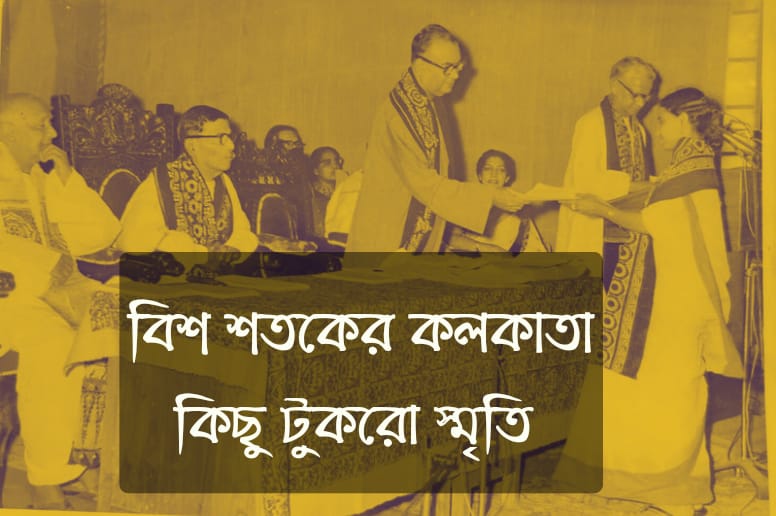আগের পর্ব পড়তে [১]
জীবন খাতার প্রতি পাতায়
প্রত্যেকের জীবনেই থাকে একটা ছেলেবেলা— বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে সেই ছেলেবেলার দিকে যখন তাকাই মনে হয়, আমি যেন দর্শক— এটা যে আমার জীবনেরই ঘটনা, ভাবতে অবাক লাগে। দর্শকের ভূমিকা নিয়ে আমি সেই স্মৃতির পাতাগুলি উল্টেপাল্টে মণি-মুক্তো খুঁজে বেড়াচ্ছি।
আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। জেঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোন মিলে মহা-আনন্দে আছি— মাঝেমাঝেই দূর সম্পর্কের আত্মীয়-পরিজন এসে বাড়িটাকে আরও ভরিয়ে তুলছে— এমনকী কখনও সখনও রাতে শোবার জায়গারও অভাব হয়ে পড়ছে।
আমাদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অতি সাধারণ মানের; মা, জ্যাঠাইমার তৈরি করা জামা ও তাঁদের নিজের হাতে ধুয়ে পরিষ্কার করা পোশাকই আমাদের পরতে হত। জামাকাপড়ের সংখ্যাও ছিল হাতেগোনা।
ছোটবেলার স্মৃতিতে যেটা সবচেয়ে বেশি করে চোখের উপর ভেসে ওঠে, সেটা হচ্ছে আমাদের চার ভাইবোনের কীর্তিকলাপ। আমার বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো— আমার ছোট দুই বোন— একজন আমার চেয়ে সাড়ে তিন বছরের ছোট, নাম তার বীথু (সুজাতা), অন্যজন পাঁচ বছরের ছোট, নাম তার নীতু (সুনীতা)। সবচেয়ে যে উল্লেখযোগ্য সে আমার জ্যাঠতুতো ভাই তাপু (তাপস)—আমার চেয়ে চার বছরের ছোট।
আমাদের অভিভাবকেরা ছোটদের খেলাধূলা বা গল্পের মধ্যে কখনই মাথা গলাতেন না। আমাদের ছোটখাটো কবিতার লড়াই, ছোটখাটো তর্ক বা ডিবেট— তার মধ্যে বড়দের কোনও স্থান ছিল না।
একটা খেলা ছিল— যে কোনও কবিতার একটা লাইন বলত একজন, অপরজনকে সেই কবিতার আগের বা পরের লাইনটা বলতে হত।
একটা খেলা ছিল— যে কোনও কবিতার একটা লাইন বলত একজন, অপরজনকে সেই কবিতার আগের বা পরের লাইনটা বলতে হত।
আমাদের বাড়িতে তখন ‘রেডিও’ ছিল না। এতে কোনও অভাববোধও আমাদের ছিল না। বসার ঘরে ইট দিয়ে ঠ্যাকা দিয়ে মুন্ডিওয়ালা একটা লাঠিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মাইক হিসেবে কল্পনা করে নিয়েছিলাম। সেই মাইকে নিজেরা গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে সারাদিন আমাদের কম্পিত ‘রেডিও স্টেশন’ চালু রেখেছি। এই ছেলেমানুষিতে বড়রা কখনও বিরক্ত হননি।

তাপু অর্থাৎ তাপসের মাথায় এক-একটা আইডিয়া আসত—আর আমরা চারজন মিলে সেটাকে রূপ দেবার চেষ্টা করতাম।
হঠাৎ একদিন তাপুর মাথায় এল ‘প্রাচীর পত্রিকা’ বার করবে। লেগে গেলাম সবাই মিলে সেটার জন্য। ‘প্রাচীর পত্রিকা’র বারো আনা অংশই তাপসের লেখাতে ভর্তি থাকত— আর থাকত খবরের কাগজের কাটিং। এই ‘প্রাচীর পত্রিকা’টি সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর বড় দেওয়ালে টাঙানো হল। আমাদের বাড়িতে যাঁরাই আসতেন. এই পত্রিকার প্রশংসা না করে পারতেন না। প্রাচীর পত্রিকাটির নাম দেওয়া হল ‘লিপিকা’। পনের দিন অন্তর এই পত্রিকা বার হত। (এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, এই পত্রিকার লেখাগুলিকে কেন যত্ন করে রাখিনি। এ ব্যাপারে বড়রাও আমাদের কোনও পরামর্শ দেয়নি, সব লেখাই জমা পড়েছে ওয়েট পেপার বক্সে)।
এরপরেই মনে হল ‘লিপিকা’ নামে একটা ‘মণিমেলা’ তৈরি করলে কেমন হয়! যেই ভাবা, অমনই কাজ শুরু। তখন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র মাধ্যমে কলকাতার নানা জায়গায় মণিমেলা সংগঠিত হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় বিমল কুমার ঘোষ মহাশয় ‘মৌমাছি’ নামে এটার কর্ণধার ছিলেন। কলকাতার নানা অঞ্চলে ‘মণিমেলা’ তৈরি হয়েছিল পাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে। আমরাও পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে মণিমেলা তৈরি করে গান, বাজনা, খেলাধূলা, আবৃত্তি ইত্যাদিতে মেতে উঠেছিলাম। এই সময় আমরা ভাইবোনেরা আবৃত্তি, গান, খেলাধূলা ইত্যাদিতে অনেক পুরস্কার পেয়ে অল্পদিনেই অন্যান্য মণিমেলার মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলাম। তাপস ছিল একটু ঘরকুনো— ও দৌড় ইত্যাদিতে কখনই অংশ নিত না। এই ব্যাপারে আমার ছোট দুই বোন ছিল প্রধান। পরবর্তীকালে বীথু প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় ও তারও পরে শিক্ষকতা করার সময় খেলাধূলার ক্ষেত্রে পারদর্শীতা দেখিয়েছে। নীতু বেথুন কলেজে পড়ার সময় এন.সি.সি. (N.C.C)-তে যোগ দিয়ে ক্যাম্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শীতা দেখিয়েছে। তাপস মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ার সময় নানা ডিবেটে অংশ নিয়েছে আর কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা, প্রবন্ধ লিখে যথেষ্ট সুনাম পেয়েছে।

আর একটি ঘটনা— যেটা আজকালকার মা, বাবাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে… একদিন খেয়াল হল, আমরা কলকাতার ‘রেডিও’তে ‘গল্পদাদুর আসর’-এ অংশগ্রহণ করব, যেই মাত্র ভাবা সেইমাত্র কাজ। তাপস চারজনের নামে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল। যথাসময়ে অডিশনের তারিখ জানিয়ে উত্তরও চলে এল (সেটা হয়তো ১৯৪৮ সনের প্রথম দিকের ঘটনা)। এই ব্যাপারেও আমাদের বাড়ির অভিভাবকেরা সম্পূর্ণ উদাসীন। তখন ১ নং গার্টিন প্লেসে ছিল রেডিও স্টেশন। কীভাবে সেখানে পৌঁছতে হবে. বাবা আমাকে বুঝিয়ে বলে দিয়েছিলেন। আমার দায়িত্বে ছোট ভাইবোনকে অনায়াসেই পাঠিয়ে দিলেন রেডিও স্টেশনের উদ্দেশ্যে।
তখন আমরা কারও কাছেই গান শিখি না, তবে শুনে শুনে ভালোই গান করতে পারি। আর একটা জিনিস ভালো করে পারি—সেটা হচ্ছে আবৃত্তি ও অভিনয়।
যথাসময়ে রেডিও স্টেশনে পৌঁছে করিডোরে বসে আছি— দুরু দুরু বুক নিয়ে—কখন আমাদের ডাক পড়ে অডিশনের।
প্রায় ঘণ্টাতিনেক অপেক্ষা করার পর আমাদের ডাক পড়ল— বাড়ির তিনতলায়। পুষ্পাঞ্জলি সেন মহাশয়া আমাদের কাছে জানতে চাইলেন— আমরা নাটকে অংশ নেবে কি না! আমরা হাতে স্বর্গ পেলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার— আমরা চারজনই অডিশনে পাশ করে গেলাম। যথাসময়ে নাটকে অংশগ্রহণ করে পাঁচ টাকা করে পারিশ্রমিক পেয়েছি।
অতীতের হাসি-মজার দিনগুলি প্রায়ই মনে পড়ে, আর ভীষণ ভাল লাগে। এখনকার ছেলেরা আমাদের সময়কার এই সব ছোটখাটো আনন্দের কথা ভাবতেই পারবে না।
এখন ২০২৩ সালে পৌঁছে আমরাও আর সেই জায়গায় নেই। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই আমরা নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়েছি। নীতু তো ২০১০ সালে মারা গেছে। বীথু তবু তার শিক্ষকতা করার সুযোগে সহকর্মীদের সঙ্গে সাহিত্য, ভ্রমণ ইত্যাদি নিয়ে অবসর জীবনেও নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। তাপস সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক হয়ে বিদেশেই থেকে গেছে। আমি জীবনের আশিটা বছর পার করে আনন্দে আছি নিজের ছোটখাটো লেখা নিয়ে। আর সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে—তাঁর গান গেয়ে, কবিতা পড়ে। মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছি ফেলে আসা সুন্দর দিনগুলির দিকে। এই বয়সে এসে উপলব্ধি করতে পেরেছি—
আনন্দই জীবনের প্রথম ও শেষ কথা—
আনন্দহীন জীবন-ই মৃত্যু।
*ছবি সৌজন্য: লেখক, Istock
সুব্রতা ঘোষ, ডাকনাম স্মৃতি। আবাসনের সকলের কাছে তাঁর পরিচয় মাসীমা নামে। ব্যক্তিত্বময়ী, হাস্যোজ্জ্বল এই মহিলা নব্বই বছর পার করেছেন। এক সময় আকাশবাণী কলকাতাতে গান গাইতেন। যেকোনও বয়সের মানুষের সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপন করার সহজাত ক্ষমতা আছে, তাই অসংখ্য তাঁর অনুরাগী। আশি বছর পার করে ফেসবুকে ঢুকে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। অবসর সময়ে নানা বিষয়ের উপর লেখালেখি করতে ভালোবাসেন।