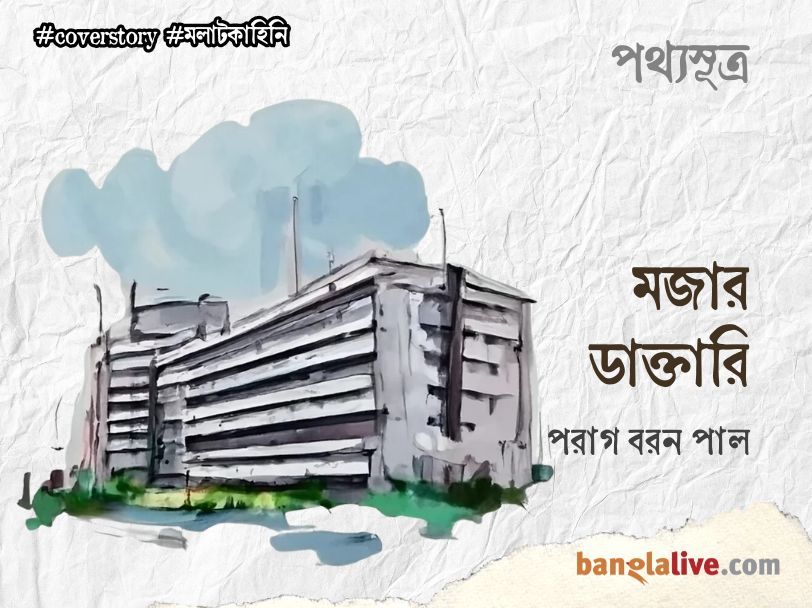ডাক্তারি পড়তেই হবে, এরকম কোনও জোরাজুরি বাড়ি থেকে আমার মাথার উপর ছিল না। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোতেই সুযোগ পাওয়ার পর কোন যুক্তিতে যে ডাক্তারিটাই পড়তে ঢুকেছিলাম, সেটাও এখন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। কিন্তু 1985 সালের অগাস্ট মাসে, এক সকালে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের চত্বরে ঢুকে প্রথমেই যেটা মনে হয়েছিল সেটা হল – বেশ খানিকটা বড় হওয়া গেছে এইবার। আর স্কুলবয় নই, এখন, যাকে বলে গিয়ে – কলেজ স্টুডেন্ট। (Cover Story)
কিন্তু মেডিকেল কলেজের পরিবেশ বা পড়াশোনার পুঙ্খানুপুঙ্খ গল্প ফাঁদতে আমি এখানে বসিনি। সেসব অন্য জায়গায় হবে। বরং এই ডাক্তারি পড়া এবং ডাক্তারি করা – এই দুটো কাজ পরপর করতে গিয়ে যেসব মজার অভিজ্ঞতার সামনে পড়েছি – তাদেরই কয়েকটার কথা বলা যাক।
আমার বাড়ি ছিল হাওড়া বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে। সেখান থেকে কলেজ যেতে দেড় থেকে দু’ঘণ্টা সময় লাগত (তখন বিদ্যাসাগর সেতু হয়নি), ফিরতেও তাই। অতএব ভর্তি হবার বছরখানেক বাদে হোস্টেলে ঠাঁই নিলাম, পড়াশোনার সময় একটু বেশি পাব বলে। এবং হোস্টেলে আমি এমন অনেক কিছু দেখলাম যা আমি তার আগে জীবনে কোনওদিন দেখিনি। যেমন রাত (বা ভোর) সাড়ে তিনটেয় শুয়ে বেলা বারোটার সময় উঠে মুচকি হেসে বলা ‘ব্রেকফাস্টের পয়সাটা কেমন বাঁচালাম বল’, বা আমার পাশের রুমের সিনিয়রের ছমাস একই জামাপ্যান্ট পরে থেকে তারপর সেটা ফেলে দিয়ে অন্য একটা জামাপ্যান্ট কিনে পরতে শুরু করা, কিংবা একজনের দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার সুযোগ নিয়ে অন্য একজন তার টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে ফেলা… ইত্যাদি। এই তালিকা সুবিশাল, তবে সবটা এখানে না লেখাই ভাল।
এসবের অবশ্যম্ভাবী ফল যা হয় তাই হল। আমার পাখা গজাল।
হোস্টেলে ভেজ মিলের দাম ছিল তিন টাকা, এগ মিল সাড়ে তিন টাকা এবং ফিশ মিল চার টাকা। সপ্তাহে একদিন চিকেন, দাম সাড়ে চার টাকা। দেড়-দুটাকায় জলখাবার হয়ে যেত। যেহেতু হাতে টাকা থাকত গোনাগুনতি, আর সিনেমা দেখা-টেখা বাবদ খরচাগুলো মাঝে মাঝেই একটু বেশি হয়ে যেত, তাই অনেকসময়ে সপ্তাহের শেষের দিকে ট্যাঁকে টান পড়ত। তখন ভরসা ছিল শিয়ালদা মার্কেটে ‘কালীর দোকান’। সেখানে এক টাকায় চারটে রুটি আর যত-চাই-আলুভাজা পাওয়া যেত। আমরা অনেকে (তাদের অধিকাংশই এখন বিগশট) সেখানে ট্রাক-লরির খালাসিদের সঙ্গে বসে আরাম করে খেতাম। তাই করতে গিয়ে একদিন এক কাণ্ড হল।
সেদিন বন্ধুরা মিলে তাস (অকশন ব্রিজ) খেলতে খেলতে কখন যে রাত একটু বেশি গভীর হয়ে গেছে খেয়াল করিনি কেউই। যখন খেয়াল হল তখন হোস্টেলের মেস বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই চল কালীর দোকান। ওটা সারারাত খোলা থাকত। আমরা চার বন্ধু মিলে খেয়েদেয়ে কালীর দোকান থেকে ফেরার সময় দেখলাম একটা জায়গায় ভারী গণ্ডগোল হচ্ছে। তাকিয়ে দেখে বুঝলাম – ব্যাপারটা মাতালের কাণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের মধ্যে তিনজন হোস্টেলের দিকে হাঁটা লাগালাম, কিন্তু একজন একটু বেশি কৌতুহলী; সে বলল ‘তোরা এগো, আমি একটু দেখে আসছি’। বলে বেশ মৌজ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে এগিয়ে গেল মাতালের কাণ্ডকারখানা দেখতে। আমরা হোস্টেলে ফিরে এসে দাঁতটাত মেজে শুয়ে পড়ার তোড়জোড় করতে লাগলাম, তখনও সে আসে না। এযুগের মতো মোবাইল ফোন তো আর ছিল না, কাজেই খবর নেওয়ার উপায়ও নেই। ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পরেও যখন সে ফিরল না, তখন একটু চিন্তাই হতে লাগল। আরো খানিকক্ষণ দেখে আমরা আবার বেরোলাম ওকে খুঁজতে। যেখানে আগে গণ্ডগোল হচ্ছিল সেই জায়গা এখন শুনশান, আশেপাশে কেউ নেই। কেউ সেরকম কিছু বলতেও পারল না। অগত্যা আমরা আবার ফিরে এলাম হোস্টেলের ঘরে।
ভোর ছটা নাগাদ দরজায় ঠকঠক। সে ফিরেছে। সঙ্গে দুজন লোক। দরজা খুলতেই বলল – ‘এক হাজার টাকা হবে?’ কী হয়েছে, জিজ্ঞেস করায় বললো – ‘পরে বলছি, আগে টাকা’। এক হাজার!!! সে যে তখনকার দিনে অনেক টাকা, সেটা খাবারের দাম দেখে পাঠকরা আন্দাজ করেছেন নিশ্চয়ই। সত্যি বলতে কী, 1990 সালে পাস করে বেরোবার পর ইন্টার্নশিপে আমাদের মাসমাইনে ছিল 1015 টাকা, আমরা মজা করে বলতাম ‘দশ-পনেরো টাকা মাইনে পাই’। সে যাই হোক, দু-তিনটে ফ্লোর ঘুরে ঘরে ঘরে ঢুকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোগাড় হল এক হাজার টাকা। তাই নিয়ে ওই দুই তালেবর চলে গেলেন। তারপর জিজ্ঞেস করে জানলাম – যখন সে দাঁড়িয়ে রগড় দেখছিল, তখন হঠাৎ পাশে একটা পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়ায়, এবং তারা নির্বিচারে অনেক লোককে ঘাড়ে ধরে ভ্যানে তুলে নেয়, যার মধ্যে সেও ছিল। ওর কোনও কথাই কেউ শোনেনি। তারপর সোজা মুচিপাড়া থানার লকআপ। এক-একজন করে লকআপ থেকে বের করে তাদের নাম জিজ্ঞেস করে লেখালেখি হচ্ছিল। ওর টার্ন আসতে অনেক দেরি হয়। আর এই সময়ের মধ্যে, যত চোর গুন্ডা পকেটমাররা লকআপে ছিল সবাই মিলে, একটু ভদ্রলোকের মতো দেখতে ছিল বলেই বোধহয়, তাকে নিয়ে প্রচুর খোরাক করে। কেউ মাথায় হাত বোলায়, কেউ কাতুকুতু দেয়, কেউ ওঠবোস করায়, কেউ বা আরও খারাপ কিছু। অবশেষে ওর টার্ন আসে। সব কথা শুনে ‘মাত্র’ একহাজার টাকার বিনিময়ে তাকে কেস না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই টাকা আনতেই তার হোস্টেলে আগমন।
সেই একই অতি-কৌতূহলী বন্ধু, প্রেমে পড়ল আমাদেরই এক ক্লাসমেটের। ফাইনাল ইয়ারে। ধরা যাক সেই মেয়েটির নাম মল্লিকা। কারোরই আসল নাম বলছি না, কারণটা খুব সহজ। এই মল্লিকার সঙ্গে সে নাকি কোনওদিনই কথা বলে উঠতে পারে না… আর রোজ সন্ধ্যেবেলা তাই নিয়ে আমাদের কাছে ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান…. কী করে বলব, কখন বলব, কী বলব… সব ব্যাপারেই তাকে নাকি একটু গাইড করে দিতে হবে। ঠিক এই অবস্থায়, তাকে একদিন সন্ধ্যেবেলা পড়াশোনার পর আমাদের আর এক ক্লাসমেট, নাম ধরা যাক ইন্দ্রনাথ, বলল – ‘মল্লিকা তোর সঙ্গে কথা বলে না? আমার সঙ্গে তো কত কথা বলে!’ ঘটনাচক্রে, তাকে কোনওদিন মল্লিকার আশেপাশেও দেখা যায়নি। আমরা সবাই কৌতুহলী হয়ে বললাম – ‘তোর সঙ্গে মল্লিকার কী কথা হল আবার?’ সে তখন বলল – ‘এইতো আজকেই একসঙ্গে ক্লাস করছিলাম – ওয়ার্ড ক্লিনিক… তখনই তো আমার সঙ্গে কথা হল।’ আমরা আবার সাগ্রহে বললাম – ‘কী কথা?’ ইন্দ্রনাথ দরজার কাছে গিয়ে পেছন ফিরে বলল – ‘আমায় মল্লিকা বলল – গায়ে পড়ছিস কেন, সরে দাঁড়া’…. বলেই দে দৌড়। পেছনে আমাদের সেই বন্ধুও তাড়া করেছে ততক্ষণে।
সেই ইন্দ্রনাথ ছিল এক ভারি মজার ছেলে। এখন সে বিলেতবাসী। তার একটা মস্ত ঝোলা গোঁফ ছিল। একদিন হঠাৎ দেখি সে মুখের সামনে হাত দিয়ে কথাবার্তা বলছে, কিছুতেই হাত সরাচ্ছে না। আমরা বললাম, ‘কী রে, গোঁফ কামিয়েছিস নাকি?’ উত্তরে সে ইতিবাচক ঘাড় নাড়ল। আমরা বললাম, ‘ঠিক আছে, হাত সরা, দেখি।’ সে বলল, ‘খুব খারাপ দেখাচ্ছিল।’ বেশ, কিন্তু ‘দেখাচ্ছিল’ বলছিস কেন? ইন্দ্রনাথ বলল, ‘আসলে খুব খারাপ দেখতে লাগছিল, তাই একটু মেক আপ করেছি আরকি।’ সেটা আবার কী? জোর করে ওর হাত সরিয়ে দিয়ে দেখা গেল – কামানো গোঁফের জায়গায় সে কালো ডটপেন দিয়ে গোঁফ এঁকেছে, কিরিকিরি করে কালো দাগ দিয়ে।
ফাইনাল এমবিবিএস পাস করার পর একবছর আমাদের যেটা করতে হত, তার নাম Rotating Internship… অর্থাৎ হাসপাতালের সব ডিপার্টমেন্টে আমাদের ঘুরে ঘুরে ডিউটি পড়ত। এর মধ্যে তিনমাস মেডিসিন, তিনমাস সার্জারি, আর তিনমাস গাইনি ওয়ার্ডে। বাকি তিনমাসের মধ্যে ছিল Eye, ENT, Chest Medicine, Psychiatry, Skin & Venereal Diseases, Community Medicine (এখানেই সবরকমের vaccine দিতে শিখেছিলাম), Forensic Medicine, Paediatrics, Urology ইত্যাদি। এই সময়ের দুটো মজার ঘটনা বলি।
গাইনিকোলজিতে কাজ করার সময়ে আমাদের সপ্তাহে দুদিন লেবার রুম ডিউটি পড়ত। Normal labour, অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রসব প্রক্রিয়া পরিচালনা করা এবং তারপর বাচ্চার প্রাথমিক শুশ্রুষার ট্রেনিং হত এখানে। প্রচুর ডেলিভারি হত, এবং আমাদের এই লেবার টেবিল থেকে ওই টেবিলে ছোটাছুটি করতে হত। একসঙ্গে চার-পাঁচজন ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে বেশ হিমশিম অবস্থা হয়ে যেত। এরই মধ্যে একদিন, নাইট ডিউটি ছিল। শীতকাল। আমার এক সহপাঠিনীর সঙ্গে আমাদের এক সিনিয়র দিদির একটু কথা কাটাকাটি হল। রেগে মেগে আমার সেই সহপাঠিনী গটগট করে বেরিয়ে গেল। লেবার রুমের ঠিক বাইরে বেরিয়ে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল, সেখানেই গিয়ে গোমড়া মুখে বসে রইল সে। আমরা নিজেদের মতন কাজ করছি, হঠাৎ শুনি বাইরে আমাদের এক আয়া মাসি কাকে যেন খুব বকাবকি করছেন। খালি বলছেন ‘কোনও কথা নয়, চলো, শিগগির চলো’। যাকে বলছেন সেও কী যেন বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু আয়া মাসি কোনও কথাই শুনছেন না। গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমাদের আক্কেল গুড়ুম! আমাদের সেই সহপাঠিনী ওই বেঞ্চে শুয়ে নাকি মাথায় ওড়না মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল! আর তাকে আয়া মাসি ডাক্তার বলে চিনতেন না। ভেবেছেন পেশেন্ট। কাজেই তাকে ডেকে ঘুম থেকে তুলে হাত ধরে বেডে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন।
দ্বিতীয় ঘটনা VD, অর্থাৎ Venereal Diseases আউটডোরে। এখন এই নামটা পাল্টে গিয়ে একে STD বা Sexually Transmitted Diseases বলা হয়। ওই সময় এই ধরনের রোগের সিংহভাগ জুড়ে থাকত সিফিলিস এবং গনোরিয়া। প্রায় সবক্ষেত্রেই ঘটনাক্রমটা ছিল একই – বারবনিতা-গমন, সংক্রামিত হওয়া, এবং সেই সংক্রমণ অন্যত্র ছড়িয়ে দেওয়া, বাড়িতে বা বাইরে। এখন Safe Sex Practices ব্যবহারের ফলে এই ধরনের রোগের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। সে যাক।
ডাক্তারি করার প্রাথমিক কাজ হচ্ছে রোগীর হিস্ট্রি নেওয়া। মজার কথা, এইসব রোগীরা অনেকেই একটা গল্প বানিয়ে বলত, সেটা হল – পাবলিক টয়লেটে বাথরুম করেছিলাম, তারপরই এরকম হয়েছে। আমরা সবাই জানি যে সরাসরি সংস্পর্শ বা Contact ছাড়া এইসব রোগ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ জীবাণুদের ওরকম লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠে কাউকে সংক্রামিত করার অভ্যাস নেই মোটেই। ওগুলো বাজে কথা।
এই ডিপার্টমেন্টে আমাদের এক স্যার ছিলেন, ভারী নির্লিপ্ত প্রকৃতির। তাঁর পরপর কথাগুলো ছিল এরকম –
কী হয়েছে?
ও আচ্ছা।
দেখি, খুলুন।
হুম, খারাপ পাড়ায় গিয়েছিলেন?
যাঁরা যাঁরা এর উত্তরে হ্যাঁ বলতেন, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশন লেখার কাজটা তখনই হয়ে যেত। কিন্তু কিছু পেশেন্ট ঠিক এই সময় ওই ওপরের গল্পটা বলতে শুরু করতেন। আর ঠিক তখনই স্যার পাশের দিকে তাকিয়ে ডাকতেন – ‘শঙ্কর!’
পাশ থেকে সেই শঙ্করবাবু এসে সেই রোগীকে বলতেন – ‘আপনি আসুন আমার সঙ্গে।’ বলে রোগীকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে উনি দরজা বন্ধ করে দিতেন। একটু বাদে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে রোগী বলতেন – ‘হ্যাঁ স্যার, গিয়েছিলাম খারাপ পাড়ায়।’ মাঝে বন্ধ দরজার আড়ালে যে কী ঘটতো কে জানে! দু একজন রোগীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘কী ব্যাপার দাদা, মারধর করলেন নাকি উনি?’ তাতে সবাই জিভ কেটে বলত – ‘না না’। ‘তাহলে?’ এর উত্তর কোনোদিনও কেউ দেয়নি। কাজেই শঙ্করবাবু যে কী করতেন আমরা কেউই আজ অবধি জানতে পারিনি।
এই ওয়ার্ডের আরও অনেক গপ্পো আছে, যেগুলো লেখা যাবে না।
যাইহোক, ইন্টার্ন হাউসস্টাফ ইত্যাদি স্তর পেরোনোর পর একবছর এদিক ওদিক খেপ মেরে শেষমেশ জয়েন করলাম হেলথ সার্ভিসে। প্রথমেই রুরাল পোস্টিং। যেখানে পোস্টেড হলাম সে-জায়গাটার নাম পলাশীপাড়া, নদীয়া জেলায়। প্রায় মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি। ইতিহাসখ্যাত পলাশী থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে। ৩০ অগাস্ট, ১৯৯৪ – এখনও মনে আছে তারিখটা।
আপাদমস্তক শহুরে ছেলে, হঠাৎ গ্রামে গিয়ে পড়ায় প্রথম প্রথম অসুবিধে হল বেশ। প্রসঙ্গত, তখনও গ্রাম এখনকার মতো শহর হয়নি। সন্ধ্যে হলেই নিঝুম অন্ধকার নামত চারদিকে, রাত বাড়লে কোয়ার্টারের জানলার পাশেই শেয়াল ডাকত। দূরদর্শনে তখন একটাই চ্যানেল (সময়টা বোঝানোর জন্য বললাম, আমার কোয়ার্টারের ঘরে যদিও তখন টিভি ছিল না)। ইন্টারনেট বা মোবাইল ফোন জাতীয় কোনও জিনিসের নামই কেউ শোনেনি। আমার হেলথ সেন্টারে একটাই ল্যান্ড ফোন ছিল, আর সেটা ছিল খারাপ। চিঠি লেখাই ছিল একমাত্র যোগাযোগের উপায়। দুসপ্তাহ অন্তর অন্তর সপ্তাহান্তে বাড়ি আসতাম, বাড়ি এলে বাড়ির লোকে জানতে পারত যে আগের সপ্তাহে ঠিকঠাক পৌঁছেছিলাম। এসবে অবশ্য কিছু মনে হয়নি, কারণ এটাই তখন ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যেটায় মনে হয়েছিল সেটা হল উদ্ভট কাজের চাপ। ডাক্তার ছিলাম মোটে দুজন। খাতায়-কলমে ’15-Bedded Block Primary Health Centre (BPHC)’ হলেও মাঝেমাঝেই বেড-মেঝে মিলিয়ে পেশেন্ট ভর্তি থাকতো ৫০ থেকে ৬০ জন, কারণ কাউকে ফেরানোর চল ছিল না। আউটডোরেও রোজ পেশেন্ট হত প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০। আর অনেক পেশেন্টের দাবিও ছিল বেশ মজার। কারোর হয়তো হাঁটুতে ব্যথা, আমি ওষুধ লিখলাম, সে তখন বলল, ‘কই, আগেরজনকে তো যন্ত্র ঠেকিয়ে দেখলে, আমায় তো দেখলে না!’ যন্ত্র অর্থাৎ স্টেথোস্কোপ। কথা না বাড়িয়ে তার হাঁটুতে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়তে হত।
যাকগে, যা বলছিলাম। আমাদের হেলথ সেন্টারে তিনমাস অন্তর একদিন করে লাইগেশন (বন্ধ্যাত্বকরণ) অপারেশনের ক্যাম্প হত। তখন ভারত সরকার সত্যিই জন্মনিয়ন্ত্রণ চায়, তাই এই কাজে সরকারি incentiveএর ব্যবস্থা ছিল, যাতে লোকে আরও বেশি করে এই কাজে উৎসাহী হয়। পেশেন্ট শুধু নয়, ডাক্তারদেরও কিছু অতিরিক্ত উপার্জন হত – পেশেন্ট-পিছু ৬ টাকা ৭৫ পয়সা। ওখানে আমরা দুজন ডাক্তার পোস্টেড ছিলাম – anaesthesia দেওয়ার কাজটা করতাম আমি, অপারেশন করার কাজটা করত অন্যজন। দিনে মোটামুটি একশো থেকে দেড়শো পেশেন্টের অপারেশন হত। সকাল থেকে চলতো চেক আপ, কোনও কারণে অপারেশনে অসুবিধে আছে – এরকম পেশেন্টদের নাকচ করা হত। দুপুরে খেয়েদেয়ে অপারেশন শুরু হত, শেষ হত মাঝরাতে বা পরদিন ভোরে। বিরাট এক কর্মযজ্ঞ চলত, যাতে সামিল হতে হত হাসপাতালের সবস্তরের কর্মীকেই। কিন্তু সবাই তো আর পেমেন্ট পেতেন না, কাজেই আমরা দুজন ডাক্তার মিলে ঠিক করেছিলাম – দুজন মিলিয়ে যে টাকাটা আমাদের প্রাপ্য হবে – ওই ১৩০০ থেকে ১৬০০-র মধ্যে একটা কিছু থাকত পরিমাণটা – সেটা আর আমরা নেব না। সেটা দিয়ে পরদিন হাসপাতালের সব কর্মীকে রাতে মাংস ভাত খাওয়ানো হত। এটাকে আমরা বলতাম ‘FPর ফিস্ট’। FP, অর্থাৎ Family Planning.
আমি তখন সদ্যবিবাহিত। আমার স্ত্রীও ডাক্তার, সে তখন একটা পরীক্ষা দিয়ে দুদিন ছুটি কাটাতে আমার কোয়ার্টারে গেছে। সে-কোয়ার্টারে একটা ঘরে একটাই খাট আর একটা আলনা, আর রান্নাঘরে একটা মিটসেফ আর স্টোভ। একটা ঘর ফাঁকা। আমার অন্য ডাক্তার কলিগ অনেকদিন সেখানে আছেন, স্ত্রীপুত্র এবং আসবাবপত্র-সহ তাঁর কোয়ার্টার একেবারে জমজমাট। তাই, ঠিক হল ফিস্ট-এর সব রান্নাবান্না আমার কোয়ার্টারের ওই ফাঁকা ঘরটাতেই হবে।
দুপুরের দিকে বাজার টাজার করে আমার কোয়ার্টারে সব রাখা হল। বিকেল থেকে আনা হতে লাগল বিরাট বড় বড় কিছু বাসনকোসন। আর সন্ধ্যে থেকে শুরু হল রান্না। পুরো ব্যাপারটা দেখাশোনা করছিলেন আমাদের হেলথ সেন্টার-এর ডায়েট কন্ট্রাক্টর, অর্থাৎ রোগীদের খাবার দেওয়ার দায়িত্ব যাঁর। ধরা যাক তাঁর নাম ‘গোকুল ঘোষ’। আসল নাম এটা নয়, তবে কাছাকাছিই। তিনি সেদিন অন্য জায়গা থেকে রান্নার লোক নিয়ে এসেছিলেন, কারণ হাসপাতালের রাঁধুনিদের ওই দেড়শো জন লাইগেশন পেশেন্টের রান্না করে আর অন্য কাজের সময় থাকতো না। ফিস্ট-এর জন্য বাজার করা এবং রান্না করা – সব দায়িত্বই গোকুলবাবুর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।
আমি সেদিন সারাদিনই ব্যস্ত। আমার স্ত্রী একা কোয়ার্টারে আছেন। গোকুল বাবু মাঝে মাঝেই গিয়ে আমার স্ত্রীকে ‘বৌদি, কাঁচা বাজার রেখে গেলাম’, ‘বৌদি, ডেকচি রেখে গেলাম’, ‘বৌদি, কড়াই রেখে গেলাম’ ইত্যাদি বলে কিছু না কিছু রেখে আসছেন। তারপর সন্ধ্যেবেলা রান্না শুরু হয়েছে, গোকুলবাবু নিজে আমার কোয়ার্টারে বসে মাংস রাঁধছেন… আমি তখনও হাসপাতাল থেকে বেরোতে পারিনি। রাতে খেতে এলাম আমার কোয়ার্টারে। খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোই হল। তারপর একটু গল্পসল্প সেরে যখন সবার যাওয়ার সময় হল, তখন হঠাৎ আমাদের দুজন কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার সমরবাবু আর বিপুলবাবু (এঁদের আসল নামই লিখলাম। এঁরা আমার গ্রাম-বাসকে সুখকর করতে পদে পদে যেভাবে আমায় সাহায্য করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান হয়নি কোনওদিন। আজ এই সুযোগে জানিয়ে রাখলাম। সমরবাবু আর নেই। বিপুলবাবু আছেন।) বললেন, ‘যাই, গোকুলদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।’ আমি বললাম, ‘ওমা, সে কী! বাচ্চা নাকি যে এগিয়ে দিতে হবে!’ সমরবাবু আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘সে অনেক কথা, পরে বলব।’
পরদিন সকালে সমরবাবু এসে আমি ও আমার স্ত্রীয়ের কাছে গোকুলবাবুর ঠিকুজি খুলে বসলেন। একেবারে প্রথম বাক্যটিই ছিল – ‘গোকুলদা খুব ভালো লোক, খুব সৎ লোক, খালি ওই একটু আট-দশটা মার্ডার করেছে আরকি, ও কিছু নয়। তাই অপোনেন্ট সবসময়ই সুযোগ খোঁজে, রাতের বেলা গোকুলদাকে একা পেলেই খুন করে দেবে।’ শুনে তো আমাদের প্রায় উল্টে পড়ার জোগাড়! বলে কী! সারা সন্ধ্যে কোয়ার্টারে একা আমার স্ত্রী ছিলেন, সেই অবস্থায় উনি রীতিমতো ঘর-বার করেছেন, এতো রীতিমত সাংঘাতিক ব্যাপার! সমর বাবু বললেন, ‘না না, ও কিছু নয়। এখন ও ভালো হয়ে গেছে।’ বলে গোকুল ঘোষের পুরো জীবন কাহিনিটা শোনালেন। সেটা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।
আর একদিন, আউটডোর সেরে কোয়ার্টারে এসে ঢুকেছি, কিছু একটা নিয়ে আবার বেরোব, কোনও একটা কাজ বাকি আছে – এরকম এক পরিস্থিতি। দরজাটা খোলা। বেরোবার জন্য পিছন ফিরেই দেখি, দরজা দিয়ে ঢুকে মাথা বাড়িয়ে আছে তিন-ফুটিয়া একটা কুমির টাইপের জীব। আমার এবং তাঁর মাঝখানে শুধু আমার খাট। দরজা দিয়ে বেরোনোর কোনও উপায় নেই। আমার এমনিতেই একটু জীবজন্তুতে ভয় বেশি, তার ওপর এরকম একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে আরও ঘাবড়ে গিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম। এর পরের মিনিট দুয়েক দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে চেয়েই কাটল। সেও নড়ে না, আমিও না। ভারী রোমান্টিক ব্যাপার আরকি! এমন সময় দরজার কাছে বিপুল বাবুর গলা শুনে আমার যেন ধড়ে প্রাণ এল, এবং গলায় আওয়াজও এল। আমার চেঁচামেচি শুনে বিপুল বাবু এসে একটা লাঠি দিয়ে ওটাকে ভয় দেখাতেই ওটা ধীরেসুস্থে বেরিয়ে গেল। আমাকে আশ্বস্ত করে বিপুলবাবু বললেন, ‘ও কিছু নয়, গোসাপ। মাঝে মাঝে বাড়িতে ঢোকে।’
গপ্পো অনেক। সম্পাদিকা আমায় যত শব্দ মঞ্জুর করেছিলেন, তা ছাড়িয়ে ফেলেছি অনেকক্ষণ আগেই। তাই এবার থামা যাক। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর পরে, আজ, যখন সেই দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাই, তখন একটাই কথা আমার বারবার মনে হয় – এতরকম ঝুটঝামেলা সত্ত্বেও আমি বা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের কেউই কিন্তু সেই সময়ে হাল ছেড়ে দিইনি। লড়ে গেছি। অল্পে খুশি থাকতাম, তাই দারুণ কিছু অভিযোগও করিনি কেউ। সবস্তরের নানান রকম মানুষের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতায়, সত্যি বলতে কী, আমার মনে হয়, আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। জীবনকে জেনেছি, চিনেছি, বোঝবার চেষ্টা করেছি। বাধা-বিপত্তিকে জয় করার চেষ্টা করেছি বুক চিতিয়ে।
তাই আমার অতীতকে আমার সেলাম। সে না থাকলে বর্তমান আমার কাছে পানসে হয়ে যেত।
পেশাগতভাবে ডাক্তার ও নেশাগতভাবে গায়ক।