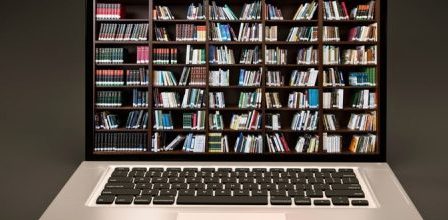গ্রন্থাগারিক পদের জন্য ইন্টারভিউ দিতে ঢুকেছেন এক পরীক্ষার্থী। ঢুকেই মুখে আঙুল দিয়ে রইলেন। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন,
– আপনার নাম বলুন।
পরীক্ষার্থী মুখ থেকে আঙুল না সরিয়ে ঠোঁটের মৃদু ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন,
– চুপ।
প্রশ্নকর্তা এবারে খানিক বিরক্ত। বললেন,
– আরে নামটা তো বলুন!
পরীক্ষার্থী দেওয়ালে পেরেক ঠোকার মতো এবারে আঙুলটি ঠোঁটের উপরে প্রায় খোদাই করে দিয়ে আরও মৃদুভাবে বললেন,
– চুপ করুন। চুপ।
প্রশ্নকর্তার মুখে এবারে স্মিত হাসি। বললেন,
– আপনি মনোনীত হয়েছেন। শুধু আপনিই। আজ থেকেই কাজ শুরু করে দিন।
একটা বিরাট হলঘরের মধ্যে আলমারি বোঝাই করা রাশি রাশি বই আর তার সামনে হরেক জায়গায় ‘কথা বলা নিষেধ’ ছাপানো বোর্ডের কথা বললে আজকের প্রজন্মের প্রতিনিধিরা হয়তো অবাক চোখে তাকাবে। বইয়ের গন্ধ নিয়ে চিরাচরিত লাইব্রেরিগুলো যেমন প্রায় উবে গিয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই বিলীন হয়েছে গ্রন্থাগারের নিয়মনকানুনও। শহর মফসসলের বিভিন্ন প্রান্তে টিমটিম করে জেগে থাকা, হাতে গোনা গ্রন্থাগারেরা আজ অন্তিম যাত্রার দিন গোনে। বেলা যে পড়ে এল, এবার ঘুম। ইট-কাঠ পাথরের গ্রন্থাগারের জায়গায় রাক্ষসের মতো থাবা বসিয়েছে ডিজিটাল লাইব্রেরি। আমার এক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ বন্ধু সম্প্রতি বলছিল,
– ডিজিটাল লাইব্রেরিতে হাইপারলিঙ্কের হাতচিহ্ন একদিকে যেমন এই বই থেকে ওই বই, এক রেফারেন্স থেকে অন্য রেফারেন্সে যাওয়ার জন্য আয় আয় চই চই বলে ডাক দেয়, ঠিক তেমনভাবে এই হাত যেন সাবেকি গ্রন্থাগারের দরজার সামনে খাড়া হয়ে বলে, ওরে থাম, থাম, থাম, থেকে থাক। এ এক আশ্চর্য সমাপতন।
ডিজিটাল লাইব্রেরি নামটার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁদের বোঝার সুবিধার জন্য বলা যেতে পারে, এ আসলে এক বাইনারি পুস্তকালয়। বই-ম্যাগাজিন-জার্নাল-খবরের কাগজ এখানে সঞ্চিত থাকে তাদের ডিজিটাল অবতারে। বই বাড়লে এ ধরনের লাইব্রেরির নতুন আলমারি কেনার প্রয়োজন পড়ে না। নাকের উপরে চশমাটা আরও একটু ঠেলে দিয়ে ক্যাটালগ লেখার জন্য প্রৌঢ় গ্রন্থাগারিকের কাজ বাড়ে না। মই বেয়ে উপরের তাকে উঠে বই পেড়ে নেওয়ার সাবেকি প্রথার বদলে বইটাই হুশ করে নেমে আসে ব্রাউজারের গহ্বরে। ডাউনলোডিং। হাজার পাতার বই নিমেষে গিলে ফেলে ডেস্কটপ-ল্যাপটপ-মোবাইল ফোনের মেমোরি। এ বইয়ের পাতা উল্টানো যায় না, আঙুল আদরে তা স্ক্রল হয় শুধু। যাঁদের মনের মধ্যে ‘ডিজিটালেই জন্ম আমার, যেন ডিজিটালেই মরি’ ধরনের কলার টিউন বাজে, তাঁরা এই বাইনারি লাইব্রেরি নিয়ে মহা উল্লাসে মাতেন। ছররা বন্দুকের গুলির মতো আউড়ে যান একের এক বুলেট পয়েন্ট। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, “লাইব্রেরি যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?” কলার উঁচিয়ে মুখে একগাল হাসি মাখিয়ে তাঁরা জানাতেই পারেন, “বইয়েরো তাক পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে!”

উপকারিতাবিধানের প্রথম পয়েন্ট— এমন গ্রন্থাগারে যাওয়ার জন্য আসলে কোথাও যাওয়ারই দরকার নেই। লাইব্রেরির ওয়েবসাইটে গিয়ে সার্চবারে নিজের বইটার কথা জানালেই হল। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে ওই বই। মানে, নির্দিষ্ট কোনও কম্পিউটারের প্রয়োজন নেই। পড়া যাবে যত্রতত্র, পরিশ্রম নামমাত্র। তিন নম্বর কথা, এই বইয়ের কোনও ভর নেই। তাই সঙ্গে থাকা ঝোলাব্যাগেরও কোনও ভার নেই। বাইনারি লিপির শূন্য আর একের জাদুতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতও ছোট্ট এক ফাইল হয়ে ঘুমোবে শান্তিতে। চার নম্বর, প্রফেসর শঙ্কুর অ্যানাইহিলিন বন্দুক রেখে দেওয়া আছে আমাদের হাতের মুঠোয়। বইটা পড়া হয়ে গেলে, কিংবা কয়েক পাতা পড়ার পরে আর ভাল না লাগলে উড়িয়ে দিলেই হল। মিনমিন করে পর্দার উপরে কম্পিউটার ভাসিয়ে দেবে একটা প্রশ্ন। ‘আপনি কি সত্যিই ফাইলটাকে ডিলিট করে দিতে চান?’ এন্টারে বাড়ি মেরে বলা যেতে পারে, চাই চাই চাই। কাগজের বইতে এমন সুযোগ কই? বই ফেরত দিতে যাওয়ার ঝামেলাও তো কম নয়। আর অপছন্দের বই হলে বিরক্তির সূচক আরও ঊর্ধ্বমুখী হয়। বই পছন্দ হলে ইচ্ছেমতো পাতার প্রিন্ট নিয়ে রেখে দেওয়া যেতে পারে নিজের সংগ্রহে। অন্যকে পড়াতে চাইলে ফাইলটা বন্ধু-বান্ধব-পরমাত্মীয়র সঙ্গে শেয়ার করে নেওয়া যেতে পারে নিমেষে। বাইনারিপ্রেমীরা বলেন, ডিজিটাল লাইব্রেরির উপকারিতার তালিকা আসলে অন্তহীন। যতই পয়েন্ট যোগ করা হোক, তা আসলে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ।
ডিজিটাল লাইব্রেরি নামটার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁদের বোঝার সুবিধার জন্য বলা যেতে পারে, এ আসলে এক বাইনারি পুস্তকালয়। বই-ম্যাগাজিন-জার্নাল-খবরের কাগজ এখানে সঞ্চিত থাকে তাদের ডিজিটাল অবতারে। বই বাড়লে এ ধরনের লাইব্রেরির নতুন আলমারি কেনার প্রয়োজন পড়ে না। নাকের উপরে চশমাটা আরও একটু ঠেলে দিয়ে ক্যাটালগ লেখার জন্য প্রৌঢ় গ্রন্থাগারিকের কাজ বাড়ে না। মই বেয়ে উপরের তাকে উঠে বই পেড়ে নেওয়ার সাবেকি প্রথার বদলে বইটাই হুশ করে নেমে আসে ব্রাউজারের গহ্বরে। ডাউনলোডিং। হাজার পাতার বই নিমেষে গিলে ফেলে ডেস্কটপ-ল্যাপটপ-মোবাইল ফোনের মেমোরি। এ বইয়ের পাতা উল্টানো যায় না, আঙুল আদরে তা স্ক্রল হয় শুধু।
২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করা এক সমীক্ষা তার রিপোর্টে বলেছিল, সপ্তাহে অন্তত একবার লাইব্রেরি যান এমন মানুষের সংখ্যা ১৬ শতাংশ। আর খুব কম লাইব্রেরিমুখো হন, এমন মানুষ ৪৭ শতাংশ। কল্পনা করতে ক্ষতি নেই, ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টেছে যত, ইট-কাঠ সিমেন্টের লাইব্রেরিমুখো মানুষের সংখ্যাও কমেছে তালে তাল মিলিয়ে। ওয়াকিবহাল শিবিরের মানুষেরা অবশ্য ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করেন,
– সাবেকি লাইব্রেরির বদলে ডিজিটাল গ্রন্থাগারের দিকে মন দিচ্ছেন, এমন বইপ্রেমীর সংখ্যা কি বাড়ছে ক্রমশ?
বাহাত্তর ফন্টে যে উত্তরটা সামনে চলে আসে, তা খড়্গ তুলে জানান দেয়, ‘না।’ দুঃখের কথা হল, মানুষের বই পড়ার অভ্যেসটাই যে ক্রমশ তলানিতে। বিশ্বজুড়ে এমন কিছু আধ-পাগলা মানুষ আছেন, যাঁরা বইগুলোর ডিজিটাল সংস্করন করছেন, দিনের পর দিন প্রবল পরিশ্রম করে স্ক্যান করে ডিজিটাল রূপ দিচ্ছেন হারিয়ে যাওয়া, পুরনো হয়ে যাওয়া, আর মুদ্রণ না হওয়া বইয়ের। বলছেন, সার্চ মেরে দেখো ভাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। তবে কুঁকড়ে যাওয়া লজ্জাবতী পাতার মতো এই রতন খোঁজার লোক দুনিয়াজুড়ে মুখ লুকোচ্ছেন, অন্তত সংখ্যার হিসেবে। আমাদের জেন এক্সরা আজ শৈশবে স্মার্ট ক্লাস আর কৈশোর-যৌবনে স্মার্ট জীবনের সন্ধানী। রেফারেন্স স্টাডির অবকাশ আজ ব্যস্ত ছাত্রের নেই। ছাত্র বড় হয়। চাকরিতে ঢোকে। সোনার ছাতার মতো তাকে আগলে থাকে ছ অঙ্কের পে-স্লিপ। আরও ব্যস্ত জীবনে লাইব্রেরি ঘাঁটার সময়ের যে বড় অভাব।
গ্রন্থাগারের দুর্দশা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, আন্তর্জালে নানা নিবন্ধ পড়ার পরে মনে হয়, এই অধঃপতন নিয়ে তাঁদের মধ্য মতভেদ স্পষ্ট। কথার জালে তাঁদের এক পক্ষ, অন্য পক্ষকে দশ গোল দেন। এক দল বলেন, “পড়ার অভ্যেস কমেনি মোটেই। বইপ্রেমীরা ভিড় জমাচ্ছেন বাইনারি গ্রন্থাগারে।” অন্য দল ফুৎকারে এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে জানান, বইপড়ার অভ্যেস যে যুগে কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে, সেখানে ডিজিটাল গ্রন্থাগার নিয়ে যাবতীয় প্রচেষ্টা কার্যত বৃথা। সন্তানহারা কোনও পিতা যেমন তাঁর যাবতীয় সম্পদ নিয়েও শূন্যচোখে তাকিয়ে থাকেন আগামী দিনের দিকে, ডিজিটাল লাইব্রেরির শ্রমিকদের ভাবনাও দিনের শেষে আসলে সেই একই সুরে বাঁধা। এই মন খারাপ থেকে আশু মুক্তি নেই কোনও।
চিরাচরিত গ্রন্থাগারের প্রেমিকরা এই ডিজিটাল লাইব্রেরির জমানাকে দুয়ো দিয়ে বলেন, “এই গ্রন্থাগারের সব বই আপনার। কিন্তু আসলে একটা বইও আপনার নয়। বই হাতে না পেলে আবার বই কি!” তাঁদের স্পষ্ট দাবি, কোনও বিষয়ের উপরে বই চাইলে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক যেভাবে সাহায্য করেন, সার্চ ইঞ্জিনের হাজারখানেক রেজাল্ট কি তার সমকক্ষ হতে পারবে কোনওদিন? কোন বইটা কোনও কাজের নয় আর কোনটা পড়লেই বা কাজের কাজ হতে পারে, তা নিয়ে সার্চ ইঞ্জিনের কি কোনও মাথাব্যথা আছে? এখানেও হতে পারে পেইড লিংক আর স্পনসরশিপের রাজত্ব। বেশি কড়ি ফেললেই কোনও সংস্থার লাইব্রেরি মাথা উঁচিয়ে রইবে সার্চ করা ফলাফলে। চিরাচরিত লাইব্রেরি যেভাবে ইতিহাসের কাছে নতজানু হয়ে থাকে, ডিজিটাল লাইব্রেরির সে ক্ষমতা আছে কি? হিজিবিজবিজ প্রশ্নগুলো মাথার ভিতর চমকায়। উত্তরও অজানা।
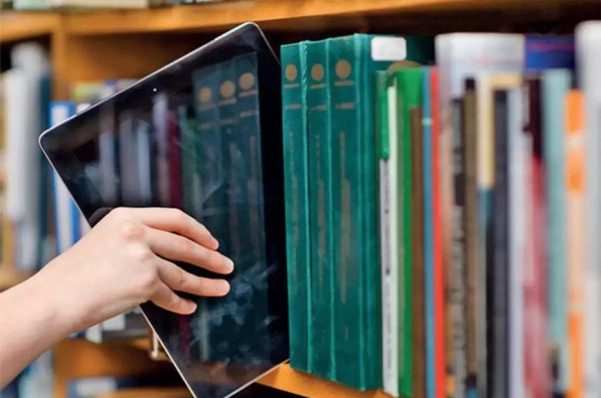
ডিজিটাল লাইব্রেরির হালহকিকত নিয়ে চর্চা করা মানুষরা এই বাইনারি গ্রন্থাগার ও তাদের ব্যবহারকারীদের ‘জয়গাথা’ নিয়ে যা বলেন, তাও ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলায় একটা ডিজিটাল লাইব্রেরির স্টলের সামনে দেখেছিলাম মেলা ভিড়। ‘এক ক্লিকে পুরো রবীন্দ্রনাথ’ নিয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন এক অষ্টাদশী। টাইট টিশার্টের উপরে বিশ্বকবির মুখের স্কেচ ঢেউ খেলছিল। এক আগ্রহীকে বলতে শুনেছিলাম, ‘রবিঠাকুরের চাঁদের পাহাড়টা আছে নাকি সংগ্রহে? পিডিএফ হবে, পিডিএফ? শুনেছি নাকি হেব্বি বই।’ অষ্টাদশী ঘাড় নাড়ালেন। আগ্রহী পড়ুয়ার সঙ্গিনী তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘পদ্মানদীর মাঝিটা একটু সার্চ মেরে দেখবেন?’ অষ্টাদশী কিন্তু সত্যি কিবোর্ডে এন্টার করছিলেন বইয়ের নাম। রবিঠাকুরের মুখ চাউমিনের রূপ নিয়েছিল আরও।
কেন্দ্রীয় ডিজিটাল লাইব্রেরির ওয়েবসাইট খুললেই যে সার্চবার আসে, তাতে লেখা আছে দেখলাম ৮ কোটি ২৫ লক্ষ ৫২ হাজার একশ পাঁচটি রিসোর্সের মধ্যে আপনার চাওয়ার সন্ধান করুন। খুঁজে নিন। শুনলাম এই ই-গ্রন্থাগারে রেজিস্ট্রি করা সদস্যের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও বেশি। তার মধ্যে কতজন প্রথমবার সাইন আপ করার পরে ফিরে এসেছেন ফের? আপাতভাবে তার কোনও উত্তর মেলে না। বড়মাপের আরও কিছু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে দেশ জুড়ে। বহু নামী স্কুল কিংবা বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই বানিয়ে ফেলেছে তাদের নিজস্ব ডিজিটাল লাইব্রেরি। এক গ্রন্থাগারের সঙ্গে অন্য গ্রন্থাগারের মধ্যে থাকছে ই-মেলবন্ধন। সোজা কথায় বলতে গেলে কনটেন্টের অভাব নেই কোনও। পর্দার ওপার থেকে শিক্ষাবিদরা বলে ওঠেন, “অভাব আসলে স্বভাবে! পড়ার অভ্যেসটা বজায় রাখাই যে ঝক্কির ব্যাপার।” তাঁদের দাবি, যে দেশে শহর ছাড়ালেই ইন্টারনেটের স্পিড খাবি খায়, যে দেশে একটা স্মার্টফোন নিয়ে কাড়াকাড়ি করে এক অভাবী পরিবারের সকলে, পড়ার সাধ থাকলেও বাস্তবিকভাবে সাধ্য থাকবে তো? প্রশ্ন তোলেন, “লকডাউনকালে অনলাইনে আক্ষরিক অর্থে ক্লাস করতে পেরেছিল কজন?”

কথার পিঠে কথা ওঠে। এমন বকবকের শেষ নেই কোনও। তবে পড়ার কথা ভাবলেই ‘দুচ্ছাই’ বলা মানুষদের কজন ই-লাইব্রেরির খোঁজে আন্তর্জালে সন্ধান চালাবেন, তাঁদের সংখ্যা আদৌ বাড়বে কি না, এক উত্তর সময়বাহাদুরের পকেটে রয়েছে। পোড়োবাড়ির মতো সাবেকি গ্রন্থাগারগুলো কি ভার্চুয়াল অট্টালিকাময় ই-লাইব্রেরিকে দেখে হিংসা করে? নাকি যা বেরিয়ে আসে তা আসলে দীর্ঘশ্বাস? উত্তর জানা নেই। আন্তর্জালে কুড়িয়ে পাওয়া একটা ঘটনার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। শেষপাতেও থাক।
– একটা ছোট গ্লাসে করে জল এনে দেবেন?
– দিচ্ছি, দিচ্ছি। এই নিন।
– বাঃ। অনেক ধন্যবাদ। আর এক গ্লাস দেবেন?
– নিশ্চয়ই। এই নিন।
– আপনাকে বাহবা দেওয়ার ভাষা নেই। আর এক গ্লাস দেবেন?
– সে না হয় দেবো। কিন্তু এত জল খাওয়া কি ভাল?
– আরে ধুর মশাই। আমার খাওয়ার জন্য জল চাইছি নাকি? ওই দেখুন। লাইব্রেরিটায় আগুন লেগেছে।
*তথ্যসূত্র: Statista, National Digital Library of India
*ছবিসূত্র: ET, Pinterest, Kivuto
অম্লানকুসুমের জন্ম‚ কর্ম‚ ধর্ম সবই এই শহরে। একেবারেই উচ্চাকাঙ্খী নয়‚ অল্প লইয়া সুখী। সাংবাদিকতা দিয়ে কেরিয়ার শুরু করলেও পরে জীবিকার খাতবদল। বর্তমানে একটি বেসরকারি সংস্থায় স্ট্র্যাটেজি অ্যানালিস্ট পদে কর্মরত। বহু পোর্টাল ও পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। প্রকাশিত হয়েছে গল্প সংকলন 'আদম ইভ আর্কিমিডিস' ও কয়েকটি অন্য রকম লেখা নিয়ে 'শব্দের সার্কাস'।