জয়া মিত্র

গত শতাব্দীর আশি নব্বই দশক আমাদের অনেকের কাছেই ছিল বেশ অদ্ভুত। টেলিভিশান ঢুকে পড়েছে ঘরে ঘরে। সন্ধ্যা আর ছুটির সকালগুলো থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যৌথ আড্ডার অভ্যাস। প্রায়ই একত্র বসেও লোকেরা মন দিয়ে রেখেছেন অন্য কোনো বাইরের বিষয়ে, যখন যেটা সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে। নিজেদের চিন্তাভাবনা নিয়ে কথা বলা, এমনকি বাইরের খুব জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা যেন অনেকেই এড়িয়ে যাচ্ছে চোখে পড়ার মতো ভাবেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে, এমনকি বন্ধু পরিচিতবৃত্তের একটা বড় অংশেও ক্রমশ ব্যক্তিগত সুখ কিংবা ব্যক্তিগত উচ্চাশা, হতাশা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।
আরও পড়ুন- ভূমধ্যসাগর: গ্রাম থেকে জাপানি ভাষায়
একই সঙ্গে এমন অনেক ঘটনা ঘটছে যা অভাবিত ছিল। যেমন ‘সবুজ বিপ্লব’, পাঞ্জাবে রাজনৈতিক বিস্ফোরণ, অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে সেনা প্রবেশের সরাসরি টিভি সম্প্রচার, শিখ নিধন, ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড গ্যাস লিকের বীভৎসতা আর তা গোপন করার সরকারী প্রচেষ্টা, ওদিকে ইরাকে নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ… অনেকখানি সময় জুড়ে এরকম অসংখ্য ঘটনা, এই অভিঘাত সঙ্কুল সময়ে যা দেশের একটা বড় অংশের মনে তীব্র সব প্রশ্ন জাগাচ্ছিল। এর সঙ্গে তফাত ছিল তার আগে পর্যন্ত নানা অর্থনৈতিক উন্নতির দাবিদাওয়া কিংবা শাসনক্ষমতা লাভের জন্য পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলির আন্দোলনের। বন্দীমুক্তি, নাগরিক অধিকার ছাড়াও প্রশ্ন উঠছিল দেশের নতুন কৃষিব্যবস্থা, বৈদেশিক ঋণ ও বিশ্বব্যাংকের ‘সহায়তা’ঘটিত প্রশ্ন, গ্যাট চুক্তি, মেধাসম্পত্তির নামে নানা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে দখলদারির এপর্যন্ত-কখনো-না-শোনা বৃত্তান্ত এরকম বহু কিছু। এসে পড়ছিল বড়বাঁধের বিরোধিতা, কৃষিতে যথেচ্ছ রাসায়নিক ব্যবহারের কুফল নিয়ে আলোচনা, পরমাণু শক্তিকেন্দ্র তৈরির বিরোধিতা— বহু বিষয়, যা এর আগে সামাজিক আলোচনার পরিসরে আসেনি। এই কথাগুলো নিয়ে সমাজের একটা অংশের অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে আলোচনা, সচেতনতা বাড়ছিল। ‘পরিবেশচর্চা’ শব্দবন্ধটি পরিচিত হয়ে উঠছিল, হয়ত তার পরিসর সম্পর্কে ধারণা সেভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। যেমন কিছুটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়েও বহু আলোচিত হচ্ছিল ‘নারীমুক্তি’, পরে যা ‘মানবীচেতনা’। ছাত্রছাত্রীদের থেকে আরেকটু বড়রাই হয়তো কিছু বেশি উদ্বেল হচ্ছিলেন এই আগে তেমন পরিচয়-না-থাকা কথাগুলো নিয়ে।
 উৎস মানুষ, ড্রাগ একশান ফোরাম, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, Safe Energy and Environment — এরকম বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনকে ঘিরে কিছু চিন্তাক্রিয় লোকজন পড়ছিলেন, ভাবছিলেন, সচেতন হয়ে উঠছিলেন। সত্তর দশকের সামাজিক ন্যায়ের ভাবনা অভ্যস্ত রাজনৈতিক প্রকরণের বাইরে অন্য পরিধির মধ্যে রূপ নিচ্ছিল। প্রাকৃতিক দিক থেকে নদীবাঁধ, খনি, পরমাণুশক্তি নিয়ে পরিকল্পনা এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাক্রিয় মানুষদের এক অংশ উদ্বেল হচ্ছিলেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বদলের জন্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সচেতন বদলের সক্রিয়তার প্রয়োজন ক্রমশ বেশি বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে কিছুটা জড়িয়ে পড়ছিলাম বাংলার বাইরের কিছু অসামান্য জন-আন্দোলনের সঙ্গে, যেমন ১৯৮৯ সালের ভাগলপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী প্রচেষ্টা (যা লাগাতার কয়েকমাস চলেছিল সাংবাদিক সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের নেতৃত্বে), বিহারের গঙ্গামুক্তি আন্দোলন, ভারতের অনেকখানি অংশে ছড়িয়ে পড়া আণবিক শক্তিবিরোধী আন্দোলন। আর, কোথাও যেন একটা গভীর অভাব অনুভব করছিলাম এইসব জীবন্ত জন-আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের মতো সাহিত্যকর্মীদের কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায়। সেটা কেবল শারীরিক উপস্থিতির প্রত্যক্ষতা নয়, বোধ হচ্ছিল সাহিত্যের নিজস্ব জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে না পারলে এই আন্দোলনগুলির জেগে ওঠা কেবল রিপোর্টিং হয়ে থাকছে, তাতে কোনও প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না।
উৎস মানুষ, ড্রাগ একশান ফোরাম, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, Safe Energy and Environment — এরকম বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনকে ঘিরে কিছু চিন্তাক্রিয় লোকজন পড়ছিলেন, ভাবছিলেন, সচেতন হয়ে উঠছিলেন। সত্তর দশকের সামাজিক ন্যায়ের ভাবনা অভ্যস্ত রাজনৈতিক প্রকরণের বাইরে অন্য পরিধির মধ্যে রূপ নিচ্ছিল। প্রাকৃতিক দিক থেকে নদীবাঁধ, খনি, পরমাণুশক্তি নিয়ে পরিকল্পনা এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাক্রিয় মানুষদের এক অংশ উদ্বেল হচ্ছিলেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বদলের জন্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সচেতন বদলের সক্রিয়তার প্রয়োজন ক্রমশ বেশি বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে কিছুটা জড়িয়ে পড়ছিলাম বাংলার বাইরের কিছু অসামান্য জন-আন্দোলনের সঙ্গে, যেমন ১৯৮৯ সালের ভাগলপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী প্রচেষ্টা (যা লাগাতার কয়েকমাস চলেছিল সাংবাদিক সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের নেতৃত্বে), বিহারের গঙ্গামুক্তি আন্দোলন, ভারতের অনেকখানি অংশে ছড়িয়ে পড়া আণবিক শক্তিবিরোধী আন্দোলন। আর, কোথাও যেন একটা গভীর অভাব অনুভব করছিলাম এইসব জীবন্ত জন-আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের মতো সাহিত্যকর্মীদের কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায়। সেটা কেবল শারীরিক উপস্থিতির প্রত্যক্ষতা নয়, বোধ হচ্ছিল সাহিত্যের নিজস্ব জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে না পারলে এই আন্দোলনগুলির জেগে ওঠা কেবল রিপোর্টিং হয়ে থাকছে, তাতে কোনও প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না।

যারা এই নতুন ধরণের ভাবনা ভাবছেন— প্রতিরোধ ও লালনের, সেই মানুষদের মুখ, তাদের ঘরসংসার, তাদের ভয় আর অভী— কোথাও ফুটে উঠছে না। অনেকের মতো আমি নিজেও কোনও পথ খুঁজছিলাম যেখানে নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে পারি আর অন্যদের ভাবনা শুনতেও পারি। এই সময় বাংলায় লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের একটা উত্তাল অবস্থা। কলকাতা শহরের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন জেলা-শহর থেকে উজ্জ্বল সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল তার কিছুদিন আগে থেকেই। কিন্তু তাতেও মন ভরছিল না। প্রত্যেকটি লিটল ম্যাগাজিনেরই কিছু নিজস্ব চরিত্র থাকে, থাকে নিজস্ব ভাবনা। ১৯৯৩-৯৪ সালের যখন থেকে একটি নতুন কাগজ করার কথা ভাবি, তখন এই ভাবনাই প্রধান ছিল আমি যে কথা বলতে চাই, আর অন্যদের কাছ থেকে যেসব কথা শুনতে চাই সেগুলো উপস্থাপনের জন্য একটি নিজস্ব জায়গা দরকার।
অনেকের মতো আমি নিজেও কোনও পথ খুঁজছিলাম যেখানে নিজের ভাবনা প্রকাশ করতে পারি আর অন্যদের ভাবনা শুনতেও পারি। এই সময় বাংলায় লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের একটা উত্তাল অবস্থা। কলকাতা শহরের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন জেলা-শহর থেকে উজ্জ্বল সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল তার কিছুদিন আগে থেকেই। কিন্তু তাতেও মন ভরছিল না।
১৯৯৫ সালের শুরুতে প্রকাশিত হল ‘ভূমধ্যসাগর’ (Vumadhyasagor)। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হল ‘বাংলায় এতগুলো এত ভালো পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও কেন আবার একটি নতুন পত্রিকা করতে যাচ্ছি আমরা। তার কারণ আমরা যেসব কথা অন্যদের শোনাতে চাই সেরকম লেখাই আমরা ছাপব।’ ‘ভূমধ্যসাগর’ আজও কম-বেশি সেটাই করে চলেছে। কোনও জনগোষ্ঠির বেঁচে থাকা ও গতিশীল থাকার মূল স্রোতকেই যে বলে তার সংস্কৃতি, আর সেই গতিশীলতার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকে মানুষের চারিপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের— এই কথা বোঝবার পর থেকে নতুন নতুন বহু ক্ষেত্রে পৌঁছতে পেরেছি আমরা, যেখানে পাঠকেরা পত্রিকাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছেন নিজেদের কথার মধ্যে। এইভাবে প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় নতুন লেখকদের লেখা পায় ‘ভূমধ্যসাগর’। ছড়িয়ে পড়ে সম্পাদকের ভাবনারও বাইরেকার বহু অজানিত প্রাঙ্গণে।

প্রশ্ন এখনো শুনি এই পত্রিকার নাম নিয়ে। অনেক ভেবেছিলাম নানা রকম অর্থপূর্ণ নাম, নতুন নাম, অপেক্ষাকৃত কম বয়সের স্পর্ধায় অসাধারণ কোনও নাম। তারপর একে একে কখনও নিজে, কখনও বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ সেসব নাম বাতিল করলেন। প্রচুর কবিতা পড়তাম তখন অন্য সকলের মতোই। গদ্য লিখি অনেক কম। শব্দের শক্তি নিয়ে ভাবি। সেই অবস্থাতেই একদিন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে গেল এই নামটি। ‘ভূমধ্যসাগর’ (Vumadhyasagor)। মনে হল ভাবনাপ্রকাশের যে মাধ্যম আমার হাতে আছে সেই শব্দই কেবল এই শক্তি ধরে, যা ভূমির মধ্যে সাগর তৈরি করতে পারে। তাছাড়া এই শব্দের মধ্যে জল আছে আর সেই জলকে ছুঁয়ে চারিদিকে আছে মাটিও। অপ্রত্যক্ষে হয়তো রয়ে গিয়েছিল কোথাও শঙ্খ ঘোষের সেই বিখ্যাত কবিতাটিও। সেই নাম আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, প্রায় খালি হাতে, প্রায় বিনা অভিজ্ঞতায় একটি যাত্রা শুরু হল। ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে।
প্রচুর কবিতা পড়তাম তখন অন্য সকলের মতোই। গদ্য লিখি অনেক কম। শব্দের শক্তি নিয়ে ভাবি। সেই অবস্থাতেই একদিন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে গেল এই নামটি। ‘ভূমধ্যসাগর’।
থাকি কলকাতা থেকে অনেকখানি দূরে, অথচ সাহিত্যসেবী বন্ধুবান্ধব বলতে বেশিরভাগই কলকাতায়। সকলেই উৎসাহ দিলেন। নিজেরও উৎসাহ কম ছিল না। প্রথম প্রথম তিন চারটির বেশি লেখা জোগাড় করতে সমস্যা হত। অনুবাদ করতাম। সেই সময়কার সব নতুন সম্পাদকের মতন বেনামে, ছদ্মনামে লিখতাম। আবার অমিতাভ দাশগুপ্ত, অঞ্জন সেন, হিরণ মিত্র, নমিতা চৌধুরী, মিহির চক্রবর্তী, কিন্নর রায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো বন্ধুস্থানীয়রা বা কার্তিক লাহিড়ী, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, দেবেশ রায়ের মতো লেখকরাও লেখা দিয়েছেন ক্রমশ। কবিতা প্রকাশিত হত অনেক বেশি। নদী, খনি, জঙ্গলের অধিকার নিয়ে গদ্য লিখেছেন, তখনও যারা লেখক হিসেবে পরিচিত নন।

প্রকাশও ছিল খুবই অনিয়মিত। ১৯৯৫-৯৬ এ প্রকাশ করা গিয়েছিল মাত্র দুটি করে সংখ্যা। টেকনিকাল বিষয়গুলো, মানে প্রেস, লে আউট ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও ধারণা অর্জন করতে পারিনি। কলকাতার প্রায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অপরিচিত প্রেস থেকেও ছাপিয়েছি দু একবার। আবার, কলেজস্ট্রিটের কিছু বন্ধুর সহায়তাও পেয়েছি। নাহলে পত্রিকা চালাতে পারতাম না। অঞ্জন সেন, কবি অমিতাভ গুপ্ত, রক্তকরবী প্রকাশনার প্রদীপ ভট্টাচার্য, ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকার বন্ধুরা দু’একজন— নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন।
কলকাতার প্রায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অপরিচিত প্রেস থেকেও ছাপিয়েছি দু একবার। আবার, কলেজস্ট্রিটের কিছু বন্ধুর সহায়তাও পেয়েছি। নাহলে পত্রিকা চালাতে পারতাম না।
কখনও কি হতাশা আসেনি? অবশ্যই এসেছে। ২০০০ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বন্ধ ছিল কাগজ। মনে হয়েছিল একা টেনে নেবার পক্ষে খুব বেশি ভারী এই বোঝা। চারিদিকের পরিস্থিতির তীব্র চাপের মুখে মনে হয়েছিল, কী হবে এই কাগজ করে? কোনও অন্যায়কেই কি আটকাবার সাধ্য আছে শিল্প সাহিত্যের? কিন্তু সে নীরবতার চাপও কম হল না। আর, ছাড়তে দিলেন না পরিচিত-অপরিচিত সেই আগ্রহীরা, কোথাও দেখা হলেই যাঁরা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করতেন, ‘কী খবর কাগজের? সে কী, বেরোচ্ছে না? কেন?’ যে একা লাগার কাছে হার মেনেছিলাম, একটি সামান্য প্রচেষ্টার প্রতি যত্নশীল কিছু মানুষের আগ্রহ একটু একটু করে সারিয়ে দিল তাকে। ২০০৫ থেকে আবার প্রকাশিত হতে লাগল কাগজ।
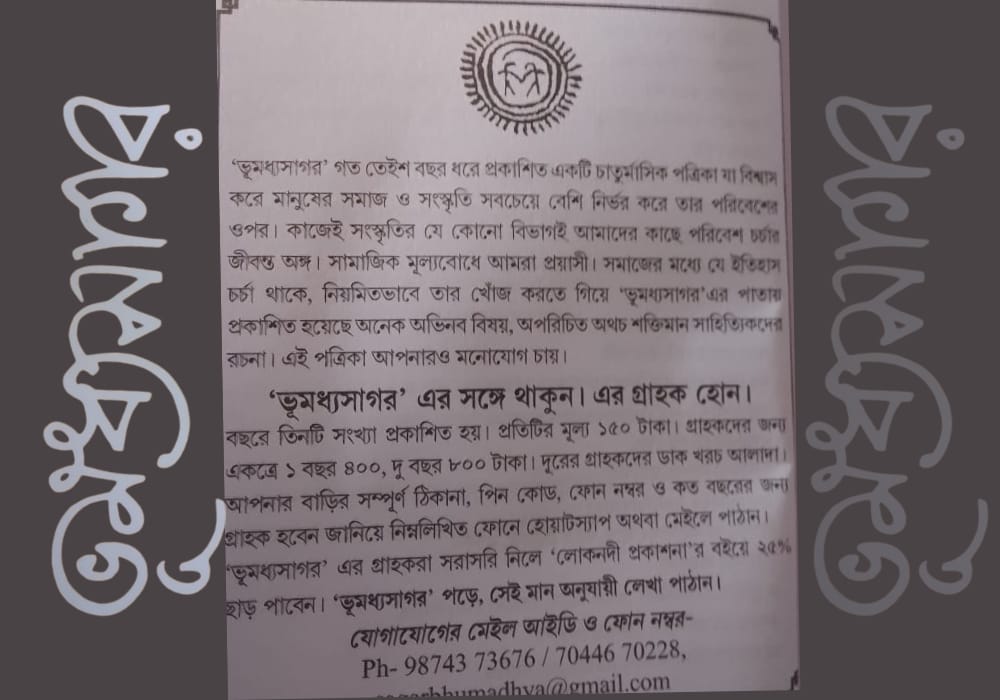
তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এরকমই… সম্পাদকের সকল দুর্বলতা, অক্ষমতার দায় ভাগ করে তুলে নিয়েছেন ধীরে ধীরে কাছে এসে পড়া বন্ধুদল। আজকে সম্পাদক, সংগঠক, লেখক, পাঠক মিলে ‘ভূমধ্যসাগর’ সত্যিই এক ভিন্নস্বভাব সংসারের মতো। সামান্য যে পাঠকসংখ্যা, তাঁদের প্রায় সকলেই পরিবারের অংশভাক। আত্মকেন্দ্রিকতার দিনকালে এই গভীর সংলগ্নতাই আমাদের পছন্দের। কতখানি সংলগ্নতা তার দুটিমাত্র উদাহরণ দিই—
এক বন্ধুর পরিচিত একজন ব্যাংককর্মীর সাহায্যে ১৯৯৬ সালে পত্রিকার ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছিল। কোনোমতে ধুঁকে ধুঁকে চলা এক রুগ্ন হিসেবখাতা। সম্পাদক সেখানে যান সারাবছরে হয়ত তিনবার। তারপর চার বছরের হাঁটুভাঙা নৈঃশব্দ। ২০০৫-এ আবার কাগজ নিয়ে ভাবনার শুরুতে ভয়ে ভয়ে সেই ব্যাংকে যাওয়া…’একাউন্টটা তো মরে গেছে নিশ্চয়ই, কী করতে হবে তাহলে?’ টেলিফোনের অপর প্রান্ত বলে ‘একবার আসতে তো হবে।’ সে তো নিশ্চয়ই। যাওয়া হল। সঙ্গে করে নিয়ে গেল দৃষ্টিহীন তরুণবন্ধু সৌরভ।
— ‘কী করতে হবে রিভাইভ করার জন্য? করা কী যাবে এতদিন পরে?’
স্মিত হেসে মফস্বল শহরের সেই অতি সাদামাটা চেহারার নাট্যকর্মী বলেন, ‘রিভাইভ করতে হবে কেন? ভূমধ্যসাগর কি অত সহজে মরে?’
জানা গেল বছরের পর বছর নিজের পকেট থেকে সামান্য করে টাকা জমা দিয়ে তিনি ওই একাউন্টকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। বললেন, ‘আমি জানতাম আপনারা ফিরে আসবেনই’।
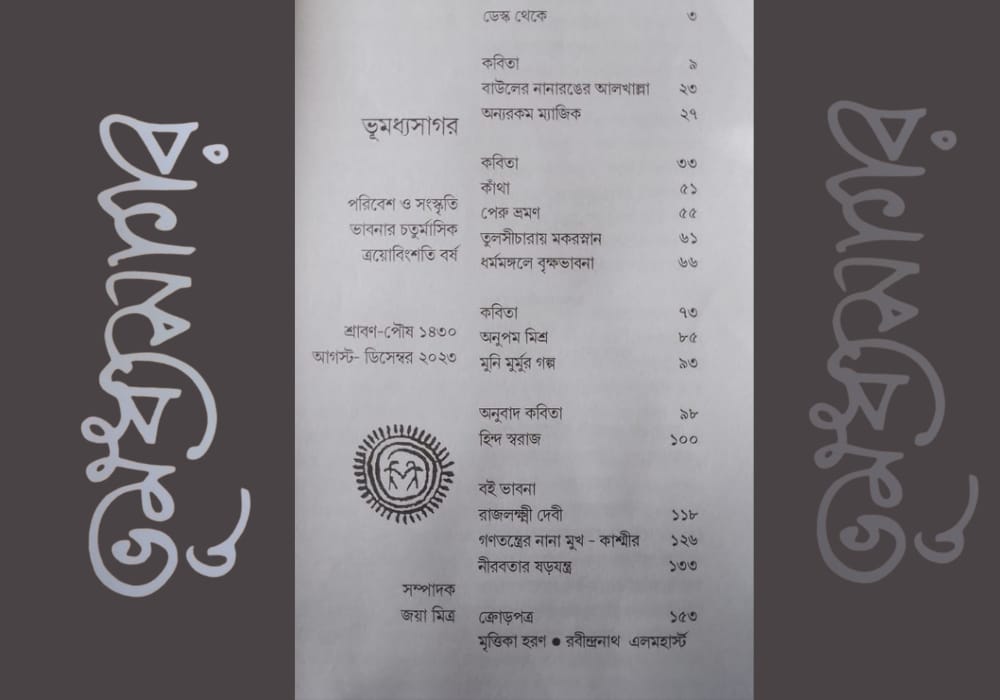
অন্যজন বৌবাজারের এক ছোট্ট প্রেসের মালিক, যিনি সম্পাদকের সমস্ত প্রযুক্তিগত অপটুতার দায় নিজে সামলে নিতেন। সামান্য কিছু সংখ্যা ছাপার টাকাও একবারে দিতে না পারা একাধিক লিটল ম্যাগাজিনের শিরায় স্যালাইন দিতে গিয়ে নিজে রক্তাল্পতায় ভুগতেন। সে সময়ে ‘ভূমধ্যসাগর’-এর এক শুভানুধ্যায়ী যোগাড় করে আনলেন একটি বিজ্ঞাপন। ক্যাশ পেমেন্টে যে টাকা দিতে রাজি বিজ্ঞাপনদাতা, তাতে প্রেসের দক্ষিণা তখুনি মিটে যাবে— এই হিসাব শুনে আসানসোলস্থ সম্পাদক রাজি হয়ে গেলেন, বিজ্ঞাপনের ম্যাটার সরাসরি প্রেসে দিয়ে দিন, ছাপার কাজ চলছে।
আধঘণ্টা পর প্রেসের ফোন, ‘দিদি, এই বিজ্ঞাপনটা কী আমরা ছাপব?’
‘কেন? কী আছে ওতে? কিসের বিজ্ঞাপন?’
— ‘এটা তো পাথর খাদান কোম্পানির বিজ্ঞাপন!’
যিনি যোগাড় করে দিয়েছিলেন, তাঁকে ফেরত দেবার কারণটা বুঝিয়ে বলতে হল। যে খনি-উদ্যোগের আমরা বিরোধিতা করি, নিজেদের কাগজে তার বিজ্ঞাপন ছাপতে পারি না। এটা তঞ্চকতা, লোভ করা। অথচ পত্রিকার সেই আদর্শকে নিজের নিশ্চিত আর্থিক প্রাপ্তির চেয়ে বড় বলে ভাবতে এক মুহূর্তেরও দ্বিধা করেননি বাদল দা। শিখিয়েছিলেন। পত্রিকার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু থেকে এই সাথীরা ঘিরে রেখেছিলেন।
আরও পড়ুন- ভূমধ্যসাগর: সিমসাং বনাম সোমেশ্বরী
আজও পায়ে পায়েই এগোচ্ছে ‘ভূমধ্যসাগর’। পত্রিকা রাখার জায়গা আর বিক্রি হওয়া কপির দাম ফেরত নেবার বাস্তব অসুবিধার জন্য মাত্র কয়েক বছর আগে সাহস করেছে গ্রাহক করার যাতে সরাসরি কাগজ পৌঁছে দেওয়া যায়। আজও পত্রিকা ছাপার সংখ্যা বেশি নয়। ভৌগোলিক দূরত্ব এখনও মেলায় বা নিয়মিত বিক্রয়কেন্দ্রে পৌঁছবার বাধা। তবু আমরা আনন্দিত পাঠকদের এবং লেখকদের নিয়েও, যেই পাঠকেরা প্রতিটি সংখ্যার পরে এনে দেন কিছু না কিছু ভাবনা, বার্তা, ভরসা। খুঁজে বার করেন কিছু না কিছু শিকড়ের সন্ধান। প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে মেলানো জীবনযাপনের প্রাচীন সংস্কৃতি আমাদের এই দেশের দীর্ঘ উত্তরাধিকার। সেই হারাতে বসা উত্তরাধিকারের শিকড়ই আমাদের সন্ধান। সেই ইতিহাস এইপত্রিকার একান্ত সন্ধান। সহজীবনে বিশ্বাসই আমাদের স্বাতন্ত্র্যের স্বভাব।
এইটুকু সম্বল নিয়ে ‘ভূমধ্যসাগর’ এখনও স্বপ্ন দেখে। পারস্পরিক নির্ভরতায় পা ফেলে। বন্ধু স্বজনদের বাড়িয়ে দেওয়া হাত দুহাতে ধরাতেই এই পত্রিকার বিশ্বাস।
যাঁরা আজ এখানে ডেকে আনলেন, তাঁরাও তো সেই বাড়ানো হাতেরই প্রতীক।
*বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভূমধ্যসাগর পত্রিকা
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।


























One Response
Really loved the article on Bhumodhyasagar by Jaya Mitra. We expect more from her on this platform.