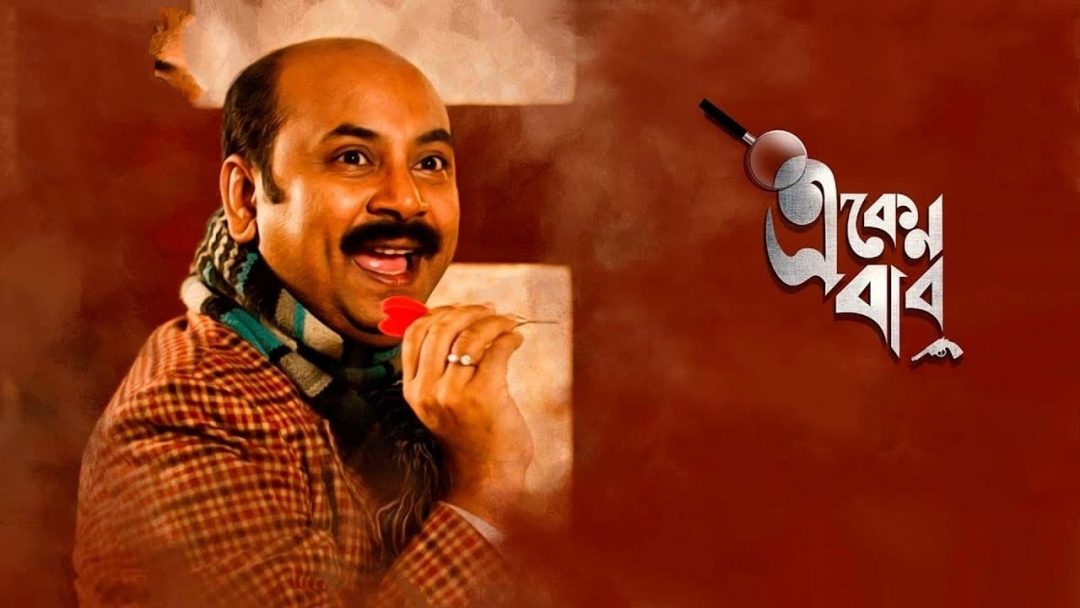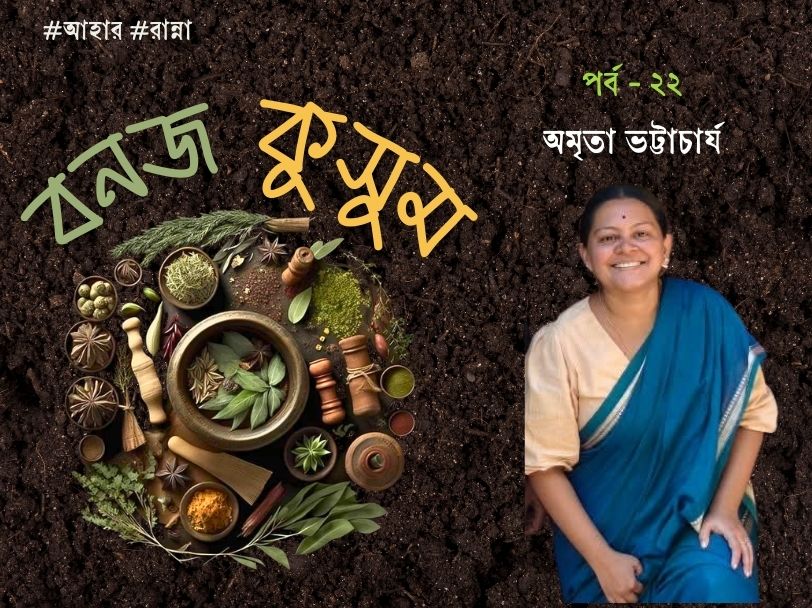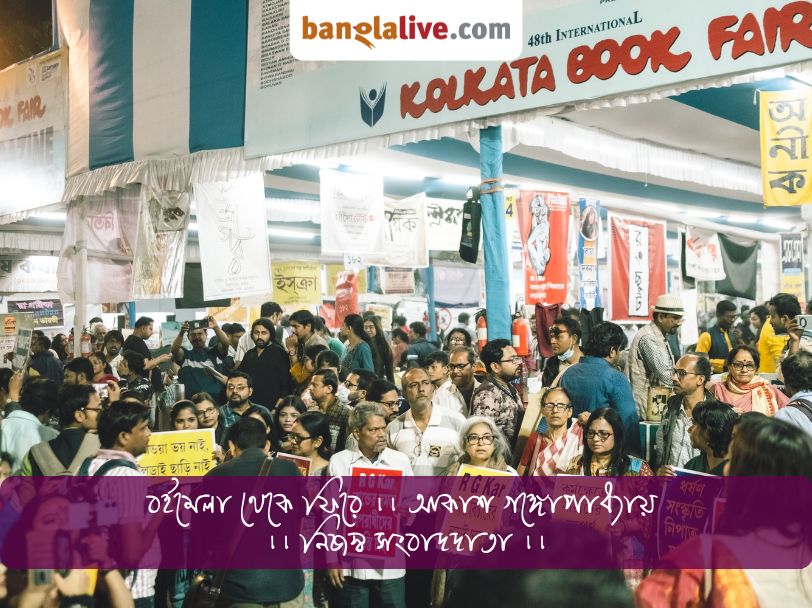বাংলালাইভের তরফ থেকে মাসদুয়েক আগে প্রথম যখন একেনবাবু সিরিজের রিভিউ লেখার অনুরোধ পাই, তখন সত্যি বলতে কি, উদ্যোগটাই অর্থহীন মনে হয়েছিল। একে তো বাংলা ওয়েব সিরিজের রিভিউ কখনও করিনি। তাছাড়া, যার চারটি সিজন সম্পূর্ণ, প্রথমদিন থেকেই অভাবিত সাফল্য, এমনকি যার দৌলতে বাংলা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের নবতম গুঞ্জন হিসাবে অনির্বাণ চক্রবর্তীর নক্ষত্রবেগে উত্থান- এতদিন পরে তার সম্বন্ধে দু’চাট্টি টেকনিক্যাল কচকচি নিতান্তই অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয়। সেই ধারণা কিছুটা পালটায় প্রধানত দু’টি ঘটনার ফলে।
প্রথমত, একেনবাবুর পঞ্চম সিজন রিলিজের খবরটা শুনি। আর দ্বিতীয়ত, যেটা প্রধান কারণ, একেনবাবুর স্রষ্টা সুজন দাশগুপ্তের একটি সাক্ষাৎকার দেখি বাংলালাইভে। সামাজিক মাধ্যম যদি মাপকাঠি হয়, তবে বাঙালির মধ্যে প্রকৃত ধী, মেধা জিনিসটা দিনে দিনে দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আর মৌলবাদের বাড়াবাড়ি দেখলে রসবোধ ব্যাপারটা তো প্রায় বিলুপ্তপ্রায় বলেই মনে হয়। অথচ এই তিনটিরই আশ্চর্য সমন্বয় পেলাম সুজনবাবুর কথায়। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে মন্তব্য করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই, এক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিকও নয়। তবে আমায় সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ। আর সেই কারণেই নতুন করে একেনবাবু দেখার একটা আগ্রহ অনুভব করি।
রিভিউয়ের আগে সিরিজে নির্মিত একেন্দ্র সেন চরিত্রটি সম্বন্ধে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, একেনবাবুর প্রথম সিজন ছাড়া বাকিগুলির মূল কাহিনি আমার এখনও পড়া হয়নি। তবে একটা জিনিস সহজেই লক্ষণীয়, গল্পে তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে অনির্বাণ চক্রবর্তীর মিল সামান্যই। সেটার প্রধান কারণ হয়তো বাণিজ্যিক। কারণ একেনবাবু সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের প্রথম ফোকাসটাই ছিল একজন গোয়েন্দা, যাঁর বুদ্ধি ফেলুদার মতো ক্ষুরধার, অথচ চেহারা সন্তোষ দত্তের জটায়ুর প্রায় অবিকল প্রতিচ্ছবি। সেটা আমার নিজেরও একেনবাবু দেখতে শুরু করার একটা প্রধান কারণ, কেননা ফেলুদার গল্প বা চলচ্চিত্রে জটায়ুই আমার প্রিয়তম চরিত্র।

কিন্তু একেনবাবু দেখতে শুরু করার পর আরও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার চোখে পড়ে। এর মধ্যে একটা যেমন আমার নিজেরও বাংলার গোয়েন্দা সম্বন্ধে বরাবর একটা খটকার কারণ। বাংলার বিখ্যাত গোয়েন্দা বলতে আমরা যাঁদের চিনি, রবার্ট ব্লেক, পাঁচকড়ি দে, ব্যোমকেশ বকসি, কিরীটি রায়, প্রদোষ মিত্র (ফেলুদা), রাজা রায়চৌধুরী (কাকাবাবু), অর্জুন, কর্নেল, এমনকী হালের মিতিনমাসি– এঁদের হয় চেহারা, নয় ব্যক্তিত্ব, নয় কথাবার্তা দেখে খুব চট করেই যে কেউ বুঝতে পারে, যে এঁরা খুব সাধারণ মানুষ নন। এইবার, এটা আমার যে কোনও গোয়েন্দার ক্ষেত্রেই একটা চূড়ান্ত ডিস-অ্যাডভান্টেজ বলে মনে হয়। মানে গোয়েন্দাকে দেখেই যদি গোয়েন্দা বা অন্তত ব্যতিক্রমী বলে চেনা যায়, তাহলে তার পরিচয় না জানলেও অপরাধী কি বেশি সাবধান হয়ে যাবে না? সেটা কি রহস্য সমাধানের পক্ষে অসুবিধাজনক নয়?
যে কজন হাতে গোনা বিখ্যাত বাঙালি গোয়েন্দা এর ব্যতিক্রম, যেমন গোগোল, মিশির আলি বা কিছুটা হালের দীপকাকু- তাঁদের ক্ষেত্রেও কিন্তু স্রষ্টা স্বয়ং গোয়েন্দাকেই গল্পের কমিক রিলিফ হিসেবে ব্যবহার করার স্পর্ধা দেখাতে পারেননি। এই জায়গায় আমি বলব, লেখক, চিত্রনাট্যকার ও প্রথম সিজনের পরিচালক অনির্বাণ মল্লিক অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছেন একেনবাবুর ক্ষেত্রে। চরিত্রনির্মাণের সময়ে তো বটেই, এমনকী, গভীর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মূল রহস্য সমাধানের সময়েও একেনবাবু ভুল হিন্দি বলেন, বা তাঁর সকসকে নোলা প্রকাশ পায়। সাফল্যের পরে তো সবই সহজ মনে হয়, কিন্তু যে জাতির কাছে তার গোয়েন্দারা গ্র্যাভিটির প্রতিমূর্তি- সেখানে প্রথমদিকে এটা যে কতখানি ঝুঁকির কাজ ছিল, তা বলার অবকাশ রাখে না। এই ত্রয়ীকে কুর্ণিশ, যে তাঁরা এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একেনবাবুর ব্যাপারে আরও একটি ব্যাপার অত্যন্ত স্বতন্ত্র বলে আমার মনে হয়েছে, কিন্তু সেটার কথায় পরে আসব।

আপাতত সিরিজটির চলচ্চিত্রায়ণের প্রসঙ্গে কথা বলা যাক। একেনবাবুর মূল কাহিনিগুলির অধিকাংশই সম্ভবত মার্কিন মুলুকে উপস্থাপিত, অর্থাৎ সুজন দাশগুপ্তের খাসতালুকে। সিরিজে হয়তো অর্থনৈতিক কারণেই সেই গল্পগুলোকে ফেলতে হয়েছে ভারতে বা বাংলাদেশে। সেই অনুযায়ী প্লটও স্বাভাবিকভাবেই পালটেছে কিছুটা। যা বললাম, আমি শুধু প্রথম গল্পটিই পড়েছি। সেই প্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রায়ণের প্রয়োজনে গল্পের ২৫-৩০% পরিবর্তিত হয়েছে। তবে তাতে গল্পের স্বাদ বা গতি, মোটের উপর অক্ষুণ্ণই আছে। সিরিজের পাঁচটি সিজনের পাঁচজন আলাদা আলাদা পরিচালক। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের মতো করে কিছু চিহ্ন রেখেছেন। এই মুহূর্তে পঞ্চম সিজনের স্মৃতিটাই সবচেয়ে টাটকা, তবে প্রতিটি সিজনেরই নিজস্ব কিছু স্বাদ আছে। প্রথম দুটি সিজন বেশ উজ্জ্বল।
প্রথম সিজনের পরিচালক অনির্বাণ মল্লিকের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে এই পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। একেনবাবু সিরিজের যে মূল সুর বা মেজাজ, যেটা একেনবাবুর সাফল্যের একটা বড় কারণ, সেটা অনির্বাণ মল্লিকের হাতেই তৈরি। এই নির্মাণশৈলীর বৈশিষ্ট্যটা আরও বেশি করে ধরা পড়ে পঞ্চম সিজনে, যখন সমস্ত পরিচালকের হাত ঘুরে আবার অনির্বাণ মল্লিকই পরিচালনার ভার নিয়েছেন। আশা করব, পরবর্তী সিজনেও তাঁকে পাওয়া যাবে।

অনির্বাণের স্টাইল দ্বিতীয় সিজনে অনুপম হরি অনেকটাই অপরিবর্তিত রেখেছেন। নির্মাণ একইরকম ঝকঝকে এবং চরিত্রগুলোও সহজ আর স্পষ্ট। অবশ্য দ্বিতীয় সিজনে কমেডির ভাগ অনেকটা বেশি। তা ছাড়াও পুজো আর ফেলুদার অনুষঙ্গ খুবই উপভোগ্য দ্বিতীয় সিজনে। তৃতীয় সিজনটা তুলনায় বেশ ডার্ক। এই সিজনে বাংলাদেশের পেশাদার অভিনেতাদের অভিনয়শৈলীর সঙ্গে ভারতীয় অভিনেতাদের বৈপরীত্য খুবই ভাল ব্যবহার করেছেন পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী। হয়তো আন্তর্জাতিক কোলাবরেশনের ফলে এই সিজনে বাজেটও কিছুটা বেশি। সম্পাদনা, ক্যামেরার কাজ, প্রযোজনা, সবেতেই সেটা চোখে পড়ে। তবে একটা সমস্যা হল, তৃতীয় সিজনে চরিত্র আর ঘটনা একটু বেশি। ফলে প্লটটা একটু গুলিয়ে যায় সময়ে সময়ে। এপিসোড আরও দু’ একটা বেশি থাকলে বোধহয় ভাল হত।
চতুর্থ সিজনটা আমার তুলনায় সবচেয়ে দুর্বল লেগেছে। সেটা খানিকটা প্লটের দুর্বলতা, আর খানিকটা চরিত্রগুলির ভূমিকা স্পষ্ট না হওয়া। সম্পাদনা বেশ ভাল সব সিজনেই। তবে পর্দায় মেদহীনতার ব্যাপারে দ্বিতীয় আর তৃতীয় সিজনের সংলাপ ভৌমিককে আমি সামান্য এগিয়ে রাখব মহঃ পিয়াসুদ্দিন বা সুজয় দত্তরায়ের থেকে। ক্যামেরার কাজে বিশাল কিছু অবদান রাখার সুযোগ কোনও সিজনেই ততটা নেই। তাও সব সিজনেই সিনেম্যাটোগ্রাফাররা তাঁদের দায়িত্বের যথেষ্ট মর্যাদারক্ষা করেছেন। বিশেষত তৃতীয় সিজনের কিছু কিছু দৃশ্যে শুভদীপ নস্করের ক্যামেরার কাজ বেশ চোখে পড়ার মতো। ময়ূখ-মৈনাকের সঙ্গীত নিঃসন্দেহে এই সিরিজের একটা বড় সম্পদ। একেনবাবুর থিম মিউজিকই হোক, বা বিভিন্ন দৃশ্যের অনুষঙ্গ, এই জুটি রহস্য আর রসিকতার মধ্যে চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

এবার আসি অভিনয়ের কথায়। অনির্বাণ চক্রবর্তী এই মুহূর্তে বাংলা ওটিটিতে সবচেয়ে বহুলব্যবহৃত অভিনেতাদের একজন। তাঁর সমস্ত কাজ আমার সমান ভাল লাগেনি অবশ্য, এবং কিছু ক্ষেত্রে একটু একমাত্রিক মনে হয়েছে। তবে বলতেই হবে, একেনবাবুর প্রত্যেক সিজনেই তিনি অত্যন্ত ভাল অভিনয় করেছেন। চরিত্রটা ওয়েবে এমনভাবেই তৈরি হয়েছে, যেখানে হাস্যরস সৃষ্টির সিংহভাগ দায়িত্ব ওঁর, আবার রহস্য সমাধানের সময়ে ওঁকেই হতে হবে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন গোয়েন্দা। কাজটা খুবই কঠিন, এবং অতি অভিনয় করে ফেলার প্রবণতা খুব বেশি। কিন্তু এই ভারসাম্যরক্ষার কাজটা অনির্বাণ করেছেন চমৎকার ভাবে। বাপির ভূমিকায় সৌম বন্দ্যোপাধ্যায় ভালই, তবে প্রমথর ভূমিকায় দেবপ্রিয় বাগচির অভিনয় একটু কাঁচা। তাঁর গলায় বিরক্তি ছাড়া আর কোনও ভাবই বিশেষ ফোটে না। মুখের ভাব আরও সীমিত। বরং ইনস্পেক্টর রুপল মেহরার চরিত্রে শ্রেয়া সিনহা অনেক বেশি সাবলীল। পার্শ্বচরিত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় সিজনে অলকানন্দা রায়, চতুর্থ সিজনে কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চম সিজনে কৃষ্ণেন্দু দেওয়ানজি – বলার মতো ভালো অভিনয় করেছেন।
আরও পড়ুন: অংশুমান ভৌমিকের লেখা: গিরিশচন্দ্রকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে
এবার আসি একেনবাবুর যেটি একেবারে স্বতন্ত্র, বা তাঁর নিজস্বতা বলে আমার মনে হয়েছে, সেটির কথায়। এবং এর সিংহভাগ কৃতিত্বই সম্ভবত সুজনবাবুর পাওনা। সেটি হল, একেনবাবুর গল্পে রহস্য উন্মোচনের গঠন। দেশবিদেশের যেসব গোয়েন্দা গল্প আমি পড়েছি, যেমন শার্লক হোমস, এরক্যুল পোয়েরো, মিস মার্পল, ফাদার ব্রাউন, টাপেন্স বা আমাদের ব্যোমকেশ, ফেলুদা, কাকাবাবু, কর্নেল, মিসির আলি, মিতিনমাসি ইত্যাদি প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই রহস্য উন্মোচনের ব্যাপারে একটা জিনিস কমন। রহস্যের পরত গোয়েন্দা কীভাবে খুলছেন বা আস্তে আস্তে কুয়াশা কী করে পরিষ্কার হয়েছে, সেটা আমরা প্রায় পুরোটাই জানতে পারি গল্পের ক্লাইম্যাক্সে, যেখানে হয় সহকারী, বা সমস্ত সন্দেহভাজনদের একত্রিত করে গোয়েন্দা রহস্যের ব্যাখ্যা করেন। কোনও কোনও সময় মূল অপরাধী বা রহস্য এই ব্যাখ্যার আগেও চিহ্নিত হয় বটে, কিন্তু গোয়েন্দা কী করে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, সেটা কিছু আপাত অপ্রাসঙ্গিক হিন্ট ছাড়া পাঠকের প্রায় অজানাই থাকে।
এটা বলার উদ্দেশ্য হল, যতই রহস্যের মাঝে মাঝে এরক্যুল পোয়ারো নিজের কোটের লাইনিং বা খাবার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হন, ব্যোমকেশ সত্যবতীর জন্য পশমের কোট কিনে আনুন, বা মিতিনমাসি বুমবুমকে ভাত খাওয়াতে খাওয়াতে রহস্য সমাধান করুন – মূল রহস্য সমাধানের ব্যাপারে পাঠকের সঙ্গে গোয়েন্দার একটা এলিয়েনেশন থেকেই যায়। সেটা হয়তো সাসপেন্সের প্রয়োজনে স্রষ্টা সচেতনভাবেই রাখেন। কিন্তু সেই কারণে, ফেলুদার মতো গোয়েন্দা যখন পাঠকের কাছে রহস্যময় হয়ে সিলিংয়ের দিকে চারমিনারের রিং ছাড়েন আর‘ চন্দ্রবিন্দুর চ, বিড়ালের তালব্য শ‘ ভাষায় কথা বলেন, তখন পাঠকের একমাত্র উপায় তোপসে আর লালমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলা, আর সেই কারণেই ওই চরিত্রগুলি বেশি আপন হয়ে ওঠে।
একেনবাবুতে এই শেষ নাটকের ব্যাপারটা ভালই আছে, কিন্তু তার সঙ্গে মজার ব্যাপার হল, গোটা গল্প জুড়ে তিনি কীভাবে ভাবছেন, এক একটা ছোট ছোট রহস্য কীভাবে সমাধান হচ্ছে, তার বেশ কিছু সূত্রও পাই বাপি আর প্রমথর সঙ্গে তাঁর কথার মাধ্যমে। এর ফলে শেষ নাটকের ছন্দপতনও হয়নি বিশেষ। কিন্তু তার ফলে গোয়েন্দার সঙ্গে এই এলিয়েনেশনটা কিন্তু অনেক কমে এসেছে বলে আমার মনে হয়েছে। একেনবাবু কিন্তু পাঠকের সামনেই চিন্তায় হোঁচট খাচ্ছেন, ভুল করছেন, রহস্য গোলমেলে বলে বিরক্ত হচ্ছেন। এখন এ ব্যাপারটা আপনি আপনার গোয়েন্দার মধ্যে পছন্দ করবেন কিনা, সেটা একেনবাবু পড়ে বা দেখে আপনিই বিচার করবেন। কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটা আমার বেশ ইউনিক লেগেছে।
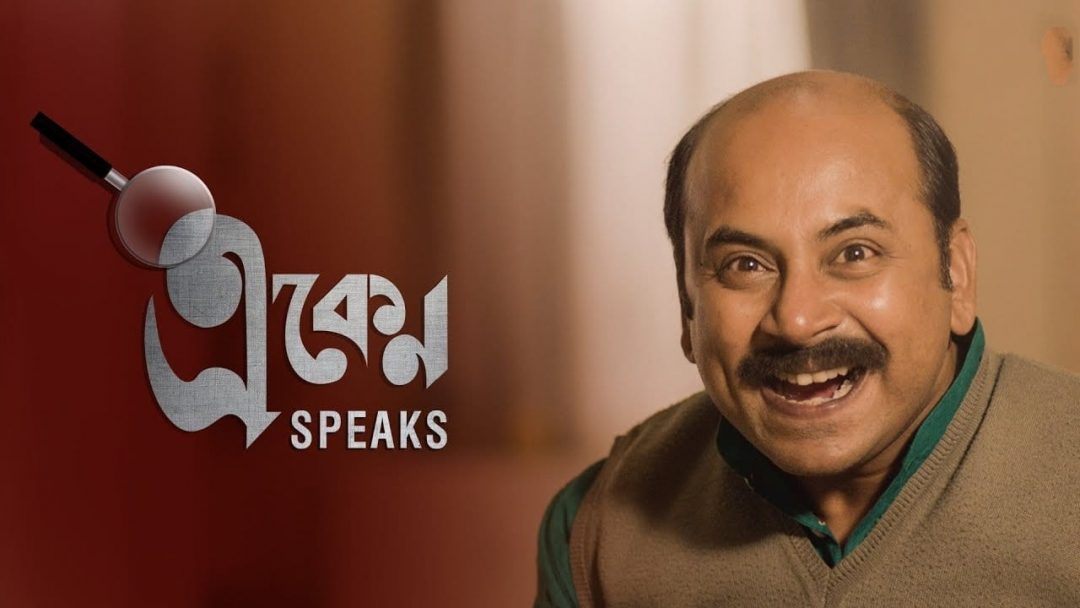
মধুরেণ সমাপয়েৎ তো সকলেই করে। আমি নাহয় শেষ পাতে তেতো আনি? এত প্রশংসনীয় ব্যাপার থাকলেও, সিরিজের কিছু কিছু দিক বেশ দুর্বল। প্রথম, কিছু কিছু জায়গায় অনর্থক হেঁয়ালির অবতারণা। যেমন, প্রথম সিজনে বস কিরীট পটেলকে হুমকি দেবার জন্য অমন দুর্বোধ্য হেঁয়ালিতে কেন চিঠি লিখলেন, বোধগম্য হয় না। হুমকি পড়ে যদি বোঝাই না যায়, সে হুমকির মানে কী? আবার ধরুন, পঞ্চম সিজনে সুরেশ মিত্র ভয়ে প্যালপিটেশনের সময়ে মারা যাওয়ার আগে এমন হেঁয়ালি লিখলেন, যে হিসাব করতে প্রায় কেশবচন্দ্র নাগের দ্বারস্থ হতে হয়। শুধু তাই না, সে হেঁয়ালির আবার ঘটনাচক্রে এমন দু’তিন রকম মানে হয়, যার প্রত্যেকটাই রহস্যে প্রাসঙ্গিক। কাহিনিকার নিঃসন্দেহে অনেক মাথা খাটিয়ে হেঁয়ালিটা বার করেছেন, কিন্তু সমাপতনটা একটু বেশিই আরোপিত লাগে। দ্বিতীয় বিষয়, একেনবাবুতে অল্প কিছু অ্যাকশন সিন। এইগুলো মূল গল্পে বোধহয় ছিল না। কিন্তু পর্দায় দৃশ্যগুলি দেখতে বেশ হাস্যকর ঠেকে। মনে হয় একেনবাবু ভয়ঙ্কর গুন্ডাদের সঙ্গে ডান্ডিয়া নাচছেন।
তবে সব মিলিয়ে বলা যায়, ডিজিটাল মাধ্যমে সেন্সরের অভাবের ফলে বাংলা ওয়েব সিরিজ যেরকম বুদ্ধিহীন, অর্থহীন, কুরুচিপূর্ণ সফট পর্নের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছিল, সেখানে এক অনির্বাণের ব্যোমকেশ ও আর এক অনির্বাণের একেন যেন কাঠফাটা গরমের পর এক পশলা ঠান্ডা তাজা হাওয়া।
*ছবি ও ভিডিও সৌজন্য: Hoichoi, Youtube, Twitter
পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তিতিবিরক্ত হতে হতেও আইটি শিল্পতালুকে মজদুরি করতে বাধ্য হন। কিন্তু সবচেয়ে পছন্দের কাজ হাতে মোবাইলটি নিয়ে আলসেমি করে শুয়ে থাকা। চেহারাছবি নিরীহ হলেও হেব্বি ভালোবাসেন অ্যাকশন ফিলিম, সুপারহিরো আর সাই ফাই। সঙ্গে চাই সুরেশের রাবড়ি, চিত্তরঞ্জনের রসগোল্লা-পান্তুয়া, কেষ্টনগরের সরভাজা ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টান্ন।