বন্দিদশার উপাখ্যান
কোনও ঘরে টাঙানো আছে বন্দিদের নামের তালিকা। মেঝেতে রাখা আছে পুষ্পস্তবক। কোথাও লেখা রয়েছে বন্দীদের জীবনযাপনের রোজনামচা। একটা ঘরে তো ছবিতে লিপিতে উপস্থাপিত হয়েছে বন্দিদের দৈনন্দিন খাদ্যের হিসেব। দু‘কাপ কফির বদলে অ্যাক্রন পানীয় দিয়ে প্রাতরাশ। ওক গাছের ফল রোস্ট করে অ্যাক্রন তৈরি হয়। যুদ্ধের সময় কফির ভাঁড়ার বাড়ন্ত। কাজেই অ্যাক্রন সেদ্ধ করা গরম জলই ভরসা। সঙ্গে সোয়াশো গ্রাম রুটি। মধ্যাহ্নভোজে পরিবেশন করা হত এক লিটার স্যুপ। কানে লাগানো যান্ত্রিক গাইড বলছে আসলে গরম জলকেই স্যুপ বলে চালানো হত। আর নৈশভোজের মেনুতে থাকত দু‘কাপ কফির বিকল্প অ্যাক্রনের সঙ্গে একশো গ্রাম রুটি। দিনে বারো ঘণ্টার কায়িক শ্রম। সময়ে অসময়ে শারীরিক অত্যাচার। তীব্র ঠান্ডা। পর্যাপ্ত পোশাক নেই। সেই পরিস্থিতিতে ডিম মাছ মাংস তো দূরের কথা শাকসবজিও বরাদ্দ নয়।
দিনের পর দিন এইভাবে জীবন কাটাতে হলে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যায়। চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। এবং ব্রিনডংকের সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি বন্দিকে এইভাবেই দিন কাটাতে হয়েছে। যাঁরা সহ্য করতে পারেননি, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তিনশোরও বেশি বন্দিকে সরাসরি হত্যা করা হয়েছে। গুলি অথবা ফাঁসি ছিল নাৎসি কর্তৃপক্ষর প্রিয় পদ্ধতি। কোনও ঘরে রয়েছে কর্মরত বন্দিদের ছবি। সাদা কালো। বেশিরভাগ ছবিতেই দেখা যাচ্ছে বন্দিরা কোদাল বেলচা দিয়ে মাটি কাটছেন। কেউ হয়তো হাতে টানা গাড়িতে মাটি বোঝাই করছেন। কানে লাগানো হেডফোন বলে চলেছে যে, বাইরে থেকে যাতে দেখা না যায়, সেইজন্য নির্মাণের সময় দুর্গের পাথরের দেওয়ালের ওপর পরতে পরতে ৫ মিটার পুরু মাটির আস্তরণ বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরিখা খননের সময় যে মাটি তোলা হয় সেই মাটি দিয়েই এই আবরণ তৈরি হয়েছিল।

বন্দিদের দিয়ে দেওয়াল থেকে মাটির আস্তরণ কাটানোর কাজ করানো হত। দুর্গ চত্বরের নিচু জমি সমান করার জন্য এই মাটি দরকার ছিল। পরিখার পাড় শক্তপোক্ত করতেও অনেক মাটি লেগেছিল। প্রতিদিন মাটি কাটার হিসেব নাৎসি কর্মকর্তারা সযত্নে নথিভুক্ত করে রাখতেন। সেই হিসেবের খাতায় লেখা আছে আড়াই লক্ষ ঘন মিটার মাটি কাটা হয়েছিল। বেশিক্ষণ এইসব ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা রীতিমতো মানসিক পীড়াদায়ক। তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না, দিনের পর দিন অল্পাহারে থেকে অপুষ্টিতে ভুগে এবং সর্বোপরি দিনে বারো ঘণ্টা কায়িক শ্রমের পর মানুষগুলো কী করুণ পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। আলোআঁধারিতে ছাওয়া দীর্ঘ করিডরের দু’পাশের ঘরগুলোর পরিচয় পাওয়ার পর মন যখন বিষাদাচ্ছন্ন তখনও বোঝা যায়নি আরও কী কী দেখতে হবে। ঘড়ির কাঁটায় ততক্ষণে দু‘ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে।
আঁধার পেরিয়ে আরও আঁধার
অন্ধকার শেষ হলে নাকি দেখা যায় আলোর দিশা। এমনটাই বলা হয় বা শোনা যায়। সুদীর্ঘ করিডরের অন্যপ্রান্তে পৌঁছনোর পর বোঝা গেল যে অন্যান্য নাৎসি কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতো ব্রিনডংক ফোর্টেও প্রচলিত ধারণা অচল। করিডর এখানে শেষ হয়নি। সামনের দিকে আরও এগিয়ে গেছে। তালা লাগানো ভারী লোহার দরজার ওপারে কী আছে, তা দেখার সুযোগ নেই। অন্ধকার এতটাই গাঢ় যে আন্দাজও করা গেল না দরজার ওপারে কী থাকতে পারে।
তবে এখানে ডান আর বাঁ দিকে শুরু হয়েছে অন্য করিডর। বাঁ দিকের করিডরে প্রবেশ নিষেধ। না, কোনও দরজা নেই। আড়াআড়িভাবে টাঙানো রয়েছে একটা শক্তপোক্ত লোহার শিকল। তার ওপরে ঝোলানো একটা সাদা বোর্ডের উপর লাল হরফে ‘প্রবেশ নিষেধ’ লিখে দায়িত্ব শেষ। অগত্যা ডানদিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। এখানেও করিডরের দু‘পাশে সাজানো আছে একের পর এক ঘর। ডান দিকের প্রতিটি ঘরের আয়তন সমান। কানে লাগানো যান্ত্রিক গাইড বলে যাচ্ছে প্রতিটি ঘরের দৈর্ঘ্য বারো মিটার। আর সাড়ে পাঁচ মিটার প্রশস্ত।

প্রথম ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বোঝা গেল কানে শোনা আর চোখে দেখার মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। শারীরিক ও মানসিক অনুভূতি তো ততক্ষণে এক ঝটকায় অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে। প্রতিটি ঘরের দু‘পাশের দেওয়াল বরাবর সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে তিনস্তরের বিছানা। ট্রেনের থ্রি টিয়ার বাঙ্ক যেমন হয়, ঠিক সেইরকম। শুধু একটাই তফাৎ, মাঝের বাঙ্কটি ভাঁজ করা যায় না। প্রতিটি বাঙ্কে বিছানো আছে একটি গদি। যান্ত্রিক গাইড জানাল, গদির ভেতরে খড় ভর্তি রয়েছে। অর্থাৎ বন্দিদের বিছানা আসলে খড়ের বস্তা। বিছানায় কোনও চাদর নেই। নেই বালিশ। পায়ের কাছে ভাঁজ করে রাখা আছে একটা কম্বল। এবার আর শুধু চোখে দেখা নয়, হাত দিয়ে যাচাই করতে হল। কম্বল যে এত পাতলা হতে পারে তা বিশ্বাস করা বেশ কষ্টকর। ভাঁজ খোলার ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। এতদিনের পুরোনো, ভাঁজ খুললেই ফেটে যেতে পারে।
পরতে পরতে সাজিয়ে রাখা ইতিহাসের নিদর্শন নষ্ট করা সমীচীন নয়। অতবড় ঘরে একটাই জানালা। ছোট্ট জানালার কাচের রঙ কিন্তু গাঢ় নীল। দু‘সারি থ্রি টিয়ার বাঙ্কের মধ্যে যেটুকু জায়গা পড়ে আছে, সেখানে পাশাপাশি দু‘জন মানুষের পক্ষে চলাফেরা সম্ভব নয়। আলোবাতাস নেই। ভরদুপুরেও দমবন্ধ হয়ে আসা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। ঠান্ডার সময় নাকি একটা ছোট্ট স্টোভ ঘরের এক কোণে জ্বালানো হত।
ঠিক সেই মুহূর্তে কানে লাগানো হেডফোন যে ধারাবিবরণী দিতে শুরু করল, তাতে শুধু মন নয়, শরীরের ভেতরেও মোচড় দিয়ে উঠল। একেবারে ওপরের বাঙ্কে জায়গা পেলে নাকি সেই রাত্রির মতো বন্দিজীবন ধন্য হয়ে যেত। রাতবিরেতে হঠাৎ করে পেটে চাপ পড়লে নীচে নামার দরকার নেই। শয্যা ত্যাগ না করেই নির্বিকারভাবে সবকিছু সেরে ফেলা যায়। মাঝের এবং নীচের বাঙ্কের বন্দির অবস্থা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না। আর নীচে নেমেও কোনও সুরাহা নেই। ঘরের এক কোণে রাখা গামলাটা তো অনেকক্ষণ আগেই উপচে পড়ছে। আর সারাদিনে দু‘বারের বেশি শৌচাগারে যাওয়া নিষিদ্ধ। তবে চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। প্রত্যেককেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উপরের বাঙ্কে রাত কাটানোর সুযোগ দেওয়া হয়। ব্রিনডংক ফোর্টের নিরাপত্তা রক্ষীদের দায়িত্ব ছিল কবে কোন বন্দি কোনতলায় ঘুমোবেন।

বীভৎসতা না বিবমিষা
করিডরের বাঁ পাশের ঘরগুলির কোনওটা ভাঁড়ার, কোনওটা আবার রান্নাঘর। লম্বাচওড়া একটা ডাইনিং রুমও রয়েছে। তবে কোনও চেয়ার বা টেবিল নেই। যান্ত্রিক গাইড জানিয়ে দিল বন্দিদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াদাওয়া সারতে হত। সত্যিই তো! প্রচন্ড ক্ষুধার মুহূর্তে ওইটুকু খাবার খাওয়ার জন্য বসার কী দরকার! এখানেই করিডরের শেষ নয়। অথবা বলা উচিত আরও বীভৎস দৃশ্য দেখা বাকি আছে। বন্দিদের শৌচাগার। দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই যে দৃশ্য দেখতে হল, তাকে অমানবিক বললে খুব মোলায়েম শোনাবে। দুই সারিতে মুখোমুখিভাবে পড়ে আছে একের পর এক দরজাবিহীন ছোটো ছোটো খুপরি। প্রতিটি খুপরিতে একটি করে পায়খানার প্যান। দু’পাশে পাদানি আছে।
১৯৪০-এর দশকে কি ইয়োরোপীয় সভ্যতায় কমোড-এর প্রচলন শুরু হয়নি? ইতিহাস তো অন্য কথা বলে। অর্থাৎ এও আরেক রকমের নির্যাতন। খুপরির তিন ফুট উঁচু দেওয়ালের জন্য পাশের মানুষকে দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু দরজার অভাবে সামনের মানুষকে তো দেখা যায়। মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার নেই। পরিস্থিতি কত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক ছিল ভাবতে শুরু করার আগেই সারা শরীর জুড়ে তোলপাড় শুরু করল চূড়ান্ত অস্বস্তি। একেই কি বিবমিষা বলে? বলা মুশকিল। তবে এক অজানা আতঙ্কে পুরো শরীর ঘামে ভিজে গেছে। কপাল থেকেও ঘাম ঝরে পড়ছে। কানে লাগানো হেডফোনের ধারাবাহিক বকবকানি বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। এবং দু‘জনেই বাকরুদ্ধ।
কোনওরকমে শৌচাগার থেকে বেরিয়ে এসে ডানদিকে তাকাতেই মনে হল কয়েক পা দূরেই বোধ হয় আঁধারের সমাপ্তি। করিডরের শেষপ্রান্তের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সবুজ প্রান্তরের ওপর ঝকঝকে রোদ খেলা করছে। করিডরের আলোআঁধারিতে গড়ে ওঠা ভয়াবহ আতঙ্কের পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই কানে লাগানো যান্ত্রিক গাইড জানিয়ে দিল, এটা ছিল চাঁদমারি। যে সব বন্দিদের গুলি করে হত্যা করা হত, তাঁদের এখানেই পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। গুলি চালানো এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে দর্শকাসনে উপবিষ্ট নাৎসি বাহিনীর কর্মকর্তারা উত্তেজিত হয়ে উল্লাসে মেতে উঠতেন। অন্য বন্দিদের বাধ্যতামূলকভাবে এই পাশবিক দৃশ্য দেখতে হত। তাঁদের চোখে জল গড়িয়ে যেত কিনা সে বিষয়ে যান্ত্রিক গাইড একটিও শব্দ উচ্চারণ করল না।

তখন শুধু কানে বাজছে ১৯৪০-এর ২০ সেপ্টেম্বর প্রথম দফায় বন্দিদের ব্রিনডংক ফোর্টে নিয়ে আসা হয়। শুরুর দিকে শুধুমাত্র ইহুদি বন্দিদের জন্য ব্রিনডংক ফোর্টের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প নির্দিষ্ট ছিল। ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর থেকে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের এখানে কারারুদ্ধ করা হতে লাগল। স্থানাভাবের জন্য ১৯৪২ নাগাদ ইহুদি বন্দীদের আউশউইৎজ্ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় একই সময়ে কমিউনিস্ট বন্দিদের নিউয়েনগাম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হয়। সবমিলিয়ে ১৯৪৪-এর ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৫৯০ জনকে ব্রিনডংক ফোর্টে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৩০৩ জনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে অথবা গুলি করে মেরে ফেলা হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অথবা অন্য ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পথে ১৭৪১ জন মারা যান। এরপরও যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁরা বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুক্তি পেলেও সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেননি। অনেকেরই নানানরকমের শারীরিক সমস্যার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু হয়।
হেডফোনের বকবকানি আর ভালো লাগছে না। সুইচ অফ্ করার সময় কানে এল ১৯৪৭-এ ব্রিনডংক ফোর্টকে জাতীয় স্মারক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মনের অবসাদ সারা শরীরে ক্লান্তি ছড়িয়ে দিয়েছে। গুটিগুটি পায়ে রিসেপশনে পৌঁছনোর পর দেখা গেল সেই প্রবীণ মহিলা হাসিমুখে অপেক্ষা করছেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনও সাড়ে চারটে বাজেনি। হেডফোন নামের যান্ত্রিক গাইড ফিরিয়ে দেওয়ার পর তিনি ধন্যবাদ জানালেন। প্রত্যুত্তরে দুই ভারতীয় কোনও শব্দ উচ্চারণ করেছিল কি? শোনা যায়নি। তবে ব্রাসেলস থেকে সরাসরি অ্যান্টোয়ার্প যাওয়ার এ১২ মোটরওয়ে দিয়ে বিরতিহীন গাড়ি চলাচলের শব্দ কিন্তু ভেসে আসছিল।
ছবি: লেখক, Wikipedia, Flickr, Historiek.net
কৃতজ্ঞতা: বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ ও পরিচিত পরিকল্পনাবিশারদ। পড়াশোনা ও পেশাগত কারণে দেশে-বিদেশে বিস্তর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। তার ফসল বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বই। জোয়াই, আহোম রাজের খোঁজে, প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণে, কাবুলনামা, বিলিতি বৃত্তান্ত ইত্যাদি।



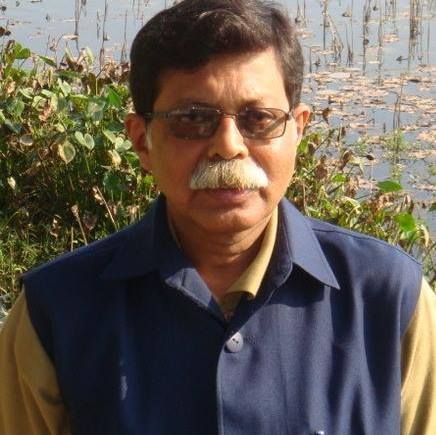






















One Response
এমন অনুপুঙ্খ বিবরণ পঢড়েই বিবমিষার অনুভূতি হয়। ফ্যাসিবাদ যে অভিশাপ বহন অরে এনেছিল তা যে বর্তমান সময়েও অনেক দেশে নৈরাজ্যের অবতারণা করে চলেছে। আমাদের দেশসহ অন্য অনেক দেশের মানুষের মধ্যে এ ধরনের লেখা বেশি প্রচারিত হলে সম্বিৎ ফিরতে পারে।