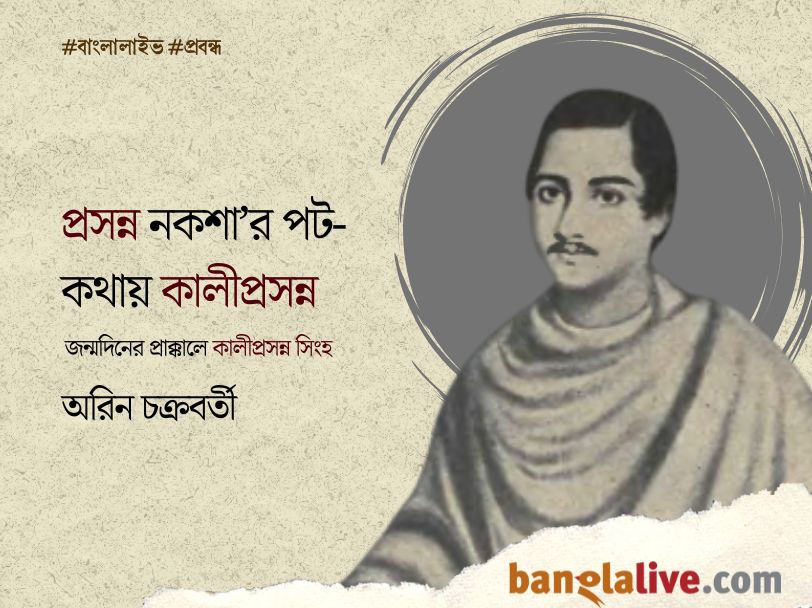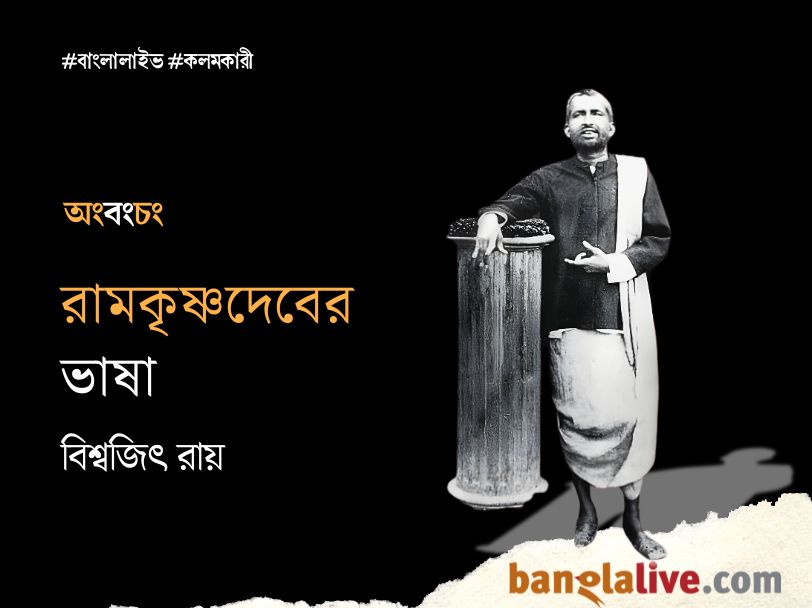গ্রাম থেকে গ্রাম চলছে শহর, শহরতলির সুর
মন ছুটছে, ছুটছি আমি, ডাকছে অচিনপুর
আমি কোনো গ্রামে থাকি না। জন্ম শহরতলিতে হলেও মামারবাড়ি গ্রামে হওয়ার সুবাদে অস্থায়ীভাবে থেকেছি বেশ কয়েকবার, ওই বেড়াতে টেড়াতে গিয়ে আর কী। তাছাড়া এক জায়গায় বেশিদিন থাকাটাও আমার পক্ষে নিতান্তই অসহনীয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনে আসছি আমার পায়ের তলায় নাকি সর্ষে। বিশেষত ঠাকুমা তাঁর বাঙাল উচ্চারণে বলতেন “হেই ছ্যামড়ার পায়ের তলায় সইর্ষা”। তা সে আর কী করা যাবে। তবে কোনওদিনই এক জায়গায় টিঁকে থাকাটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঠাকুমার ভাষায় “মাথায় ক্যারাপোকা।” এই হয়তো পাড়ার মোড়ে বা ক্লাবে আড্ডা দিচ্ছি, পরক্ষণেই আবার আমাকে খুঁজে পাওয়া গেল গঙ্গার ঘাটে তাস পেটাতে।
ঠাকুরদা নাট্য ব্যক্তিত্ব হবার সুবাদে, এবং আমি তাঁর ও তিনি আমার প্রিয় হওয়ার দরুণ দুজনের স্বভাবে প্রভূত মিল ছিল। কিছুটা হয়তো তাঁর আর আমার রক্ত এক হওয়ার কারণে। বাঙালি জীবনে “বাড়ি থেকে পালিয়ে” খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। বাবা মায়ের বকুনি খেয়ে কিংবা রেজাল্ট খারাপ করে মামারবাড়ি, পিসিরবাড়ি কেটে পড়াটা বাঙালি ছেলেদের কাছে জলভাত। আর প্রেম-ট্রেম তো রয়েইছে। আমার কেসটা সম্পুর্ণ আলাদা। পুরো মাত্রায় উড়নচণ্ডী। যদিও শুরুটা হয়েছিল ওই রেজাল্ট খারাপ দিয়েই। চুঁচুড়া শহরের কিছু মার্কামারা জায়গা ছিলো আমাদের ঠেক। তুলাপট্টি ঘাট, ষন্ডেশ্বর তলার ঘাট, ময়ুরপঙ্খী ঘাট, জোড়াঘাট, হুগলি জেলখানার মাঠ ও ঘাট তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল চুঁচুড়ার বিখ্যাত সব মাঠ। চুঁচুড়া ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড গ্রাউন্ড। কিছু মাঠের নাম তো আবার তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো – রূপনগর, প্রেমনগর ইত্যাদি।
আজ লিখতে বসে সেইসব ফেলে আসা দিনের স্মৃতি ভিড় করে আসছে মাথায়। কখনও লিখতে লিখতে সেইসব ঘটনা মনে করে হেসে ফেলছি একা একাই, আবার কখনও ভিজে যাচ্ছে চোখের কোল; সেই সঙ্গে বুকের ভিতর একটা মৃদু চিন্চিনে ব্যাথা। বুঝে উঠতে পারছি না এই লেখার শেষ কোথায়।

ঠাকুরদার মুখে শুনেছি আমরা নাকি বরিশালের তালুকদার ছিলাম। স্বাধীনতার পর যে সব বাঙালি ওপার বাংলা থেকে এপারে এসেছে তাদের সবার মুখেই শুনেছি ওপারে তারা জমিদার ছিল অথবা প্রচুর জায়গা জমি ছেড়ে এপারে এসেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে ঠাকুরদার কেসটা সেরকম নয়। শুনেছি তিনিও বাড়ি থেকে যেখানে সেখানে কেটে পড়তেন। একবার নাকি বাড়ি থেকে রাগ করে বেরিয়ে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে কাজ নিয়েছিলেন। খোঁজ পেয়ে আমার প্রপিতামহ কান ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে এসেছিলেন বাড়িতে। রাতের অন্ধকারে তিনি মাঝে মাঝেই নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, দুরদুরান্তে যাত্রা দেখতে। সেই তাঁর যাত্রা প্রেম শুরু। তারপর বেশ কয়েক বছর একটি যাত্রা দলের সঙ্গে উধাও হয়ে যান। পরে ফিরেও আসেন। তাঁর গলার স্বর ছিল মিহি, সঙ্গে গানটাও গাইতেন দারুণ। তাই প্রথম দিকে তাঁকে নায়িকার পার্ট করতে হতো। তাঁর মুখে গল্প শুনেছি দর্শকরা তাঁর জন্য পাগল ছিলেন। নারী ভেবে অনেকেই তাঁকে প্রেম নিবেদনও করেছেন। তবে ছেলেরা যাত্রা-নাটকে মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করলে যেমন তাদের স্বাভাবিক আচার আচরণে মেয়েলি প্রভাব পড়ত, অভিনয়ের বাইরে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তাদের মেয়েদের চলন বলন প্রভাব লক্ষ করা যেত, আমার ঠাকুরদার ক্ষেত্রে আমি সেরকমটি কখনও দেখিনি। ৫ ফুটের ওই ছোটখাট শরীরের মানুষটার অভিজ্ঞতার ঝুলি ছিল বিচিত্র সব ঘটনায় ভরা। তাঁর জীবনের বৈচিত্র ছিল সমুদ্রসমান। অনেকেই বলে থাকেন মুখের মিল না থাকলেও শরীরী উচ্চতা আর স্বভাবে আমি তাঁর দিকেই গিয়েছি। আমার যদিও কিছুটা সন্দেহ আছে।
আজ লিখতে বসে সেইসব ফেলে আসা দিনের স্মৃতি ভিড় করে আসছে মাথায়। কখনও লিখতে লিখতে সেইসব ঘটনা মনে করে হেসে ফেলছি একা একাই, আবার কখনও ভিজে যাচ্ছে চোখের কোল; সেই সঙ্গে বুকের ভিতর একটা মৃদু চিন্চিনে ব্যাথা। বুঝে উঠতে পারছি না এই লেখার শেষ কোথায়।
জোয়ারে জল ছলাৎ ছলাৎ ডাকছে নদী আয়
চিকন চিকন রূপোর রূপে চোখ ধাঁধিয়ে যায়
ক্লাস সিক্সের পর থেকে অংকের সঙ্গে আমার ‘জানি দুশমনি’। ক্লাস সেভেনের হাফ ইয়ার্লি আর অ্যানুয়াল মিলে পেয়েছিলাম যথাক্রমে ৯ আর ২০। তখন তিনখানা বিষয় মিলে গড় হতো বলে কোনওমতে পাস করে গেছিলাম। সেই থেকে অংক আর আমার ছত্রিশ কা আঁকড়া। সেবার ক্লাস এইটের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্ট। আগের দিনই বাবা সমন জারি করেছিলেন, যদি এবার অংকের নাম্বার ৫০ এর ঘরে না থাকে তাহলে পেঁদিয়ে কুলকাঠ করবেন। সেই থেকে ভয়ে ভয়েই ছিলাম। আমি তো জানি আমি কী করেছি অংকের খাতায়। রেজাল্ট হাতে পেয়ে দেখলাম, যা আশা করেছিলাম, তার থেকে অনেক ভাল নাম্বারই পেয়েছি। আমার কাছে একেবারে ‘ছপ্পড় ফাড়কে’ নাম্বার। আশা করেছিলাম পাবো পাঁচ, কারণ মাত্র একটা অংকই আমার হিসাবে ঠিক হয়েছিলো। আর পেয়েছি চোদ্দ। আমার জন্য অভাবনীয় সাফল্য। কিন্তু বাড়ির বৃদ্ধ থুড়ি প্রৌঢ় লোকটিকে বোঝাবে কে! সাড়ে চোদ্দ পেয়ে আমার তো চার আনার আলুকাবলি খাওয়ার কথা, কিন্তু বাবার বুলডগের মতো মুখটা যাচ্ছেতাই ভাবে মনে পড়ে হাত পা একেবারে পেটের মধ্যে। স্কুল থেকে সাইকেল নিয়ে সোজা ষণ্ডেশ্বরতলা ঘাটে।

একেবারে শেষ মাথার সিঁড়িতে বসে বাবুদার দোকান থেকে পঁচাত্তর পয়সা দিয়ে কেনা ফ্লেকটা ধরিয়েছি। বাড়িতে কোনওমতেই ঢোকা যাবে না। চামড়া গুটিয়ে একেবারে আমড়া বানিয়ে দেবে পিতৃদেব। এদিকে ধুঁয়োতে ধুঁয়োতে সিগারেটের কোম্পানিতে আগুন। ঘাটের পাশেই তখন জেলে নৌকায় সনাতনদা (সনাতন মাঝি) তার সহকর্মী আমাদের বয়সি হেবো, আর বৃদ্ধ মনসুর মিঞা ইলিশের ফিনফিনে জাল ছাড়াচ্ছে। হেবোটা ছিল মহা খচ্চর। আমাকে আমসি বসে থাকতে দেখে ফোড়ন কাটলো, “কী কাকা, এরকম জনি লিভার মার্কা থোবড়া কেন তোর? গাড্ডু খেয়েছিস নাকি?” “শালা গা…” খিঁচিয়ে উঠেছিলাম। শেষে ওই বুদ্ধি দিলো, “কেটে পড় কাকা”। বৃদ্ধ মনসুরও বলল “মামা বাড়ি চলে যাও বা’জান”। কিন্তু যাওয়া যাবে না। আমার যা ট্রিমেন্ডাস বাপ, খবর পেলে সেখানে গিয়েই পেঁদাবে। অংকের জন্য তো বটেই, পালানোর জন্যও পুজোর বোনাস দিয়ে দেবে। শেষে মামাবাড়ির পাড়ার মেয়েগুলোর কাছে প্রেস্টিজে একেবারে গ্যামাক্সিন। মনসুর চাচাকে বললাম, “তোমরা কখন মাছ ধরতে যাবে? কতো দুরেই বা যাবে?” চাচা জবাব দিল, বেলা পড়ার পরই বেরোবে। কুন্তিঘাট, ত্রিবেণী হয়ে কোলাঘাট অবধি যাবে। ফিরবে দিনচারেক পর। বললাম আমাকে সঙ্গে নেবে? চাচা আঁতকে উঠে বলে, “বলো কী বা’জান, তুমি ভদ্দরলোকের পোলা, নৌকায় থাকতি পারো কখনও? রোদ জল আছে”। আমিও নাছোড়। চাচা বলে “তোমারে না পেলি বাড়ির লোকে খোঁজ করবে, পুলিশে আমারে ধরবে”। আমি আরও নাছোড়। শেষে সনাতনদা বলে উঠলো “চলুক ও। ওরে আমি চিনি, ও যাবেই। আর ও যা ছেলে সব সইয়ে নেবে, ওরে তুমি চেনো না চাচা”।
আরও পড়ুন: যে ঠিকানা লেখা যায় না, সেই ঘরে যাদের বাস! পর্দার ভবঘুরেরা
ঠাকুরদার মুখে শুনেছি আমরা নাকি বরিশালের তালুকদার ছিলাম। স্বাধীনতার পর যে সব বাঙালি ওপার বাংলা থেকে এপারে এসেছে তাদের সবার মুখেই শুনেছি ওপারে তারা জমিদার ছিল অথবা প্রচুর জায়গা জমি ছেড়ে এপারে এসেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে ঠাকুরদার কেসটা সেরকম নয়।
ব্যাস! সেই আমার প্রথম হারিয়ে যাওয়া। ছইয়ে ঘেরা নৌকার মাঝে বসে একে একে পেরিয়ে যেতে লাগলাম চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল, বাঁশবেড়িয়া, কুন্তিঘাট হয়ে আরও আরও দূরে। কেরোসিনের জনতায় হেবো রান্না করে, আমি হাত লাগাই। কখনও-বা জাল থেকে মাছ জড়ো করি নৌকার খোলে। সন্ধেবেলা জালের ধারে ধারে বাঁধা আলোগুলো গঙ্গায় ভাসতে থাকে। নৌকায় জ্বলে কেরোসিনের লম্ফ। ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে লম্ফ কেঁপে ওঠে হাওয়ায়। আর বিস্তীর্ণ গঙ্গার দু’পাড়ে সভ্যতার আলোগুলো কেমন দাঁত ভেংচে আমাদের নৌকাটাকে বিদ্রুপ করতে থাকে। নৌকার দুই মাথায় সনাতনদা আর মনসুর চাচা দাঁড় টেনে চলে; আর হেবো মাঝে মাঝে লগি দিয়ে ঠেলে দেয় জালের গায়ে লেগে থাকা কচুরিপানা কিংবা গঙ্গায় ভেসে আসা আবর্জনা। নৌকার পাশ দিয়ে আবার কখনও কখনও মাছে ঠুকরে খাওয়া ছেতড়ে যাওয়া লাশ। নৌকার রেডিয়োয় গান ভাসে। কখনও চটুল হিন্দি গান, কখনও-বা হেমন্তর ‘কোনো এক গাঁ’য়ের বধু’ আবার কখনও-বা উৎপলেন্দু চৌধুরী। নৌকার ছইয়ের ভেতর আমি বসে বসে ঝিমাই। রাত বাড়ে।

চুল্লুর নেশায় নৌকার দুই মাথায় সনাতনদা আর মনসুর চাচার দাঁড় টানাও বন্ধ। নৌকা ভেসে চলেছে স্রোতের টানে। জোয়ারে নৌকার দুই ধারের গায়ে জলের বাজনা বাজে ছলাৎ ছলাৎ। অসংখ্য মশার ঘুম পাড়ানি গানে ঘুমের দেশে চলে যায় হেবো। ঝিমুনিতে মাঝে মাঝে চটকা ভেঙে যায় আমার। সেই মায়াবী রাতে আমি দেখতে পাই, জলের উপর অসংখ্য মানিক জ্বলে রয়েছে। ওগুলো আসলে আমাদের আর আশে পাশের নৌকার জালের গায়ে লাগানো আলো। কখনও কখনও হাওয়ার টানে মেঘ এসে ঢেকে দেয় অষ্টাদশী চাঁদ, ঝিকিমিকি তারাদের আলো, কখনও-বা দমকা হাওয়াতেই মেঘ সরে গিয়ে চাঁদের আলোয় দুধসাদা হয়ে যায় বিস্তীর্ণ গঙ্গার জল। সব থেকে মায়াবী হয়ে ধরা দেয় ভোর। আস্তে আস্তে অন্ধকার কেটে গিয়ে একটা ঘোলাটে ভাবে ভরে যায় চারপাশ। তখনও সূর্য ওঠেনি। পূবের আকাশে সব মায়া ভরা আলো দেখা দিতে শুরু করেছে। খোলা আকাশ দিয়ে ডানা ঝাপ্টে তখন সবে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বেরিয়ে যায় একঝাঁক পাখি। আকাশের এক কোণে চাঁদ তখন হালকা আবছায়া হতে হতে বিদায় নিচ্ছে ঘুমের দেশে। এই সময় পূব আকাশ আলো করে আধসেদ্ধ ডিমের কুসুমের মতো আধখানা লাল সূর্য দেখা দিতে দিতে পূর্ণ মায়াবী গোলক হয়ে যায়।

আমরা গঙ্গার জল আঁজলা ভরে নিয়ে মুখ ধুই, তারপর হেবোর বানানো আদা দিয়ে গাঢ় লাল চায়ে চুমুক দিয়ে ঘুম ছাড়াই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের ঘাটে নৌকা লাগিয়ে জাল গোটানোর কাজ শুরু। রোদের আলোয় তখন রূপালি পাতের ঝিলিক দিচ্ছে আমাদের নৌকাময়। শুধু ইলিশ নয়, জালে ধরা পরে অনেক কিছু, বাচ্ছা কচ্ছপ, ছোট ছোট ট্যাংরা, কাঁকড়া, আরও কত কি। একবার তো একটা বেশ বড়োসড়ো গোছের শুশুক ধরা পড়েছিল। সেটা অবশ্য মনসুর মিঞা ছেড়ে দিয়েছিল গঙ্গায়। কিছু মাছ গঙ্গার ঘাট থেকেই বিকিয়ে যেতো, সঙ্গে ধরা পড়া কচ্ছপ ও অন্যান্য মাছ। ইলিশ বাদ দিয়ে অন্যান্য কিছু মাছ রেখে দেওয়া হতো আমাদের খাবার জন্য। দুপুরে আদা পেঁয়াজ দিয়ে গরগরে মাছের ঝোল আর ভাত। সেই ঝাল খেয়ে বাঘেরও পাছা জ্বলবে নির্ঘাত। এ ভাবেই একদিন রূপালি পাতে ভরা নৌকা ফের ভেড়ে ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাটে। আর সেই রূপালী মায়াবী স্বপ্নগুলো ছাড়িয়ে ভয়ংকর বাস্তবে আমি এসে দাঁড়াই। যথারীতি বাবার পেদানিতে কুলকাঠ হওয়া আটকানো যায়নি সে যাত্রায়।
পেশা সাংবাদিকতা, নেশা বাউন্ডুলেপনা। বাড়ি থেকে পালানো শুরু জীবন দেখার নেশায়। ডাকাত থেকে বাউল, এক জীবনে বহু সঙ্গ, আর সেই সঙ্গই ছড়িয়ে পড়ে গদ্য থেকে কবিতায়। ওহ হ্যাঁ, চা ভালবাসি, তাই আমাকে চাতালও বলা যায়