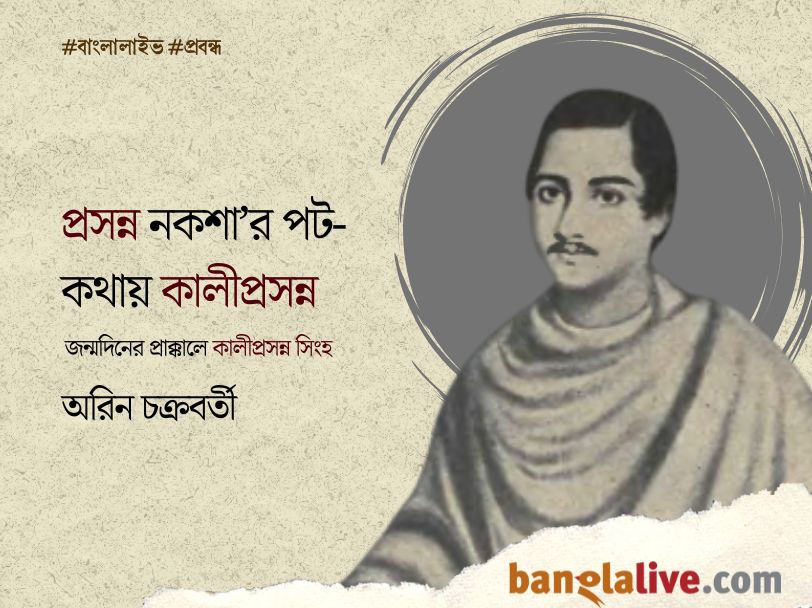বাংলা গানের দুনিয়ায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটা আলাদা বিস্ময় তৈরি হয়। তাঁকে ঘিরে এরকম ধারণার কারণ একাধিক। হেমন্ত-র প্রথাগত সংগীতশিক্ষা সেভাবে প্রায় ছিল না। অগাধ সাংগীতিক প্রতিভা ও ক্ষুরধার সংগীত-বুদ্ধিমত্তা নিয়ে এগিয়ে নিজেকে যেভাবে সেরা করে তুলেছেন, তা বিস্ময়কর! হেমন্তের এই প্রতিভার নিদর্শন শুরুতেই দেখা গিয়েছিল।
শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রকট প্রভাব কাটিয়ে, ১৯৩০-এর দশকেই বলা যায়, জন্ম নিলো ভাব ও কাব্যধর্মী ‘আধুনিক বাংলা গান’। ১৯০১-এ গ্রামোফোন রেকর্ড, ১৯২৭-এ রেডিও ও ১৯৩১ সালে বাংলা ছবির সবাক হয়ে ওঠা, সংগীতের নির্মাণ ও পরিবেশনের ধরনে একটা বড় পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। দরকার হল অনেক গানের। দ্রুত প্রস্তুতির প্রয়োজনে, একেকটা গান তৈরির ক্ষেত্রে জন্ম নিল তিনটি শ্রেণি― গীতিকার, সুরকার ও গায়ক-গায়িকা। উঠে এলেন বহু নবীন প্রতিভা। যাঁদের চিন্তায় এল, এতদিন যে বাংলা গানে সুরের কালোয়াতির প্রাধান্য দেখা যেত, তার থেকে বেরিয়ে, সহজ কাব্যধর্মী কথায়, মেলডিতে ভরা সুরে গান সৃষ্টি করার কথা। যে গান গাইতে হবে, উপযুক্ত নাটকীয়তার সঙ্গে ভাবধর্মী প্রকাশে। আর মোটামুটি এরকম সময়েই গানের জগতে এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বেনারসের মামারবাড়িতে ১৯২০ সালের ১৬ জুন জন্ম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। সংগীতময় শহর কাশী। সেখানে জন্মের পর থেকে মাঝেমধ্যেই যেতে হত। বড়দের সঙ্গে হাজির হতেন সেখানকার বিভিন্ন সংগীত-আসরে। মামাবাড়িতেও গানবাজনা হত। হেমন্ত-র বড়মাসির মেয়ে, তাঁর ‘লীলাদি’ ভালো গাইতেন। তাঁর কাছ থেকে একটার পর একটা গান উঠে আসত ছোট্ট হেমন্ত-র গলায়। তখন থেকেই খুব তাড়াতাড়ি গান শিখে ফেলার ক্ষমতা ছিল। পরবর্তীকালে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের চটজলদি গান শিখে ফেলা ও সুর করার দক্ষতার কথা তো অনেকের লেখাতেই এসেছে। গান শিখে নেওয়ার পাশাপাশি, ছোট থেকেই সুর করার প্রবণতাও ছিল। কাশীর মামারবাড়িতে স্বদেশি আন্দোলনের হ্যান্ডবিল আসতো। স্বদেশি কর্মীরা বিভিন্ন বাড়িতে এসব ছড়িয়ে যেতেন। এতে থাকত অনেক বিদ্রোহী কবিতা। মামারবাড়িতে থাকার সময়, এইসব কবিতায় সুর বসানোর চেষ্টা করতেন হেমন্ত। সংগীত ক্রমশ নেশায় পরিণত হওয়ার শুরু তখন থেকেই।
আরও পড়ুন: প্রবাসে হেমন্ত, হেমন্তে প্রবাস (স্মৃতিতর্পণ)
হেমন্তদের আদি বাসস্থান ২৪ পরগণার (এখন দক্ষিণ ২৪ পরগণা) বহড়ু গ্রামে। তাঁরা থাকতেন কলকাতার ভবানীপুরে। পড়াশোনার জন্য এখনকার মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হলেন। সেখানে বন্ধু হিসেবে কয়েকজনের মধ্যে পেলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় (পরে বিখ্যাত কবি), রমাকৃষ্ণ মৈত্র-র মতো সাহিত্যপ্রেমীদের। ফলে, হেমন্ত-র মাথাতেও সাহিত্য-পোকা ঢুকল। লেখালেখির ইচ্ছেটা চাগাড় দিল। কিছুদিন পরে তো একটা সাহিত্য সংঘও গড়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। নিয়মিত গল্প লিখতে লাগলেন। ‘দেশ’ পত্রিকাতেও গল্প বেরোলো। আর সুভাষের তো জন্মগত কাব্যপ্রতিভা। তিনিও ছাত্রাবস্থা থেকেই কাব্যরথের সারথি। তখন হেমন্তর মনে কিন্তু সংগীতশিল্পী নয়, সাহিত্যিক হবার বাসনাই গেড়ে বসেছিল। এ ব্যাপারে বাধ সেধেছিলেন সুভাষ। আপামর গানপ্রেমীদের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। ইস্কুলের অফ পিরিয়ডে বেঞ্চি বাজিয়ে গান গাইতেন হেমন্ত। তাই দেখে সুভাষ একদিন তাঁকে বলেছিলেন, গানই হেমন্তর দুনিয়া। সাহিত্য নয়। তার পরেও বেশ কিছুদিন অবশ্য হেমন্তর সাহিত্য-পাগলামি বজায় ছিল। তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন, সাহিত্য করলে হেমন্ত মোটামুটি একটা জায়গা পর্যন্ত পৌঁছবে। কিন্তু সংগীতে সে সেরার পর্যায়ে যেতে পারে। ঐ বয়সেই কী জহুরীর চোখ ছিল স্বনামধন্য কবির!

সুভাষের জোরাজুরিতেই ১৯৩৫ সালে রেডিওতে গাওয়া হয়ে গেল হেমন্ত-র। বয়স তখন ১৫। দুটি গান গাইলেন। সুভাষ লিখলেন একটি, “আমার গানেতে নবরূপে এলে চিরন্তনী/ বাণীময় নীলিমায় শুনি তব চরণধ্বনি…” এবং অন্যটি পাড়ার একজনের কাছ থেকে শেখা একটি প্রচলিত লোকগীতি, “আকাশের আরশিতে ভাই…”। সুভাষের কবিতাটিতে হেমন্ত সুর বসিয়েছিলেন। ঐ ১৯৩৫ সালেই রেকর্ডে নিজের সুরে কমল দাশগুপ্তের গাওয়া, “তোমার হাসিতে জাগে…” গানটি খুব জনপ্রিয় হয়। এই সুরের ধাঁচেই “আমার গানেতে নবরূপে এলে…” কবিতায় সুর করেছিলেন হেমন্ত। এখানে একটি লক্ষ্যণীয় দিক আছে। কোনও গানের কথায় যখন সুর বসানো হয়, তাতে কথার সঙ্গে সুরের একটা মিটারের মাপ থাকে, যা থাকলে, তবেই বাণী-সুর খাপে খাপে মেলে। এখানে আমরা দেখছি, অন্য একটি গানের সুরের ধাঁচে হেমন্ত সুর করছেন সুভাষের কবিতাটিতে। তার মানে, ঐ ১৫ বছর বয়সেই তাঁর এই ধারণা স্পষ্ট রয়েছে, কোন গানের সুরটি এই কবিতায় খাপ খাবে। অর্থাৎ মিটারে মিলবে। বোঝাই যাচ্ছে, শুরু থেকেই তাঁর সত্তা পরিপূর্ণ সংগীতে। তখন কিন্তু তাঁর প্রথাগত সংগীত-শিক্ষার ছিটেফোঁটাও হয়নি। শুধুমাত্র বেঞ্চি বাজিয়ে আর এলোমেলোভাবে কিছু গান তুলে গাওয়া অবধি দৌড়।
হেমন্ত, তাঁর গানপ্রীতির ব্যাপারে মা কিরণবালা দেবীর উৎসাহ ছোট থেকে পেলেও, বাবা কালিদাস মুখোপাধ্যায় এসব একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন, হেমন্ত ইঞ্জিনিয়ার হোক। সেইমতো, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হেমন্ত ভর্তিও হয়েছিলেন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। যদিও থার্ড ইয়ারে সেসব ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি ডুবে যান গানে। সে যাই হোক, এহেন বাবাই হঠাৎ একদিন আশ্চর্যজনকভাবে ছেলেকে তাঁর অফিসে নিয়ে গিয়ে এক কলিগের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন, যিনি তখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে চেলো বাজাতেন। সেই ভদ্রলোক মারফত হেমন্ত গিয়ে পড়লেন তখনকার অন্যতম গুণী সংগীত পরিচালক ও শিক্ষক শৈলেশ দত্তগুপ্তের কাছে। একবার হেমন্ত-র গান শুনেই, তাঁকে দিয়ে রেকর্ড করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন শৈলেশবাবু। ফলে, ১৭ বছর বয়সে শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ও নরেশ্বর ভট্টাচার্যের কথায় প্রথমবার রেকর্ডে হেমন্ত গাইলেন, “জানিতে যদি গো তুমি…” ও “বলো গো বলো মোরে…”। সময়টা ১৯৩৭ (রেকর্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে)। শুরু হল সংগীত-অভিযান।

প্রথম রেকর্ডের হেমন্ত-কণ্ঠ থেকে শুরু করে, পরবর্তীকালে তাঁর গানগুলির দিকে পরপর নজর দিলে, একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যা থেকে বোঝা যায়, শুরু থেকেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাংগীতিক ধ্যানধারণার বিশিষ্টতার দিকটি।
হেমন্ত-কণ্ঠকে বলা হয় ‘স্বর্ণকণ্ঠ'(Golden voice)। কিন্তু এর অর্থ কী? প্রথম রেকর্ডে তাঁর গান শুনলে আমরা একটুও খুঁজে পাই না চেনা গলার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। এক বিশেষ ধরনের উচ্চারণ, সঙ্গে নাকিসুরের প্রাধান্য। তখন যেসব অসামান্য শিল্পীরা গাইছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম-প্রাপ্ত। কিন্তু আধুনিক বাংলা গান তাঁরা গাইতেন মেলডির ভাবধর্মী পথে। সহজ ভঙ্গিতে গাইলেও, তাঁদের কণ্ঠ প্রক্ষেপণে হয়তো কিছুটা শাস্ত্রীয় সংগীতের ছোঁয়া থেকে যেত। তখন এক ধরনের তীক্ষ্ণ সুরে উঁচু পর্দায় রেওয়াজি পরিবেশনের প্রবণতা ছিল। অনুমান করা যায়, এটা অনেকটাই ঠুংরির প্রভাবজাত। এছাড়া, হিন্দুস্থানি সংগীত পরিবেশনে একটা বিশেষ ধরনের উচ্চারণের প্রবণতা থাকে। যা বাংলা গান পরিবেশনেও কিছুটা এসে যেত, আর ঠুংরির প্রভাবে থাকত নাকিসুরের প্রাধান্য। যদিও সামগ্রিকভাবে আধুনিক বাংলা গানের শিল্পীরা সংগীত-পরিবেশনে ভাবকেই প্রাধান্য দিতেন। আরও একটা কথা, গ্রামোফোন কোম্পানিতে দীর্ঘদিন অন্যতম ট্রেনার হিসেবে ছিলেন ঠুংরি-সম্রাট উস্তাদ জমীরুদ্দিন খাঁ। তখনকার বহু শিল্পী তাঁর কাছে ট্রেনিং পেতেন। সেই প্রভাবও হয়তো বাংলা গান গাওয়ার ক্ষেত্রে পড়ত। এই ধরনের গায়কীর ধাঁচেই হেমন্তও রেকর্ডে গাওয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর ক্ষেত্রে তফাৎ হচ্ছে, অন্যদের মতো তাঁর শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষা ছিল না। এছাড়া, তখনকার প্রখ্যাত গায়ক ও সুরকার পঙ্কজ মল্লিকের প্রভাব হেমন্ত-র ওপরে শুরু থেকেই পড়েছিল। পঙ্কজবাবুরও সেইভাবে প্রথাগত সংগীত শিক্ষা ছিল না। তাছাড়া, তিনি সেইসময় রবীন্দ্রনাথের গানকে জনসমক্ষে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে ছিলেন প্রধান স্থপতি। পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও স্বীকৃতি। নিজের কবিতায় দেওয়া পঙ্কজ মল্লিকের সুরকে অনুমোদন দিয়েছিলেন স্বয়ং কবি। এই একই সাংগীতিক পথে হেমন্তও নিজেকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। শৈলেশ দত্তগুপ্তের শিক্ষায় অনেক গানের মতো রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল। জেনেছিলেন কীভাবে স্বরলিপি দেখে গান তুলতে হয়। এই সবকিছু মিলিয়ে, পেশাগত সংগীতের দুনিয়ায় এসে পঙ্কজ মল্লিককে তাঁর মানসগুরু হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন হেমন্ত । কিন্তু স্বকীয়তার সন্ধান ছিল তাঁর প্রথম থেকেই। অর্থাৎ, নিজেকে আলাদা করে চেনানোর তাগিদ। যেটা দেখা গিয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কণ্ঠ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এই নিবন্ধের এটিই আলোচ্য বিষয়।

প্রথম রেকর্ডের পর, পরপর কয়েকটি বছরে হেমন্ত-র আরও কয়েকটি গানের রেকর্ড বেরলো। একইরকম কণ্ঠচলন। গানগুলোও তেমন মনকাড়া কিছু নয়। সব গানের সুরকারই শৈলেশ দত্তগুপ্ত। কিন্তু তখন হেমন্ত-র অন্তরে যে সাংগীতিক বোধ ও বুদ্ধিমত্তা কাজ করছিল, তা তাঁকে এক নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছিল হয়তো। আজকের ‘হেমন্ত মুখোপাধ্যায়’ হয়ে ওঠার পথে সেই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৪১ সালে, নিজের পাঁচ নম্বর রেকর্ডে সুবোধ পুরকায়স্থ-র কথায় ও শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে হেমন্ত গাইলেন― “রজনীগন্ধা ঘুমাও ঘুমাও…” এবং “চাঁদেরে স্মরিয়া শিউলি…”। সেই প্রথম আমরা পেলাম পরিচিত হেমন্ত-কণ্ঠের ছোঁয়া। অদ্ভুত বেসের ব্যবহার, শব্দ ধরে ধরে সুরের পথে উপযুক্ত নাটকীয়তার প্রয়োগ, মেলডির যথাযথ পরিবেশন, পরিমিত নাকের ব্যবহার ও পরিশীলিত উচ্চারণ। সেইসময় কিন্তু অন্যান্য পুরুষশিল্পীদের কণ্ঠপ্রক্ষেপণে এই জিনিস দেখা যাচ্ছিল না সেভাবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সামগ্রিকভাবে দেখা যেতে লাগল স্বাভাবিক কণ্ঠের গায়নরীতি। এছাড়া, যেসব পুরুষশিল্পীদের তখন উত্থান ঘটছে, শুরু থেকেই তাঁরা গাইছেন অনেকটা স্বাভাবিক গলায়। তাহলে কি এরকম অনুমান করা যায় যে, কণ্ঠচলনে এই ধরনের আধুনিকতা আনার ক্ষেত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনেকটাই? বাংলা গানে অমন আমূল বদল আনলেন এমন একজন, যাঁর সেইভাবে প্রথাগত সংগীত-তালিম প্রায় হয়নি বললেই চলে!
সেইসময় রাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে আন্তর্জাতিক ধ্যানধারণার প্রবেশ ঘটছে। গানের জগতে রেকর্ডের মারফত পাশ্চাত্য শিল্পীদের গানবাজনা শোনার চল বাড়ছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে এই সবকিছুর প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। সেই কারণেই হয়তো উচ্চারণে স্পষ্টতা ও নিজের কণ্ঠের ব্যারিটোন ভয়েসকে তিনি বের করে আনার ভাবনা ভাবছেন গভীরভাবে। তখনকার সাধারণ বাংলা গানের সব ধরনের পরিসরে নিজেকে মেশাচ্ছেন। গাইছেন। চেষ্টা করছেন সুরারোপে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে। সমস্ত জায়গা থেকে আহরণ করছেন বিভিন্ন রীতির সংগীত-উপাদান, আর মিশিয়ে নিচ্ছেন নিজের সংগীত-সত্তার সঙ্গে। সব সৃষ্টিশীল মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁর নিজের ক্ষমতা ও পরিসর সম্পর্কে তাঁরা গভীরভাবে সচেতন। হেমন্ত-র এই ধারণাটি বোধহয় একটু বেশিই ছিল। তাই চিরকাল তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ সাংগীতিক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সংগীত-পথে এগিয়েছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পেয়েছেন সাফল্য। যার শুরু, গোড়াতেই কণ্ঠপ্রক্ষেপণ নিয়ে তাঁর নজরকাড়া ভাবনার প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। যাঁকে আমরা বলি ‘স্বর্ণকণ্ঠ’। যাকে শুধুমাত্র প্রকৃতিপ্রদত্ত বললেই হবে না। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি গভীরভাবে ভেবেছিলেন তাঁর কণ্ঠচলন নিয়ে।
অদ্ভুত বেসের ব্যবহার, শব্দ ধরে ধরে সুরের পথে উপযুক্ত নাটকীয়তার প্রয়োগ, মেলডির যথাযথ পরিবেশন, পরিমিত নাকের ব্যবহার ও পরিশীলিত উচ্চারণ। সেইসময় কিন্তু অন্যান্য পুরুষশিল্পীদের কণ্ঠপ্রক্ষেপণে এই জিনিস দেখা যাচ্ছিল না সেভাবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সামগ্রিকভাবে দেখা যেতে লাগল স্বাভাবিক কণ্ঠের গায়নরীতি।
সংগীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর বলেছিলেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শুনলে তাঁর মনে হয়, যেন কোনও সন্ন্যাসী দেবস্থানে বসে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। সংগীত পরিচালক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমন্ত-কণ্ঠকে বলতেন “দেব-কণ্ঠ”। আর যশস্বী সলিল চৌধুরী বলেছিলেন যে, ভগবান যদি গান করতেন, তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাইতেন। এরপর আর কীই-বা বলার থাকে আমাদের? ১৯৫৮ সালে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় ও নচিকেতা ঘোষের সুরে হেমন্ত গেয়েছিলেন, “আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে…”। তাঁর এই আত্মবিশ্বাসী আবেদন যে কতদূর সত্যি হয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি, যখন অনুভব করি আমাদের হৃদয়ে হেমন্ত-গানের স্বরলিপি কীভাবে চিরকালের জন্যে গাঁথা হয়ে গেছে। আগামী পৃথিবীকে যা কান পেতে শুনতেই হবে।
তথ্যঋণ :
১) “আনন্দধারা”― হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা: অভীক চট্টোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি প্রকাশন ২০১৩)
২) প্রসাদ, হেমন্ত সংখ্যা ১৯৬৯
৩) জীবনপুরের পথিক হেমন্ত (সংকলন ও সম্পাদনা: ধীরাজ সাহা, ওপেন মাইন্ড, ২০০৯)
৪) আলোর পথযাত্রী (সংকলন ও সম্পাদনা: ধীরাজ সাহা, ২০১৩)
৫) অনন্য হেমন্ত (নিবন্ধ)― অভীক চট্টোপাধ্যায় (জাগ্রত বিবেক,জুন ২০১৮)
জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।