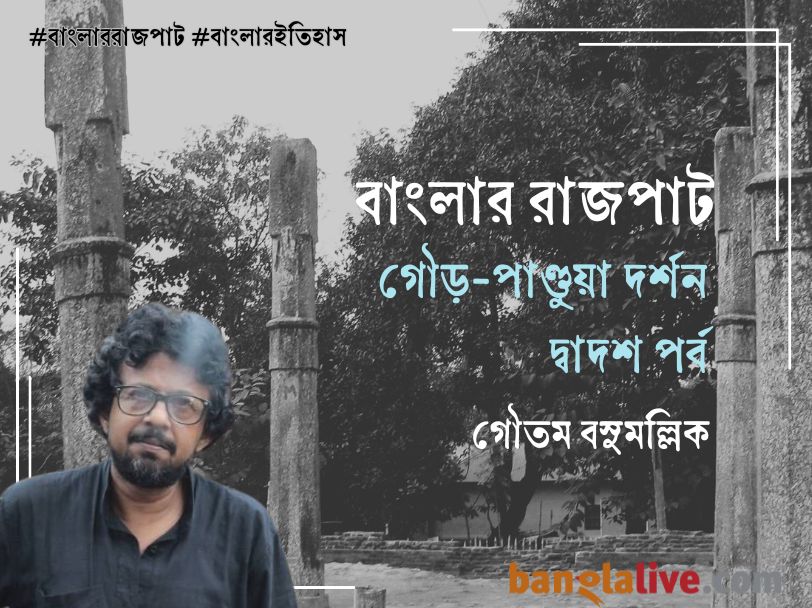শশাঙ্কই ছিলেন গৌড়বঙ্গের প্রথম স্বাধীন সম্রাট
আগের পর্ব পড়তে: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১]
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা ক্ষেদোক্তি করেছিলেন এই বলে যে এ দেশের কোনও ইতিহাস নাই৷ বাস্তবিকই এ দেশের ইতিহাস লেখার কাজটা প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছিল বিদেশি ইতিহাসবিদদের হাত ধরেই৷ কিন্তু সে সব লেখার একটা বড়ো অংশই ছিল বিদেশি শাসকদের নিজেদের প্রশংসার কথা৷ এ দেশের জনগণের কথা, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ভাবে বিখ্যাত নয় এমন এমন জায়গার কথা, স্থাপত্যের কথা, জনজাতির কথা বা সব মিলিয়ে আমজনতার জীবনচর্যার কথা তেমন ভাবে প্রতিফলিত হয়নি সেই সব মূল স্রোতের ইতিহাসে৷ সেই ঘাটতি পূরণ হয় পরবর্তীকালের আঞ্চলিক ইতিহাস রচয়িতাদের লেখার মধ্যে দিয়ে৷ (Gour banga)

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অনেক জায়গার তবু খানিক ইতিহাস পাওয়া গেলেও বাংলার ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগের ইতিহাস প্রায় নেই বললেই চলে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ও তৎপরবর্তী কালে গ্রিক পর্যটকদের বিবরণে পূর্বভারতে এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্যের ইঙ্গিত থাকলেও তা নিয়ে বিস্তৃত কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। বস্তুত ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ থেকে বাংলার ইতিহাস পাওয়া আরম্ভ হয়। তার আগে বঙ্গদেশ-সহ গোটা পর্ব ভারতের ইতিহাস অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন।
সাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ থেকে অনুমান করা হয়, ষষ্ঠ শতকের একেবারে শেষ ভাগে, ৫৯৩ সাধারণাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন রাজা শশাঙ্ক এবং রাজত্ব করেন ৬৩৮ সাধারণাব্দ পর্যন্ত।
অনেক ইতিহাসবিদ শশাঙ্ককে প্রথম স্বাধীন বাঙালি নৃপতি বলে উল্লেখ করলেও, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আলাদা বৈশিষ্টযুক্ত কোনও বাঙালি জাতিসত্ত্বা তখন গড়ে ওঠেনি বলেই মনে করা যেতে পারে। আর বঙ্গদেশ বলতে গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন নামের বিভিন্ন অংশকে বোঝানো হতো।

সম্রাট শশাঙ্ক ও তাঁর রাজ্য:
শশাঙ্ক হয়তো গুপ্তদেরই কোনও এক শাখার সদস্য। তাঁর আসল নাম সম্ভবত নরেন্দ্রগুপ্ত। তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না তবে মনে করা হয় তিনি গুপ্তরাজা মহাসেনগুপ্তর অধীনে কোনও মহাসামন্ত হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করছিলেন, তৎকালীন উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে তিনি গৌড় অধিকার করেন। তথ্যের এবং ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে শশাঙ্ক সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানা যায় না। শশাঙ্কের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শত্রু হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টর কিছু লেখা এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পর বঙ্গভূমিতে আসা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ থেকেই শশাঙ্ক সম্পর্কে সামান্য কিছু জানা যায়। তবে শশাঙ্ক যেহেতু বৌদ্ধ-বিরোধী ছিলেন তাই বাণভট্ট বা হিউয়েন সাং তাঁর সম্পর্কে তেমন ভালো কথা লিখে যাননি। তবে অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায় যে নরেন্দ্রগুপ্ত বা শশাঙ্কই বঙ্গভূমির প্রথম পরাক্রমশালী নৃপতি যিনি কিছু সময়ের জন্য হলেও উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পাল ও সেন রাজবংশ:
শশাঙ্কের মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁর গড়ে তোলা গৌড় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। পুরনো শত্রু হর্ষবর্ধনের আক্রমণ তো ছিলই তার পাশাপাশি ছোট ছোট সামন্তরাজেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তী প্রায় একশো বছরেরও কিছু বেশি সময় ধরে এই নৈরাজ্য চলেছিল। ইতিহাসে ওই সময়কালকে ‘মাৎস্যন্যায় যুগ’ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

দীর্ঘ শতবর্ষ ধরে নৈরাজ্য চলবার পর, বাংলার তৎকালীন প্রভাবশালী সামন্তরাজারা মিলিত হয়ে গোপাল নামে এক বিচক্ষণ সামন্তরাজাকে গৌড়ের রাজা হিসেবে মনোনীত করেন। ৭৫০ সাধারণাব্দে গোপাল গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন।
পাল রাজবংশের উদ্ভব সম্পর্কে কয়েকটা পুরাণ ও বৌদ্ধ পর্যটকদের কিছু বিবরণ পাওয়া গেলেও সেগুলো পরস্পরবিরোধী তথ্যে পরিপূর্ণ। উনিশ শতকের শেষ ভাগে দিনাজপুরের খালিমপুর থেকে উদ্ধার হওয়া ধর্মপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, গোপালের পিতার নাম বপ্যট এবং পিতামহের নাম দয়িতবিষ্ণু। দয়িতবিষ্ণু এবং বপ্যটের রাজ্য সম্পর্কে তেমন বিস্তৃত কোনও তথ্য না থাকলেও ওই দু’জন যে বীর ছিলেন, সে কথা বলা হয়েছে।

পাল রাজবংশ বাংলায় কমবেশি সাড়ে চারশো বছর রাজত্ব করেন। তবে ওই পুরো সময়কাল যে তাঁরা সকলেই খুব নিরুপদ্রব ভাবে রাজ্য শাসন করতে পেরেছিলেন তা নয়। পাল রাজাদের আমলে কোনও একক রাজধানী নগর ছিল কী না তার তেমন কোনও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সময়ে গৌড় (উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলা ও সংলগ্ন অঞ্চল), বিক্রমপুর, পাটলিপুত্র, মুঙ্গের, মহীপাল (মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ সংলগ্ন অঞ্চল), রামাবতী প্রভৃতি অঞ্চলকে পালরাজারা রাজধানী নগর হিসেবে ব্যবহার করেছেন বলে মনে করা হয়। পাল রাজত্বের শেষ ভাগ থেকে দক্ষিণ ভারতের কর্নাট থেকে আসা সেন বংশীয় সামন্তরাজারা ধীরে ধীরে ক্ষমতা বিস্তার করে এক সময়ে গৌড় অধিকার করেন। তবে সেন রাজবংশ সম্পূর্ণ গৌড়ের অধিকার পেয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সময়কালে। কিন্তু সে ক্ষমতা তাঁরা ধরে রাখতে পারেননি। অনুমান করা হয় অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বিক্রপুরের কাছে অবস্থিত বিজয়নগর ছিল বল্লালসেনের রাজধানী শহর। তবে নামের মিল থাকলেও এই বিজয়নগরের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের কর্নাটক রাজ্যের হাম্পির নিকটবর্তী বিজয়নগরের কোনও সংযোগ নেই। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে, ১৩৩৬ সাধারণাব্দে সঙ্গম বংশীয় দুই ভাই হরিহর ও বুক্ক বিজয়নগর প্রতিষ্ঠা করেন। বিপরীত দিকে গৌড়বঙ্গের উত্তর অংশে সম্ভবত সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তাঁর পুত্র বল্লালসেন মহানন্দা নদীর পশ্চিমপারে মালদহ-গৌড়ের একটা জায়গায় লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী সরিয়ে আনেন। বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণের রাজধানীও ছিল এই লক্ষ্মণাবতী, কিন্তু তিনি কোনও কারণে নদিয়া বা নবদ্বীপেও একটা রাজধানী স্থাপন করেন। ঠিক কোন জায়গায় ছিল লক্ষ্মণাবতী, তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবু স্থানীয়ভাবে পাতালচণ্ডী সংলগ্ন অঞ্চলকেই লক্ষ্মণাবতীর আনুমানিক অবস্থান বলে ধরে নেওয়া হয়।
বর্তমানে ওই জায়গায় যে নদীখাতের অংশ দেখা যায় সেখানে পাথরের গায়ে জাহাজ বা নৌকা বাঁধবার লোহার আংটার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। এ ছাড়া খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্মণাবতীর স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

ইসলাম শাসনের সূচনা:
আনুমানিক ১২০৩-০৪ সাধারণাব্দ নাগাদ ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি অতর্কিতে নদিয়া তথা নবদ্বীপ আক্রমণ করে রাজা লক্ষ্মণসেনকে বিতাড়িত করে সেখানে কিছু সৈন্যসামন্ত রেখে উত্তর দিকে বাংলার তৎকালীন রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর দিকে যাত্রা করেন। তিনি প্রায় বিনা বাধায় লক্ষ্মণাবতী জয় করেন এবং নগরীর নাম দেন লখনউতি। জয় করলেও ইখতিয়ার সেখানে রাজধানী স্থাপন না করে আরও উত্তরে বর্তমান দিনাজপুর জেলার দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করলেন এবং কয়েকটা প্রায় অসফল সৈন্য অভিযানের পর ওই দেবকোটেই নিজের পরিচিত আলি মর্দান কর্তৃক নিহত হলেন।
ইখতিয়ারের মৃত্যুর পরেও অন্তত শতাধিক বা তার বেশি সময়কাল ধরে লখনউতি বা তার কাছাকাছি অঞ্চল জুড়েই ছিল বাংলার রাজধানী নগর। রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হলেও লখনউতি ক্রমাগত বসবাস-অযোগ্য নগরীতে পরিণত হয়ে চলেছিল। শেষ অবধি হাজি ইলিয়াস শাহ ১৩৪৩ সাধারণাব্দ নাগাদ পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।
পরের পর্বগুলো থেকে আমরা বাংলার সুলতানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পরবর্তী স্বাধীন সুলতানদের কথা আলোচনা করবো।
গ্রন্থঋণ:
১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দে‘জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩
২। মালদহ: জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা
৪। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা
৫। কেদারনাথ গুপ্ত, গৌরবময় গৌড়বঙ্গ, সোপান, কলকাতা
৬। অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৭। প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস: প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
৮। সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু’শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮—১৫৩৮), ভারতী বুক স্টল, কলকাতা
৯। সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা
১০। সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস: দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা
১১। Alexander Cunningham, ASI Report of A Tour in Bihar and Bengal in 1879-80 from Patna to Sunargaon_Volume XV, ASI, New Delhi
১২। Creighton Henry, The Ruins of Gour described and represented in eighteen views; with a topographical map, Londan
১৩। John Henry Ravenshaw, Gaur its Ruins and Inscriptions, C. Kegan Paul & Co. London.
১৪। Khan Sahib M. Abid Ali Khan, Memoirs of Gour and Pandua, Bengal Secretariat Book depot, Calcutta.
১৫। Ghulam Husain Salim, The Riyazu-S-Salatin: A History of Bengal, Asiatic Society, Calcutta (মূল বইটা ফার্সি ভাষায় লেখা। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন Maulavi Abdus Salam.)
গৌতম বসুমল্লিকের জন্ম ১৯৬৪ সালে, কলকাতায়। আজন্ম কলকাতাবাসী এই সাংবাদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে-বেড়ানো আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার সুবাদে। মূলত কলকাতার ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও, এখনও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান ইতিহাস, স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন’ [UGC, Human Resource Development Centre (HRDC)]-র আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন দীর্ঘকাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কলকাতার পারিবারিক দুর্গাপুজো’।