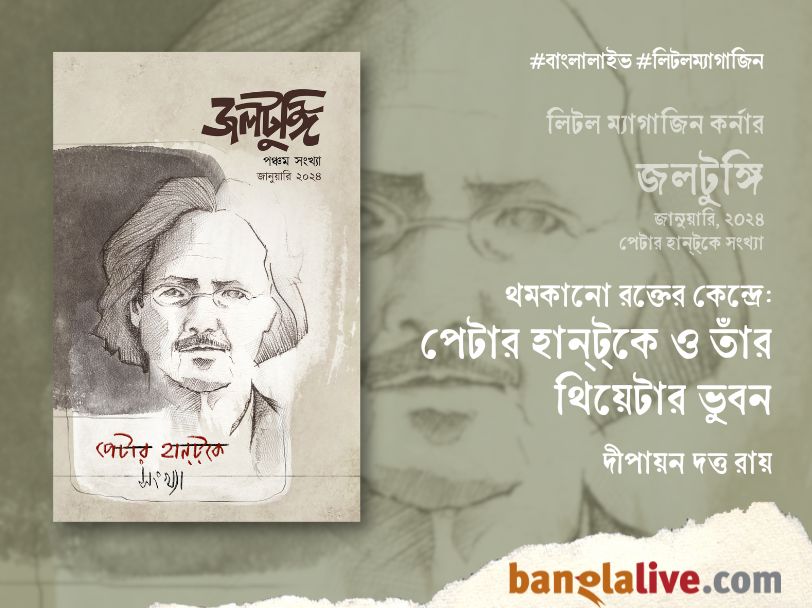(Little Magazine)
১৯৬৬ সাল। ততদিনে স্যামুয়েল বেকেট এবং য়্যজেন ইওনেস্কো অ্যাবসার্ড নাটক লিখে ইউরোপে সমাদৃত। তার দু-বছর পরেই প্যারিসে সংঘটিত হবে অতিকায় ছাত্র আন্দোলন, তার জন্য তৈরি হচ্ছিল ফ্রান্স। জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দু-দশক কাটিয়ে ফেলেও স্মৃতির নোনা প্রাচীর থেকে মুছে ফেলতে পারেনি রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ব্যস্ত চোরাগোপ্তা হানাহানিতে। এমতাবস্থায় এটুকুই আশা করা যায়, একজন নাটক-লিখিয়ে আরও বেশি করে সংকল্প নেবেন বিপর্যস্ত হন্যমান সময়ের দর্পণ, প্রাণের আলো হয়ে ওঠার, যেমনটা নিয়েছিলেন বেকেট, ইওনেস্কো, কাম্যু, আদামভ, আরাবালরা। কিন্তু অস্ট্রিয়ার বছর তেইশের এক যুবক ‘playwright’ সংকল্পবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি বললেন:
“The theatre as a social institution seems to me useless as a way of changing social customs. It is no good when it comes to suggesting solutions.”
(Little Magazine)
থিয়েটারের কোনো নৈতিক বা সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। যিনি বললেন এই কথা তিনি অস্ট্রিয়ার নাটক-লিখিয়ে (নাটককার বলা সমীচীন হবে না) পেটার হান্ট্কে, যাঁর সঙ্গে আমাদের ক্ষীণ পরিচয় ২০১৯ সালের নোবেল পুরষ্কারের (সাহিত্য) মধ্যেই সীমায়িত। খুব অল্প বয়সেই যে-কয়েকটা কথা বলে হান্ট্কে পশ্চিমী জগতের থিয়েটারকে দেখার দৃষ্টি পালটে দিয়েছিলেন, তার একটি ছিল:
“I want to make people aware of the world of the theatre— not of the world outside. My idea is to have the spectators thrown back upon themselves.”
অর্থাৎ এ-যাবৎ থিয়েটারকে বাস্তবের প্রতিনিধিত্বমূলক ‘মঞ্চ’ হিসেবে দেখার অ্যারিস্টটলীয় প্রবণতা থেকে সরে আসছেন পেটার হান্ট্কে। উপরন্তু অ্যারিস্টটল-কথিত ‘ethos’ (চরিত্র) থেকে মুক্ত করছেন থিয়েটারের স্পেসকে। হান্ট্কের নাটকে তাই কোনো চরিত্র থাকে না, থাকে শুধু অভিনেতা। নাটককে চরিত্র-মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল প্লটকে নস্যাৎ করা, কেন-না তা না-করতে পারলে ‘mythos’ সম্বলিত নাটক/থিয়েটার কখনোই অপ্রতিনিধিত্বমূলক (anti-mimetic) হতে পারবে না। প্লটের পরিবর্তে হান্ট্কে ব্যবহার করলেন এমন এক মঞ্চপ্রত্ন ধাঁচ (ethno-stage type) যাকে রঁলা বার্ত ‘performative narration’ বলেছেন। আর এই ‘performative narration’ গড়ে তোলবার তাগিদেই হান্ট্কে থিয়েটারে দৃশ্যনির্মাণের পরিবর্তে আনলেন দৃশ্যলেখন। ভাষাকে ভেতর থেকে বাইরে অবধি ছিঁড়েখুঁড়ে বের করলেন চেতনার পাতালছায়ায় নিহিত অমসৃণ বল্কল, ভাষাকে দান্তের ‘ইনফার্নো’-র সঙ্গে তুলনা করে খনন করতে করতে ঢুকে পড়লেন সবচেয়ে গভীরে থাকা স্তরে, আবিষ্কার করলেন থিয়েটারের নতুন এক ডিসকোর্স। (Little Magazine)
প্লটের পরিবর্তে হান্ট্কে ব্যবহার করলেন এমন এক মঞ্চপ্রত্ন ধাঁচ (ethno-stage type) যাকে রঁলা বার্ত ‘performative narration’ বলেছেন। আর এই ‘performative narration’ গড়ে তোলবার তাগিদেই হান্ট্কে থিয়েটারে দৃশ্যনির্মাণের পরিবর্তে আনলেন দৃশ্যলেখন।
হান্ট্কে তাঁর ‘অভিনেতাদের জন্য নিয়মাবলি’ প্রবন্ধে পরিচালক ব্রেশ্টের নাট্যদর্শনের সমালোচনা এবং নিজের নাটকে সময় ও পরিসরের অনুপস্থিতির কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করছেন স্ট্রিন্ডবার্গের ‘আ ড্রিম প্লে’ (১৯০২)-এর ভূমিকায় বলা সেই বিখ্যাত কথা: “Time and space do not exist.” কিন্তু কেন স্ট্রিন্ডবার্গের এই কথাটিকেই তুলে নিলেন হান্ট্কে? কারণ, ওঁর নাটকের অভিমুখ ছিল মালার্মে কথিত সেই মিথিক থিয়েটার “যা স্থান, কাল— যাকে চরিত্র বলা হয়— তার থেকে মুক্ত” (‘নাটকে বিকল্প ভাষ্য ও য়্যজেন ইউনেস্কো’, চিন্ময় গুহ)। এহেন মিথিক থিয়েটারের প্রত্যক্ষতম উদাহরণ আলফ্রেদ জারি-র ‘উ্যব্যু রোয়া’ (১৮৯৬) নাটকটি, যা হান্ট্কে নিজেই বলেছেন তাঁকে চমকে দিয়েছিল। সম্ভবত ‘উ্যব্যু রোয়া’ থেকেই হান্ট্কে পেয়েছিলেন নিজের নাটকে ‘sprechstuck’ (আক্ষরিক অর্থে speak-in) পদ্ধতি উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণা। ‘sprechstuck’ কী, জানতে চাইলে হান্ট্কে বলেন: “sprechstucks or speak-ins are readymades or materials from the language of the daily existence: maxims, honorifics, slogans, officialese, advertisements, greetings…” জারি-র ‘উ্যব্যু রোয়া’-তেও তো আমরা এরকম ‘readymades’ ঢের পেয়েছি: পাখির কূজন, কান ঝালাপালা করে দেওয়া বাঁশির আচমকা শব্দ, অট্টহাসি। জারি এবং হান্ট্কে দু-জনেই থিয়েটারের ভাষ্যের প্রথাগত স্ট্রাকচারকে ভেঙেচুরে করে তুলেছেন আরও রক্তাক্ত, অসহায় (verletzlich)।
(Little Magazine)
‘Nachmittag eines Schriftstellers’ (‘এক লেখকের সন্ধ্যা’) উপন্যাসে হান্ট্কের ‘actor’ বার বার করে বলছে সে ‘বাস্তব’-এ আগ্রহী নয়, কেন-না বাস্তব তৈরি ভাষা দিয়ে। ভাষা কী? শব্দের যথাযথ অর্থবহ বিন্যাস। কিন্তু সে-বিন্যাস পল্লবগ্রাহী (superficial)। তাই বাস্তব নেই, যেহেতু প্রকৃত ভাষা বলেও কিছু নেই (যে-ভাষা হান্ট্কে খুঁজছেন) বরং আছে শুধু চিহ্নসর্বস্বতা। আমরা ভাষা বলতে যাকে বুঝি তার একটাই কাজ: প্রতিনিধিত্ব করা (to represent), যা শঙ্খ ঘোষ একটু অন্যভাবে বলেছেন:
“নদী খুব নদী নয়, ভেজায় পায়ের মূল, পাতা
প্রেম তত প্রেম নয়, ঘিরে আছে সীমানা কেবল
শ্মশানও তেমন ধুনি সাধনার বিশালতা নয়
রাত্রি শুধু বীজময়, ভোর শুধু ভোরের বাগিচা।”
(‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’, ২৪ সংখ্যক কবিতা)
ভাষা কী? শব্দের যথাযথ অর্থবহ বিন্যাস। কিন্তু সে-বিন্যাস পল্লবগ্রাহী (superficial)। তাই বাস্তব নেই, যেহেতু প্রকৃত ভাষা বলেও কিছু নেই (যে-ভাষা হান্ট্কে খুঁজছেন) বরং আছে শুধু চিহ্নসর্বস্বতা।
(Little Magazine)
এই একইরকম কথা তো হুগো ফন হফমানস্তাল-ও বলেছিলেন তাঁর ‘Ein Brief’ গদ্যগ্রন্থে। সেখানে অগাস্ট, ১৬০৩ সালে লর্ড চান্দোস চিঠিতে জনৈক ফ্রান্সিস বেকনকে জানাচ্ছিলেন তাঁর ভাষা-ব্যবহারের অক্ষমতার কথা। চিঠিটি দেখে আমরা চান্দোসের বক্তব্য ঠিকই বুঝতে পারব, তবে এও বুঝতে পারব, যে তিনি শব্দকে বোধগম্য বিন্যাসের স্তরে পৌঁছাতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন, তাই ভাষার প্রচলিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ বাস্তবের প্রতিনিধিত্ব করা সফল হচ্ছে না। চান্দোস বেকনকে চিঠিতে লিখে জানাচ্ছেন তাঁর কথা বলা বা লেখায় কোনো পারম্পর্য (association) তিনি গড়ে তুলতে পারছেন না, ফলত তাঁর কোনো কথারই কোনো প্রসঙ্গক্রম (zusammenhang) তৈরি হচ্ছে না। অথচ তাঁর অনেক কথা আছে, সবকিছু তিনি বলতে চান। আসলে চান্দোসের সমস্যা নতুন কিছু তো নয়। এই জাতীয় অসুবিধেকে রোমান য়াকোবসন বলেছিলেন “contiguity disorder” বা “লগ্নবিক্ষোভ”, যার সংজ্ঞাস্বরূপ য়াকোবসন বলেছেন:
“It is a damage to the ability to combine and integrate elements into a proper context on the horizontal or syntagmatic level. The result is a fragmentation of elements with the possibility of disintegration, chaos and loss of meaning.”
এই ‘disorder’-এর শিকার হান্ট্কের কাসপার চরিত্রটিও। জনশ্রুতি আছে, ১৮২৮-এর ন্যুরেমবার্গে হঠাৎ এক যুবকের দেখা মেলে যে জানত না কোন জিনিসকে কী বলা হয়, এমনকী সে এ-ও জানত না যে মানুষকে ‘মানুষ’ বলা হয়ে থাকে। এহেন কাসপার আস্তে-আস্তে ভাষার ব্যবহার শেখে এবং এর পাঁচ বছর পরেই রহস্যজনকভাবে অজ্ঞাতকারণে মারা যায়। হান্ট্কে এই জনশ্রুতিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে লেখেন ‘কাসপার’ নাটকটি।
নাটককে non-representational বা অপ্রতিনিধিত্বমূলক করে তোলার পক্ষপাতী হান্ট্কে রূপক ব্যবহার করলেও নাটকে উপমা ব্যবহারের ঘোর বিরোধী তিনি। এখানেই হান্ট্কে, বেকেট বা ইওনেস্কোর থেকে পৃথক মেরুতে অবস্থান করেন। এই পৃথকতা ওঁর ‘Prophecy’ (১৯৬৬) নাটকটি ‘দেখলে’ আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। (Little Magazine)
‘Steers will bellow like steers.’
‘The average citizen will act like average citizen.’
‘Gary Cooper will walk like Gary Cooper.’
নাটকের এই অংশটি দেখে কারুর মনে পড়তেই পারে ‘মারা/সাদ’ খ্যাত নাটককার পিটার উলরিখ ওয়েইশের অপর একটি নাটক ‘The Song of the Lusitanian Bogey’ (১৯৬৭)-এর কথা যেখানে একজন ‘সামাজিক মানুষ’ ক্রমাগত বলছে:
“I have a steady work.
I have a regular income.
I have always paid my taxes on time.
I go regularly to church service.”
বাঙালির অবশ্য ফোরম্যানেরও কয়েক বছর আগেই এমন নাটক দেখা হয়ে গিয়েছিল যখন ১৯৬৩ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘কণ্ঠনালিতে সূর্য’ কলকাতায় প্রথম মঞ্চায়িত হয়।
(Little Magazine) তাহলে ‘সামাজিক মানুষ’ কে? যার ভাষা সুসংহত এবং যার ভাষার সংহতিই তার জীবনকে লগ্নতা দিয়েছে। যে-মানুষের ভাষা সংহত নয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তার অস্তিত্ব ছন্নছাড়া (patternless)। তেমন মানুষের এ-পৃথিবীর বৌদ্ধিক প্রপঞ্চে স্থান না থাকতেই পারে তবে হান্ট্কের থিয়েটারের ‘বাস্তবরহিত’ মঞ্চের শব্দনির্মিত ব্রহ্মস্থাপত্যে তারা সমোত্তীর্ণ। অনেকটা যেন রিচার্ড ফোরম্যানের অস্তিবাদী ইতিহাসবিধৃত থিয়েটারের (Ontological Historical Theatre) মতো। সংলাপহীন, দ্বিরালাপহীন, চরিত্রবিহীন, দৃশ্যরহিত কথনের (narration) পারফরমেন্স। তফাত একটাই: হান্ট্কের লক্ষ্য ভাষার আ(য়)ত্তীকরণ, ফোরম্যানের উদ্দেশ্য জ্ঞানের স্বরূপকে (nature of episteme) বোঝা। বাঙালির অবশ্য ফোরম্যানেরও কয়েক বছর আগেই এমন নাটক দেখা হয়ে গিয়েছিল যখন ১৯৬৩ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘কণ্ঠনালিতে সূর্য’ কলকাতায় প্রথম মঞ্চায়িত হয়। (Little Magazine)
বাস্তবকে উপমায় সীমায়িত করার কট্টর বিরোধী হান্ট্কে নানান সাক্ষাৎকারে একাধিকবার বলেছেন “Theatre represents nothing”। এই কথা শুনে অনেকেই হয়তো হান্ট্কে আর বের্টোল্ট ব্রেশ্টের নাট্যদর্শনের মধ্যে তুলনা খুঁজতে উদ্যত হবেন, তবে যথাযথ পাঠ বলে দেবে হান্ট্কে ও ব্রেশ্টের থিয়েটার বিশেষ একটি বিন্দুতে এসে পরস্পরের থেকে অনেকখানি দূরে সরে যায়। ব্রেশ্ট তাঁর থিয়েটারকে যতই অপ্রতিনিধিত্বমূলক করুন-না-কেন, তাঁর নাটকেও কিন্তু ঘুরে-ফিরে ‘দৃশ্য’ই থাকত, কিন্তু হান্ট্কের নাটকেরা তো “spectacles without pictures”। তাই ব্রেশ্ট আর হান্ট্কের মধ্যে তুলনা যদি করতেই হয়, তাহলে তা মূলত হবে দৃশ্য আর শব্দের তুলনা। ব্রেশ্ট যদি দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, “We will show you” (‘The Measures Taken’), তবে হান্ট্কে বলবেন “We will tell you” (‘Publikumsbeschimpfung’)।
(Little Magazine)
শব্দ নিয়ে খেলার ছলে আমরা কোনো এক ‘actor’-এর মুখে শুনছি “Aus-Schwitzen” শব্দটি, জার্মান ভাষায় যার অর্থ ‘ঘর্মাক্ত হওয়া’।
ব্রেশ্ট এবং নিজের থিয়েটারের মধ্যে তফাত যে শুধু আঙ্গিকেই নয় বরং নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নেও তা ‘ব্রেশ্ট, নাটক, মঞ্চ, বিক্ষোভ’ প্রবন্ধে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন পেটার হান্ট্কে: “Unlike Brecht, I do not aim to bring any paradigm shift, or, at least, change in society with my theatre.” দায়মুক্ত নাটক-লিখিয়ে হান্ট্কে কিন্তু তাঁর ‘অভিনেতা’দের (চরিত্র নয়) সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ভাষার সংহতি, লগ্নতা, পারম্পর্যকেও বিপন্ন করে তোলেন আর এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা। কারেল চাপেক-এর ছোটোগল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত ওঁর ‘Calling for Help’ (১৯৬৭) নাটকটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেখানে সব ‘অভিনেতা’রা একজোট হয়ে “Help” (জার্মান “Hilfe”) শব্দটিকে খুঁজছে কিন্তু শব্দটিকে খুঁজে পেতে তাদের “Help” (সাহায্য) প্রয়োজন। যেই তারা “Help” শব্দটিকে খুঁজে পেয়ে গেল, তাদের আর ‘help’-এর প্রয়োজন পড়ল না। শব্দ নিয়ে এই মজার খেলা তাত্ত্বিক মোড় নেয় যখন আমরা জানতে পারি জার্মান মূল শব্দ ‘Hilfe’-এর একটি অর্থ ‘বিকল্প’-ও। অর্থাৎ বিকল্পেরও বিকল্প আছে। আর-একটু সহজ করে বললে সব বিকল্পই অন্য কোনো-না-কোনো বিকল্পের বিকল্প। তবে এই প্রতিটা বিকল্পই বাঁধা আছে এক অজ্ঞেয় পারম্পর্যসূত্রে, যা খানিকটা মজার ছলেই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন হান্ট্কে তাঁর ‘Quodlibet’ (১৯৬৯) নাটকে। শব্দ নিয়ে খেলার ছলে আমরা কোনো এক ‘actor’-এর মুখে শুনছি “Aus-Schwitzen” শব্দটি, জার্মান ভাষায় যার অর্থ ‘ঘর্মাক্ত হওয়া’। কিন্তু এ-কথা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারব না যে শব্দটি শোনামাত্র আমাদের অধিকাংশেরই আউশভিৎস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথাই সবার আগে মনে পড়ে। এভাবেই হান্ট্কে বিস্মরণযোগ্য স্মৃতিকে মঞ্চে সরাসরি না দেখিয়েও, সরাসরি না উল্লেখ করেও খুব সচেতনভাবে উপস্থিত আর অনুপস্থিত শব্দের শ্রাব্যলগ্নতার পারম্পর্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন। (Little Magazine)
অগোছালো এই বিন্যাসই আমাদের চেতনা যা ভাষার অতীত, ভাষার ভবিষ্যৎ এবং এই দুইয়ের মেরুমৈত্রী সাধন হয় সেই ভাষায় যা একমাত্র সাকার, একমাত্র বর্তমান।
প্রথম যে-নাটকটির কারণে হান্ট্কে আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন সেই ‘Offending the Audience’ (১৯৬৬)-এ হান্ট্কে দর্শকের উদ্দেশে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সুদীর্ঘ এক ঘুম থেকে জাগাতে এসেছেন তিনি, দিতে এসেছেন তীব্র ধাক্কা। ১৯৭০-এর লন্ডনে তাঁর নাটকের একজন ‘অভিনেতা’ মঞ্চের সামনে এসে দর্শকের দিকে তাকিয়ে বলছে:
“You wax figures. You impersonators. You bad-hats. You troupers. You tear-jerkers. You foul-mouths. You sell-outs. You deadbeats. You phonies…”
পেটার হান্ট্কে বৃদ্ধ হয়েছেন। আরও প্রাসঙ্গিক হয়েছে তাঁর নাটকের ভর্ৎসনা। তবে সে-ভর্ৎসনাও অগোছালো, খাপছাড়া, অপরিকল্পিত এবং প্রত্যেকটি ভর্ৎসনাই অন্য কোনো ভর্ৎসনার বিকল্প এবং তার সঙ্গে পারম্পর্যসূত্রে কোনো এক অসীমের বিন্যাসে আবদ্ধ।
(Little Magazine) অগোছালো এই বিন্যাসই আমাদের চেতনা যা ভাষার অতীত, ভাষার ভবিষ্যৎ এবং এই দুইয়ের মেরুমৈত্রী সাধন হয় সেই ভাষায় যা একমাত্র সাকার, একমাত্র বর্তমান। তবে ভাষা সমগ্র চেতনা নয়, বরং সমগ্রের অপ্রতিনিধিত্বমূলক (Non-representional) খণ্ডবিশেষ, তাই তার বিন্যাস অবিচল নয়, অবিঘ্নিত নয়। ভাষাকে তার স্বাভাবিকতম অবিন্যাসের অসহায়তায় তুলে ধরার এরকম একটি প্রয়াস আমরা বাদল সরকারের ‘ভোমা’-তেও লক্ষ করেছি যেখানে অসংলগ্ন, অসংগত শব্দগুলিও চেতনায় হঠাৎ স্থগনের পর নতুন এক অর্থবহতা খুঁজে পায়। সেখানেও আমরা দেখি ক্রমব্যাহত প্রস্তরস্রোতের মতো থমকানো ভাষার গতায়ত, যা বয়ে যেতে যেতে ছিটকে আসে অস্তিত্বের কেন্দ্রকণার দিকে আর সঙ্গে-সঙ্গে উন্মীলিত হয় ভাষার অন্তর্নিহিত বৈকল্যের সম্ভাবনা। বোধহয় সেই কারণেই অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেছিলেন, “ভাষা সবচেয়ে বেশি মানবিক এবং সম্ভাবনাময় যখন ভাষার বৈকল্য প্রকট”। (Little Magazine)
অগোছালো এই বিন্যাসই আমাদের চেতনা যা ভাষার অতীত, ভাষার ভবিষ্যৎ এবং এই দুইয়ের মেরুমৈত্রী সাধন হয় সেই ভাষায় যা একমাত্র সাকার, একমাত্র বর্তমান।
হান্ট্কের শব্দনির্ভর নাটকগুলি যেন এক-একটি কবিতা, যাদের ‘দেখা’র চেয়ে ‘পড়া’ আশু প্রয়োজন। হান্ট্কের থিয়েটার যতখানি অভিনেতার, ততখানিই দর্শকের। এই থিয়েটার প্রশ্ন করার থিয়েটার। আমরা তাই বিব্রত হব, সন্দিহান হব আর বলব:
“চতুর্দিকের অন্ধকার ভরা তছনছ
মানুষের কান্নার মুহূর্ত
হাতপায়ের গিঁটে আটকে থাকে…
ঢেউয়ের ঘষায় জ্বলে
আমরা কতক্ষণ এই থমকানো রক্তের কেন্দ্রে ভাসব।”
(‘এখন’, চিন্ময় গুহ)
(Little Magazine)
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।