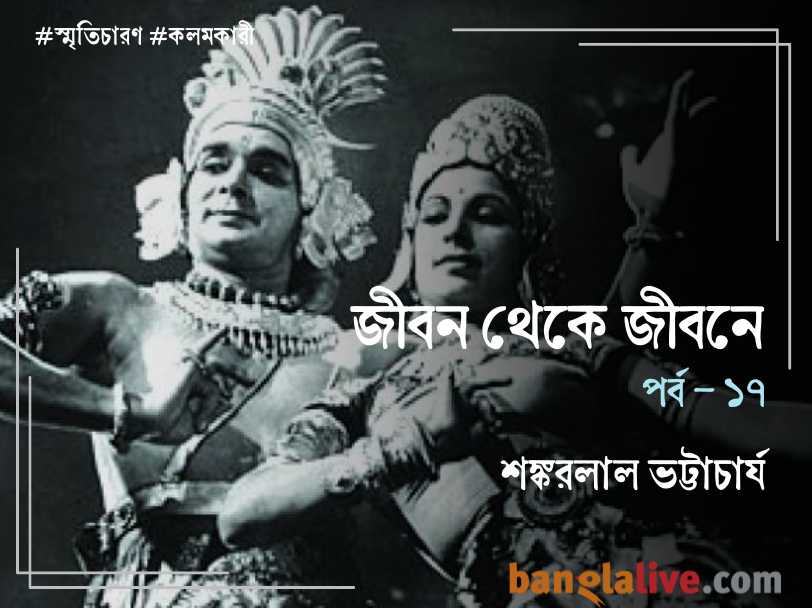আগের পর্ব পড়তে: [১] , [২], [৩], [৪], [৫], [৬], [৭], [৮] , [৯], [১০], [১১], [১২], [১৩] [১৪][১৫][১৬]
লন্ডনে(London) রবিশঙ্করের(Ravi Shankar) সঙ্গে ‘রাগ-অনুরাগ’-এর কাজ করতে করতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেল যা জীবনস্মৃতি হয়ে থেকে গেল। যা আগেও লিখেছি পত্র-পত্রিকায় স্মরণ, সংবাদ কিংবা সাক্ষাৎকার হিসেবে, কিন্তু এইবার আত্মকথার উজ্জ্বল স্মৃতি। স্মরণ বলতে রবুদার দাদা উদয়শঙ্করের প্রয়াণ ও সেই দাদাকে নিয়ে রবুদার অপূর্ব স্মৃতিচারণ ‘আমার দাদা’, যা আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় বেরোল খবর হিসেবে মৃত্যুর পরদিন! কী করে, কী ভাবে সে-কথায় একটু পরে আসছি।
সংবাদ নাকি আশ্চর্য সংবাদ বলব, তখনকার বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলির(Muhammad Ali) এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়ে ফেলা লন্ডনে। সেই ইন্টারভিউ দু’দিন ধরে বেরিয়েছিল আনন্দবাজারে। তদবধি কোনও ভারতীয় দূরস্থান, এশিয়ার কোনও সাংবাদিক আলির সাক্ষাৎকার জোগাড় করে উঠতে পারেননি। রবিশঙ্কর নিজেও খুবই অবাক হয়েছিলেন আমি এটা কী ভাবে করে ফেলেছিলাম শুনে।
আশ্চর্য সংবাদটি হল তখনকার বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলির এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়ে ফেলা লন্ডনে। সেই ইন্টারভিউ দু’দিন ধরে বেরিয়েছিল আনন্দবাজারে। তদবধি কোনও ভারতীয় দূরস্থান, এশিয়ার কোনও সাংবাদিক আলির সাক্ষাৎকার জোগাড় করে উঠতে পারেননি।
তৃতীয়টিও সাক্ষাৎকার, বিশ্বের সর্বকালের এক সেরা বেহালা শিল্পী ইহুদি মেনুহিনের সাক্ষাৎকার। মহম্মদ আলির মতো এই ইন্টারভিউ টেপ রেকর্ড করা, অথচ অর্ধশতাব্দী কাল পরেও ওঁদের প্রতিটি উচ্চারণ, অভিব্যক্তি ও ধ্বনি আমার কানে ও মনে বাঁধা ভালোবেসে ধরে রাখা কোনও গানের মতো।
সবচেয়ে করুণ ঘটনাটা দিয়েই শুরু করি। উদয়শঙ্করের মহাপ্রয়াণ। একদিন ‘রাগ-অনুরাগ’ রেকর্ডিং-এর জন্য রবুদার চেলসি ক্লয়েস্টার্ন হোটেলে গিয়ে দেখলাম ওঁর মুখ ভার। শরীরটাও অসুস্থ। কমলাদি বললেন, কলকাতা থেকে খবর এসেছে দাদা উদয়শঙ্করজি মরণাপন্ন। রবু ইজ ভেরি আপসেট।
রবুদাকে নিয়ে কমলাদি ও আমি ডাক্তারের বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, হঠাৎ আনন্দবাজারের লন্ডন অফিস থেকে ফোন। অফিসের বস তারাপদ বসু জানালেন, উদয়শঙ্কর যে-কোনও মুহুর্তে এক্সপায়ার করতে পারেন। অভীকবাবু চান যে আমি যেন ওঁর দাদার ওপর রবিশঙ্করের একটা লেখা আর আলাদাভাবে আমার একটা লেখা টেলেকসে পাঠাই।
ডাক্তারের ওখান থেকে ফেরার পর রবুদাকে বললাম, আপনি কি এখন লিখবেন? উনি বললেন, তুমি খুব ক্লান্ত। বাড়ি যাও। আমি সন্ধেবেলা যা-হোক একটা লিখে ফেলব। কাল খুব তাড়াতাড়ি চলে এসো এখানে।

সেদিন রাতে রবুদা আর উদয়শঙ্করের চিন্তায় ঘুম মোটেই এল না। পরদিন স্নানটান না করেই রওনা হলাম। গিয়ে দেখি রবুদা তাঁর তৈরি লেখা টেবিলে রেখে বসে আছেন। আমায় বললেন, বানান-টানানগুলো একটু দেখে দাও। আর দেখো লেখাটা কিছু দাঁড়াল কী না। আমি লেখাটার প্রথম বাক্য পড়তেই চমকে উঠলাম। কী আধুনিক! সাংবাদিক স্টাইল! শুরু করেছেন এই বলে ‘দাদার কথা আর কী বলব! উনি যে আমার কাছে কী ছিলেন তা বুঝিয়ে বলার অবস্থা বা ক্ষমতা আমার নেই।’ কয়েকটা বানান ঠিক করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় ছিল না আমার। লেখাটা হাতে নিয়েই আনন্দবাজারের অফিসে ছুটলাম। ঠিক তখনই খবর এল যে উদয়শঙ্কর চলে গেছেন।
শুরু হল আমাদের লড়াই, সময়ের দৌড়ের বিরুদ্ধে। লন্ডন অফিসের অশোকদা(গুপ্ত)বললেন, শঙ্কর, তোমার লেখাটাও লিখে ফেলো ঝটপট। আর লাঞ্চ সেরে নাও। তারপর চারটের সময় বেরিয়ে আমরা টেলেকসে বসব।
পারতপক্ষে আধঘণ্টায় আমার দীর্ঘ প্রবন্ধটা শেষ করি। রবিশঙ্করের লেখাটাও ছিল দীর্ঘ। অশোকদা আর আমি ঠিক চারটেতে টেমস নদীর ধারে, কাগজপাড়ার এক প্রান্তের ইন্টারন্যাশনাল টেলেকস সার্ভিসের অফিসে চড়াও হলাম। মিনিট দশেক টাইপ মেশিন খালি পেলাম এবং সেই মুহূর্ত থেকে বাংলা লেখা আমি রোমান অক্ষরে বানান করে পড়তে থাকলাম। যা দাঁড়ায় এরকম: Dadar katha aar ki bolbo! Uni je aamar kachhe ki chhilen… ইত্যাদি ইত্যাদি।
অশোকদা কোনও দিকে না তাকিয়ে চিতা বাঘের দৌড়ের গতিতে মেশিনে টাইপ করতে থাকলেন। দুজনকেই আমাদের সেদিন ভূতে ভর করেছিল। পাশে কর্মরত বিদেশি সাংবাদিকরা কেবলই টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল। হয়তো ভাবছিল, এ দুজনের হল কী! দেশে কি যুদ্ধ লাগল?
আর অশোকদা কোনও দিকে না তাকিয়ে চিতা বাঘের দৌড়ের গতিতে মেশিনে টাইপ করতে থাকলেন। দুজনকেই আমাদের সেদিন ভূতে ভর করেছিল। পাশে কর্মরত বিদেশি সাংবাদিকরা কেবলই টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল। হয়তো ভাবছিল, এ দুজনের হল কী! দেশে কি যুদ্ধ লাগল? যে- স্পিডে খবর লিখছে। নাকি ব্রিটিশ সরকার উল্টাল বলে। ওদের সেদিন বোঝানোর উপায় ছিল না, কত বড় একটা যুদ্ধে নেমেছিলাম আমরা। আমাদের গতির উপরেই নির্ভর করছিল পরদিন আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় উদয়শঙ্করের বিষয়ে রবিশঙ্করের লেখা বেরোবে কী বেরোবে না।
আমরা যে স্পিডে টাইপ করা পাতা জমা দিচ্ছিলাম টেলেকসে ধরানোর জন্য, তাতে রিসেপশনের মহিলাও কিছুটা অবাক হচ্ছিলেন। মাঝে একসময় অশোকদা বললেন, শঙ্কর, রবুদার লেখা ফিনিশড। এবার তোমারটা ধরব। তুমি এই ফাঁকে এক পাইট বিয়ার খেয়ে এসো। ততক্ষণ আমি নিজেই কাজটা এগিয়ে নিচ্ছি।
কোনোমতে এক পাইট টারটান বিয়ার খেয়ে ফিরে এসে দেখি অশোকদা একাই ঝড়ের বেগে লড়ে যাচ্ছেন। আমি বসে পড়া শুরু করতেই সেই স্পিড দ্বিগুণ হয়ে গেল। যখন শেষ কপি জমা দিলাম তখন ইংল্যান্ডের ঘড়িতে সন্ধে আটটা। অর্থাৎ কলকাতায় রাত দুটো। অশোকদা বললেন, শঙ্কর, দিস ইজ অ্যান অ্যাচিভমেন্ট, নাও লেটস সেলিব্রেট।
দুজন মিলে ফ্লিট স্ট্রিটের এক পাবে ঝাঁপ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সমানে বিয়ার টানলাম। ঘরে ফিরে দেখি সুভাষ আমার জন্য দামি দামি সব খাবার এনে সাজিয়ে বসে আছে। আমি খাবারগুলো দেখলাম, কিছু মুখে তুলতে পারলাম না। শ্রমে আর বিয়ারে আমার চোখ বুজে আসছে তখন। আমি স্যুট পরেই বিছানায় পড়ে ঘুমিয়ে গেলাম। আলির ইন্টারভিউয়ের মতন(যে-কথায় আসছি পরের পর্বে) উদয়শঙ্করের লেখাতেও ঝড় উঠেছিল কলকাতায়। সবাই অবাক হয়ে গেল, কী করে দিনের দিনে লন্ডন থেকে এত বড় লেখা এল রবিশঙ্করের কাছ থেকে? টাইম গ্যাপ বলে কি কোনও জিনিস নেই? আজকের ইন্টারনেটের যুগের মানুষের পক্ষে এই ব্যাপারটা বুঝে ওঠাও খুব সহজ হবে না।
দু’দিন পরে অভীকবাবু এবং অরূপের কাছ থেকে অভিনন্দনবার্তা জানিয়ে টেলিগ্রাম এল। আর তারাপদবাবুর কাছে এও জানলাম যে সপ্তাহ দেড়েকের মধ্যে অভীকবাবু সপরিবারে লন্ডন আসছেন।
(চলবে)
শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।