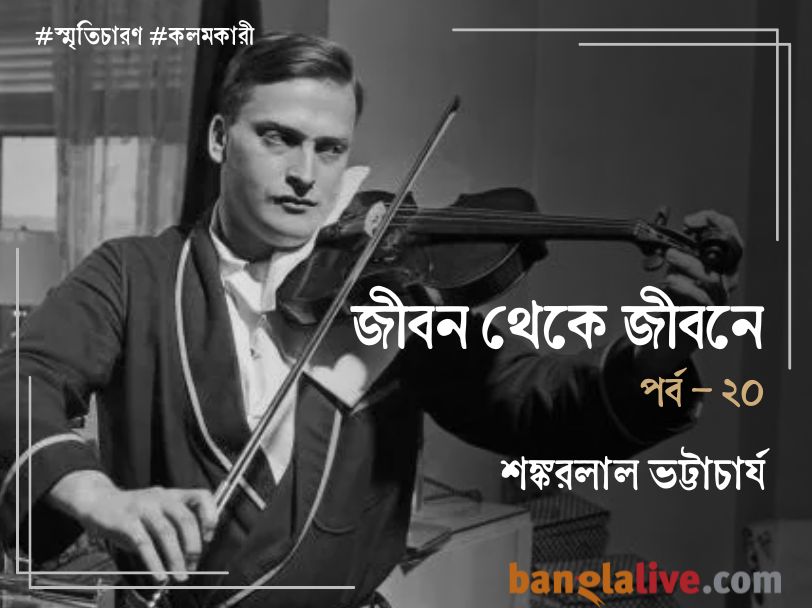যবেকার ঘটনা সেই থেকে মনের মধ্যে ঘোরে এই স্মৃতি, সুভাষ আর নিশীথদাকে (নিশীথ গাঙ্গুলি, পরে আসবে এঁর আরও প্রসঙ্গ) নিয়ে। নিশীথদার গাড়িতে করে লন্ডনের পশ এলাকা হাইগেট ভিলেজে ইহুদি মেনুহিনকে (Yehudi Menuhin) দেখতে যাওয়া। তীর্থে পৌঁছে দেবদর্শনের মতো ব্যাপার ছিল সেটা।
ঠিক তার আগের দিন ষোলো অক্টোবর সম্ভবত, আমি রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে মেনুহিনের কনসার্টে গিয়েছিলাম। অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তহবিল সংগ্রহের জন্য মহতী অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত ছিল। বিরতির আগে অবধি বেটোফেনের ‘ফিদেলিও’ বা ‘বন্দির গান’ সম্মেলক সংগীত কনডাক্ট করলেন মেনুহিন। বিরতির পরে এই মহান বেহালা শিল্পী বাজালেন বেটোফেন, বাখ এবং বার্তোক থেকে। কিন্তু সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা ঘটালেন ঠিক বিরতির সময়ে। স্টেজ ছেড়ে চলে গিয়ে ফের স্টেজে এসে ঘোষণা করলেন, এইমাত্র খবর এসেছে যে অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ বছরের নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেয়েছে। তখন সারা হল জুড়ে কর্নবিদারক হর্ষধ্বনি।

মেনুহিনকে আমার কথা বলেছিলেন রবিশঙ্কর। সাহেব খুশি হয়েই বলেছিলেন, তাহলে ওকে ঠিক তিনটের সময় কাল পাঠিয়ে দিয়ো। রবুদা আমাকে তাই বারবার স্মরণ করিয়েছিলেন, টাইমের যেন এতটুকু এদিক ওদিক না হয়। আমরাও তাই ভয়ে ভয়ে দুপুর একটাতেই রওনা দিয়েছিলাম। এবং দেখলাম যে সময়ের অনেক আগেই হাইগেটে পৌঁছে গেছি। কিন্তু বিলেতে টাইমের আগে পৌঁছেও বেল টেপা অভদ্রতা। তাই নিশীথদাকে বললাম ‘শুনেছি হাইগেট সিমেট্রিতে কার্ল মার্কসের কবর আছে, সেটা দেখতে চাই’। এতকাল লন্ডনে থেকেও নকশালপন্থী সুভাষের সেটা দেখা হয়নি। ফুটফুটে শীতশীত দুপুরে আমরা বহুক্ষণ কাটালাম নিপীড়িত মানুষের সবচেয়ে বড় প্রবক্তার সমাধিস্থলে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল ততটা শীতের কামড়ে নয় যতটা মার্কসের সমাধিফলক দর্শনে।
আমরা একটু পর পৌঁছে গেলাম মেনুহিনের বাড়িতে। খুব বনেদি রুচি ও চরিত্রের বাড়ি এবং তার আসবাবপত্র। মেনুহিন নিজে এই প্রবীণ বয়সে দেবদূতের মতন সুন্দর ও স্নিগ্ধ। আমি অজস্র প্রশ্ন মনে মনে তৈরি করে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় মনে পড়ে গেল আরও অনেক নতুন প্রশ্ন। মেনুহিন গভীর আগ্রহে ও স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে সে-সবের দীর্ঘ উত্তর দিলেন। ওঁর স্ট্রাডিভেরিয়াস বেহালা যন্ত্রটিকে নিয়েও বললেন। বেটোফেনের কম্পোজিশন, বাখ, বার্তোকের পিস বাজানো থেকে রবিশঙ্করের সঙ্গে ‘ওয়েস্ট গ্রিটস ইস্ট’ অ্যালবামে বাজানোর আনন্দের কথা বললেন। সবই এত সূক্ষ্ম ডিটেলে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতের ক্লাস নিচ্ছেন। আর এই বলতে বলতে থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তা তোমার ওয়েস্টার্ন ভায়োলিনে এত কৌতূহল হল কেন?’
বললাম, ‘বাবার কারণে। উনি সেভেন্টি এইটে আরপিএস- এর রেকর্ড চালিয়ে ফ্রিৎজ ক্রাইসলারের বেহালা শুনতেন’।
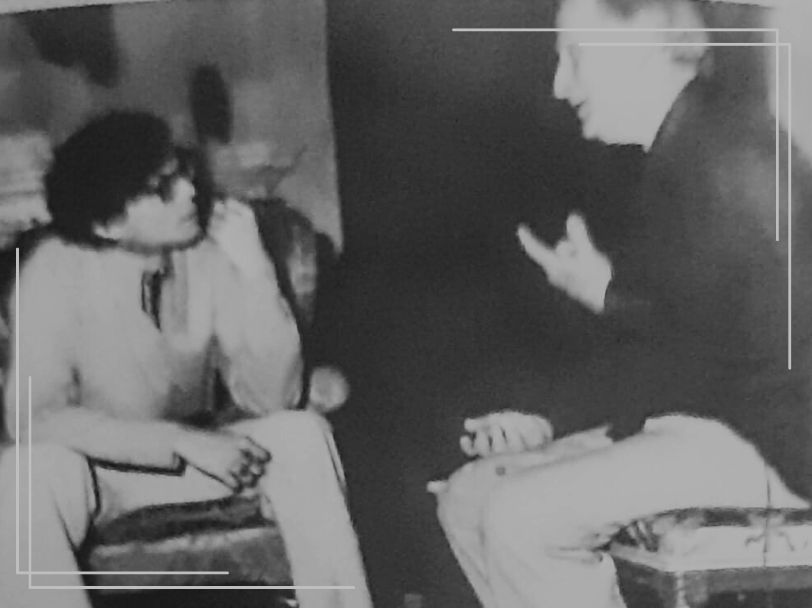
মেনুহিন রীতিমত চমকে গিয়ে বললেন, ‘ফ্রিৎজ ক্রাইসলার! তাহলে তো তোমার দারুণ শুরুয়াত হয়েছে পাশ্চাত্য সুরে’।
বললাম ভায়োলিনে আরও নেশা হল আপনার যন্ত্রে বার্তোক শুনে’।
মেনুহিন বললেন, ‘আর তোমাদের সংগীতে আমার কৌতূহল, নেশা যার প্রেম হল রাভির (রবিশঙ্কর) সঙ্গে বাজিয়ে, কাজ করে। কী শিল্পী একজন! ভারতীয় সংগীতের মোৎজার্ট’।
সেই দীর্ঘ আলাপের একটা ঝলক মাত্র এটা। অত সুন্দর ইন্টারভিউ আমি জীবনে বেশি করিনি। রবুদার মুখে শুনেছি মেনুহিনও আমার ইন্টারভিউয়ের ঢং ও প্রশ্নে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যা আমার জীবনের খুব বড় সন্মান, খুব বড় স্মৃতি।
এক সময়ে আমাদের চা খাওয়ালেন মেনুহিন। সুভাষ অনেক ছবি তুলল আমাদের। আমি শিল্পীর হাতে তুলে দিলাম ওঁরই জন্য আঁকা কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী অন্নদা মুন্সীর ছবি। মেনুহিন তো তাতে রীতিমত মুগ্ধ ও বিস্মিত। বললেন, ‘আমার বাজনা শুনেই আমাকে এত ভালবাসেন ভারতের একজন আর্টিস্ট! ইন্ডিয়ানজ আর রিয়েলি ফুল অফ লাভ’। আমি মেনুহিনের দুটো রেকর্ডে ওঁর সই করিয়ে নিলাম। সুভাষ যখন ওঁর রেকর্ডে সই করাচ্ছে, তখন ওঁর বিরাট কাঠের প্যানেল করা লাইব্রেরিতে চোখ গেল আমার। ঘরের পর ঘর শুধু বই। আর তারই এক কোণে শিল্পীর লেখা ও পড়ার টেবিল। চোখের সামনে র্যাক করে সেই সব বই রাখা যা উনি নিয়মিত পড়েন। সেখানে বাখ, বেটোফেন, মোৎজার্ট সংক্রান্ত বইয়ের পাশে জ্বলজ্বল করছে দেখলাম আমার জীবনের এক অতি প্রিয় বই। ক্রিস্টোফার ইশারউডের ‘রামকৃষ্ণ অ্যান্ড হিজ ডিসাইপলজ’।
বইটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘স্যর ডু ইউ রেগুলারলি রিড দিস বুক?’
আমাকে যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ করে বেহালা শিল্পের এক অবতার বললেন, ‘রিড? আই লিভ বাই ইট’। আমি তো ওটা পড়েই বাঁচি।
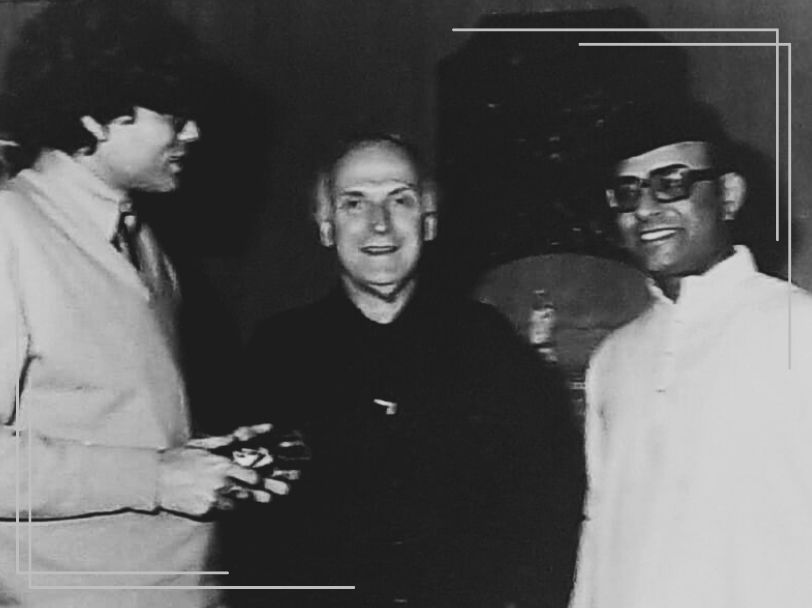
বাড়ির বাইরে এসে দেখি শিল্পীর জন্য যন্ত্রপাতি নিয়ে সদলবলে অপেক্ষা করছে ফরাসি টিভি ইউনিট। মেনুহিনের অপর একটা ডকুমেন্টারি তুলবে তখনই। অথচ দু- আড়াই ঘণ্টার সাক্ষাৎকারে সাহেব তার বিন্দুমাত্র আভাস আমাদের দেননি। এত বিস্মিত হয়েছিলাম তিনজনই আমরা যে বেশ কিছুক্ষণ কেউ মুখ খুলতে পারিনি। খুললাম যখন তখন শুধু এই কথাটাই ঘুরে ঘুরে আসছিল।
(চলবে)
শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।