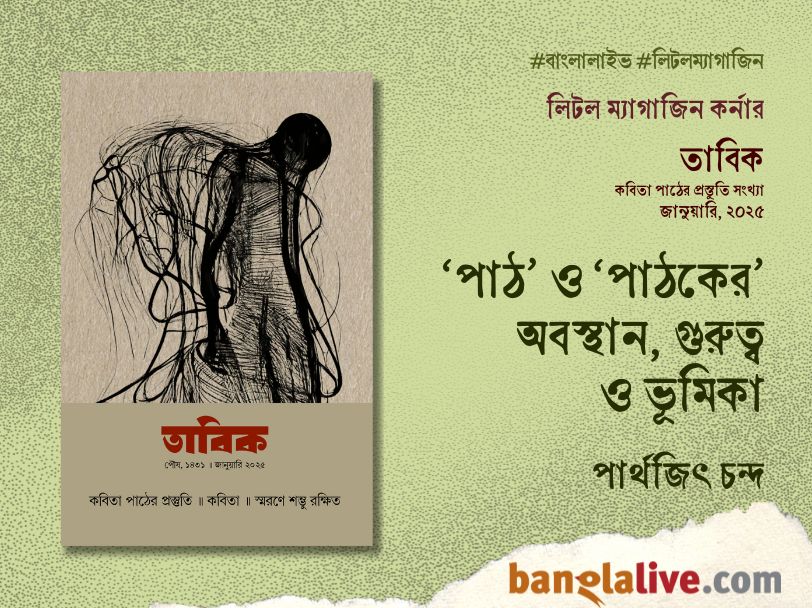(Little Magazine)
To organize a text. its author has to rely upon a series of codes that assign given contents to the expressions he uses. To make his text communicative the author has to assume that the ensemble of codes he relies upon is the same as that shared by his possible reader. The author has thus to foresee a model of the possible reader hereafter Model Reader supposedly able to deal interpretatively with the expressions in the same way as the author deals generatively with them. —The Role of the Reader, Umberto Eco
পাঠক ও লেখকের মধ্যে বিচিত্র সম্পর্ক ও তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উমবার্র্তে একো’র জটিল তত্ত্বের কাছে এসে ও তাকে গুরুত্ব-সহযোগে বিচার করার পর একপাশে সরিয়ে রেখে আপাতত হেমেন্দ্রলাল রায় নামে ক্ষণজন্মা, স্বল্পপরিচিত লেখকের লেখা একটি রূপকথার কাছে ফিরে যাওয়া যাক৷ লেখকের ‘জন্ম’ ও ‘মৃত্যু’-র সঙ্গে-সঙ্গে পাঠকের জন্ম, একটি কবিতাপাঠের প্রস্তুতি অথবা একটি শিল্পকর্মের ভেতর প্রবেশ করবার যে রহস্যময়, বহুমাত্রিক পদ্ধতি ক্রিয়া করে চলে সেটিকে রূপকের আড়ালে দেখে নেওয়া যাক ৷ (Little Magazine)
আরও পড়ুন: বিদুর: একটি কবিতা ও তার নির্মাণ- রাণা রায়চৌধুরী
পাঠক’-কে খেয়াল রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে এখানে হেমেন্দ্রলাল উমবার্র্তে একো’-র ‘সুপারম্যানের’ মতো কোনও বিষয়কে আশ্রয় করেননি ৷ তাঁর রাজপুত্র আক্ষরিক অর্থেই রাজপুত্র ৷ এবারে কাহিনির বিন্যাস লক্ষ করা যাক, রাজপুত্র হঠাৎ একদিন এক রাজকন্যার ছবি দেখেছিল ৷ ছবিটি দেখেই সে প্রেমে পড়ে যায় এবং প্রায় প্রতিজ্ঞা করে বসে যে ওই রাজকন্যাকেই সে বিবাহ করবে৷ কিন্তু, রাজকন্যা যে দেশে বাস করে সেখানকার নিয়ম জটিল; রাজকন্যা রাজ্যের বাইরে কারও গলায় মালা পরাতে পারবে না ৷ (Little Magazine)
নিটশে তাঁর ‘দাস স্পোক জরাথুষ্ট্র’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, Of all that is written I love only what a person hath written with his blood. Write with blood and thou wilt find that blood is spirit. It is no easy task to understand unfamiliar blood I hate the reading idlers.’
নিটশের এই কথাগুলির সঙ্গে ওই রূপকথার জগতের একটি সমান্তরাল পাঠ শুরু হতে পারে৷ রাজকন্যার ছবি দেখে তার প্রেমে উদ্বেল হয়ে ওঠা এবং দর্শনকারী’র (পাঠান্তরে‘পাঠক’) মধ্যে তৈরি হওয়া তীব্র অভিঘাত ও চিন্তাস্রোতের একমুখীনতার কথা স্মরণে রেখেও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে এখনও পর্যন্ত লেখক (রাজকন্যা) এবং পাঠক (রাজপুত্র) একে অপরের কাছে ‘অপরিচিত’, ‘্যনফ্যামিলিয়র ব্লাড’৷ কিন্তু, নিটশে’র তীব্র অপছন্দের idlers’ এর বিপরীতক্রমে এখানে তৈরি হতে শুরু করেছে রাজপুত্রের (পাঠকের) ‘সক্রিয়তা’৷ এই সক্রিয়তাই তাকে ছুটিয়ে মারবে এবং পেরিয়ে যেতে সাহায্য করবে সমুদ্র ও পাহাড়৷ কবিতার অন্দরমহলে প্রবেশ করবার জন্য পাঠকের এই সক্রিয়তা ভীষণভাবে প্রয়োজন৷ অপরিহার্য শর্তও বলা যায় ৷ (Little Magazine)
এরপর হেমেন্দ্রলালের কাহিনিতে তৈরি হয়েছিল সুতীব্র গতি ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রহরের দীর্ঘ ধারাপাত৷ অজানা অন্ধকারের মধ্যে নিঃসংশয়ে মৃত্যু-সম্ভাবনা থেকে শুরু করে রাজপুত্রের হাতে রাজকন্যার প্রাণ-বেঁচে যাওয়ার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে পাঠক ও লেখকের সম্ভাব্য সম্পর্ক মিলেমিশে যায়৷ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে রাজকন্যার প্রাণ বাঁচানোর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে বা নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে লেখকের অস্তিত্ব ক্রমাগত মিশে গিয়ে পাঠক ধীরে-ধীরে লেখকের ‘অপর’-সত্তায় পরিণত হয়ে ওঠেন এবং এই পথে তিনি লেখকের সম্ভাব্য মৃত্যু প্রতিরোধ করবার মধ্যে দিয়ে নিজের মৃত্যু সম্ভাবনাটিকেও প্রলম্বিত করেন অথবা সেটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন ৷ (Little Magazine)
এই রূপকথাটিতে রাজপুত্রের বলা একটি কথার কাছে বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয়, ‘আমার প্রাণের চেয়ে তোমার প্রাণের দাম ঢের বেশি রাজকন্যা, তাইতো তোমাকে বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণের দিকে তাকাবারও আমার অবসর হয়নি!’
“এই রূপকথাটিতে রাজকন্যা ও রাজপুত্রের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক বিবাহে রূপ পাবার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় ঘাতক হয়ে উঠেছিল ‘পুরোহিত’”
কবিতার পাঠ-প্রস্তুতির প্রহরে একজন সৎ ও সমর্পিত পাঠকের মনে কি এই ধারণাই কাজ করে? টেক্সটের বা শিল্পবস্তুর কাছে দাঁড়িয়ে পাঠক কি অনুভব করেন ‘অভিন্নতা’? রাজপুত্র যেমন রাজকন্যার গলায় মালা দিয়ে তাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতে চায় তেমনই একজন পাঠক ও লেখক সংঘর্ষময় সম্পর্কের ভেতর দিয়ে একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হতে চান৷ কিন্তু, নানা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ‘ফ্যাক্টরস’ তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘনিয়ে তোলে ৷ এখানে প্রশ্ণ উঠতে পারে, রাজকন্যা ও রাজপুত্রের মধ্যে প্রণয়-সম্পর্কের আলোয় লেখক ও পাঠকের সম্পর্ক’-কে কি বিচার করা উচিত? আসলে ‘সংঘর্ষ’-ময় পরিস্থিতি যে সবসময় টেক্সটের মধ্যেই লুকিয়ে থাকবে বা প্রকট হয়ে থাকবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই৷ কারণ, লেখক ও পাঠকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বহুবিধ অবস্থানগত পার্থক্যের কারণেও সে সংঘর্ষ ঘনিয়ে উঠতে পারে৷ সেখানে লেখক ও পাঠকের দর্শন-প্রস্থানের মধ্যে নিহিত সংঘর্ষটিকেও মাথায় রাখা জরুরি৷ রাজকন্যার রাজত্বের যে নিয়ম, অর্থাৎ যে ফ্রেমের মধ্যে তার অবস্থান সেটিকে তছনছ করে তাকে নিয়ে যুগল-যাপনের প্রণোদনার সৃষ্টিও আবার এখান থেকেই ৷ (Little Magazine)
এই রূপকথাটিতে রাজকন্যা ও রাজপুত্রের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক বিবাহে রূপ পাবার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় ঘাতক হয়ে উঠেছিল ‘পুরোহিত’, ভাবতে অবাক লাগলেও এটিই সত্যি যে পাঠাভ্যাসের বা পাঠ-পরম্পরার ‘মৌলবাদ’ একটি স্থানের বা ‘স্টেটের’ রাজনৈতিক শক্তির থেকেও বেশি ক্ষমতা ধারণ করে থাকে৷ ফলে, সব প্রতিবন্ধকতা ও বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করেও শেষ পর্যন্ত চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওই পাঠাভ্যাসের ‘পরম্পরা’৷ এই ঘাতক পরম্পরাকে প্রতিক্ষেত্রে অতিক্রম করে যেতে হয় ব্যক্তিপাঠককে৷ বলা ভাল, প্রত্যেক ব্যক্তিপাঠকের সফর শুরুই হয়ে থাকে এই তথাকথিত ‘পরম্পরা’কে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ছোট্ট একটি পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে ৷ (Little Magazine)
কেন পাঠকের প্রস্তুতি নিয়ে লেখার সময় এই রূপকথাটির কাছে আমি বারবার ফিরে আসছি তার সপক্ষে আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে৷ প্রস্তুতির যে ধারা মেনে পাঠকের জন্ম সে ধারা মেনে পাঠকের ও লেখকের অন্তিম পরিণতি কী হতে পারে সে নিয়ে সঙ্গত প্রশ্ণের অবতারণা করতেই পারেন কেউ-কেউ৷ এই রূপকথায় রাজকুমারী ওই পুরোহিতের, (যে কিনা দেশের রাজার থেকেও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন), ছোড়া ঘাতক বরফের টুকরোর আঘাতে সংজ্ঞা হারায়৷ রূপকথার রীতি মেনেই রাজকন্যার দেহ শূন্যে মিলিয়ে গেল, বিষয়টির ‘শেষ’ কিন্তু এখানে ঘটল না৷ আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম রাজকুমার তলোয়ারের কোপে সে-পুরোহিতের মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দিল৷ ফলে, অবসান ঘটল একটি পরম্পরাকে নিয়ন্ত্রণ করার ঘাতক শক্তির৷ (Little Magazine)
“রাজকন্যাও এক অর্থে রাজপুত্রের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিল এবং সে উৎসর্গের পিছনে শুধুমাত্র নিজেকে ‘উৎসর্গ করার আনন্দ’ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ৷”
এভাবেই কি পাঠকের হাত ধরে প্রত্যেক ‘প্রথমবার’ পরম্পরার অবসান সূচিত হয়ে থাকে? এভাবেই কি ব্যক্তি-পাঠক আসলে প্রতিক্ষেত্রেই ‘রেবেল’ ও প্রথাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার কারিগর?
রাজকন্যার দেহ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল, এবং রাজপুত্র ও রাজকন্যার আবার দেখা হয়েছিল৷ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল রাজকুমার’ও ৷ রাজকন্যাও এক অর্থে রাজপুত্রের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিল এবং সে উৎসর্গের পিছনে শুধুমাত্র নিজেকে ‘উৎসর্গ করার আনন্দ’ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ৷ এই ‘আনন্দ’ শব্দটির সঙ্গে যে চরম তামস প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকতে পারে সেটিও স্বীকার করে নেওয়া দরকার। (Little Magazine)
রাজপুত্র রক্তমাংসের রাজকন্যার পরিবর্তে পেয়েছিল রাজকন্যারূপী ফুল৷ সেটিকেই সে মরুপ্রান্তর পেরিয়ে নিয়ে এসেছিল নিজের দেশে৷ মূলশুদ্ধ ফুলটিকে স্থাপন করেছিল শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চায়৷ বরফের দেশের রাজকন্যা রূপান্তরিত হয়েছিল শ্বেতপদ্মে৷ চিহ্ণ ও সংকেতের ডিকোডিং পদ্ধতি বারবার সম্পন্ন হবার পর সম্পূর্ণ এক নতুন অস্তিত্ব লাভ করেছিল রাজকন্যা (এখানে মূল ‘শিল্পবস্তু’)৷ রাজকন্যার এই নতুন রূপটির বিষয়ে কাহিনির শুরুতে অবহিত ছিল না রাজপুত্র৷ সংঘর্ষময় পরিস্থিতির শেষে পাঠকের প্রাপ্তি এবং পাঠ্যবস্তুর পরিণতি আমাদের অবাক করতে পারে, এমনকি স্বস্তি দিতে পারে৷ কিন্তু, স্বীকার করতেই হবে এই পরিণতি সম্পূর্ণরূপে লেখক ও পাঠকের মধ্যে লক্ষ-সম্ভাবনার একটি প্রকাশ৷ আরও হাজারো পরিণতি অপেক্ষা করেছিল বা করে থাকতে পারে৷ তার প্রতিটি’ই একই রকমভাবে সত্য ও সম্ভবপর৷ এক্ষেত্রে একটি বিষয়ই শুধুমাত্র ধ্রুবক- লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংঘর্ষময় সম্পর্ক ছাড়া কোনও একটি পরিণতিও ‘পরিণতি’ পেতে পারে না৷ সত্যি-সত্যিই ‘্যনফ্যামিলিয়র ব্লাডের’ একে অপরের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া এতটাই জটিল ও গূঢ় ৷ (Little Magazine)
আরও পড়ুন: বিদুর: মিথ মিথ্যার নিকটাত্মীয়- কমলকুমার দত্ত
দুই
ব্যক্তি-পাঠকের প্রতিটি পাঠই ‘প্রথম পাঠ’, এমনকি কোনও টেক্সট দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবার পঠিত হলেও প্রতিবারই সেটি ‘প্রথম’ হিসাবে বিবেচিত হয় আমার কাছে৷ কারণ, প্রতিটি পাঠে শিল্প ও তার রহস্যের নতুন-নতুন মাত্রা যুক্ত না-হলে তাকে আমি ‘পাঠ’ হিসাবে গণ্য করতে নারাজ৷ ফলে, প্রতিটি পাঠের ক্ষেত্রে পাঠ-প্রস্তুতি পাঠকের ক্ষেত্রে ঘটতেই হবে, অনিবার্য এই প্রক্রিয়া ৷ (Little Magazine)
ধরা যাক, ব্যক্তি-পাঠক, যিনি আমার কাছে আদর্শ পাঠকের ভূমিকা পালন করবেন বা সেই পাঠক ‘ব্যক্তি-আমি’— এ-মুহূর্তে এসে বসেছি উৎপলকুমার বসু’-র ‘যুদ্ধ বিষয়ে কয়েকটি ভগ্ণাংশ’ নামে কবিতার দ্বিতীয় অংশে৷ পাঠ-পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই কবিতাটির ভিতর প্রবেশ করার সময় প্রতিটি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা রহস্য ও গূঢ়-সংকেতের বিষয়ে গোয়েন্দার মতো সতর্ক থাকা দরকার ৷ (Little Magazine)
উৎপলকুমার বসু’র কবিতাটি আবার পড়তে গিয়ে (যা কিনা আমার কাছে প্রথম-পাঠের নামান্তর) পাচ্ছি, ‘আমরা ভুল করেই এবারকার ছুটিতে চলে গিয়েছিলাম ব্যবিলনের মায়াবী নিসর্গে, ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিসের সেই দোয়াবে, যেখানকার ইডেন গার্ডেনে একটি আপেল এগিয়ে দিয়ে আদমের মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল ঈভ৷’ (Little Magazine)
কবিতাটির পূর্বপাঠে যে ‘আমি’ ব্যক্তিপাঠক তার কাছে ধরা দেয়নি, ‘ভুল করেই’ শব্দ দুটির অভিঘাত৷ শব্দ দুটির প্রবল অভিঘাত অনুভব করতে শুরু করলাম এই মাত্র এবং কবিতাটির ভিন্ন এক সফর শুরু হল আমার কাছে৷ ‘ভুল করেই’, অর্থাৎ এই দৃশ্য দেখার কথা ছিল না লেখকের, নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছেন তিনি৷ শব্দটির মধ্যে আধুনিকতার অনুচ্চ ইশারা রয়েছে, রয়েছে ‘ক্যাজুয়াল’ হত্যা ও হত্যা-পদ্ধতির ইশারা; সেটি যদিও স্পষ্ট হয়ে উঠবে কবিতাটির পরবর্তী অংশে ৷ (Little Magazine)
“মানুষ কি আদপে তার সৃষ্টি থেকেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রাণী, যে প্রাণী তার সমস্ত জ্ঞান ও চেতনার স্ফূরণ নিয়ে ছুটে চলেছে নিশ্চিত অবলুপ্তির দিকে?”
কবিতাটিতে মহাপ্লাবনের মিথ ব্যবহার করেছিলেন উৎপলকুমার৷ নোয়ার নৌকা এবং দেড়শো দিন প্লাবনের পর তার পাহাড়চূড়া স্পর্শ করার বিষয়টি ধরা দিয়েছে, ‘দেড়শো দিন প্লাবন পরিক্রমার পর যে-পাহাড়ে তিনি নোঙর করেছিলেন তার চূড়া থেকে দেখলাম সেই সমস্ত তেলখনি যাদের সৌজন্যে আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটছে৷’ এরপরেই কবিতাটির উল্লম্ফন শুরু হয়েছিল, উৎপলকুমার লিখছেন, ‘আবু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উপেক্ষা করে এখনও অক্ষুণ্ণ্ দাঁড়িয়ে আছে মর্মর-প্লাস্টারে গড়া একটা দম্পতিঃ নারীর চোখে চশমা, পুরুষটির মুখাবয়ব ছেয়ে গ্যাস-মুখোশ— তখনই কি তার ভয় ছিল যুদ্ধে ব্যবহৃত বিষবাষ্পে পুরুষজাতি একদিন নির্বংশ হয়ে যেতে পারে?’ (Little Magazine)
‘মর্মর’ শব্দটির ভেতর যেমন রয়েছে পেলব এবং কিছুটা লিরিক্যাল ইশারা (যা কিনা আবার দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পাঠ-পদ্ধতি এবং পাঠের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া চিহ্ণ ও তার একমাত্রিক ডিকোডিং পদ্ধতিকে সূচিত করে) তেমনই আমাদের সচকিত হয়ে আবিষ্কার করতে হবে যে এই শব্দটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে মার্বেল-পাথরের ইশারাও৷ সেই প্লাস্টার-দম্পতির মূর্তি এবং তাদের চশমা ও গ্যাস-মুখোশ মনে করিয়ে দিচ্ছে সমকালীন যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও বিষবাষ্প ব্যবহারের কথা৷ প্রতিরক্ষার এই প্রাচীন পদ্ধতি বা পদ্ধতি-সম্ভাবনা কি আসলে মানুষের ভেতর লুকিয়ে থাকা গভীর-গভীর বিপন্নতা, জিঘাংসা এবং আত্মহত্যাকামী রূপটিকেই প্রকাশ করছে? মানুষ কি আদপে তার সৃষ্টি থেকেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রাণী, যে প্রাণী তার সমস্ত জ্ঞান ও চেতনার স্ফূরণ নিয়ে ছুটে চলেছে নিশ্চিত অবলুপ্তির দিকে? কবিতাটি শেষ হচ্ছে এভাবে, ‘একজন ট্যুরিস্ট অপ্রসঙ্গক্রমে আমায় প্রশ্ণ করলেন: ‘মানুষ কি সেই জায়গাটিতেই মরতে চলেছে, যেখানে মানবসভ্যতা শুরু হয়েছিল?’ (Little Magazine)
একজন সচেতন পাঠক, যিনি প্রবেশ করেছেন কবিতাটির শরীরে, তিনি নিশ্চিতভাবে সচকিত হয়ে উঠবেন কবিতাটির রচনাকালের কথা মনে করে৷ উপসাগরীয় যুদ্ধ… তেলের খনির দখল নিয়ে ঘনিয়ে ওঠা যুদ্ধ প্রায়-বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল৷ শেষ ‘পঙ্ক্তি’-টি ‘পাঠক’-কে মনে করাতে বাধ্য ইতিহাস ও সময়ের চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ার বিষয়টিও৷ এবং, আমাদের ঘাতক উদাসীনতা ক্রমশ সমার্থক হয়ে উঠবে আপাত-শান্তিকল্যাণের৷ কারণ ট্যুরিস্ট প্রশ্ণ করেছেন, ‘অপ্রসঙ্গক্রমে’৷ অর্থাৎ, যুদ্ধের এই ভয়াবহ প্রেতযোনির ভেতর দাঁড়িয়েও ‘ট্যুরিস্ট মানসিকতা’ আমাদের উদাসীন করে রেখেছে এবং মানুষের বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনার কথাও আমরা ‘প্রসঙ্গক্রমে’ উচ্চারণ করতে চাইছি না৷ এটি আমাদের কাছে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা তারও পরের কোনও ক্রমে অবস্থান করছে ৷ (Little Magazine)
“পতঙ্গের আয়ু নিয়ে এই মহাপ্রশ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে রহস্য-সন্ধান করে চলাই একজন লেখকের নিয়তি৷ একজন পাঠকের’ও৷ ফলে তার যোগ্য হয়ে ওঠা একান্ত জরুরি ৷”
এ-লেখা শেষ হবে অমিতাভ মৈত্রের একটি কবিতা দিয়ে, বস্তুত এই পাঁচ-লাইনের ‘ছোট্ট’ কবিতাটির সামনে দাঁড়িয়ে একজন পাঠক ‘সম্ভাব্য’ কীভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে এবং একটি-একটি করে শব্দের বাধা ও সহায়তাকে আশ্রয় করে কীভাবে কবিতাটির অন্দরমহলে প্রবেশ পারে তার ইশারা রইল৷ কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল—
‘সেই দস্তানাই সুখী, হাত থেকে যে হারিয়ে যেতে পেরেছে৷
সামনে ঝকঝক করছে দুধের রাস্তা৷ ঝকঝক করছে সার্ডিন৷
আগুন জ্বলছে জানালাগুলোয়৷ টেলিফোন, ভেষজ ওষুধ জ্বলে উঠছে৷
দূরের হাইওয়ে তবু থমথম করছে
পিছলে যাওয়া মোটরবাইকের চিৎকারের জন্য৷’ (Little Magazine)
—কবিতাটি পড়া শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে যে প্যারাডক্স আক্রান্ত করবে তা হল, কে আসলে কাকে আশ্রয় করে থাকে! দস্তানার আশ্রয় হাত? না কি হাতের আশ্রয় দস্তানা? দেহ, চৈতন্য, সত্তা— কে কাকে আশ্রয় করে রয়েছে সে নিয়ে ডিসকোর্স ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে নজরে পড়তে বাধ্য দস্তানার হাত থেকে হারিয়ে গিয়ে সুখী হবার বিষয়টি৷ এই সন্ত্রাসময় বিষয়টির মিমাংসার লক্ষ্যে আমাদের পাঠ শুরু হবার কথা নয়, হয়ওনি৷ আমরা শুধুমাত্র এই সন্ত্রাসের সামনে দাঁড়াতে চেয়েছি, সন্ত্রাসের অংশ হয়েও উঠতে চেয়েছি গোপনে৷ কিন্তু, সামনে ঝকঝক করা দুধের রাস্তা ও ঝকঝকে সার্ডিন আমাদের মনে করিয়ে দেবে ‘শ্বেত’, অর্থাৎ শাদা রাস্তার ইশারায় সন্ত্রাসহীনতার বিষয়টি ৷ কিন্তু এও কি বাহ্য? একমাত্রিক একটি দৃশ্য মাত্র? না হলে জানালায় আগুন জ্বলবে কেন? আবার এর পাশেই কবি স্থাপন করেছেন জ্বলে ওঠা টেলিফোন ও ভেষজ ওষুধের কথা৷ যাবতীয় উপশম ও সংযোগ’ও কি একই রকম সন্ত্রাসময়? মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে যে চিনের প্রাচীর তা আসলে কি জলের আলপনা? (Little Magazine)
আরও পড়ুন: ভ্রমি: রুকমণিয়ার ঘরবাড়ি- শ্ৰীমা সেন মুখার্জি
কবিতাটির শেষে এসে আমরা পাচ্ছি, ‘দূরের হাইওয়ে তবু থমথম করছে/ পিছলে যাওয়া মোটরবাইকের চিৎকারের জন্য৷’ হাইওয়ে, অর্থাৎ দীর্ঘ, অফুরান রাস্তা, অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর পরিসর অতিক্রম করে ‘সময়’ এবং তাকে আশ্রয় করে থাকা গ্র্যান্ড-ডিজাইন— তার থমথম করে ওঠা পিছলে যাওয়া মোটরসাইকেলের চিৎকারের জন্য! পিছলে যাওয়া, অর্থাৎ খুঁত-যুক্ত বাইকচালন পদ্ধতি, যার সঙ্গে আমাদের জীবনের ক্ষত, অপরিণামদর্শিতা, ব্যক্তির ত্রুটি ইত্যাদি যুক্ত হয়ে রয়েছে তাকে ছাড়া কি সেই মহা-সময় (সময়ের ‘গ্র্যান্ড’ ধারণা) ‘অসম্পূর্ণ’? সেই মোটরসাইকেলের পিছলে যাওয়া আর্তনাদ’ই কি রাস্তাটিকে ‘রাস্তা’ করে তুলেছে? এখানে আরেকটি ধারণাও উঁকি দিয়ে যেতে পারে, এই মহাসড়ক কি অপেক্ষারত ছিল ওই পিছলেপড়া মোটরসাইকেলের আর্তনাদ শোনার জন্য? অর্থাৎ, সে কি এভাবেই ডিজাইনড, যাতে সে একদিন অপেক্ষা করতে শুরু করে সেই আর্তনাদ শোনার জন্য? (Little Magazine)
শক্তিশালী বা দুর্বল— ‘অ্যান্থ্রোপিক’ ধারণার কাছাকাছি আমরা হয়তো ঘুরতে শুরু করব এই কবিতাটি পাঠ করার পর৷ দেহ, আত্মা, চৈতন্য, সময়, ধারক ও আধারিত বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক ও দ্বিমেরু বাস্তবতা থেকে ক্রমশ একমেরু বা ‘এককের’ ইশারা- এই সমস্তই আমাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে৷ যত পাঠ করা হবে তত এই অস্বস্তি তীব্র হবে৷ আর ততবার নতুন-নতুন প্রস্তুতি; এবং ততবার আবিষ্কার করা যে শিল্পের ভেতরে প্রবেশ করে, তার অংশ হয়ে ওঠার পরেও পৃথিবী আজও কার্টেশিয়ান প্যারডক্সটিকে সমাধান করতে পারেনি৷ এ-প্যারাডক্স যতটা দর্শনের ততটাই শিল্পের ৷ (Little Magazine)
পতঙ্গের আয়ু নিয়ে এই মহাপ্রশ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে রহস্য-সন্ধান করে চলাই একজন লেখকের নিয়তি৷ একজন পাঠকের’ও৷ ফলে তার যোগ্য হয়ে ওঠা একান্ত জরুরি ৷ মন এক কবিকে সচেতনভাবে দূরে ঠেলে আমরা বাংলা কবিতাকে অনেকখানি পিছিয়ে দিয়েছি ৷ (Little Magazine)
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।