(M. N. Roy)
ঠিকানাটা ঠিক এরকম-
মেরিডা ১৮৬, রোমা
কুয়াউহেটেমোক, ০৬৭০০, সিউদাদ দে মেক্সিকো
মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে নামলে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। অনেকেরই পরিচিত। (M. N. Roy)
একটা পুরোনো আমলের বাড়ি। ভেতরের দেওয়ালে দুই নামী ফরাসি শিল্পীর আঁকা ছবিটা এখনও রয়েছে কী না জানি না। বাড়িটার নাম এম এন রায় নাইট ক্লাব। (M. N. Roy)
আরও পড়ুন: পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এলি কোহেন
এই এম এন রায়ই আমাদের চির পরিচিত মানবেন্দ্রনাথ রায়। মেক্সিকোয় কমিউনিস্ট পার্টির জনক। ওই বাড়িতেই থাকতেন তিনি। মেক্সিকো তাঁকে ভোলেনি আজও, একশো বছর পরেও। (M. N. Roy)
ওই বাড়িতে মানবেন্দ্রনাথ যাঁর সঙ্গে থাকতেন, সেই ইভলিন লিওনেরারা ট্রেন্ট, তাঁর স্ত্রী। মানবেন্দ্রকে কমিউনিজমে আকৃষ্ট করার পিছনে বিশাল ভূমিকা ছিল ওই আমেরিকান মহিলার। (M. N. Roy)

একশো পেরিয়ে যাওয়া ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার দুই বিদেশিনী স্ত্রীর জীবন খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, মানবেন্দ্রর জীবনে কতটা প্রভাব পড়েছিল তাঁদের। অথচ কীভাবে তাঁরা শেষ দিকে উপেক্ষিত থেকে গিয়েছিলেন! (M. N. Roy)
মানবেন্দ্রর সঙ্গে অর্ধেক পৃথিবী ঘোরা লিওনোরা ইভলিন ট্রেন্টকে মানবেন্দ্রর অনুগামীরা অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। মেক্সিকো থেকে রাশিয়া, আমেরিকা থেকে ভারত— কমিউনিজম প্রসারে বড় উদ্যোগ ছিল ইভলিনের। সিপিএমের প্রবাদপ্রতিম মুজজফর আমেদকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন ইভলিন। বিস্ময় উপচে পড়ে, যখন দেখি, মানবেন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে ইভলিনের নামোল্লেখ করেননি। কেন? তা এক বড় রহস্য! প্রেমেরও, কমিউনিজমেরও। (M. N. Roy)
ইভলিন জীবনের শেষ দিকে আমেরিকায় যে বাড়িতে থাকতেন, সেখানে আগুন লেগে তাঁর সব চিঠিপত্র, লেখালেখি ছাই হয়ে যায়। কিছু কাগজপত্র তাঁর ভাইপো পরে দান করেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুভার ইন্সটিটিউশন অফ ওয়ার প্রতিষ্ঠানে। সেখানেই মিলেছিল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি বহু পুরোনো ছবি। যার পিছনে লেখা, “To my Goddess from her loving worshipper”। (M. N. Roy)
“কারা, কেন এম এম রায়ের দ্বিতীয় স্ত্রীকে খুন করল, তা রহস্যই থেকে গিয়েছে আজও।”
সেই ঈশ্বরীকে ভারতীয় কমিউনিজমের জনক সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন কী করে? ইভলিন শুধু মানবেন্দ্রকে কমিউনিজমে টেনে আানেননি, আমেরিকায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার পিছনে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। সেখানেও এই বহুমুখী প্রতিভা অবহেলিত থেকে গিয়েছেন। মুজফফর আমেদের মতো অনেকেই এই ব্যাখ্যাহীন উপেক্ষা-অবহেলার জন্য মানবেন্দ্রকে ক্ষমা করতে পারেননি। বাকি ভারতীয় কমিউনিস্টরা সেভাবে মনে রেখেছেন কি ইভলিনকে? (M. N. Roy)
মানবেন্দ্র দ্বিতীয় বিয়ে করেন এলেন গটসচককে। জার্মান-ইহুদি বাবা-মায়ের সন্তান এলেনের জন্ম প্যারিসে। পড়াশোনা জার্মানির কোলনে। মানবেন্দ্রর সঙ্গে আলাপের এক বছর আগে থেকেই তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। সাল, ১৯২৭। মানবেন্দ্র যখন জেলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ এলেনের। (M. N. Roy)
মানবেন্দ্র জেল থেকে বেরোলেন ১৯৩৬ সালে। পরের বছরই বিয়ে। এঁরা চলে আসেন দেরাদুন। চুটিয়ে রাজনীতি করেন কর্তা-গিন্নি। এম এন রায় মারা যান, ১৯৫৪ সালে। ছয় বছর পরে দেরাদুনে ছবির মতো বাড়িতে কে বা কারা খুন করে চলে যান এলেনকে। বীভৎসভাবে। তাঁর বাড়ির একটা কিছু নেওয়া হয়নি। ছবির মতো বাগানও অবিকৃত ছিল। অথচ তাঁর খুনিরা ধরা পড়েনি। (M. N. Roy)
এলেন যেভাবে দেরাদুনে খুন হয়েছিলেন, অনেকটা সেরকম রহস্যজনকভাবে সম্পূর্ণ আড়ালে চলে যান মানবেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী ইভলিন।
কারা, কেন এম এম রায়ের দ্বিতীয় স্ত্রীকে খুন করল, তা রহস্যই থেকে গিয়েছে আজও। বোঝাই গিয়েছিল, খুনটা রাজনৈতিক। এত বড় এক ব্যক্তিত্ব খুন হলেন, খুনীকে ধরা গেল না? (M. N. Roy)
এলেন যেভাবে দেরাদুনে খুন হয়েছিলেন, অনেকটা সেরকম রহস্যজনকভাবে সম্পূর্ণ আড়ালে চলে যান মানবেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী ইভলিন। তাঁর ঘনিষ্ঠরা অনেকে বলেন, মানবেন্দ্র অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়াচ্ছেন দেখেই ট্রেন্ট সরে যান ধীরে ধীরে। ডাচ কমিউনিস্ট নেতা হেঙ্ক স্নিভলিয়েতকে ১৯২৭ সালের ১৩ মার্চে লেখা ইভলিনের একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। সেখানেই প্রকাশিত ইভলিনের নানা হতাশা। স্বামীর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তৈরির কথা তো লিখেছেনই, লিখেছেন, তাঁকে কী ভাবে নানা কুকথা শুনতে হচ্ছে আমেরিকায়। মানবেন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদেরই জের। তিনি ব্রিটিশের চর, অর্থ তছরূপ করেছেন, স্বামী ও আন্দোলনকে পরিত্যক্ত করে চলে গিয়েছেন। তাঁর পাশে আজ আর কেউ নেই। তিনি বড় একা। (M. N. Roy)
“বিপ্লবের সঙ্গে রোমান্টিসিজমের সংঘাত হয়নি কোনও। একবার ভাবুন, ওই তিনজন ভারতের স্বাধীনতার জন্য কার কার সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিদেশে। লেনিন, স্টালিন, হিটলার, আইনস্টাইন, সান ইয়াৎ সেন…।”
লিখতে লিখতেই মনে পড়ল কিছু আকর্ষণীয় তথ্য। কাকতালীয়ই, কিন্তু আকর্ষণীয়। স্বাধীনতার আগে যে তিন বঙ্গসন্তান বিদেশে পালিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান, যে তিন জন বাঙালি সব তরুণের স্বপ্নকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে নিয়ে যেতে সফল, সেই তিনজনই প্রেমে পড়েন বিদেশিনীর। বিয়েও করেন। তিনজনেরই অন্যতম কর্মকাণ্ড ছিল জাপানে। সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়। (M. N. Roy)
বিপ্লবের সঙ্গে রোমান্টিসিজমের সংঘাত হয়নি কোনও। একবার ভাবুন, ওই তিনজন ভারতের স্বাধীনতার জন্য কার কার সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিদেশে। লেনিন, স্টালিন, হিটলার, আইনস্টাইন, সান ইয়াৎ সেন…। (M. N. Roy)
ভিনদেশি বিপ্লবীকে প্রেমের জন্য সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারীর স্ত্রীর আত্মত্যাগের গল্প একেবারে উপন্যাসের মতো ফুটে রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে।
অস্ট্রিয়ান এমিলি শেঙ্কল এবং জাপানি তোশিকো সোমা সম্পর্কে অনেকটাই জানে আম-বাঙালি। ভিনদেশি বিপ্লবীকে প্রেমের জন্য সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারীর স্ত্রীর আত্মত্যাগের গল্প একেবারে উপন্যাসের মতো ফুটে রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে। (M. N. Roy)
ইভলিন এবং এলেনই অনেকটা আড়ালে পড়ে। তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের বিদ্রোহের গল্পও অনেকটা আড়ালে। বিস্ময়করভাবে রাজনৈতিক সচেতনতার বিচারে এই দু’জনই অনেক এগিয়ে। তরুণ মানবেন্দ্রর জীবনের ভাবনা ও দর্শন পাল্টে দেওয়ার পিছনে দু’জনের ভূমিকা আকাশছোঁয়া। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রকৃত দলিল তৈরি হলে এই দুই মহিলার নাম আসবেই। স্রেফ বিপ্লবীর স্ত্রী হিসেবে নয়, নিজস্ব অবদানের জন্যই। (M. N. Roy)

ইভলিন কীভাবে লন্ডন বা প্যারিস থেকে ভারতীয় কমিউনিস্টদের উদ্দীপ্ত করে যেতেন, তার উল্লেখ রয়েছে মুজফফর আমেদ (কাকাবাবু) এর লেখায়। সে সময় ভারতীয় তরুণদের বার্তা পাঠাতে শার্টের মধ্যে খবর সেলাই করে পাঠাতেন ইভলিন। কাকাবাবু এমনও বলেছেন, ইভলিন মোটেই মানবেন্দ্রর সহচরী ছিলেন না, বরং মেন্টর ছিলেন। স্রেফ এক স্ত্রী নন, এক থিওরিটিক্যাল নেতাও। (M. N. Roy)
“সেই সময় ভারতীয় কমিউনিস্টদের তর্ক চলছে, পার্টির জন্ম আসলে কবে! ১৯২০ সালে তাসখন্দে, না ১৯২৫ সালে কানপুরে। ওই প্রেক্ষিতে ইভলিন রায়ের অবদান নতুন করে লিখেছিলেন কাকাবাবু।”
ইভলিনকে আত্মজীবনীতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার কারণেই এম এন রায়ের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন কাকাবাবু। ইভলিন রাজনীতি থেকে বহু দূরে চলে যাওয়ার পরেও সেই বিদেশিনীকে ভারতীয় কমিউনিস্ট বলতেন তিনি। নিজের চোখে ক্লান্তিহীন কাজ করতে দেখেছেন বলে। কাকাবাবুর যুক্তি ছিল, পার্টি তো ইভলিনকে বহিষ্কার করেনি, ইভলিনও নিজে সরে যাননি পার্টি থেকে। (M. N. Roy)
সেই সময় ভারতীয় কমিউনিস্টদের তর্ক চলছে, পার্টির জন্ম আসলে কবে! ১৯২০ সালে তাসখন্দে, না ১৯২৫ সালে কানপুরে। ওই প্রেক্ষিতে ইভলিন রায়ের অবদান নতুন করে লিখেছিলেন কাকাবাবু। একটা সময় ছিল, যখন তরুণ মুজাফফর ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে ‘বেআইনিভাবে’ ইভলিনের লেখা, অনেক কমরেডকে সরবরাহ করতেন। ট্রেন্টের অবদানের কথা লিখে গিয়েছেন ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের আর এক স্থপতি ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদও।
ইভলিন ট্রেন্টের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আলাপ হল কী করে? পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে মানবেন্দ্র তখন আজকের সিলিকন ভ্যালিতে। সান ফ্রান্সিসকোর কাছে, পালো আল্টো শহরে। যেখানে বিশ্বখ্যাত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। (M. N. Roy)
তাঁর তখন মানবেন্দ্র নামটা হয়নি। আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও ব্যবহার করেন না। তিনি এক ধর্মযাজক হিসেবে পরিচিত— রেভারেন্ড সি এ মার্টিন।
তাঁর তখন মানবেন্দ্র নামটা হয়নি। আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও ব্যবহার করেন না। তিনি এক ধর্মযাজক হিসেবে পরিচিত— রেভারেন্ড সি এ মার্টিন। স্ট্যানফোর্ডে তখন অতি পরিচিত নাম লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়— বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাই। তিনি প্রেম করছেন এথেল রায় দুগান নামে এক আমেরিকান তরুণীর সঙ্গে। (M. N. Roy)
ইভলিন ছিলেন, এথেলের প্রিয় বান্ধবী। সেসময় ইভলিন আমেরিকান ছাত্রসমাজে এক ঝলসানো বিদ্যুৎ। টেনিসে তুখোড়, ফেন্সিং-এ অসাধারণ। তারপর স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা কোয়াডের সহযোগী সম্পাদক। থিয়েটারে মাতিয়ে দিচ্ছেন। গরীব শিশুদের পড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছেন। প্রবন্ধ লিখছেন এক মায়ের সঙ্গে মেয়ের কথোপকথন নিয়ে। বিষয় এই যে, বিশ্বযুদ্ধে এত খরচ হচ্ছে, তা তো অনাথ শিশুদের সাহায্যে কাজে লাগানো যেত! (M. N. Roy)
আরও পড়ুন: তিব্বত, টিনটিন অথবা এক প্রেম কাহিনি
এবং আরও বড় তথ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে।
এই সময়ই মানবেন্দ্রর সঙ্গে দেখা ইভলিনের। একজন ২৯, একজনের বয়স ২৪। ধনগোপালের বাড়িতে। বান্ধবী এথেলের সঙ্গে এসেছিলেন তিনি। আর মানবেন্দ্র এসেছিলেন ধনগোপালের সঙ্গে দেখা করতে। বড় বিস্ময়কর চরিত্র ধনগোপাল। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি ইংরেজিতে লেখালেখি করে পুরস্কার পান আমেরিকায়। তিনিই জানতেন ছদ্মবেশী রেভারেন্ডের আসল পরিচয়। ধনগোপালই ভারতীয় বিপ্লবীকে বলেছিলেন, আসল নামের বদলে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামটা ব্যবহার করতে। ওখানে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ করতে করতেই মানবেন্দ্র-ইভলিন প্রেম শুরু। (M. N. Roy)
ওই সময় মানবেন্দ্র জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। চেষ্টায় রয়েছেন সাবমেরিনে জার্মানি যেতে, সেখান থেকে গুলি গোলা পেতে। গ্র্যাজুয়েট হয়ে চাকরি খুঁজছিলেন ইভলিন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মানবেন্দ্রর সঙ্গে ইউরোপ যাবেন। এদিকে বাড়িতে প্রবল অসন্তোষ। মেয়ে অজানা অচেনা এক হিন্দু বিপ্লবীর সঙ্গে প্রেম করছে, একশো বছর আগে কোনও আমেরিকান বাবা-মা মেনে নিতেন? (M. N. Roy)
মানবেন্দ্র সে সময় মাসছয়েক ছিলেন পালো আল্টোতে, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই, ২৪৫ রামোনা স্ট্রিটে। পরে পুলিশ খোঁজখবর নিচ্ছে শুনে প্রেমিকাকে নিয়ে চলে যান নিউ ইয়র্কে।
মানবেন্দ্র সে সময় মাসছয়েক ছিলেন পালো আল্টোতে, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই, ২৪৫ রামোনা স্ট্রিটে। পরে পুলিশ খোঁজখবর নিচ্ছে শুনে প্রেমিকাকে নিয়ে চলে যান নিউ ইয়র্কে। সেখানে অতি কষ্টে চলত জীবন। থাকার জায়গা নেই, অর্থ নেই। এক রেস্তোরাঁর ঠিকানা দেওয়া ছিল পরিচিতদের কাছে। সেখানেই তাঁর সব চিঠিপত্র আসত। ইভলিনকে কয়েক মাসের জন্য নিজের সচিবের কাজ দেন লালা লাজপত রায়। কিছুই না, অর্থ সাহায্য করার জন্য। ইভলিন নাম দিয়েছিলেন শান্তি দেবী। অনেকে বলেন, মানবেন্দ্রকে রাজনৈতিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বিয়ে করেছিলেন ইভলিন। (M. N. Roy)
আজ মার্কিস্টদের অন্যতম সেরা ওয়েবসাইটে ইভলিন ট্রেন্টের লেখালেখির তালিকা দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য। ১৯২০ সালে তিনি লিখেছিলেন, ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো। ড্রাফটটা হয়েছিল বার্লিনে। লেখাটা শেষ হয় মেক্সিকো থেকে মস্কো যাওয়ার পথে। অনেকে যে বলেন, ভারতীয় কমিউনিজমের সূচনা ১৯২০ সালে, সেই ধারণাকে আরও জমাট করে দেয় লেখাটা। ইভলিন লিখেছেন, ভারতে জাতীয়তাবাদের সংকট নিয়ে। গান্ধিইজমের ভরাডুবি উঠে এসেছে এক প্রবন্ধে। গান্ধিকে একদিকে প্রশংসা করেছেন, অন্যদিকে ধুইয়ে দিয়েছেন সমালোচনায়। (M. N. Roy)
বহু পরে নাম্বুদ্রিপাদ যখন গান্ধিকে নিয়ে লিখেছেন, সেখানে বলেছেন, ইভলিন রায়ের ক্ষুরধার পর্যালোচনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধি নিয়ে ইএমএসের বইটি ছিল কমিউনিস্ট মহলে বহু আলোচিত। কাকাবাবুর মতো ইএমএসও কিন্তু ইভলিনকে ভোলেননি। (M. N. Roy)
“তিনটে লেখা আলাদা করে চোখে পড়ে। ১) মহাত্মা গান্ধি— রিভলিউশনারি, না কাউন্টার রিভলিউশনারি? ২) ফিউনেরাল সেরিমনি ইন গয়া। ৩) থ্রি লির্ডার্স অফ মেন— চার্চিল, গান্ধি অ্যান্ড লেনিন।”
কতরকম বিষয় ছিল বিদেশিনী ভদ্রমহিলার লেখার— চিত্তরঞ্জন দাশের ক্রমবিবর্তন, ভারতীয় কৃষক নেতা মোতা সিং, গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন, পাঞ্জাবে অকালি শিখদের সমস্যা, বোম্বাই শহরের ধর্মঘট, ভারতের চেতনা, ফ্রান্সে বিপ্লবী ভারতীয়দের সমস্যা, ভারতে লেবার পার্টির ভবিষ্যৎ, মস্কোয় রেড আর্মির চতুর্থ বার্ষিকী, ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট মনটাগুর জীবন, ভারতের রাজনৈতিক বন্দিরা। (M. N. Roy)
সব বলে দেয়, কীভাবে ভারতীয় রাজনীতির সমস্যা গুলে খেয়েছিলেন ইভলিন রায়। এ নামেই লিখতেন তিনি। তিনটে লেখা আলাদা করে চোখে পড়ে। ১) মহাত্মা গান্ধি— রিভলিউশনারি, না কাউন্টার রিভলিউশনারি? ২) ফিউনেরাল সেরিমনি ইন গয়া। ৩) থ্রি লির্ডার্স অফ মেন— চার্চিল, গান্ধি অ্যান্ড লেনিন। এর পাশে এম এন রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছিলেন এ রিভিউ অফ ইন্ডিয়ান সিচুয়েশন। সেটা লেখা ১৯২২ সালে। মানবেন্দ্রর সঙ্গে তিনিই যৌথভাবে লিখেছিলেন, ‘অ্যান ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো’। (M. N. Roy)
ওই লেখাগুলোর পাশে যখন ডাচ কমিউনিস্ট নেতা হেঙ্ক স্নিভলিয়েতকে লেখা ১৯২৭ সালের চিঠি দেখি, তখন মানবেন্দ্র ঘরণীর জন্য তীব্র যন্ত্রণাই জাগে।
ওই লেখাগুলোর পাশে যখন ডাচ কমিউনিস্ট নেতা হেঙ্ক স্নিভলিয়েতকে লেখা ১৯২৭ সালের চিঠি দেখি, তখন মানবেন্দ্র ঘরণীর জন্য তীব্র যন্ত্রণাই জাগে। স্নিভলিয়েত ছিলেন রায় দম্পতির অতি ঘনিষ্ঠ। তাঁকে দুজনেই জ্যাক হরনার ছদ্মনামে লিখতেন। ইভলিন মানবেন্দ্র সম্পর্কে লিখতে হলে লিখতেন ‘আর’। (M. N. Roy)
ইভলিন লিখেছিলেন, ‘ইউরোপ থেকে তিন মাসের বেশি কারও কোনও খবর পাইনি। ‘আর’ আমাকে শুধু ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। আর একটা কথাও বলেনি। ডিসেম্বরে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। এই মার্চ পর্যন্ত কোনও উত্তর আসেনি।’ (M. N. Roy)
দীর্ঘ চিঠিতে বিশ্বখ্যাত স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব, স্বামীর চরম ঔদাসীন্য নিয়ে তাঁর মন্তব্য, ‘ছয়মাস অপেক্ষা করে ‘আর’কে অনেক চিঠি দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আবার সম্পর্কটা শুরু করতে। ও শুধু একটা কথা লিখেছে, হয় আমেরিকায় থাকো, না হয় চিনে চলে যাও। এদিকে আমাকে ব্রিটিশের চর বলা হচ্ছে। অর্থ তছরূপের কথা বলা হয়েছে।’ (M. N. Roy)
“দেরাদুনের ১৩ মোহিনী রোড. পালো আল্টোর ২৪৫ রামোনা স্ট্রিট. মেক্সিকো সিটির মেরিডা ১৮৬— বিশ্বের তিন প্রান্তে তিনটি বাড়ি আজও পড়ে আছে একইরকমভাবে।“
ইভলিন নিজে ওই সময় ভারতে ফিরে গেলেন না কেন? সেই ব্যাখ্যাও রয়েছে তাঁর চিঠিতে। ফুটে উঠেছে অসহায়ত্ব। ‘যদি ভারতে ফিরেও যেতাম, তা হলে আমার কোনও স্বস্তি থাকত না। সব কিছু বিমূর্ত মনে হত। আমার সঙ্গে ভারতের একমাত্র জীবন্ত যোগাযোগ ছিলেন আমার স্বামী। ওই যোগসূত্র যখন ভেঙে গেছে, তখন আর কিছু জীবন্ত পড়ে নেই। জানি না, আমার ভবিষ্যৎ কী। মাঝে মাঝে মনে হয়, সামনে পড়ে শুধু শূন্যতা।’ (M. N. Roy)
স্বামী ‘আর’-এর প্রতি তাঁর অভিমান বারবার ফুটে উঠেছে ওই দীর্ঘ চিঠির বিশাল অংশে। তিনি তখন বিপ্লবী নেত্রী নন, অসহায় এক নারী। ‘আমার স্বামীকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। শুধু আশা করেছিলাম, উনি খোলা মনে আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন। এমন চূড়ান্ত উপেক্ষা করবেন না। উনি যদি সত্যিই আমায় মন থেকে চাইতেন, আমি হয়তো ওঁর কাছে ফিরে যেতাম। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত ছিল যে, উনি সত্যিই আর আমায় চান না। যখন সত্যিই উনি বলে দিলেন, আমি দূরে থাকলেই ভাল, ততদিনে আমার সাত মাস নষ্ট হয়ে গিয়েছে।’ (M. N. Roy)

পরবর্তী সংযোজন, ‘আমার মনে হয়, উনিও যথেষ্ট দ্বিধায় ছিলেন। তবে উনিই প্রথম বুঝিয়ে দেন, আমার সঙ্গে থাকার আর ইচ্ছে নেই ওঁর। মুক্তি চান। সম্ভবত ১৯২১ থেকেই এই ভাবনাটা ছিল। উনি যদি সত্যি তখন এটা বলে দিতেন, আমি তখনই আমেরিকা ফিরে যেতাম। চার বছর অর্থহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হত না। এটাই আমি ওকে শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম।’ (M. N. Roy)
এই চিঠিই স্পষ্ট করে দেয়, এককালের আদর্শ রায় দম্পতির বোঝাপড়া কেমন তলানিতে পৌঁছেছিল শেষদিকে। অনেকেই বলেন, আজকের উজবেকিস্তানের তাসখন্দে ১৯২০ সালে জন্ম হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির। সেই প্রথম সভায় মানবেন্দ্রনাথ রায়, ইভলিন ট্রেন্ট রায় মধ্যমণি ছিলেন অবনী নাথ মুখোপাধ্যায়, রোজা ফিটিংগোফ, মহম্মদ আলী, মহম্মদ শফিক সিদ্দিকি এবং এম প্রতিবাদী বায়াংকার আচার্যের সঙ্গে। তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না স্বামী-স্ত্রীর শেষ দিকের সম্পর্কের তিক্ততার কথা জানলে। (M. N. Roy)
১৯২৮ থেকে ১৯৩০, মস্কো থেকে পালিয়ে এম এন রায় ছিলেন জার্মানিতে। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগাযোগ হলে বেশ কয়েকজন মহিলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয়। শিবনারায়ণ রায়ের মতো এম এন রায়কে নিয়ে লেখালেখা করেছেন শ্রীনিবাস রাও। তাঁর লেখা থেকে জানা গেল, সেই সময় জার্মানির কমিউনিস্ট ও ফেমিনিস্ট ক্লারা জেটকিনের সম্পর্ক তৈরি হয় তাঁর। তারপর লুই গেসলারের সঙ্গে লিভ ইন করেন কয়েকদিন। গেসলার ছিলেন অনেকদিনের চেনা। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সদস্য। রোজা লুক্সেমবুর্গের সদস্য। (M. N. Roy)
“পাশ দিয়ে কত দেশের কত রকম লোক হেঁটে যান প্রতিদিন। কত স্বপ্নের রোদ ওঠে সেখানে। অধিকাংশই জানেন না, এখানে একদিন বিপ্লব ও ভালবাসা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যেত সৃষ্টির আনন্দে, স্বাধীনতার খোঁজে।”
মানবেন্দ্র পরে যাঁকে বিয়ে করেন, সেই এলেন গোটসচকও ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। জন্ম প্যারিসে। পড়াশোনা কোলনে। ফরাসি ও ইহুদি বাবা মায়ের সন্তান, এলেন অনেক আগে থেকেই কমিউনিজম নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। লেখালেখি করতেন। জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টিও করতেন। এম এন রায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা ১৯২৮ সালে। পরে এলেন একবার বলেছিলেন, ‘ওঁর বিশাল প্রতিভা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।’ মানবেন্দ্র ভারতে ফিরে এসে গ্রেফতার হলেন। (M. N. Roy)
ওদিকে এলেন পালালেন ফ্রান্স। তবু দুজনের যোগাযোগ নষ্ট হয়নি। দূর দেশে থেকেও প্রেমিকের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দেখিয়েছেন এলেন। (M. N. Roy)
মানবেন্দ্রর উত্তরণে ইভলিনের মতো বড় ভূমিকা ছিল এলেনেরও। তাঁর দুই স্ত্রী লেখালেখি করতেন নিজেদের পদবি মুছে ফেলে। স্বামীর পদবি ব্যবহার করে। ইভলিন রায় ও এলেন রায়। এখানেও দুই বিদেশিনীর কী মিল! (M. N. Roy)
এলেনের ফ্রান্সে চলে যাওয়ার কথা হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে। সেখানে গিয়ে এলেন কী করলেন? রমাঁ রলাঁ, আন্দ্রে মার্লো, আলবার্ট আইনস্টাইন, পল রবসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ব্রিটিশদের হাতে বন্দি এম এন রায়ের হয়ে।
এলেনের ফ্রান্সে চলে যাওয়ার কথা হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে। সেখানে গিয়ে এলেন কী করলেন? রমাঁ রলাঁ, আন্দ্রে মার্লো, আলবার্ট আইনস্টাইন, পল রবসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ব্রিটিশদের হাতে বন্দি এম এন রায়ের হয়ে। দেখা করেন নেহরুর সঙ্গে। একটা সময় বন্দি এম এন রায়ের সঙ্গে যেমন তিনি চিঠিতে যোগাযোগ করে যাচ্ছেন, তেমনই চেষ্টা চালাচ্ছেন প্রেমিকের মুক্তির জন্য আবেদনে সই সংগ্রহের। তাঁর উদ্যোগেই ব্রিটিশ সরকারকে চিঠি লেখেন নেহরু, আইনস্টাইন, বাল্ডউইন, ব্রকওয়েরা। মানবেন্দ্রর বারো বছর জেলের মেয়াদ কমে দাঁড়ায় ছয় বছরে। তাঁকে দেওয়া হয় ‘ক্লাস বি’ কয়েদির স্বীকৃতি। ওই সময় এলেন তাঁকে পাঠাতেন অজস্র বই। এলেনের সঙ্গে তাঁর চিঠিগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে চিরকালীন প্রেমের প্রতীক। যেখানে ধরা পড়ে সেই আমলের সমাজের প্রতিফলনও। (M. N. Roy)
মানবেন্দ্রনাথের এক জীবনীকার ভিবি কার্নিক লিখেছিলেন, ‘এলেনকে বিয়ের পর রায় সত্যি সত্যিই এক ভালোবাসার মানুষ পেয়েছিলেন। যিনি তাঁকে রাজনৈতিক ভাবনাতেও সাহায্য করে গিয়েছেন নিয়মিত।’ বিয়ের পর দেরাদুনের মোহিনী রোডে যে বাড়িতে থাকতেন মানবেন্দ্র, তা তাঁর ভাষায় ‘হিউম্যানিস্ট হোম’। ১৬ বছর তাঁরা ছিলেন ওই বাড়িতে। প্রথমে এসেছিলেন ছয় সপ্তাহ থাকবেন বলে। এলেনও ছিলেন ইভলিনের মতো এক ঝলক বিদ্যুৎ। মানবেন্দ্রর সৃষ্টিশীলতাকে আরও ধারালো করেছিল যা। মানবেন্দ্রর মৃত্যুর পর তাঁর রাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পত্রিকার সম্পাদনা করতেন এলেনই। তাঁর মৃত্যুর ৬৫ বছর পরেও কেন তাঁর হত্যাকারীকে শনাক্ত করা গেল না, এটাই ভাবায় খুব। (M. N. Roy)
আরও পড়ুন: স্মৃতির আকাশ থেকে: প্রিয় মৃণালদা
দেরাদুনের ১৩ মোহিনী রোড. পালো আল্টোর ২৪৫ রামোনা স্ট্রিট. মেক্সিকো সিটির মেরিডা ১৮৬— বিশ্বের তিন প্রান্তে তিনটি বাড়ি আজও পড়ে আছে একইরকমভাবে। (M. N. Roy)
পাশ দিয়ে কত দেশের কত রকম লোক হেঁটে যান প্রতিদিন। কত স্বপ্নের রোদ ওঠে সেখানে। অধিকাংশই জানেন না, এখানে একদিন বিপ্লব ও ভালবাসা হাত ধরাধরি করে হেঁটে যেত সৃষ্টির আনন্দে, স্বাধীনতার খোঁজে। বিদেশি দুই তরুণীর কাছে সম্পূর্ণ অচেনা ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল অনন্ত প্রেম ও সূর্যের এক নাম। (M. N. Roy)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
বিশিষ্ট সাংবাদিক। এই সময় সংবাদপত্রের প্রাক্তন সম্পাদক ও ক্রীড়া সম্পাদক। উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সম্পাদক। আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে কভার করেছেন একাধিক বিশ্বকাপ ফুটবল ও অলিম্পিক গেমস। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, খেলা, গান, সিনেমা, ভ্রমণ, খাবারদাবার, মুক্তগদ্য— বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখতে ভালবাসেন।



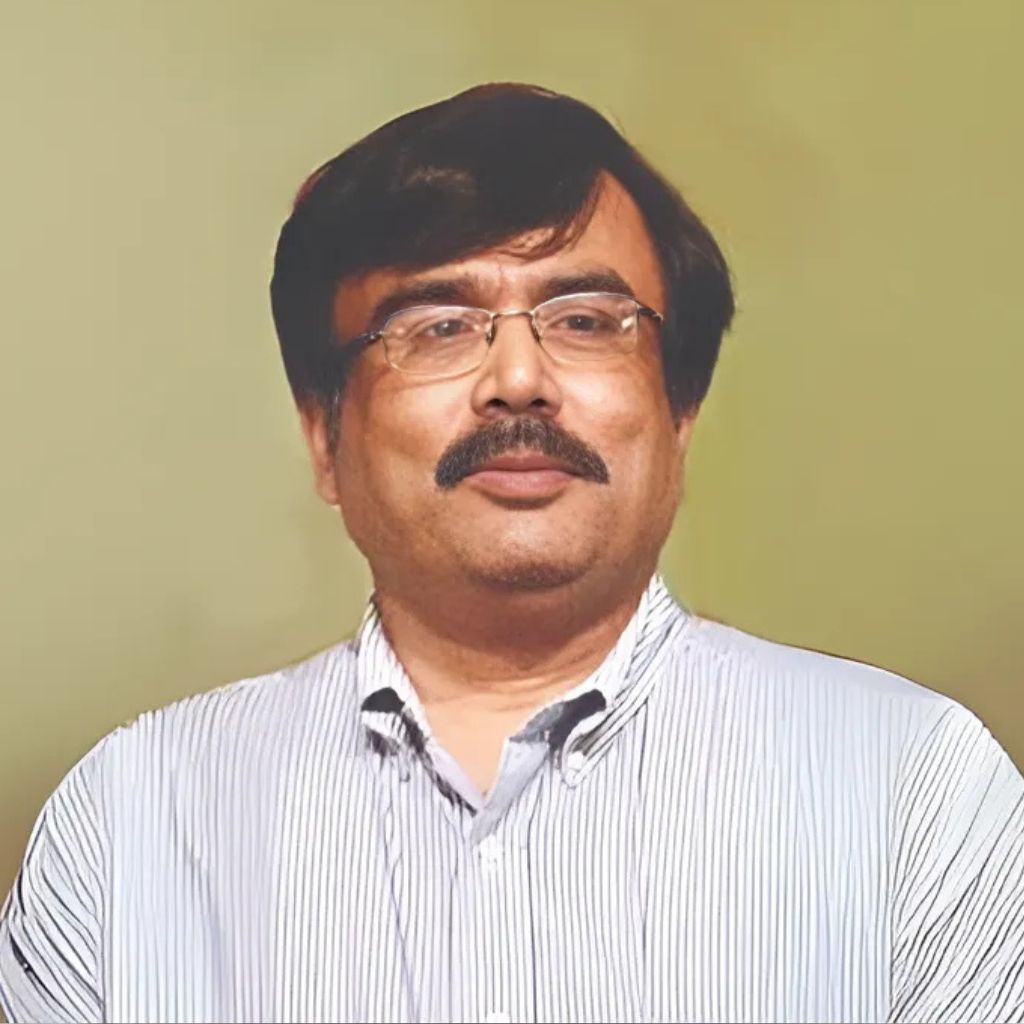
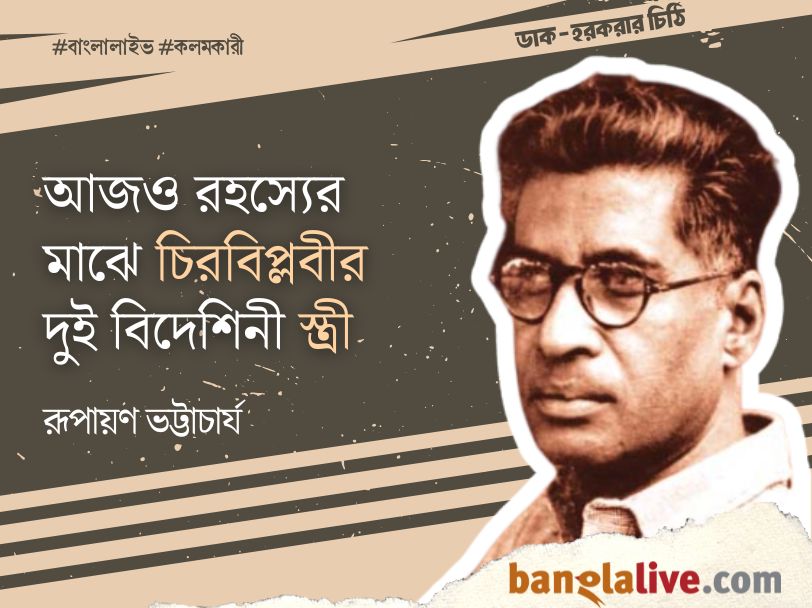





















One Response
খুব ভালো লাগলো..,. র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পত্রিকা ও মানবেন্দ্র নিয়ে ভাসাভাসা ধারনা ছিল… ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো ধারনা ছিল না… ব্যক্তিগত সত্তা সৃষ্টিশীল সত্তায় মিল ও দ্বন্দ্ব অনেক সময় থাকে, কিছুটা জানা হল… কত বিষয়ে কত অনুসন্ধান করে বিষয়গুলো সহজ করেন আমাদের কাছে..,রূপায়ণদা …