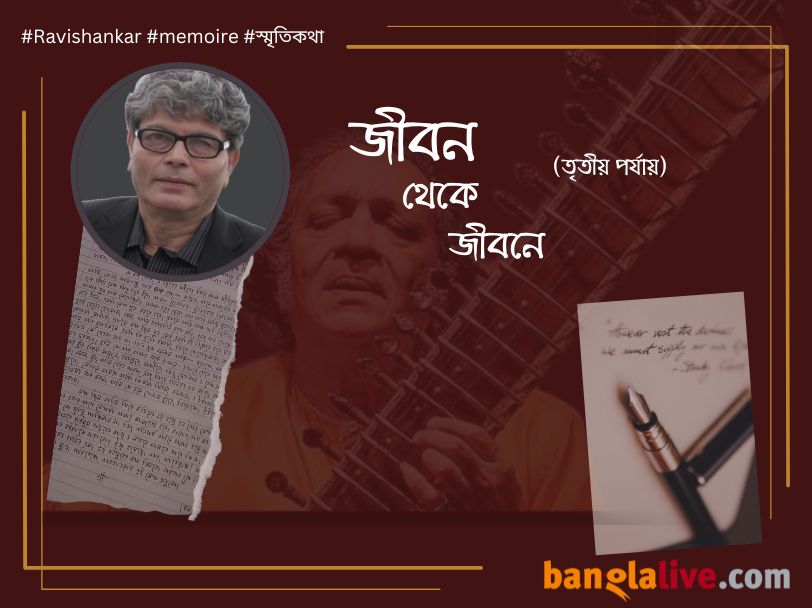মাদ্রাজে রবিশঙ্করের (ravishankar) থাকার ব্যবস্থা ছিল ভরতরামের বাড়িতে। ভরতরামদের কুলগুরুর মতন তিনি। যদ্দুর মনে পড়ে ভরতরামদের বাড়ির বউ শীলা ভরতরাম ছিল রবিশঙ্করের ছাত্রী। রবিশঙ্করের অন্ধ ভক্ত গোটা পরিবার ওঁদের। প্লেনে যেতে যেতেই রবিশঙ্কর বললেন, তুমি আল্লারাখার সঙ্গে ‘সাবেরা’ হোটেলে থেকো। খুব কাছাকাছি হবে।
ব্যাগেজ কুড়িয়েই আমি ‘সাবেরা’-র দিকে ছুটলাম। জিনিসপত্র নামিয়েই ছুটলাম স্নান করতে। মাদ্রাজে তখন রীতিমতন গরম, সোয়েটার পরে বিশ্রী রকম ঘামছিলাম। ওদিকে কাঁটায় কাঁটায় আটটায় শুরু হবে রবিশঙ্করের সেতার। রবিশঙ্কর বলেছিলেন আমি বলে রাখব তোমার কথা। পরিচয় দিয়ে ঢুকে যেও।
স্নান করে এক কাপ কফি খেয়ে চলে গেলাম মিউজিক অ্যাকাডেমিতে। রবিশঙ্কর তখন গ্রিনরুমে। আমি নাম বলাতে একজন আমায় নিয়ে বসিয়ে দিল হলে। মিনিট কয়েকের মধ্যে শুরু হল বাজনা। তাকিয়ে দেখি আমার সামনের সারিতে বসে আছেন সব বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষজন। একঝলকে চিনে ফেললাম এম এস শুভলক্ষ্মীকে। মনে হচ্ছে বালাসরস্বতীও ছিলেন, তবে আমি নিশ্চিত নই। অনতিদূরে স্বামীকে নিয়ে বসেছিলেন বৈজয়ন্তীমালা। অনেকেই হয়তো জানেন যে বৈজয়ন্তীমালার ‘চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যে সুরের কাজ রবিশঙ্করের।
আর কে কে আছেন দেখার আগেই আমি বুঁদ হয়ে গেলাম ওঁর আলাপচারিতে। এবং প্রথম সেই আচ্ছন্নতা কাটল যখন দেখি গোটা হলই সেতারের গৎ বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত হিসেবে কড়ি গুণে মাত্রা রাখছে। আর সামনের সারির পণ্ডিত ব্যক্তিরা তো যেভাবে ঝোঁক, ফাঁক, সম ধরছেন তাতে কে বলবে তাঁরা নিছক শ্রোতা, বৃহৎ অকের্স্ট্রার সদস্য নন?
কলকাতায় এর ক’দিন আগে রবিশঙ্কর খেয়ালাঙ্গে খাম্বাজ বাজাতে গিয়ে ফিরৎ করেছিলেন শুদ্ধ নি-ধা-পা দিয়ে। যদিও খাম্বাজের অবরোহীতে কোমল ‘নি’ ধরা আছে। শুদ্ধ নি-ধা-পা অবরোহণে একটা ঠুংরির ছোঁয়া আসে, খানিকটা রঙের আমেজ হয়। তাতে নীলাক্ষ তীব্র সমালোচনা লিখেছিল রবিশঙ্কর কেন ওই ঠুংরিভাব আনলেন। কথাটা আমার এবং রবিশঙ্কর উভয়েরই মনে ছিল। কিন্তু অ্যাকাডেমির বাজনাতেও রবিশঙ্কর খেয়ালাঙ্গে খাম্বাজ ধরে বিশেষ ওই প্রয়োগ ফের করলেন। যাতে মনে হল ওই প্রয়োগটা তিনি নিয়মসম্মত বলেই মনে করেন। আমি মনে মনে ঠিক করলাম সাক্ষাৎকারের সময়ে আমি ওই প্রশ্নটা তুলব।

বাজনার শেষে স্টেজে দেখি লোকে লোকারণ্য। গোটা হলটাই উঠে এসেছে স্টেজে। শুভলক্ষ্মী তো শিল্পীর হাত চেপে ধরে কত কীই বলছিলেন। আর সামনে তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন বৈজয়ন্তীমালা। আমি খুব দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। যাতে রবিশঙ্করও আমায় দেখতে না পান। কিন্তু পালিয়ে বাঁচিনি। হঠাৎ হাত তুলে ‘শঙ্কর! শঙ্কর!’ করে ডাক দিলেন। কাছে যেতেই বললেন, আমার যে কী দুঃখ হচ্ছিল ভাই, ভাবলাম তুমি বুঝি আর বাজনাতে এলেই না।
আমার সঠিক মনে পড়ছে রবিশঙ্করের কথায় এই প্রথম আমার মনে হল যে লোকটির আমার প্রতি মমতা জন্মেছে। তিনি আমায় ভালবেসেছেন। আমরা তো মানুষকে অনেক সময়ে অনেকভাবেই প্রশংসা করি। কিন্তু তার সবটাই কি প্রীতির লক্ষণ? ভালবাসা তো অনেক পরের কথা। কেন জানি না ভালবাসাকে আমি ততখানি পূণর্তার সঙ্গে মেলাই না, যতটা অভাববোধের সঙ্গে। যাকে ভালবাসি তার উপস্থিতিতে ততটা বিহ্বল হই না, যতটা হই তার অনুপস্থিতিতে। ভালবাসাও এক ধরনের জটিল, স্বার্থপর অনুভূতি। মিউজিক অ্যাকাডেমির স্টেজে দাঁড়িয়ে রবিশঙ্করের ওই কথাটা শোনার পর আমার আর কোনো সন্দেহ থাকেনি যে লেখাটা সত্যিই আন্তরিক এবং সুন্দর হবে।
তাকিয়ে দেখি আমার সামনের সারিতে বসে আছেন সব বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষজন। একঝলকে চিনে ফেললাম এম এস শুভলক্ষ্মীকে। মনে হচ্ছে বালাসরস্বতীও ছিলেন, তবে আমি নিশ্চিত নই। অনতিদূরে স্বামীকে নিয়ে বসেছিলেন বৈজয়ন্তীমালা।
কাছে যেতে রবিশঙ্কর আলাপ করিয়ে দিলেন শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে। শুভলক্ষ্মী বললেন, পরশু দুপুরে পণ্ডিতজির সঙ্গে আপনি আমাদের বাড়িতে যাবেন। আমি বললাম, আপনার গান কবে শুনব? মহিলা হাসলেন। বললেন, যবে ঈশ্বর চাইবেন।
পরদিন সকালে স্নান সেরে টেপ রেকর্ডার নিয়ে রওনা হলাম ভরতরামদের বাড়ির দিকে। তার আগে অবধি সবসময় শার্ট-প্যান্ট পরে থাকতাম। সেদিন পরলাম সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি। যাতে জুনিয়র স্টেটসম্যান বলে আর ভুল না করেন আমাকে। পৌঁছতেই দেখি রবিশঙ্কর সেতার হাতে তালিম দিচ্ছেন দুটি শিষ্যকে। যারা দুজনেই নিতান্ত বালক। আর পাশে বসে আছেন (তখন চিনিনি) গায়িকা বাণী জয়রাম। রবিশঙ্কর বললেন, ‘মীরা’ ফিল্মে আমি বাণীকে দিয়ে গান করিয়েছি। দুর্ধর্ষ গেয়েছে। আর এই হচ্ছে শঙ্কর, আমার সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘুরছে বই লেখার জন্য।
বাণী তাঁর সুন্দর বড়ো বড়ো চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বললেন, তাই নাকি! তাহলে তো খুব জ্ঞানীগুণী লোক হবেন। রবিশঙ্কর বললেন, হবে কী? হয়েছে। আমি ভয়ঙ্কর বিব্রত বোধ করে বললাম, বইয়ের একটা বাক্যও শুরু হয়নি। হলেই টের পাবেন আমি কত বড় অপদার্থ।
বাণী চলে যাওয়ার পর ছাত্রেরাও উঠে গেল। আমি দুরু-দুরু বক্ষে টেপ চালিয়ে অন্তত বিশবার ঝালানো কথাগুলো দিয়ে প্রশ্ন শুরু করলাম। রবিশঙ্কর চোখ বুজে বহুক্ষণ ভাবলেন, মুখের সামনে হাত মুঠো করে কাশলেন, তারপর আস্তে আস্তে, নিরবচ্ছিন্নভাবে কথা কইতে শুরু করলেন, ‘রাগ-অনুরাগ’ শুরু হয়ে গেল।
রবিশঙ্কর বলছেন : “দেখুন মশাই, আমি লেখক নই, গানবাজনার কারবার করি। আর তাতেই তো এখনও অনেক বাকি। লেখার কথা ছেড়ে দিন। তবে হ্যাঁ, অনেক দিন থেকে লোকে বলে এসেছে, একটা কিছু লিখুন। হয়তো ইচ্ছেও ছিল কোনও না কোনও দিন লিখব। যদি পরে কোনওদিন সময় করে বসতে পারি। কিন্তু করব-করব করেও সেটা হয়ে ওঠে না। আর, তা ছাড়া কী লিখতে গিয়ে কী লিখে বসি এই সব ভাবনাও থাকত।…

তা যাই হোক, এ বছরের শীতের দিন লালা শ্রীধরের বাড়িতে ছিলাম আমি, ২০ নং বালিগঞ্জ পার্ক রোডে। শঙ্কর, মানে আমাদের শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, ওকে চিনি বেশ কিছুদিন ধরে। আমার স্যুভেনির-ট্যুভেনির লিখেছিল, ওর লেখা আমার খুব ভাল লেগেছিল। চালাক-চতুর ছেলে, আর ভারি মিষ্টি স্বভাব। তো ও অনেক করে ধরল, একটা লেখা শুরু করতে হবে। প্রথমে আমি ততটা গা-ই দিইনি। কিন্তু ওর ইচ্ছেটা খুবই জেনুইন দেখলাম। বলল, আমি ইন্টারভিউ মতো করি এবং তার থেকে বার করে লেখাটা সাজাই। প্রথমে কথা ছিল খুব ছোট্ট একটা বই হিসেবে হবে সবটা। এবং তখন আমি অতি মুশকিলে একটা কি দুটো সিটিং দিতে পেরেছিলাম। তাতে খুব বেশি জিনিস তো দেওয়া যায় না। তখন ওকে বললাম—দ্যাখো, আমাদের আরও সময় দরকার। তুমি তো আর আমার সঙ্গে এখানে-ওখানে যেতে পারবে না। তখন আমার ট্যুর হচ্ছিল মাদ্রাজে, দিল্লিতে, কাশীতে। কিন্তু দেখলাম ও বেশ নাছোড়বান্দা ছেলে। বলল, হ্যাঁ, আমি যেতে পারব। এবং গিয়ে হাজিরও হল সত্যি। মাদ্রাজে, পরে দিল্লিতে। সেখানে আমরা আটটা কি ন’টা সিটিং করলাম। ও ইন্টারভিউ করে অনেকখানি জিনিসও বার করল। আমি তো চলে গেলাম ট্যুরে, বিদেশে। ইউরোপে, পরে আমেরিকায়।
কথা ছিল আমি ফিরে ক’দিনের জন্য বম্বেতে বসে ওর তৈরি লেখাটা দেখব। অন্তত বার হওয়ার আগে লেখাটা আমায় ঝালাতেই হবে। তাড়াহুড়োয় কত কী বলেছি, না দেখে তো স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। কিন্তু অনিবার্য কারণে আমার বম্বে যাওয়া হল না। চিঠিতে জানতে চাইলুম শঙ্করের কাছে, ও লন্ডনে আসতে পারে কি না। এদিকে ওদেরও তখন বইটাকে বাড়ানোর ইচ্ছে হয়েছে। আর, আরেব্বাস! শঙ্কর সেই লন্ডনে এসেও হাজির হল। এই ভবঘুরের কথা কিনতে। তারপর তো দিনের পর দিন অদ্ভুত অদ্ভুত মুডে, পরিবেশে, আবহাওয়ায় এই লেখা এগুলো।’’
(চলবে)
*ছবি সৌজন্য: লেখক, britannica
শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।