আমির খাঁ সাহেব (Ustad Amir Khan) তো বলেই দিলেন, ‘নাও, শুরু করা যাক’, কিন্তু আমি তো ভেবে মরছি কোথায় কীভাবে শুরু করি।
ইতিমধ্যে চা এসেছে, আমরা দু’জনাই কাপে চুমুক দিচ্ছি। মনে মনে শেষ সেই প্রশ্নটাই বাছলাম যেটা খাঁ সাহেবকে প্রথম শোনা ইস্তক মাথায় ঘোরাফেরা করেছে। ঠোঁট থেকে কাপ সরিয়ে একসময় সেটাই পেশ করে বসলাম, ‘উস্তাদজি, আপনি আপনার আশ্চর্য খেয়াল আস্থায়ী গেয়ে শেষ করেন। অন্তরা গানই না। কোনও বিশেষ কারণ?’
খাঁ সাহেব ভারি সুন্দর একটা হাসি হেসে ওঁর চায়ের কাপটা সামনের টেবিল রাখতে রাখতে বললেন, ‘আস্থায়ীটাই তো একটা সমুদ্রের মতো, তার কিনারার খোঁজেই তো জীবন কেটে যায়। অন্তরায় পৌঁছে উঠতে পারি না।’
আর কারও জবানিতে এই কথা শুনলে ভাবতাম এ এক রঙিন, কাল্পনিক উত্তর। কিন্তু উস্তাদ আমির খাঁ সাহেব! উনি তো খেয়াল পেশ করেন না, খেয়াল নিয়ে ধ্যানে বসেন। কতবারই তো ওঁর খেয়ালের আস্থায়ী শুনতে শুনতে মনে হয়েছে এ তো এক অশেষ বিস্তার, যার আর পর নেই। ‘জয় মাতে বিলাম্ভ’ হোক চাই ‘গুরু বিনা জ্ঞান ন আয়ে’ কী ‘কৌন মতন সো পিয়াকো মনাও’ কিংবা ‘মন সুমরত নিশিদিন তুমহারে নাম’ অথবা ‘বরসন লাগি রে’—যেটুকু যা কথা তার রূপ, ভাব, অর্থ, স্পর্শ, গুঞ্জন যেন শেষ হওয়ার না।
‘গুরু বিনা জ্ঞান ন আয়ে’— আমির খাঁয়ের কণ্ঠে অসাধারণ খেয়াল
খাঁ সাহেবের ছোট্ট উত্তরটাকেই একটা ছোট্ট কবিতা মনে হচ্ছে তখন। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কবিতার মূল্য কীরকম একটা খেয়ালে, উস্তাদজি?’ বললেন, ‘যতটা তার সুরে, লয়ে, ভাবে, বিস্তারে। খেয়াল তো একটা ছবির মতো, যা তুমি তোমার সারা জীবনের চিন্তা, ভাবনা, স্মৃতি দিয়ে আঁকছ। তার পরেও ভাবছ—কতটুকুই বা পারছি? আমি মির্জা গালিবের ওপর ডকুমেন্টারিতে ওঁর কবিতাও গেয়েছি। গজল হিসেবে; কথা ছিল ‘রহিয়ে অব অ্যায়সি জগহ।’ আলি আকবর ভাই তো আমাকে বাংলা ছবিতেও ঠুংরি গাইয়ে নিয়েছে যদিও আমি ঠুংরি গাই না।’
তখন না বলে পারিনি, ‘আপনার সেই ঠুংরি— পিয়া কে আবন কে ম্যায় খবরিয়া’— আজও শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কী অপূর্ব একটা গান! খাঁ সাহেব তাতে বললেন, ‘আমি কিন্তু আলি ভাইকে আগের থেকে বলে দিয়েছিলাম তবলিয়া রাধাকান্ত (নন্দী) যেন গানে লগ্গি না বাজায়। আমাকে দিয়ে গাওয়ানোর ওটাই ছিল শর্ত। আলি ভাই তাতেও রাজি ছিল। গান হল, তারপর সবাই আমরা শুনতে বসলাম। সবাই হায়! হায়! করছে, বাপরে, কী গান হয়েছে। শুনতে শুনতে খেয়াল করলাম রাধাকান্ত কী সুন্দর লগ্গি করে গেছে। গাইবার সময় খেয়ালই করিনি। গাইছিলাম যখন তখনই রাধাকান্তকে চোখ মেরে লগ্গি চালাতে বলেছে আলি ভাই।’
ক্ষুধিত পাষাণ ছবিতে গাওয়া ঠুংরি— ‘পিয়া কে আবন কে ম্যায় খবরিয়া’… তবলায় রাধাকান্ত নন্দী
খাঁ সাহেবের সঙ্গে দু’ঘণ্টা কথা বলে বেরোবার সময়ও মনে হচ্ছিল কথা যেন সবে শুরু হচ্ছে। দেখতে দেখতে লোক আসা শুরু হয়েছে বাড়িতে। খাঁ সাহেব আমাকে নিয়ে বুফে টেবিল থেকে পরোটা, কাবাব, বিরিয়ানি, মিষ্টি তুলে দিতে লাগলেন। যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হয়ে বললাম, ‘উস্তাদজি, আপনি আমায় খাবার তুলে দিচ্ছেন!’
আমির খাঁ ওঁর পিতৃসুলভ কেতায় বললেন, ‘আজ না তোমার সালগিরা!’
আজও স্পষ্ট মনে করতে পারি সেদিন ওঁর এই কথায় আমার হাতে ধরা প্লেট কেঁপে গিয়েছিল। আবেগের বশে শুধু বলতে পেরেছিলাম, ‘আজ অনেকে আসবেন এখানে, কিন্তু আমার থাকা হবে না। আমার বাড়িতে বন্ধুরা আসবে।’
খাঁ সাহেব বললেন, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকেও তো যেতে হবে।’
বললাম, ‘আরও লম্বা সময় ধরে কথা বলার ইচ্ছে রয়ে গেল। তা কি সম্ভব?’ খাঁ সাহেব আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সম্ভব। কলকাতায় তো সবসময়ই আসি। এখানে, নয় অরুণ ভাইয়ের ওখানে। যেখানে সুবিধে এসে যেও।’
এরপর অরুণদার বাড়িতে এসে যখন থাকছেন তখন বার কয়েক গিয়ে ওখানে ওঁর গান শোনা হল, কথাবার্তায় কত কী যে শেখা হল, কিন্তু মুখ ফুটে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়নি। একবার অরুণদাকে বললাম; উনি খুশি হয়ে বললেন, ‘করো, করো। আমি time fix করছি। তুমি খাতা-কলমে যা লেখার লিখ। আর গোটা interview আমি spool tape-এ record করে রাখব।’ (Ustad Amir Khan)
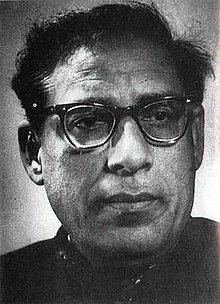
লন্ডনে ১৯৭৭-এ যখন পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে ওঁর স্মৃতিকথা ‘রাগ-অনুরাগ’-এর কাজ করছি তখন একদিন কথায় কথায় ওঁকে বলেছিলাম, ‘আমির খাঁ সাহেবেরও একটা লম্বা interview নেবার কথা হয়েছিল। কপালদোষে তা আর ঘটে ওঠেনি।’
কথা হচ্ছিল আমির খাঁকে নিয়ে ওঁর স্মৃতিকথার জন্য, তাই রীতিমতো উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেন? কেন হল না?’
বলেছিলাম, ‘সে বছরই ফেব্রুয়ারিতে উনি চলে গেলেন রোড অ্যাক্সিডেন্টে।’
শচীনদেব বর্মনের সাক্ষাৎকারের কথা যেদিন তুললেন অরুণ বাগচী, আমার একটাই মন্তব্য ছিল: ‘আমি কিন্তু শুধু হিন্দি সিনেমা আর বাংলা গানে থাকব না, ওঁর পল্লিগানের চেহারা-চরিত্র, ডিটেল নিয়ে কথা বলতে চাইব।’ অরুণবাবু বেশ দরাজকণ্ঠে বলেছিলেন, ‘আপনার যা মনে হয় জিজ্ঞেস করবেন। শুধু মনে রাখবেন আপনার লেংথ থাকতে হবে আটশ’ থেকে হাজার শব্দের মধ্যে।’
কী আর বলব, এই লেংথ আর লেংথ ব্যাপারটা তাড়া করে ফেরে আমাকে, যখন কিছু লিখতে বসি। অরুণবাবু বলেন, ‘আপনার লেখায় কলম ছোঁয়ানো যায় না বলে পাতার সব জায়গাই তো কেড়ে নিতে পারেন না।’
জিজ্ঞেস করলাম, ‘শচীনদেবের ঠিকানা কী কলকাতায়?’
অরুণবাবু বললেন, ‘ওটা সাগরবাবুকে (সাগরময় ঘোষ) জিজ্ঞেস করে নিন। ‘দেশ’-এই তো লিখছেন স্মৃতিকথা।’
সাগরদাকে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন, ‘তুমি সুনীলকে (গঙ্গোপাধ্যায়) জিজ্ঞেস করো। ওর বাড়ির পাশের রাস্তায়।’
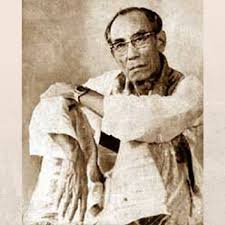
সুনীলদা তখন থাকেন গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের পাশেই একটা ফ্ল্যাটে। জিজ্ঞেস করতে বললেন, ‘আমার ফ্ল্যাট যে বাড়িতে সেটা পেরিয়ে পরের রাস্তায় ঢুকে ডান দিকের দ্বিতীয় বাড়িটা।’
যেদিন যাব শচীনকর্তা সময় দিলেন বিকেল চারটে। যা পরে জেনেছিলাম ওঁর বিকেলের চায়ের সময়। ফটোগ্রাফার নিয়ে বেরোনোর তোড়জোড় করছি, হঠাৎ উদয় হল আমার কলেজের বন্ধু আর স্টেটসম্যান পত্রিকার দুরন্ত জার্নালিস্ট অমিত মুখার্জি— যার সঙ্গে মাসে এক-আধবার পুরনো ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকাল রেকর্ড কিনতে বেরনো হয়। তারপর নিজামের রোল কিনে কিড স্ট্রিটের প্যালেস কোর্টে ওদের পেল্লায় গর্জাস ফ্ল্যাটে চা নিয়ে বসা হয়। ও তখন বাখ, বেটোফেন বা মোৎজার্টের কোনও পিস চালিয়ে দেয় আর নিমেষে আমরা হারিয়ে যাই অন্য কোনও সময়ে, অন্য কোনওখানে।
আমি বেরনোর তোড়জোড় করছি দেখে অমিত বলল, ‘কোথায় যাচ্ছ? আজ তো রেকর্ড কিনতে যাবার কথা ছিল। বাড়িতেও দুটো শুবের্ট আর শুমান এল পি বার করে রেখেছি। একসঙ্গে শুনব বলে।’
বললাম, ‘যেখানে যাচ্ছি সেখানেও গান শোনা হবে। তুমিও চলো।’
অমিত জিজ্ঞেস করল, ‘সেটা কোথায়?’
বললাম, ‘এস ডি বর্মনের ইন্টারভিউ নিতে।’
অমিত একটা চিৎকার চাপতে গিয়েও পারল না ‘W-h-a-t!! You mean S-D-Burman? মানে Guide, মানে Aradhana, মানে Solva Saal?’
বললাম, ‘Yes. মানে ‘হ্যায় অপনা দিল তো আওয়ারা’। হবে তো? নাও চলো।’
অমিত আবার একটু অস্ফুটে বলল, ‘Wow!’ ও তখনও আন্দাজ করতে পারছে না কী একটা বিকেল আর সন্ধে অপেক্ষায় আছে আমাদের।
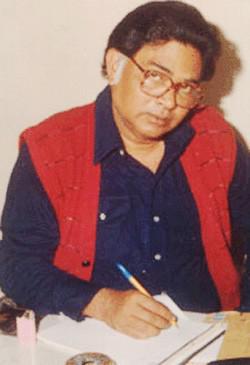
গাড়িতে যেতে যেতে অমিত বলল, ‘তোমাদের আর্টস পেজটায় এইসব বিষয়গুলো সত্যিই marvelous. Like what you did with Ravi Shankar. And now S.P. আমাদের পেপারেও এরকম কিছু করা দরকার।’
বললাম, ‘সেটা তুমিও শুরু কর তাহলে।’
অমিত ফের একটা অস্ফুট আর্তি ছড়াল, ‘তার আগে তো আমাদেরও একটা অভীক সরকার চাই।’
ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে আমাদের গাড়ি যখন শচীনদেবের বাড়ির সামনে দাঁড়াল ঘড়িতে দেখলাম কাঁটায় কাঁটায় চার। না বলে পারলাম না, ‘এটা কর্তার চায়ের টাইম।’
শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।


























One Response
প্রত্যেকটা লেখা একেকটা বসরাই মুক্তো। পুরো হার টার অপেক্ষায় আছি অধীর আগ্রহে।