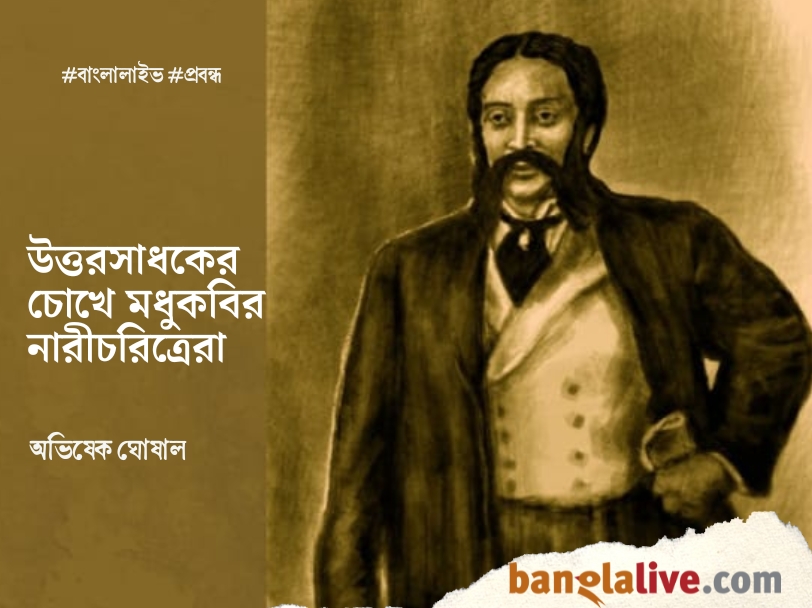মাইকেল মধুসূদন দত্তের (Michael Madhusudan Dutta) ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ আপাতভাবে ভারতীয় হিন্দু পুরাণ ও মহাকাব্যের নারীর জবানি হলেও, এর অন্তরে সমসময়ের অন্দরমহলের ছায়া স্পষ্ট। হিন্দু পুরাণ আর মহাকাব্যের পরিচিত, স্বল্প পরিচিত, প্রায় অপরিচিত নায়িকাদের চিঠির আকারে তৈরি এই কাব্যের কাল্পনিক চিঠিগুলোর পরতে পরতে থাকে অভিযোগ, আকুতি, প্রশ্ন। প্রশ্ন পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে, অভিযোগ পুরুষের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে। বোঝাই যায়, এইসব বয়ান নিছক পৌরাণিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে রয়ে গেছে প্রচলনের বিপ্রতীপ এক সুর। পুরাণ-মহাকাব্যের আদল তার বহিরঙ্গে, অন্তরে তা প্রতিফলিত করছে উনিশ শতকের অন্তপুরকে। আদি মহাকাব্যে ‘উপেক্ষিতা’র যে দিকগুলো ব্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা হয়তো ছিল, সেইসব অনালোচিত দিকের উপরেই আলো ফেললেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’-তে। (Michael Madhusudan Dutta)১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত এই কাব্যে শকুন্তলা, কৈকেয়ী, দ্রৌপদী বা জনা চিঠি লেখেন তাঁদের স্বামীকে। প্রশ্ন করেন। বিদ্রূপ করতেও পিছপা হন না। রুক্মিণী পত্র পাঠান দ্বারকানাথ কৃষ্ণকে, স্বেচ্ছায় হরণ প্রার্থনা করে। বৃহস্পতির শিষ্য সোমদেব, চন্দ্রের রূপে মুগ্ধ গুরুপত্নী তারা, সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে শারীরিক আশ্লেষ ব্যক্ত করেন পুত্রপ্রতিমের কাছে। আঙ্গিকের অভিনবত্বে, বক্তব্যের সাহসিকতায় এই পত্রকাব্য সমসময়ে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে এর ‘উত্তর’ অংশের একটি ধারাই সেই সময় তৈরী হয়ে যায়। মধুসূদনের এই ছাঁদ অনুসরণ করে বীরাঙ্গনা রচনার বছর দশেক পর থেকেই শুরু হয় ‘উত্তর’-বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য রচনার চল। প্রত্যুত্তর কাব্য হিসেবে কখনও তাতে ধরা থাকে মূল কাব্যে অভিযুক্ত পুরুষের আত্মপক্ষ সমর্থনের নজির। কখনও অনুসারী কাব্যে মেলে অন্য কোনও মহাকাব্যিক নারী চরিত্রের বক্তব্য। সেই কাব্যধারাও মুখ্যত পত্রকাব্য, মূলত অমিত্রাক্ষরই তাদেরও আধার। (Michael Madhusudan Dutta)
উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যখন বীরাঙ্গনা রচিত হয়, বাংলার বুদ্ধিজীবী মহল তখন সংস্কার আন্দোলনের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত। সামাজিক ও পারিবারিক পরিসরে নারীর অবস্থান নিয়ে বক্তব্য রাখছেন প্রায় সকল অগ্রণী চিন্তক। এই পরিস্থিতিতে বীরাঙ্গনা কাব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টেক্সট। আর বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্যের ধারাও সেই হিসেবে সমান প্রয়োজনীয়। মাইকেলের জন্মদিনে, আজ মূল বীরাঙ্গনার পাশাপাশি আমরা আলোচনার চেষ্টা করব তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর প্রকাশিত একটি অনুসারী কাব্য নিয়ে, যার নাম ‘অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা’। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ সেন এই কাব্য লেখেন। অমিত্রাক্ষরে রচিত চারটি পত্রের সমাহার এই অনুসারী বীরাঙ্গনা কাব্য বেশ কয়েকটি কারণে প্রণিধানযোগ্য। (Michael Madhusudan Dutta)
এই কাব্যের প্রথম পত্রটি ‘দশরথের প্রতি কৈকেয়ী’। মাইকেলের বীরাঙ্গনার চতুর্থ পত্র, যেখানে কেকয়ী, রাজা দশরথকে তীব্র আক্রমণ করেন রামরাজ্য সংস্থাপন উদ্যোগের প্রতিক্রিয়ায়, সেখানে দেবেন্দ্রনাথের কৈকেয়ী স্বামীর আচরণে ব্যথিত হয়েও তাঁকে আক্রমণ থেকে বিরত থাকেন। বীরাঙ্গনার কেকয়ীর দ্রোহ, ‘অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা’র কৈকেয়ীতে রীতিমতো প্রশমিত। কেকয়ী যেখানে স্বামী দশরথের কৌশল্যার প্রতি অতিরিক্ত ও অযথা আসক্তিকে কটাক্ষ করেন, সূর্যবংশী রঘুকুলপতির চরিত্রগত দুর্বলতা বারবার তাঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়, পঞ্চাশ বছর পর দেবেন সেনের কৈকেয়ী কিন্তু সপত্নীর অনন্ত যৌবন, জরাহীন আয়ু, এমনকি কৌশল্যার ‘পীন পয়োধরে চির লাবণ্য’ পর্যন্ত চেয়ে বসেন ঈশ্বরের কাছে। এই সহনশীলতা আপাতভাবে মাইকেলের বিপরীত। এই সহিষ্ণুতা ভারতীয় দাম্পত্যের চিরাচরিত ধারণার সঙ্গে বেশ খাপ খায়। দেবেন্দ্রনাথের কৈকেয়ী যখন বলেন,
”গালি দাও, কর ঘৃণা, বক্ষে কর পদাঘাত
হে স্বামীন, তবু! কৌস্তুভরতন সম বুকে
লব পাতি!”
তখন বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারীর অবস্থান ও অনুভূতি প্রশ্নে কিঞ্চিৎ দ্বন্দ্বে থাকা এক কবির দেখা মেলে, যিনি মাইকেলের নায়িকার সরব প্রশ্নের ব্যাপারটি নিয়েও হয়তো তেমন স্বস্তিতে ছিলেন না। দুই কবিরই কৈকেয়ী তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন স্বামী, তথা রাজা দশরথের প্রতি তীব্র অভিমানের অনুভূতি থেকে। মাইকেলের কেকয়ী যেখানে এক অসহ্য প্রবঞ্চনার বোধে অপমানিত, পঞ্চাশ বছর পর সেই একই অনুভূতির প্রকাশে দেবেন্দ্রনাথের কৈকেয়ী এতো মৃদু কেন? এর উত্তর নিহিত কবিচরিত্রের পার্থক্যে, সময়ের অভিঘাতও দায়ী বইকি। আর শুধু স্ত্রী হিসেবেই তো নয়, একজন প্রজা হিসেবেও কেকয়ী যে প্রশ্নটি তোলেন, তা স্বামী দশরথকে যতটা না অভিযুক্ত করে, তার চেয়ে অনেক বেশি ‘রঘুকুলপতি’কে অপমানে উদ্যত হয়। মাইকেল (Michael Madhusudan Dutta) তাঁর বীরাঙ্গনার বকলমে লেখেন —
‘পথিকে গৃহস্থে রাজে কাঙালে তাপসে
যেখানে যাহারে পাবো, কব তার কাছে,
পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি।’
তখন অভিযোগের তীর স্পষ্টতই তাক করা থাকে দশরথের ‘রঘুকুলপতি’ পরিচয়ের দিকে। কেকয়ীর প্রচার উদ্দিষ্টের তালিকায় রাজা ও কাঙালের সহাবস্থান, তাঁর অ্যাজেন্ডার একমাত্রিক প্রকৃতিকেই দর্শায়, প্রচার বিষয়ের পিনদ্ধতাই এতে প্রতীত হয়। আর প্রায় একই ভঙ্গিতে দেবেন্দ্রনাথ যখন লেখেন,
”হরিদ্বারে, হৃষীকেশে, কাশীতে, পুষ্করে
নৈমিষ অরণ্যে, দূর বদরিকাশ্রমে।
ঋষিমন্ডলীর মাঝে উঠিবে এ প্রশ্ন
‘ভূমন্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ কোন্ মহামতি?’
আমি(কৈকেয়ী) দিব সদুত্তর ত্রিশুল ঘুরায়ে,
‘অযোধ্যার পতি, দেব, অযোধ্যার পতি!’ ”
তখন, ‘পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি’র ‘ভূমন্ডলে ধর্ম্মপ্রাণ’ মহামতি হয়ে ওঠার অর্ধশতকীয় প্রকল্পটি কিছুটা অবাক করে বইকি। দেবেন্দ্রনাথের ‘দশরথের প্রতি কৈকেয়ী’ যেন মাইকেলের কেকয়ীর একটি সচেতন সাবধানী অ্যান্টিডোট, আর এখানেই এই ‘উত্তর’ কাব্যের ধারা মূল কাব্যের নতুনতর পাঠের চেষ্টায় অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। (Michael Madhusudan Dutta)
‘অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা’র তৃতীয় পত্র ‘শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জা’। এই পত্র প্রত্যক্ষত মাইকেলের কোনো বীরাঙ্গনা পত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু এক আশ্চর্য সম্পর্কসূত্রে এটি বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্তত দু’টি পত্রের সঙ্গে আবদ্ধ, যে সম্পর্ক বেশ চমকে দেওয়ার মতো। কংসের দাসী কুব্জা ছিলেন ত্রিবক্রা। অর্থাৎ তাঁর দেহ তিনভাগে বাঁকা। ‘কুরূপা’ কুব্জা স্বামী পরিত্যক্তা, এমনকি বারবণিতা হিসেবেও প্রত্যাখ্যাতা, কারণ তাঁর দেহবিকৃতি। কৃষ্ণকে তিনি একমনে কামনা করেন, আর কৃষ্ণও তাঁকে কৃপা ক’রে সুদর্শন তন্বীতে রূপান্তরিত করলে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হন। এর নানান বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যা আছে, আপাতত সেসবের প্রয়োজন আমাদের নেই। (Michael Madhusudan Dutta)
কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কুব্জার পত্রটি এই মিলনের পরবর্তী প্রতীক্ষা নিয়ে লেখা। যে অপেক্ষা শকুন্তলায়, যে অপেক্ষা প্রোষিতভর্তৃকা দ্রৌপদীর, সেই একইরকম অপেক্ষা কুব্জারও। এই শ্রীকৃষ্ণই দ্বারকানাথ হিসেবে রুক্মিণীর চিঠির উদ্দিষ্ট বহুপঠিত বীরাঙ্গনা কাব্যে। আবার, ‘উত্তর’ পত্রের ধারায় আরেকটি খুব জরুরি কিন্তু অধুনাবিস্মৃত টেক্সট, দেনুড় থেকে প্রকাশিত শ্রী অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর ‘পত্রাষ্টক কাব্য’র (১৮৮৫ খৃ.) প্রথম পত্রটিও শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করেই লেখা। প্রেরকের নাম রাধা। ‘শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধা’ পত্রটিতে প্রথম থেকেই কৃষ্ণকে মানিনী নায়িকা ‘কুব্জাবিলাসী’ ব’লে অভিহিত করেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন হয়তো পড়েছিলেন ‘পত্রাষ্টক কাব্য’। আর তাই মাইকেল থেকে অম্বিকাচরণ হয়ে দেবেন সেন অবধি এক কৃষ্ণকেন্দ্রিক পত্রালাপের যাত্রা আমরা দেখতে পাই। (Michael Madhusudan Dutta)
বোঝাই যাচ্ছে, ‘শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জা’, ‘অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা’র এই পত্রটির সঙ্গে যে দু’টি বীরাঙ্গনা পত্রের সম্পর্ক রয়েছে বলেছিলাম, তার একটি ‘দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী’, অন্যটি লক্ষ্মণকে লেখা। রামানুজ লক্ষ্মণ। তাঁর উদাসীন সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে রাবণ ভগ্নী শূর্পনখা পত্র লেখেন তাঁকে। মাইকেল এই পত্রের শুরুতেই বাল্মীকির শূর্পনখার বিকটদর্শন সংস্কার পাঠকমন থেকে দূরীভূত করার আবেদন জানিয়েছেন। শূর্পনখা এই পত্রে অসম্ভব প্যাশনেট এবং সমর্পিত। এখন কোন সূত্রে এই পত্র দেবেন সেনের কুব্জা পত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত? তার উত্তর পুরাণে ও মহাকাব্যে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে কুব্জা পূর্বজন্মে ছিলেন রাবণভগিনী শূর্পনখা। অদ্ভুত রামায়ণের আখ্যান অনুসারেও রামচন্দ্রকে কামনা করার অপরাধে সীতার মাধ্যমে অভিশপ্ত হন তিনি। পরজন্মে তাঁর দেহ ত্রিভঙ্গে বেঁকে যায়। (Michael Madhusudan Dutta)
দেবেন সেনের এই কুব্জা পত্রটিতে তার ফলে মিশে আছে মাইকেলের রুক্মিণী পত্রের আকাঙ্ক্ষা, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর ‘পত্রাষ্টক কাব্য’র রাধার শ্লেষ। আবার অন্য এক সূত্রে লক্ষ্মণকে লেখা শূর্পনখার পত্র, সেই অসামান্য অপৌরাণিকীকরণের সূত্রে দেবেন্দ্রনাথও একটি মানবিক পত্র রচনা করলেন, যাতে ধরা রইলো ‘সাধারণী রতি’র বশবর্তী ত্রিবক্রার কৃষ্ণ সান্নিধ্যের আকুতি। (Michael Madhusudan Dutta)
যখন দেখি, ‘অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা’ কাব্যের শেষ পত্রটিও লক্ষ্মণকে লেখা ঊর্মিলার চিঠি, তখন আসলে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার হদিশ পাই। এভাবেই পঞ্চাশ বছর পরে লেখা একটি অনুসারী কাব্য ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’কেই খানিক অন্যভাবে পড়তে আমাদের সহায়তা করে। কবিপ্রতিভায় দেবেন্দ্রনাথ সেন মাইকেলের সঙ্গে আদৌ তুলনীয় কি না, সেই প্রশ্ন এক্ষেত্রে গৌণ। প্রধান আগ্রহের বিষয় একটি প্রবণতা, একটি বহুস্তরীয় পরিগ্রহণের পরত সরিয়ে সরিয়ে দেখা, যে দেখা আদতে মধুসূদনকেই নতুন ভাবে পড়তে, বুঝতে প্রাণিত করে। মাইকেলের জন্মদিনে এও এক ধরণের গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোই। (Michael Madhusudan Dutta)
অভিষেক ঘোষাল (জন্ম ১৯৮৭) প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পাঠ সম্পূর্ণ ক'রে বর্তমানে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপনা করেন। এর আগে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাংলা বিভাগে পড়িয়েছেন। প্রাগাধুনিক সাহিত্য ও উনিশ শতকের বঙ্গীয় সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহী।