মনে পড়ে যায় সায়নের— সেবারেও এই গ্রামে পা রাখার পরেই কেউ যেন তাকে বলেছিল একবার পুজো দিয়ে যেতে। তখন আরও গরিব ছিল এই গ্রাম। এখন তো অনেক ভালো দেখছে চারপাশের অবস্থা। এবার অবিশ্যি সীমাকে বলাই আছে, আগেভাগে গিয়ে পুজোটা দিয়ে দেবার জন্য। কে জানে কীসের থেকে কী হয়! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি, জীবনদর্শন সবকিছুই যেন বদলাতে শুরু করে। ধর্মে মতি হল বুঝি তার! ভেবে নিজের মনেই হাসে সায়ন।
সীমা ডালা কিনে মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে ঢুকলে সায়ন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মন্দিরের দিকে। মৌলীক্ষা মায়ের মন্দিরটি বাংলার দোচালা রীতিতে তৈরি। সে ছবি তোলে একের পর এক। সেই সঙ্গে টুক করে গর্ভগৃহে ঢুকে মোবাইল ক্যামেরাতে দেবীমূর্তিরও কয়েকটা ছবি নেয় পুরোহিতের সম্মতি নিয়ে। সীমা পুরোহিতের সঙ্গে তখন মায়ের পায়ে জবা ফুল চড়াতে ব্যস্ত।
বাইরে বেরিয়ে ছিদামের দিকে মনোযোগ দেয় সায়ন, “হ্যাঁ রে, তুই মৌলীক্ষা নামের মানে জানিস?” ইতিমধ্যে সীমাও এসে পড়েছে পুজো দিয়ে।
ছিদাম বলে, “জানি তো। দিদিমণি পুজো দিয়ে এলে একেবারে বলতাম। মৌলি মানে মাথা আর ঈক্ষা মানে দেখা। সেই যে ইশকুলে বাংলা ব্যাকরণে পড়েছি ই-কারের পরে ঈ-কার থাকলে সন্ধি করে ঈ হয়। মায়ের শুধু মৌলি মানে মাথাটাই দেখা যায় কী না, তাই অমন নাম।

সায়ন হেসে ফেলে ছিদামের কথায়। বলে, “বাহ! খুব বুদ্ধি তো তোর! পড়াশোনায় মন দে। ক্লাস এইট মানেই মাধ্যমিকের প্রস্তুতি কিন্তু। একদম ফাঁকি দিবি না। তা ইনি কোন দেবী? কালী তো নয়। জিভ বের করে নেই। আবার দুর্গাও না। তবে?”
ছিদাম জানায়, ইনি মলুটী রাজবংশের কুলদেবী। সিংহবাহিনী দুর্গা।
সায়ন বলে, “দেখতে কিন্তু দুর্গার মত একেবারেই নয়।”
সীমা অবশ্য আসার সময় নেট সার্চ করে দেখেছিল কী সব বৌদ্ধযুগের কানেকশন আছে এই দেবীমূর্তির সঙ্গে। মলুটীর দেবী তার মানে নির্ঘাত বৌদ্ধযানি তান্ত্রিকদের পূজিত মূর্তি! সায়ন দুয়ে দুয়ে চার করে।
“তোর হবে, বুঝলি!” সায়ন বলে ছিদামকে।
ছিদাম তো অবাক, বলে “কী হবে? আমি ইশকুলের পড়া আর নেপালদাদুর কাছে যাওয়া, এই নিয়েই থাকি। কেবল ছুটির দিনে গাইডগিরি করি। দুটো পয়সা আসে, মায়ের হাতে তুলে দিই। আমার দিদির খুব ইচ্ছে একটা স্মার্ট ফোন কেনার। দিদি আমাকে পড়ায়। তাই দিদিকে একদিন সারপ্রাইজ দেব ভেবেছি। আমাদের মলুটী দেব-গ্রাম। দেবীর ইচ্ছে হলে ঠিক পারব।”
সায়ন বলে, “বাহ! রোজ অংক করিস তো? তোর নাম্বার আছে? যোগাযোগ রাখবি আমার সঙ্গে। অংক, বিজ্ঞান এসবে কোনও সাহায্য লাগলে জানাবি। আমরা দুজনেই স্কুল টিচার। ভিডিও কলে তোকে বুঝিয়ে দেব বিষয়টা।”
ছিদাম বলে, “আমার তো হেব্বি ভালো লাগে অংক করতে, কিন্তু উত্তর না মিললে খুব রাগ হয়। তখন দিদি বলে দেয়। দিদি না পারলে ইশকুলের স্যারকে দেখাই। এবার তাহলে আপনাকেই ডিসটাপ করব।”
“আরে না না। রাতের দিকে ফোন করবি।” এই বলে সায়ন পকেট থেকে কাগজ বের করে ওদের মোবাইল নাম্বার দুটো লিখে দেয় ছিদামকে।
সায়ন দেখে আর ভাবে— অরণ্য লুটেপুটে যেন দারিদ্র্য গিলে নিচ্ছে আর মানুষও পেটের প্রতিশোধ নিতে দেদার গাছ কাটছে জ্বালানির জন্য। অথচ অরণ্যের দয়াতেই দিনযাপন করছে তারা সেখানে।

“তা এখানে গ্রামের লোকের চলে কীভাবে রে?”
ছিদাম বলে, “কী আবার? চাষবাস আর সামান্য ব্যবসাপাতি।”
“তোর বাবা কী করেন?” সীমা প্রশ্ন করে।
“আমার বাবা তো নেই। ভ্যান গাড়ি চালাত। একবার ভ্যানে ইট আনতে গিয়ে ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেছে। আমি তখন খুব ছোট। দিদির মনে আছে। আমার তো মনেও পড়ে না বাবার মুখ।” ছিদাম বলে।
খুব কষ্ট পায় ওরা ছিদামের কথা শুনে। কিছুটা ইতস্তত করে সীমা জিজ্ঞাসা করে “তাহলে তোদের চলে কী করে?”
“পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে দিদি আদিবাসী গ্রামে হাতের কাজ শিখে সব জিনিস বানায়। দু’চার টাকার বিক্রি করে এখানকার উৎসবে, মেলায়। মা চাষের কাজ করে। আমি গাইড হয়েছি। এভাবেই চলে আর কী! চাল, ডাল, ডিম কিনতে হয় না আমাদের। হাঁস, মুরগি, ছাগল আছে ক’টা। দুটো গরুও আছে। মা দুধ বিক্রি করে। আমাদের ঘরটা বাবা বানিয়ে গেছিল তাই। আমরা লোক তো মোটে তিনজন বাবু। কোনওমতে ঠিকঠাক চলে যায় মা মৌলীক্ষার দয়ায়।”
সায়নরা ঘুরে ঘুরে মন্দির চত্বর দেখে।
ছিদাম বলে, “মৌলীক্ষা মন্দিরের সামনে ওই যে শিবমন্দিরটা দেখলেন ওটা রাজা রাখড়চন্দ্রের বানানো। এখানকার সব রাজারা তখন নামের আগে ‘রাজা’ লিখত। মুসলমানরা রাজা হবার পরেও ‘রাজা’ লিখত। তারপর সেটা ‘বাবু’ হয়ে যায়।”
সায়ন বলে, “তা এই রাজা রাখড়চন্দ্রের নামেই কি লাভপুর যাওয়ার পথে রাখড়েশ্বর শিব মন্দির? আমরা গিয়েছিলাম সেবার।”
ছিদাম বলে “তা তো জানি না বাবু। তবে এই রাখড়চন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুটো অলৌকিক গল্প। প্রমাণও আছে তার।”
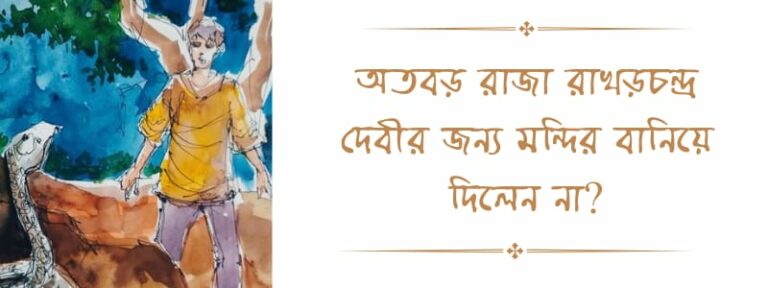
শিবমন্দিরের সামনের উপর অংশে রাজার নাম এবং মন্দির নির্মাণের সময়ের উল্লেখ আছে। ছিদামের কথা শুনে সায়ন ছবি তুলে নেয়।
“কেমন সেই অলৌকিক গল্প? শোনা দিকিনি আমাদের।” সীমা বলে ওঠে।
ছিদাম শুরু করে—
“এই গল্প মলুটীর পাশের গ্রাম মাসড়ার পার্বতী নিয়ে। নিমি বুড়ির গল্প। নিমিবুড়ি খুব ঠাকুরদেবতা করত। একদিন রাতে এক দেবীর স্বপ্ন পেল সে। স্বপ্নে দেবী তাকে বললেন- ‘আমি এই পুকুরে পড়ে রয়েছি, আমাকে তুলে প্রতিষ্ঠা কর এখুনি, আর আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিপদে বলিদান দিবি কিন্তু’…
নিমিবুড়ি নিজে তো খুব গরিব! সে কী করে আর বলিদানের যোগাড়যন্ত্র করবে? তাই মাসড়া মহালের জমিদার রাজা রাখড়চন্দ্রকে গিয়ে নিমিবুড়ি তার স্বপ্নের কথা জানালো। রাজা রাখড়চন্দ্র তো শোনামাত্রই মাসড়ার সুঁড়িপুকুর থেকে দেবীকে তুলে ঘাটে নিয়ে আসতে বলেন। তবে দেবীর মূর্তি ছিল প্রায় গোলাকার একটি পাথর। তার দু’পাশে দুটি ফণা তোলা সাপ।”
উত্তেজিত গলায় সীমা বলে, “অতএব এ আমার তিন নম্বর কানেকশন। এই দেবী তো তবে পার্বতী নয়। মনসা রে!”
ছিদাম বলে, “শুনবেন তো আমার কথা—
নিমিবুড়িই নিজের হাতে দেবীকে তুলে নিয়ে প্রথমে নিজের মাটির ঘরে রাখে। কিন্তু সেই ঘরে আগুন লেগে যায় আর মাটির ঘর ভেঙে পড়ে যায়।”
সীমা বলে, “তার মানে দেবীর ইচ্ছে মাটির ঘর নয়, মন্দির বানানো হোক। তাই তো?”
“না না তেমন নয়। শুনুন না পুরোটা! আগুন লেগে সেই পাথরের দেবী মূর্তিরও অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। মাসড়ার সুঁড়িপুকুরের ঘাটেই দেবীর প্রথম পুজো হয়েছিল। তারপর নিমিবুড়ির ওপর পার্বতী মা ভর করলেন। দেবী ওইখানেই থাকবেন বললেন। তাই আরেকটা মাটির ঘর বানিয়ে সেখানেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হল।”
সায়ন তো অবাক, “অতবড় রাজা রাখড়চন্দ্র দেবীর জন্য মন্দির বানিয়ে দিলেন না?”
“কে জানে! মায়ের ইচ্ছে বলেই হয়ত!” ছিদাম বলে।

“সে আমলে গ্রামে-গঞ্জে যখন ডাক্তার, ওষুধপাতি কিছুই ছিল না তখন মন্দিরে, দেবীর থানে হত্যে দেওয়া, তন্ত্র-মন্ত্র, জলপড়া এসবেই ছিল মানুষের বিশ্বাস। মহামারী হলে সব লোকালয় খালি হয়ে যেত। লোকে বলত মড়ক লেগেছে। মাসড়ার পার্বতী মায়ের পুজো করেই নিস্তার মিলত মানুষের। তিনি মড়ক থামিয়ে দিতেন তাই মাসড়ার পার্বতী মাকে ‘মোড়কি পার্বতী’ বলি আমরা। আমাদের অসুখ করলেও মা মানত করে। সেরে উঠলে পুজো দেয়…”
ছিদামের কথার সূত্র ধরেই সীমা আবারও বলে, “তবে তুই যা বললি তাতে আমার মনে হয় এই পার্বতী কিন্তু নাগদেবী মনসা।”
সায়ন একটু চমকে ওঠে। পুরনো অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। সবার সামনে সবকিছু শেয়ার করা যায় না সবসময়। সীমাকেও এসব বলেনি সে কোনওদিন। সীমা শুধুই জানত স্কুলের চাকরি পাওয়ার আগে সায়ন সামান্য একটা সেলসের কাজ করত।
এমন সব গল্প অনেকদিন আগে শুনেছিল সায়ন। রোগ-ভোগ হলে গ্রামের মানুষের একমাত্র আশা ভরসার জায়গা হল সতীমায়ের ভর, জলপড়া, তাবিচ, কবচ, মাদুলি, মানসিক আর মানিকপীরের ঝেড়ে দেওয়া অথবা নদীতে স্নান করে ভিজে কাপড়ে দণ্ডি কাটা। এই স্কুলের চাকরিটা পাওয়ার আগে হন্যে হয়ে সায়নকে ঘুরতে হত অফিসের ট্যুরে— সামান্য একটা সেলসের কাজে। সেই সূত্রেই বিহার, ওড়িশা, বাংলার জঙ্গুলে অরণ্যময়তার সঙ্গে তার পরিচয় বহুদিনের।
ওষুধ কোম্পানির হয়ে প্রোডাক্ট বেচতে হত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। তখন সে সব প্রোডাক্টের ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে এসবই মুখস্থ বলতে হত তাকে। কোম্পানির ইউএসপি ছিল সেটাই। ঠাকুরের থানে হত্যে দেওয়া, দণ্ডি কাটা, উপোস— এসবে রোগ সারে না বুঝলে? রোগ হলে ওষুধ খেতে হয়। নয়ত রোগ বেড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়। অল্প থাকতেই ওষুধ খেতে হবে… এসব ছিল সায়নের বাঁধা বুলি। পিঠে থাকত বুকজ্বালা, ভেদবমি, জ্বর, আন্ত্রিক, অম্লশূলের ট্যাবলেট আর মিক্সচার। ওষুধ ফেরি করত সে গ্রাম থেকে গ্রামে। গ্রামের এ মোড়ে একটা ডাক্তারের ডিসপেনসারি তো আবার খানিক জঙ্গল পেরিয়ে পাশের গ্রামে একটা টিমটিম করে জ্বলা ওষুধের দোকান।

সেবার ভরা শ্রাবণের বৃষ্টির দিনে খালবিল সব টইটুম্বুর। ঝাড়খণ্ড তখনও বিহারে, মানে আলাদা রাজ্য হয়নি। কিছু বোঝবার আগেই হঠাৎ করে তাকে সাপে কেটেছিল। অবিশ্যি ভয়ানক কিছু ঘটনা ঘটেনি, কারণ সাপটা বিষাক্ত ছিল না। নয়ত সায়ন আজ এখানে থাকত না। ঘটনাটা ঘটেছিল দুমকা জেলার আশেপাশের কোনও রাস্তায়। হয়ত বা সেই রাস্তা মলুটী গ্রামের খুব কাছেই। তখন মন্দির, মসজিদ, গির্জা কিছু নিয়েই এত চর্চা করত না সায়ন। আগ্রহও ছিল না এসবে। শুধু একটা পার্মানেন্ট চাকরি আর মাস গেলে চলনসই মোটা মাইনের স্বপ্নে বিভোর থাকত। অংকে সে বরাবরই ভালো, তাই ছুটির দিনে প্রচুর টিউশানি ছিল হাতের পাঁচ। বসে থাকেনি সে কোনওদিন। তারপর তো তলে তলে স্কুল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি। চাকরিটা পেয়ে যাওয়ার পর থেকে সব ছেড়েছুড়ে শুধু চাকরি আর বেড়ানোয় মজে আছে সে। সংসারে টাকা রোজগারের চাপ না থাকলে বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এসব ঘাঁটতে কার না ভালো লাগে!
তবে সীমার এই সাপ নিয়ে আদিখ্যেতাটা মোটেও পছন্দের নয় সায়নের। সাপেদের বিশ্বাস নেই। তারা সর্বকালীন সিনেমার খলনায়কের মতো। এমনটাই ভাবে সে এখনও। সীমা অবিশ্যি জানেও না বিয়ের আগে সায়নকে সাপে কাটার এই গল্প।
অলংকরণ: শুভ্রনীল ঘোষ
*পরের পর্ব প্রকাশ পাবে ৫ এপ্রিল, ২০২৩
রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।


























One Response
হচ্ছে, আগ্রহ বেড়েই চলেছে।বুঝতে চাইছি ইতিহাসের সঙ্গে এই কাহিনীর যোগসূত্র ।আগে আর একটি মাত্র পর্ব । এর আগের পর্বে কিছু জানতে চেয়েছি, লেখক যদি উত্তর দেন খুব ভালো লাগবে