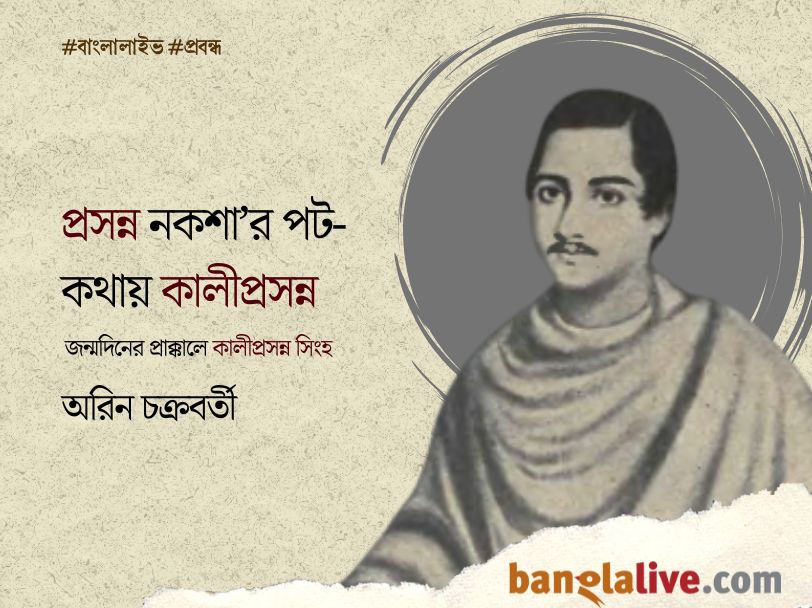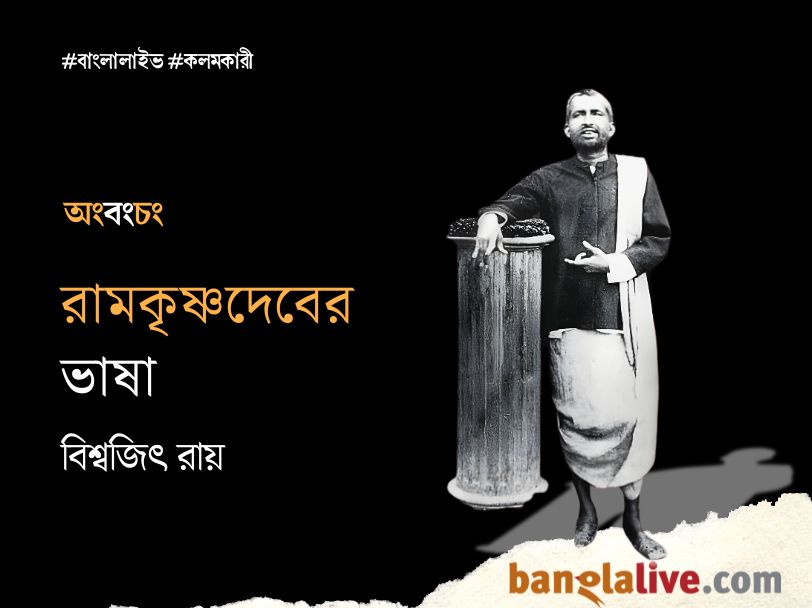পার্থজিৎ চন্দ
 ডিসেম্বর ১৯৯৬ (অগ্রহায়ণ ১৪০৩), কবিতা পাক্ষিক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একটি কবিতার বই, ‘ঋতুচক্র’। এই কাব্যগ্রন্থের কবি অপরাপর ক্ষেত্রে আসামান্য সব সম্মানের অধিকারী। সুসম্পাদক, চিকিৎসক। জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে প্রখ্যাত গবেষক। কিন্তু বাংলাভাষার নিয়তি এই, তিনি কবি হিসেবে যে-উচ্চতার, সেই পরিমাণে আলোড়ন ওঠেনি তাঁকে নিয়ে। এই প্রজন্মের তরুণ কবিদের কাছে তিনি কতটা পরিচিত নাম সে-নিয়েও সন্দেহ আছে বিস্তর। যদিও এই প্রজন্মের পাঠক বা কবিদের দোষও দেওয়া যায় না তেমন। কারণ তাঁর সমকালই তো তাঁর সম্পর্কে এক ‘সম্ভ্রমভরা’ উদাসীনতা দেখিয়ে ছিল। সম্ভ্রম একটা ছিলই; কিন্তু তাঁর কবিতা নিয়ে ঘাতক উদাসীনতাও ছিল।
ডিসেম্বর ১৯৯৬ (অগ্রহায়ণ ১৪০৩), কবিতা পাক্ষিক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একটি কবিতার বই, ‘ঋতুচক্র’। এই কাব্যগ্রন্থের কবি অপরাপর ক্ষেত্রে আসামান্য সব সম্মানের অধিকারী। সুসম্পাদক, চিকিৎসক। জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে প্রখ্যাত গবেষক। কিন্তু বাংলাভাষার নিয়তি এই, তিনি কবি হিসেবে যে-উচ্চতার, সেই পরিমাণে আলোড়ন ওঠেনি তাঁকে নিয়ে। এই প্রজন্মের তরুণ কবিদের কাছে তিনি কতটা পরিচিত নাম সে-নিয়েও সন্দেহ আছে বিস্তর। যদিও এই প্রজন্মের পাঠক বা কবিদের দোষও দেওয়া যায় না তেমন। কারণ তাঁর সমকালই তো তাঁর সম্পর্কে এক ‘সম্ভ্রমভরা’ উদাসীনতা দেখিয়ে ছিল। সম্ভ্রম একটা ছিলই; কিন্তু তাঁর কবিতা নিয়ে ঘাতক উদাসীনতাও ছিল।
সেই বইটি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই এক পুণ্যের বশে হাতে চলে আসে। একের পর এক কবিতা পড়তে গিয়ে ঘোর আচ্ছন্ন করে ফেলে। বলা ভালো, এই বইটির ঘোর থেকে আমি বেরুতে পারিনি আজও। ১০০ পাতার এই বইটির একটি-দুটি বাদে প্রতিটি কবিতাই ‘টানা গদ্যে’ লেখা। এমন নয় যে এই প্রথম কেউ বাংলা কবিতায় এই প্রকরণটি আনয়ন করলেন। এমনও নয় যে প্রচলিত যে-প্রকরণ আছে ‘টানা গদ্যে’ লেখা কবিতার, সেখান থেকে তিনি খুব উল্লেখযোগ্য কোনও বাঁক নিয়েছিলেন। বলার কথা এই যে এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই উচ্চমানের।
বস্তুনিরীক্ষার পরেও পড়ে থাকে যে-বিশাল এক জগৎ, যে-জগৎ এক উত্তুঙ্গ বোধের দ্বারা জারিত, সেই জগতের সন্ধান পেয়ে যাওয়া একজন কবির দর্শন ও অনুভূতি প্রকাশিত হয় এইভাবে,
এই যে আমি মধুপুরের পাহাড়গুলি খইয়ে ফেলি: জল উঠবে ভাবি। মাটি এবং ভরা বাদল, রক্তমাখা ন্যাতা। সেই শিশুটি জারজ বালক, মাতার অহংকার। বস্তুপিণ্ড গুহার ভিতর, গাধায় ঘোড়ায় জল খেয়েছে, খড় রেখেছে শিশুর উপাধানে। পরিবর্তে অন্য পাহাড়, আমার পাহাড়, ছোটো নদীর ধাক্কা খাওয়া, বর্ষা জলে গৃহস্থের পায়ের কাছে কান্নাকাটি করা ছোটো মেয়ের মতন। বোকা ছেলে, বস্তুগুলি টুকরো টুকরো গুছিয়ে তোল আধো শীতে অন্ধকারে দূরাগত তারার মতন খসে পড়া। (মধুপুর)
কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠবে, অমিমাংসীত একটি প্রশ্ন। বেশ অনেকটা সময় ধরে পাঠক ও সমালোচকদের মধ্যে এই প্রশ্নটি ঘুরপাক খেয়েই চলেছে। কবিতা কি আদৌ ‘টানা গদ্যে’ বা ‘গদ্যের ছন্দে বা চলনে’ লেখা সম্ভব! কবি-পাঠক মহলে এই ফর্মের কবিতা বোঝাতে সচরাচর যে-টার্মটি ব্যবহার করা হয়, সেটি কি অ্যকাডেমিকভাবে সমর্থন পাবার যোগ্য? শুধু ভূমেন্দ্র গুহই নন; তাঁর আগে-পরে এই ফর্মে বেশ উল্লেখ্য সংখ্যায় কবিতা আয়ু পেয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই ফর্মটিকে সাবালক করে গেছেন। গত কয়েক দশকে অরুণ মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল বসু, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, জয় গোস্বামী, রণজিৎ দাশ, জহর সেনমজুমদার, জয়দেব বসু-সহ বেশ কয়েকজন কবি এই ফর্মে অসামান্য সব কবিতা উপহার দিয়েছেন বাংলাভাষাকে। কিন্তু সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি আজও। সত্যিই কি গদ্যকবিতা বলে কিছু হয়? এমন কি কোনও সীমারেখা আছে যেখান থেকে কোনও লেখায় গদ্য ছাপিয়ে এসে কবিতার শরীরে তার চিহ্ন রেখে যায়?
 এখানে দাঁড়িয়ে একটা কথা বার বার মনে হয়। ভাষা ও শিল্পের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সাংঘাতিক এক ফান্ডামেন্টালিজ্ম। ভাষার কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে যে-সামজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি তা নিজের স্বার্থেই এক স্থিতাবস্থার দিকে ঝুঁকে থাকে। লিঙ্গ নির্মাণ, রাষ্ট্রের ধারণা নির্মাণ, শহিদ মনস্তত্বের নির্মাণ থেকে ভাষার ও শিল্পের প্রচলিত ধারাটিকে সুকৌশলে রক্ষা করা একই মুদ্রার দুই পিঠ। genre নামে যেটিকে আখ্যায়িত করা হয়, তা আসলে একটি accepted form-কে মান্যতা দেবার কৌশল। শিল্পের ভিতরে নির্মাণ করে দেওয়া হয় নন্দনতত্ত্বের নির্ধারিত সীমারেখাটিকে। স্মৃতি ও শ্রুতি-নির্ভরতার কারণে কবিতার যে-ফর্ম আমরা দেখতে অভ্যস্ত, আজ কবিতা যখন ব্যক্তিমানুষের একান্ত পাঠের উপকরণ হয়ে উঠেছে তখনও তাকে সেই ফর্মেই দেখার চেষ্টা করা বাতুলতা। শুধু গদ্যকবিতা কেন, অন্য অনেক ফর্মেই কবিতা লিখিত হতে পারে। এমনকী গদ্য ও কবিতার মধ্যে শান্তভাবে শুয়ে থাকা অদৃশ্য সীমারেখাটি মুছে গিয়ে অন্য কোনও ফর্মও তৈরি হতে পারে। হয়েওছে। এই বাংলায় এমন কিছু অসামান্য লেখা হয়েছে যাকে গদ্য ও কবিতা— কোনও একটি genre-য়েই পুরোপুরি ধরা যায় না। যেমন অনুরাধা মহাপাত্রের ‘আমমুকুলের গন্ধ’। এই বইটি যতবার পড়ি স্তব্ধ হয়ে যাই। যেন এক অন্ধ একতারা নিয়ে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে। তার কোথাও যাবার তাড়া নেই। কোথাও পৌঁছোনোর নেই। সারা শরীরে তার অসংখ্য স্নায়ুর কান পেতে থাকা। সে শুষে নিচ্ছে প্রকৃতির সব শব্দ। এই বইটির একটি লেখায় অনুরাধা লিখছেন,
এখানে দাঁড়িয়ে একটা কথা বার বার মনে হয়। ভাষা ও শিল্পের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সাংঘাতিক এক ফান্ডামেন্টালিজ্ম। ভাষার কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে যে-সামজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি তা নিজের স্বার্থেই এক স্থিতাবস্থার দিকে ঝুঁকে থাকে। লিঙ্গ নির্মাণ, রাষ্ট্রের ধারণা নির্মাণ, শহিদ মনস্তত্বের নির্মাণ থেকে ভাষার ও শিল্পের প্রচলিত ধারাটিকে সুকৌশলে রক্ষা করা একই মুদ্রার দুই পিঠ। genre নামে যেটিকে আখ্যায়িত করা হয়, তা আসলে একটি accepted form-কে মান্যতা দেবার কৌশল। শিল্পের ভিতরে নির্মাণ করে দেওয়া হয় নন্দনতত্ত্বের নির্ধারিত সীমারেখাটিকে। স্মৃতি ও শ্রুতি-নির্ভরতার কারণে কবিতার যে-ফর্ম আমরা দেখতে অভ্যস্ত, আজ কবিতা যখন ব্যক্তিমানুষের একান্ত পাঠের উপকরণ হয়ে উঠেছে তখনও তাকে সেই ফর্মেই দেখার চেষ্টা করা বাতুলতা। শুধু গদ্যকবিতা কেন, অন্য অনেক ফর্মেই কবিতা লিখিত হতে পারে। এমনকী গদ্য ও কবিতার মধ্যে শান্তভাবে শুয়ে থাকা অদৃশ্য সীমারেখাটি মুছে গিয়ে অন্য কোনও ফর্মও তৈরি হতে পারে। হয়েওছে। এই বাংলায় এমন কিছু অসামান্য লেখা হয়েছে যাকে গদ্য ও কবিতা— কোনও একটি genre-য়েই পুরোপুরি ধরা যায় না। যেমন অনুরাধা মহাপাত্রের ‘আমমুকুলের গন্ধ’। এই বইটি যতবার পড়ি স্তব্ধ হয়ে যাই। যেন এক অন্ধ একতারা নিয়ে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে। তার কোথাও যাবার তাড়া নেই। কোথাও পৌঁছোনোর নেই। সারা শরীরে তার অসংখ্য স্নায়ুর কান পেতে থাকা। সে শুষে নিচ্ছে প্রকৃতির সব শব্দ। এই বইটির একটি লেখায় অনুরাধা লিখছেন,
শরকলমে খুব সুন্দর লিখতেন আমার ছেলেবেলার মাস্টারমশাই এবং বলতেন আমাদের। কারণ, শরকলমে লেখা প্রকৃতির মতো হবে। আমি কখনো সখনো দুপুরে ও সন্ধ্যায় শরকলমের সন্ধানে শরবনে চলে যেতাম। আর কুবো পাখির কুব কুব ডাক শুনতে শুনতে অন্ধকার হয়ে যেত। মাথায় শাদা কাশের মতো চুল নিয়ে মাস্টারমশাই এখনো বেঁচে আছেন। ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করি, মাস্টারমশাই, আপনি কি জীবনভর প্রকৃতির শান্তি পেয়েছেন?
বইটি বার বার পড়ার পর, একদিন ব্যাক কভারে চোখ পড়তে শুরু হয়েছিল সেই অস্বস্তি। উর্বী প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এই বইটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে মুক্তগদ্যের সংকলন হিসেবেই। এই চিহ্নিতকরণের পর পাঠকের আর তেমন কোনও স্পেস থাকে না, যেখানে সে লেখাটিকে অন্য একটি genre বা নিছক প্রচলিত একটি genre-এর বাইরে বেরিয়ে সেটিকে গ্রহণ করতে পারবে। ব্যক্তি-পাঠকের পাঠ বহু ইন্টারপ্রিটেশনের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু তা বেশিরভাগ সময়েই কনটেন্টের দিকে ঝুঁকে থাকে। একটি ফর্মে লিখিত কোনও টেক্সট (যা প্রকাশের সময়ে নিশ্চিতভাবেই লেখকের অনুমোদিত), সেটিকে অন্য ফর্মে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। উচিৎও নয়। ফলে এখানে পাঠক ভয়াবহভাবে অসহায়। এবং পাঠকের এই অসহায়তাকে জল-হাওয়া দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। রাখা হয় বাণিজ্যের স্বার্থেই। এক অর্থে genre-য়েই যে গদ্যকবিতাকে চিহ্নিত করে দেওয়া, সেটিও এর বাইরে নয়।
কিন্তু কবিতার ইতিহাস তো এইসব নির্মিত ঘেরাটোপ আর মৌলবাদী, মনুবাদী চিন্তাধারণাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবারই ইতিহাস।
সময়ই কবিতার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় নিয়তি। সে নিজেই ব্যুবিট্র্যাপ, বিস্ফোরক পুঁতে রাখা এক অস্তিত্ব। একটি নির্দিষ্ট সময়ের কবিরা সেই সব বিস্ফোরকগুলিতে পেতে দেওয়া জীবন। নিজেদের উড়িয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত। নয়ের দশকও এর ব্যতিক্রম নয়। নয়ের দশক ঠিক একইভাবে ডেসটাইনড, তার নিজের জন্মদাগকে কবিতার শরীরে বুনে দেবার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু, বাংলা কবিতার সব থেকে বেশি ডেসটাইনড দশক হয়তো এই দশকটিই।
দুটি বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, গ্রাম-দিয়ে-শহর ঘেরা ইত্যাদি বাংলা কবিতাকে আলোড়িত করেছে নিশ্চয়। ঐতিহাসিকভাবে তা সত্য। কিন্তু রক্তপাতহীন একটা যুদ্ধপরিস্থিতি, একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ‘এনিমি স্টেট’… ভার্চুয়াল বলে যাকে ডাকতে শুরু করবে মানুষ কিছুদিন পর… তার দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়া পৃথিবী, বাইপোলার পৃথিবীর অবলুপ্তি ও টেলিক্যমুনিকেশন বুম, এ-দশকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেই রেখেছিল। ‘একক মানুষের দর্শন’ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল বোধের জগৎকে।
নয়ের দশকের অত্যন্ত শক্তিশালী কবি শুভাশীষ ভাদুড়ী। শুভাশীষের ‘পয়মন্ত কারুকথাময়’ বইটির অধিকাংশ কবিতাই টানা গদ্যে লেখা। নয়ের দশকে বাংলা কবিতায় প্রবল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছিল বিশ্বায়নের প্রভাব। কিন্তু হাইরাইজের ছায়ার নীচে দানবের মতো খিদে নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে আরেকটা জীবন। সে রূপান্তরের বহিরঙ্গের, তার বাইরে রয়ে গেছে আরেকটা পৃথিবী। সেই পৃথিবীর কথা অসামান্যভাবে লিখে রাখেন শুভাশীষ, গদ্যকবিতার ফর্মে,
শহরের কলতলায় সন্ধে নামে স্প্রাইটের বড়ো বড়ো সবুজ বোতলে। হাতকাটা নাইটি পরা বউদিগুলোর ঘাম-চকচকে মুখ গর্জনতেলে রাঙানো। হাইল্যান্ড এনক্লেভের পার্কিং লটে সূর্যাস্ত মিইয়ে আসে ধীরে। রাতের শহর চট আর কয়্যারম্যাট্রেসে খেলতে শুরু করে। আলো নিবিয়ে পঞ্চু ঘুমুতে যায়। (মহাজীবন-মহাকাল)
কবি রাণা রায়চৌধুরীর ‘অগাস্ট মাসের রাস্তা’-র সবকটি কবিতা টানা গদ্যে লেখা। সংখ্যাচিহ্নিত কবিতাগুলি এক আশ্চর্য স্বগতকথন। এক অর্থে হয়তো সব কবিতাই স্বগতকথন; কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থে রাণা নিজের সঙ্গে নিজে এক নির্জন আলাপে মেতে উঠেছেন। নিজেকে অ্যড্রেস করতে করতে চলেছেন। কাব্যগ্রন্থের ৪৭তম কবিতায় রাণা লিখছেন,
একটা বালিশে মাথা রেখে আমরা দু-জনে শুয়ে আছি। আমি আর আমার ইনহেলার। আমার ইনহেলারের গায়ের রং সবুজ। আর আমার গায়ের রং কালো। আমরা দুই মাতৃহীন বালক এখন একসঙ্গে ঘুমোবো। ইনহেলার আমার পিঠে সুড়সুড়ি দেবে, আমি ইনহেলারের পিঠে গান বুলিয়ে দেব। বাইরে তখন অনেক রাত, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হবে। শিয়াল খুঁজতে বেরোবে তার অবুঝ সন্তানকে।
ইনহেলারের সঙ্গে কবির শ্বাসকষ্ট ও শিয়ালের তার সন্তানের খোঁজে বেরিয়ে পড়া এসে মিশে যাচ্ছে কোথায়। শিয়াল ধূর্ত, অন্তত আমাদের ফেব্লগুলি সে-কথাই বলে। কিন্তু শিয়ালের নিজস্ব কোনও বিষণ্ণতা কি নেই? ‘অবুঝ সন্তান’ কি অবাধ্য কবিজীবন? এসবের থেকেও যেটা পাঠককে তাড়িয়ে বেড়ায় তা হল, এই শিয়াল আসলে কী বা কে? আমাদের নিয়তি? না, মৃত্যু?
হিন্দোল ভট্টাচার্য তার কবিতায় সন্ধান দেয় এক হারানো কলকাতার। হারানোও নয় হয়তো, এই কলকাতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকা আরেক কলকাতা,
ঘামে জমে থাকা পাউডারের গন্ধের ভিতর আছে লক্ষ বছরের যৌনতা। মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে পারো এই কলকাতা শহরে। কয়েক পলকের মধ্যে বদলে যাচ্ছে সব হিসেব। মুখোমুখি হচ্ছে কবি ও কুকুর। সংসার সংসারের সঙ্গে আর প্রেম প্রেমের সঙ্গে হা হা হি হি করতে নিজেদের বেঁচে দিচ্ছে এক আকাশছোঁয়া বিষাদের ভিতর। এবার সহজ হও। (তালপাতার পুথি/৫১)
নয়ের দশকের প্রথম দিকেই যে-কবি নিজের স্বর চিনিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতার নিমগ্ন পাঠককে, তিনি চিরঞ্জীব বসু। অসাধারণ allusion প্রয়োগে চিরঞ্জীব কবিতার ভিতর পাঠককে টেনে আনতে পেরেছিলেন, তৈরি করতে পেরেছিলেন সেই ঘূর্ণি, যা কবিতার সব থেকে বড়ো সম্পদ,
জ্যোৎস্না দেখাবে বলে এ তুমি কোন অন্ধকারে নিয়ে এসে ফেললে আমাকে। আমি এই অনঙ্গ অন্ধকারে হাত দেখি না পা দেখি না… আমি এই অন্ধকারে ছুটে আসা বুলেটের তীব্র গন্ধ পাচ্ছি। হাত দেখি না পা দেখি না তবে কীভাবে বাঁচাব নিজেকে? কীভাবে হাজার নিষেধ না মেনে তোমার সঙ্গে জ্যোৎস্না দেখতে যাব আবার?
আদিগন্ত শস্য খেতের ওপর চাঁদ তার স্তন থেকে ঢেলে দিচ্ছে দুধ— (২৫শে নভেম্বর, ১৯৯৭)
এই কবিতাটি পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে পড়বেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অসামান্য কবিতাটির কথা। কিন্তু চিরঞ্জীব সেই অনুসঙ্গকে একবার মাত্র ছুঁয়ে একটা স্পেস তৈরি করলেন। সেই স্পেসে তিনি স্থাপন করলেন তার হাহাকার। বুলেট গন্ধের কথা আছে কবিতাটিতে। এবং কবিতাটির প্রতিটি শব্দ ছুটে গেছে বুলেটের মতো, এক অব্যর্থ নিশানায়। টানা গদ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে যে-অনন্ত গতির সম্ভাবনা, সেটিকে উন্মোচন করেছেন চিরঞ্জীব।
একটি কবিতার কাছে বার বার কেন ফিরে আসতে হয়, কীসের কারণে দৈব-চুম্বকের মতো সে আচ্ছন্ন করে রাখে আমাদের দিনের পর দিন, সেটির উত্তর লুকিয়ে আছে বিপ্লব চৌধুরীর কবিতার মধ্যে। ‘বৃক্ষ-লোক’ নামক গদ্যকবিতায় বিপ্লব লিখছেন,
সামান্য লোক থেকে কোথাও পৌঁছোতে চাই। যাই নদীর নির্জন তীরে। স্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকেছি আর সন্ধ্যাকাশে ফুটে গেছে তারা। জলে তার প্রতিবিম্ব দেখি।
কখনো নিশ্চল নয় আমার দু-খানি পা। কাদা, রক্তে মাখা। মেঘেরা বৃষ্টি দিলে ধুয়ে যাবে সব। হয়তো, সবুজ পাতা-ই বেরোবে আমার শরীর থেকে। কোনো অরণ্যের বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকব আমি।
একই দশকের দুই কবি, চিরঞ্জীব বসু ও বিপ্লব চৌধুরী। দু-জনেই দু-টি কবিতায় আশ্রয় করেছেন গদ্যকবিতার চলন। একজন একজন্মের সব নীল উগরে দিয়ে শান্ত হতে চেয়েছেন। আরেকজন সব নীল বিষ শুষে বৃক্ষের জীবন ছুঁতে চেয়েছেন। দু-জন আশ্রয় করেছেন দুটি ন্যারেটিভ। মৌল লক্ষণে তারা এক হলেও, গদ্যকবিতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বহুস্তরীয় সম্ভাবনার অন্তত দুটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁরা।
অংশুমান কর নয়ের দশকের সেই কবি যিনি কবিতায় স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন ক্যাজুয়াল অ্যপ্রোচে লেখার কথা। কিন্তু তাঁর ক্যাজুয়াল ভঙ্গি আসলে একটা ক্যামোফ্লেজ। অতি চেনা নানান অনুষঙ্গ ব্যবহার করে মাত্র একটা মোচড়েই একটি কবিতাকে উচ্চতর মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারেন অংশুমান। তার একটি গদ্যকবিতা এই স্বাক্ষর বহন করে চলেছে,
টিমটিমে আলোর নীচে দু-কাপ চা নিয়ে বসে দুই বৃদ্ধ। আলুচাষিদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে তরুণ। সেলুনের বাইরের টুলে যুবাটি উদাসীন বসে। একলা তরুণী কারও প্রতীক্ষায় আছে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝাই করে, ধুলো উড়িয়ে, এসে দাঁড়াল শেষ বাস।
গঞ্জের বাজার। ছোটো। সকলেই সকলকে চেনে। শুধু ওই যে অচেনা লোকটি অন্ধকারের মধ্যে হনহন করে হেঁটে মিলিয়ে যাচ্ছেন, উনি দেবদূত। কিছু পরে মানুষের দুঃখ-কষ্টের ওপর ঝরে পড়বেন হিম হয়ে।
কবিতাটির প্রথম অংশে একটি ছবি এঁকেছেন অংশুমান। খুব চেনা একটি ছবি। কিন্তু, পরের অংশে এসেই কবিতাটির উড়াল শুরু হয়। সেই অচেনা মানুষটির মধ্যে আমরা আবিষ্কার করতে চাই এক শুশ্রূষার আনন্দকে। যে-শুশ্রূষা একদিন মুছিয়ে দেবে আমাদের যাপিত জীবনের সব গ্লানি আর মালিন্যকে।
নয়ের দশকের শেষদিকে লিখতে এসেছিল শোভন পাত্র। গদ্যকবিতার এক বড় বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যে এক কাহিনি বা কাহিনির আদল এঁকে রাখা যায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কবিতা কতদূর কাহিনিকে আশ্রয় দিতে পারে তা নিয়ে। যে-প্রশ্ন গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে উঠে আসে, সেই প্রশ্নের থেকে যে কবিতার অন্যান্য ফর্মও মুক্ত নয়। যদিও গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে সেই কাহিনিকে বুনে দিয়ে কবিতাকে নির্মাণ করা সহজও নয়। শোভন তার ‘বড়োমা’ কবিতায় লিখছে,
…তাকিয়ে ছিলাম জ্যাঠামশাইয়ের দিকে। ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। আমার কাঁধে হাত রেখে বিড়বিড় করে বলে চলেন— অমন কালো, দাঁত উঁচু, কুৎসিত স্ত্রী; পরিচয় দিতে লজ্জা হত তাঁর। রাস্তায় বেরোলে সজোরে হাঁটতেন তিনি, যথেষ্ট তফাতে। আর তাঁকে ধরার জন্য আমার বড়োমাকে প্রায় দৌড়োতে হত। একদিন রাস্তায় পড়ে গিয়ে পা মচকে যায়, উঠে যায় ওই নখ। ততক্ষণে বড়োমার দুই পা গ্রাস করে নিয়েছে চিতার আগুন।
শোভনের এই গদ্যকবিতাটিতে ন্যারেটিভ ঝরঝরে। এক সামান্য মহিলা, যিনি আজীবন সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছেন, পাননি স্বামীর স্বাভাবিক সঙ্গ, তাঁকে গ্রাস করে নিচ্ছে চিতার আগুন। কিন্তু কবিতাটির মধ্যে একটি উল্লেখ, পড়ে গিয়ে নখ উঠে যাওয়ার প্রসঙ্গ, যেটিকে প্রথমবার পড়ার সময়ে মনে হবে সামান্য এক উল্লেখ, সেটিই পাঠককে গ্রাস করবে কবিতাটি শেষ করার পর। নখ উঠে যাবার চিনচিনে ব্যথার পরিসমাপ্তি হল চিতার আগুনে। সব যন্ত্রণার অন্তে লীন হয়ে যাওয়া এক জীবন। কেউ জানবে না সেই যন্ত্রণার কথা, শুধু যে-মানুষটি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন এতদিন, তিনি হয়তো ক্ষতবিক্ষত হবেন দংশনে। বিবেকের কাছে।

পঙ্কজ চক্রবর্তী নয়ের দশকের একটা পর্বে উচ্চমানের সব কবিতা লিখে নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন। শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে যে-গুপ্তটানেল, যেখান দিয়ে অবিরত তাঁদের দু-জনের মধ্যে গোপন সংযোগ বজায় থাকে, সেই টানেলের কথা লিখেছেন পঙ্কজ,
আমি কি তাকে একলব্য বলব? এই পরিচয় খান খান হয়ে পড়ে মধ্যরাতে; মুঠো-ভরতি আলোয় আলোয় পড়ে থাকে গুরুদক্ষিণা। এভাবেই যেকোনো মহৎ শিল্প ভেঙে পড়ে আর আমরা পুরোনো গল্পের সেই বুড়োটাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করি (একলব্য)
গদ্যকবিতায়, কাহিনিকে ক্যামোফ্লেজের স্তরে রেখে কবিতার বিরাট ও অনন্ত পরিসরকে ছুঁয়ে ফেলা সহজ নয়। এই ট্র্যাপিজের খেলায় সামান্য বিচ্যুতি কাহিনিকেই সামনে এনে ফেলতে পারে। অতি-দক্ষ কবি ছাড়া সেই স্তরটিকে অতিক্রম করতে পারেন না অনেকেই। এই বিরল দক্ষতা দেখা যায় কবি প্রদীপ সিংহের কবিতাতে। প্রতি রবিবারের অতি চেনা একটি দৃশ্যের মধ্যে থেকে প্রদীপ তুলে আনেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিভেদ দর্শনের বিভাকে,
রান্নার এই সূক্ষ্মতম ব্যবহারিক দিকটি প্রতিদিন নজর এড়িয়ে যায়, কারণ আমার নজর সবসময় সুবিধা গ্রহণের দিকে ঝুঁকে থাকে। তবু কোনো এক শান্ত শ্লথ দিনে দৃষ্টিবান হয়ে উঠি। দেখি গৃহকর্মনিপুণতা— বিশুদ্ধ নিপুণতাকে ছাড়িয়ে চলে যায় কোনো এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিভেদ দর্শেনের দিকে। (চা)
ঠিক এরকমই একটা ‘গতকাল’-কে দেখেছে শ্রীজাত। দেখেছে প্রতিটা দিন যাপনের গায়ে লেগে থাকা গ্লানির শ্যাওলার ছোপ। প্রায় ‘শূন্য’ থেকে কবিতাটি এসে আমাদের আচ্ছন্ন করে দেয়,
আবার হিসি করলাম, চোখে-মুখে জল দিলাম। তারপর জামাকাপড় পালটে বেরোলাম। অটো ধরে অনির্বাণের বাড়ি গেলাম। অনির্বাণ ছিল না। বসলাম। কিছু পরে অনির্বাণ ফিরল। দু-জনে মুড়িমাখা খেলাম। তারপর চা খেলাম। অনির্বাণ নিজের কিছু কবিতা শোনাল। আমিও আমার কিছু কবিতা শোনালাম। তারপর এদিক-ওদিক কিছু কথা হল। আটটা নাগাদ আবার চা খেলাম। ন-টার সময়ে বাড়ি ফেরার অটো ধরলাম। সোয়া ন-টায় বাড়ি ফিরলাম। দু-তিনটে ফোন এল। এগারোটা নাগাদ খেতে বসলাম। খেয়ে উঠে ঘণ্টাখানেক টিভি দেখলাম। তারপর হিসি করে শুতে গেলাম। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। (তোমার জীবনে স্মরণীয় দিন)
খুব ছোট ছোট বাক্য আর ক্রিয়াপদের ঘন ঘন ব্যবহার কবিতাটির মধ্যে একটি monotonous rhythm সঞ্চার করেছে। এবং এটি কবির উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই ডিকশন ও ফর্ম ছাড়া ‘গতকাল’-এর যাপনের ক্লান্তিকে ছোঁয়া যেত না কিছুতেই।
গদ্যকবিতার আরেকটি প্রকরণ সাধু ভাষাকে আশ্রয় করে পুষ্ট হয়েছে। এই ভাষা ব্যবহার করে নিমেষে মুছে ফেলা সম্ভব প্রায় দু-শতকের এক কালসীমা। যে-টাইমফ্রেমের মধ্যে অবস্থান করেন একজন কবি, সেটিকে দুমড়ে মুচড়ে তিনি পিছিয়ে যেতে পারেন অনেকটা সময়। এই প্রকরণ তাঁর সামনে খুলে দেয় এক কল্পবাস্তব জগতের দিগন্ত। এই প্রকরণের সার্থক প্রয়োগ আমরা দেখছিলাম কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালের কবিতায়। অকল্পনীয় দক্ষতায় তিনি লিখেছিলেন,
চলিত ক্রিয়াপদের বাংলা আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। এই বাংলা বড়ো সাহিত্যিক। যদিও আমার বয়স ত্রিশ বৎসর ও ২ মাস পূর্ণ হইয়াছে এবং এক্ষণে আমি রবিবারের মধ্যাহ্নে, ত্রিতলে, খাটে বসিয়া আছি, চারদিক বেশ শান্ত, একটি কাক ডাকিতেছে—…
‘আত্মকথন’ নামে এই কবিতাটি শেষ হয় এইভাবে,
আজ হয়তো তাহার মুখ চুম্বনে চুম্বনে পূর্ণশশীকে জানাইয়া দিবে সে ডাগর হইয়াছে, সে শহরে গিয়া সব জানিয়াছে; কিন্তু ওই তাহাকে দেখা যায়, পূর্ণশশীর হাত হইতে জাম খাইতেছে যেভাবে পোষা ঘোড়ায় মানুষের নিকট হইতে দানা খায়, শুধু একটি করতল পূর্ণশশীর পদমূলে। জামবনে হাওয়া অতি ধীরে বহিতেছে। পাঠক, আপনাকে ভগবান জানিয়া বলিতেছি, আমি এই।।
লিরিকাশ্রিত সার্থক প্রেমের কবিতা বাংলায় লেখা হয়েছে অসংখ্য। পার্থপ্রতিমের এই গদ্যের চলনে লেখা প্রেমের কবিতাটিও বাংলা কবিতার সম্পদ। যে-বাংলা লুপ্তপ্রায়, চালধোয়া গন্ধের মতো সেই বাংলাকে তুলে এনেছিলেন কবি পার্থপ্রতিম।
নয়ের দশকের কবি শ্বেতা চক্রবর্তী একইভাবে প্রায় চিত্রিত করেছে সেই কলোনি ও নবজাগরণের দিনগুলিকে। নর-নারীর মধ্যে আলো-ছায়া ফেলে শুয়ে থাকে যে-সম্পর্ক, যে-সম্পর্কের কোনও নাম ও পরিণতি নেই, শীতের আমলকি বনে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে হতে হয়তো গলা টিপে মেরে ফেলার প্রস্তুতি নিতে হয় যে-সম্পর্ককে, তাকেই ধরে রেখেছে শ্বেতা,
ফিরিতেছিলেন রবি নিজস্ব শকটে। শীত শেষ হইতে হইতেও হইতে চাহে না। বসন্ত সমীপবর্তী। ধীরে ধীরে গাহিতেছিলেন— ‘বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে…।’ ‘ভগিনী’ সুশ্রাব্য শব্দ, তাহারও অপেক্ষা সুশ্রাব্যতা নদীর কলধ্বনিতে, মার্গারেটের লজ্জাহীন, নিঃসন্ধিগ্ধ, নিরুপদ্রব মুখে, কণ্ঠে, জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে। একজন কবি কী আর বলিতে পারে— গান ছাড়া, ভাষা ছাড়া? নরেন দত্ত, আপনার পৌরুষ বাঁচিয়া থাকুক, না বাঁচুক কাব্য আমার— না বাঁচুক বঙ্গ কাব্যস্রোত। কেবল বাঁচিয়া থাক এ-বিকাল, এ-মাধুর্য, এই কথা, এই না বলিতে পারার নীরবতা— কর্মহীনতাই বটে কাব্য। কর্ম বটে দেশে সংস্কার সাধন। কর্ম বটে ভগিনী না বলিতা পারা স্পর্ধা— কর্ম বটে সুন্দরীকে সুন্দরী না বলিয়া কেবল সঙ্গসুধা, কেবল বাসুকী, কেবল অমৃতলক্ষ্মী, কেবল সে-দেবতার জন্ম— অমরত্ব নহে যাহা, প্রেম যাহা মালিন্যহীনার। আই উইল কাম সুন, নিবেদিতা, বন্ধু রূপে, বন্ধু বেদনায়…
এই কবিতার দিকে তাকিয়ে এক কল্পবাস্তব হত্যলীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। খুব পরিকল্পিত, বেদনার সেই লীলা। কিন্তু এক কবি ও কবির কাছে তা আর গোপন থাকে না। রবীন্দ্রনাথের গানে গানে ফুটে ওঠে সেই অনন্ত বেদনার প্রবাহ। লক্ষ করার বিষয়, এই ডিকশনটিকে ব্যবহার করে শ্বেতা মুছে দিয়েছেন প্রায় দেড় শতকের এক সময়সীমাকে।
নয়ের দশকে আবীর সিংহ, রোশনারা মিশ্র, প্রবুদ্ধসুন্দর কর, বিরূপাক্ষ পণ্ডা, রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মাজি, অর্ণব সাহা অসামান্য কবিতা লিখেছেন। গদ্য কবিতায় এঁদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। শুধু নির্মাণ দক্ষতা নয়, এঁরা প্রত্যেকেই কবিতার অন্তর্জগতের বাসিন্দা। আবীরের কবিতায় এক ব্যথার পৃথিবী বার বার ছায়া ফেলে যায়। ‘যদি এমন হয়’ কবিতায় আবীর লিখছেন,
কাগজে জলীয় খবরে সুরাহা নেই বলে মেয়েটি ইদানীং দাঁড়ায় হালকা বাতির নীচে প্রসাধনে; আর তুমি তার কাছে গিয়ে চমকে উঠে দ্যাখো; অবিকল গতজন্মের বোনের মতো মুখ
কবিতাটি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সিনেম্যাটিক উপাদানকে আশ্রয় করে কবিতাটি গড়ে উঠতে উঠতেও ঢলে পড়ে একটি সার্থক কবিতার দিকেই। যে-মেয়েটি পণ্য হয়ে যাওয়া, তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কেউ আবিষ্কার করে ফেলে গতজন্মের বোনের মুখ। একটি মেলোড্রামাটিক উপাদান কী রহস্যে যে কবিতার শরীর পায়, আয়ু পায় তা আবীরের এই কবিতাটি না পড়লে অজানা থেকে যেতে বাধ্য।
রাজনীতি, প্রেম ও নানা সোশিও-ইকোনমিক ঘূর্ণি অর্ণব সাহার কবিতার সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য। অর্ণব তার কবিতার পরিসরে এই সবগুলিকেই ঠেসে দিতে পারে। সত্তর দশকের যে-রাজনৈতিক আলোড়ন, শ্রেণি সংগ্রামের যে-ইতিহাস, সেই স্পেসের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করে অর্ণব নিজেকে। ‘নীচু গিলোটিন’ কাব্যগ্রন্থের ৪৩ নম্বর কবিতায় সে লেখে,
শেহেরজাদি প্রত্যেক রাতে নতুন গল্প বলত সুলতানের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবে বলে, ১০১ আরব্যরজণীর জন্ম এভাবেই, তুমিও একদিন আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে মৃত্যুপরোয়ানা, ৫ অগস্ট, ১৯৭১, ময়দানের কুয়াশামাখা ভোর বেলার মতো, যেদিন প্রিজনভ্যান থেকে নামিয়ে ওরা আমায় বলেছিল: ‘যা এবার ছুটে পালা’… দিগন্তরেখার আগে, কার্নিশের বুড়ি ছোঁয়ার মুহূর্তেও আমি অজান্তে কোনও রাইফেলের ট্রিগার গর্জে উঠবে, আর ফিনিশিং লাইনে হাত রাখার পর, রক্তে ভেজা আত্মা উড়াল দিয়েছিল অচেনা গ্রহে, মৃত্যুর উলটো পিঠে, যেখানে হাজার এক রূপকথার গল্পে ধাক্কা খায় গ্রহান্তরের স্পর্ধা, হৃৎপিণ্ডে পাথর ভরে শুরু হয় উল্কার দৌড়, শেহেরজাদির ভূমিকায় নিজেকে দাঁড় করাবে বলে…
অর্ণবের এই কবিতাটি আরেক জলবিভাজিকাও খুলে দেয় আমাদের সামনে। নয়ের দশকে বিশ্বায়নের প্রভাবের বাইরেও আরেকটি পৃথিবী হয়তো রয়ে গেছে আজও। মানুষের বেঁচে থাকা, দিন পালটানোর স্বপ্ন আজও ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সেই পৃথিবীর মাথার ওপরে।
শিল্পের অবিরত সন্ধান ও ব্যক্তিজীবনের হাহাকারের মধ্যে অন্তর্যোগ— সায়ন রায়ের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গদ্যকবিতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা তীব্র গতিকে দারুণভাবে ব্যবহার করেছে সায়ন,
বন্ধুবান্ধবহীন একা অন্ধকার কুয়োর মধ্যে গেঁথে আছে বুক। হা হা বুক! বুকের শ্বাস রিনিঝিনি উথালপাথাল। দূরে নদীতীরে বিন্দু বিন্দু আলোর মালার মাঝে জেগে আছে গান। গানের বিভাব। আমি সেই গান থেকে বহু দূরে দিকশূন্যপুরে বসে আছি। সেই গান আমার বিদ্যুৎ। ভোরবেলা শান্ত জীবনের খোঁজে বেরিয়েছিল একা আর এই ছেলেখেলা এই চঞ্চলতা। যে-অস্থিরতা গড়ে তোলে শিল্পের প্রাসাদ সেই পথ ভুল হয়ে ভাঙনে মিশেছে। সন্ন্যাসীর সাদা থান চিরকালীন স্বপ্ন হয়ে ঝুলে আছে।
নয়ের দশক কি এক মেটামরফোসিসের স্বপ্ন দেখিয়েছিল? যা ছিল আদতে এক স্কন্ধকাটার উলঙ্গ নৃত্য? কবি কি অনেক আগেই সেই বাস্তবতাকে অনুভব করতে পারে? নাহলে, পৌলমী সেনগুপ্ত কেন লিখেছিলেন,
চামড়ায় লণ্ঠন জ্বলে, ঠোঁট রক্তিম। ভুরু দুটো লাফ দিল, চোখের দু-পাশে পিঁপড়ের মৃদু চলাচল। শ্যাম্পু দুলিয়ে এক নিভাঁজ মহিলা বললেন,— ‘আহা! পানপাতা মুখ, চোখদুটো যদি হত সামান্য বড়ো’… আড়ে চেয়ে দেখি মনুমেন্ট ধুয়ে যায়, ঝাপসা হয় ব্যান্ডেল চার্চ— সূর্যরথের চাকা ঘুরে যায় এই বাতানুকূল কামরায় আর আয়নায় উড়তে থাকে চমৎকার এক সোনালি পায়রা (বিউটি পার্লারে)
যে-স্বপ্ন অনবরত দেখানো হবে, তুমি তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে বা পারবে না। কিন্তু এই অমোঘ টানে তোমাকে বার বার ছুটে যেতে হবে সেই বিউটি পার্লারে।
নয়ের দশকের কবিতা যে-বহু জলবিভাজিকার মিলন, পৌলোমীর কবিতার পাশে রোশনারা মিশ্রের কবিতা পড়লেই সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক সুতীব্র স্মৃতিকাতরতায় রোশনারা লেখে,
মুখ খুলতেই বলে ফেলেছিলাম— উষ্ট্র, এত তীব্র ছিল সেই ডাক। তারপর অনর্গল মরা মরা, আপাদমস্তক বল্মীক, কিন্তু আমার কাব্য হল না। আমি তাকে ছেড়ে যেতে দেখেছিলাম সে-রাতেই। যেন উপেক্ষা নিয়েই সে এসেছিল, রোয়াকে উষ্ট্রটি সে নিজেই বেঁধে রেখেছিল। এরপর মেঘ নিয়ে অনাবশ্যক খোরাক রাখিনি, খুঁট থেকে উটটিকে খুলে বৃষ্টিহীন দেশেই নির্বাসনে চলে যেতে হল। (স্মৃতিকাতরতা)
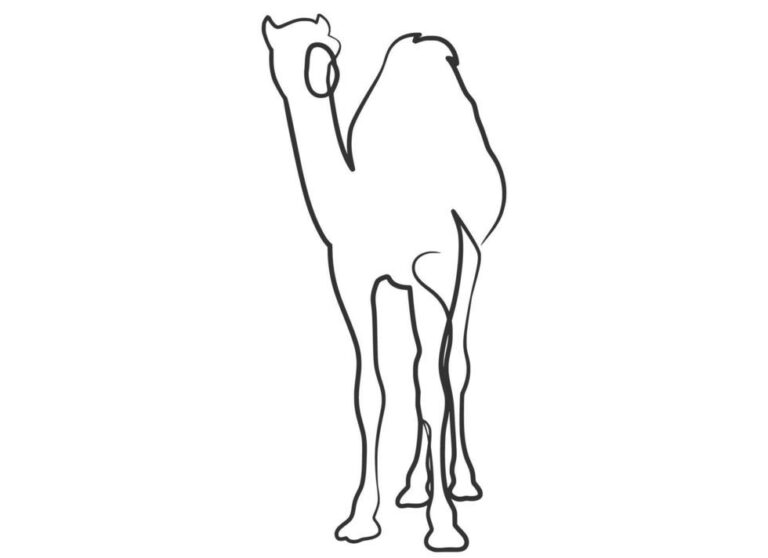
নয়ের দশকের একদম প্রথম থেকেই মৃদু ও স্বতন্ত্র কাব্যভাষাকে আশ্রয় করে অসামান্য কবিতা উপহার দিয়েছিলেন সুদীপ বসু। ‘ওঃ ভগবান’ কবিতায় তিনি লেখেন,
ছেলেটি জানলার বাইরে তাকাল। সরু রাস্তাটা সটান চলে গেছে স্টেশনের দিকে। একটা বাতিল এয়ারোড্রামের মাঝখানে শহিদ বেদি। তার ওপরে সিটিগোল্ডের রোশনাই। বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং রেলিঙের ওপর টাঙানো। ক্যালেনডুলার একটা জাম্বো টিউবের ওপর কাত হয়ে শুয়ে একটা মেয়ে হাসছে।
এই গদ্যকবিতাটি তার শরীরে ধারণ করে থাকে বাতিল এয়ারোড্রোম, শহিদ বেদি ও সিটিগোল্ডের রোশনাই। নয়ের দশকের অনিবার্য লক্ষণ, বিপরীতমুখী নানা জলবিভাজিকার সমাহার ফুটে ওঠে সুদীপের এই কবিতায়।
প্রবুদ্ধসুন্দরের কবিতা কতটা প্রতিকবিতার দিকে ঝুঁকে সে পৃথক প্রশ্ন। কিন্তু লিরিক শাসিত বাংলা কবিতায় প্রবুদ্ধসুন্দর এক ঝলক টাটকা বাতাস। ‘সাপলুডো’ কবিতায় আমরা পেলাম,
সাপলুডোর এই ১০০ সংখ্যাটি, দার্শনিকদের কাছে নির্বাণ বা জন্মান্তর বা নাস্তি, অধ্যাত্মবাদীদের ব্রহ্ম, উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের আমলাতন্ত্র, রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা এবং কবিসাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্ণিত হয়ে এসেছে। এভাবে, উত্থান-পতন, আর সর্পদংশনের ভেতর দিয়ে যেসব হতভাগ্য ছেলেরা, শেষ পর্যন্ত ওই ১০০ সংখ্যাটিকে আজও ছুঁতে পারেনি, আমি তাদেরই একজন।
এখানেও লক্ষ করার বিষয়, কবিতাটির প্রতিটি শব্দের মধ্যে দিয়ে প্রবুদ্ধসুন্দর যে-আক্রমণ ঘটাতে চেয়েছেন, সেই আক্রমণকে পুষ্ট করতে করতে এগিয়ে গেছে কবিতাটি। প্রথাগত পঙ্ক্তিবিন্যাসের দরকার হয়নি সেখানে। আরেক ধাপ এগিয়ে বলা যেতে পারে, এই টানা গদ্যের রুদ্ধশ্বাস চলন ছাড়া কবিতাটি সম্পূর্ণ হত না।
নয়ের দশকের একদম শেষ পর্বে বাংলা কবিতা লিখতে এসেছিল শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মেধাবী এই কবির ‘ঋতু দ্বিপ্রহর’ নামে কবিতার বইটির একটি পর্ব গদ্যকবিতা আকীর্ণ। পাঠকের নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না যখন শুভ্র লেখে,
আর যেখানে শরীর বলে কিছু কিছু নেই স্পষ্টতা মানে এই রাস্তা, আমি আচমকা আবিষ্কার করছি আমার এই মৃত সংখ্যা পতঙ্গের ছোটো উড়ানে ভরে আছে— সন্ধান বা বাড়ির নম্বর নেই শুধু এই দীর্ঘ এক সন্তানকামনাহীন নদীপথ, বাঁকে কিছু তন্দ্রা লেগে থাকা
এই ছোট গদ্যকবিতাটি পড়বার সময় বার বার মৃদু মৃদু ঠোক্কর খেতে হবে। প্রথম লাইনেই পরপর ‘নেই’ শব্দটির ব্যবহার তাকে থমকে দেবে কিছুটা। পঙ্ক্তি বিন্যাস না করে, গদ্যের ফর্মটিকে বেছে নেবার কারণও বোধ হয় এটাও। শুভ্র ঠিক এইভাবেই এক দীর্ঘ নদীর গতিপথটিকে বোঝাতে চেয়েছে।
২
বাংলা কবিতার নয়ের দশক ও শূন্য দশকের মধ্যে কয়েক আলোকবর্ষ দূরত্ব থাকলেও, একটি ব্যাপারে এই দু-টি দশকের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। নয়ের দশক ও আটের দশকের কবিতার মধ্যে যে-দূরত্ব, নয় ও শূন্যের মধ্যেও সেই দূরত্বই। হয়তো কিছুটা বেশিই দূরত্ব শূন্য ও নয়ের দশকের মধ্যে।
শূন্যের কবিরা লিরিক্যাল কবিতা লেখেনিই প্রায়। উল্লেখ্য প্রায় সব কবিই প্রথাগত ছন্দের বারান্দা থেকে সরে এসে আলো-অন্ধকার জাফরির কারুকাজের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। এই দশকে গদ্যকবিতা লেখা হয়েছে বহু। প্রখর মেধা ও নির্মাণদক্ষতা সেই সব কবিতার সম্পদ। তবে তার কবচকুণ্ডল অনিবার্যভাবেই কবিতার অন্তর্গত স্বর। পাঠকপ্রিয়তার দিক থেকে বিচার করলে এই সময়ের কবিতা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ; প্রতিষ্ঠানের প্রথাগত ধারণা নস্যাৎ হয়ে যাবার ফলে সে আর তাকিয়ে নেই প্রতিষ্ঠানের দিকে। মুদ্রিত কবিতাপত্রের বাইরে ভার্চুয়াল পৃথিবীর এক কল্পনাতীত দিগন্ত খুলে গেছে তার সামনে।
এই দশকের কবিতার দিকে চোখ ফেরালে বার বার যেটা মনে হয়, নয়ের দশক যে-purgatory-র সামনে গিয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, এই দশক সেই স্টেটটির মধ্যেই গড়ে নিল তার ঘরবাড়ি। নয়ের দশক প্রাথমিক অভিঘাতে কেঁপে উঠেছিল; শূন্য তাকে আত্মস্থ করে নিল। যে-পারাপারহীন ট্র্যাপের মধ্যে তার বেড়ে ওঠা, সেখানে গুপ্ত রেডিয়েশন তাকে ধ্বংস করার গুপ্তসৈন্য পাঠাতে থাকে প্রতিদিন। ফলে সেই বাস্তবতাকে গ্রহণ করে নেওয়া ছাড়া তার সামনে আর কোনও পথ খোলা থাকেনি। নির্দিষ্ট কোনও দর্শন নয়, ব্যক্তিমানুষের দর্শন এই দশকে প্রধান হয়ে উঠল। ইন্ডিভ্যিজুয়ালিটি এই সময়ের একমাত্র পথ। এই দশক যূথবদ্ধতার দশক নয়, এই দশক বিচ্ছিন্নতার। এই দশকের গদ্যকবিতার দিকে চোখ ফেরালে এই ধারার ছায়াপাতই ভেসে ওঠে।
তারেক কাজীর ৪৮ পৃষ্ঠার কাব্যগ্রন্থের সবকটি কবিতাই গদ্যকবিতা। এই কাব্যগ্রন্থে এক মরমী সাধকের সন্ধান পাওয়া যায়। যেন খোলা আকাশে নীচে দাঁড়িয়ে, নির্জন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এক সমর্পিত প্রাণ বলে চলেছে তার কথাগুলি। তারেক লিখেছে,
ঈশ্বরও জানেন না কিছু— যতটা জেনেছ তুমি। নিজের জীবন দিয়ে। সুখ-দুঃখের পরীক্ষায়— খোলা আকাশের নীচে বৃষ্টিতে ভিজেছ কত, কতদিন একা একা রৌদ্রে সয়েছ ক্ষতের অসহ্য ক্ষরণ। আবার কখনো অবসরে ধূ ধূ প্রান্তরের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে ভেবেছ— নিশ্চয়, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিকালের সোনারোদ মলিন পাতার ফাঁক গলে চুঁইয়ে নামবে নীচে। তোমার উপর থেকে কালো ছায়া উড়ে যাবে দূর। মেঘে মেঘে রটে যাবে কত কী গুঞ্জন। (অবিশ্বাসী)
শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের ‘হলুদ দাগের বাইরে পথচারী’ কবিতাটিতেও আমরা এই জগতেরই সন্ধান পাই। বিলীয়মান এক পৃথিবী ও যাপনের দিকে তাকিয়ে যেন কোনও লুন্যাটিক এইমাত্র বলে উঠল,
বিকেলের বুক চিরে চলে গেছে ঝকঝকে হাইওয়ে। পথচারী হলুদ দাগের বাইরে হাঁটে। শ্রান্ত পোশাক তার এলোমেলো করে যায় আশ্চর্য মারুতি, যা থেকে ক্ষণমাত্র চোখে পড়ে ফর্সা হাত, পলার রক্তাক্ত আলোড়ন।
#
বিকেলের বুক চিরে চলে গেছে ঝকঝকে হাইওয়ে। পথচারী হলুদ দাগের বাইরে হাঁটে। সে শুধু বিড়বিড় করে বলে— ‘আস্তে গেলে ভালো হত, সামনে আমাদের বাচ্চাদের স্কুল।’
এই পথচারী হয়তো আরেকটু দীর্ঘ দর্শন চায় সেই ফর্সা, পলা পরা হাতের। কিন্তু ‘বাচ্চাদের স্কুল’-এর উল্লেখ আরেকটি সম্ভাবনাকেও তুলে ধরে। এই পথচারী কি সন্তানসম্ভাবনাহীন? যার গর্ভজাত সন্তানের যাবার ছিল সামনের স্কুলে, সেই কি আজ দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে হাইওয়ের কালো অজগরের মতো অন্ধকারের দিকে?
গদ্যকবিতার কথা উঠলেই যাঁরা শুধুমাত্র কাহিনি-নির্ভর কবিতা লেখার শৃগালকৌশলের কথা বলেন, তাঁরা এক ফান্ডামেন্টালিস্ট প্রবণতা বহন করে চলেছেন। এই সময়ের তরুণ-তরুণতর কবিরা যে গভীর এক মহাজগতকেও ধরে রেখেছে তাদের কবিতায়, সে কথা তারা ঘাতক উদাসীনতার অলৌকিক ‘পুণ্যবলে’ ভুলে যায়। অচিন্ত্য মাজীর কবিতায় ধরা রয়ে গেল এক টুকরো বিভূতিভূষণের পৃথিবী। প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে, হতবাক এক তরুণের বোধের জগৎ,
ওই তো দেখা যায় ডোরা কাটা মেঘের নকশায় রূপহীন অবয়ব নাচছে। নিজের খেয়ালে নিজেই সে ভাঙছে আবার নিজেই নিজেকে গড়ছে। তার ঝুমঝুম শব্দে পায়ের নীচে খলবলিয়ে উঠছে মাটি। কুমড়ো ফলের উপর উড়ে এসে পড়ছে ডুমুর পাতা।
#
আমাকে আগন্তুকের ছোঁয়া দেবে বলে প্রকৃতি আনন্দে ফুলে ফুলে উঠছে। (আগন্তুক)
শূন্য ও শূন্য পরবর্তী সময়ে, ডায়াস্পোরা যত স্ফটিকস্বচ্ছ হয়েছে, যত ভার্চুয়াল জগতের কল্পবাস্তবতা বাস্তবতার সমনাম হয়ে উঠেছে, তত বেশি করে কবিরা রুটের দিকে ছুটে গেছে। এই ‘কোয়েস্ট’ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এই সময়ের কবিদের। লুপ্ত বাংলার কাছে তাদের আশ্রয়। এই তাড়না থেকেই জিৎ মুখোপাধ্যায়কে লিখে ফেলতে হয়,
অস্ফুটে জানতে চাই: ‘ওগো তুমি কবেকার, কোন মানবজন্মের? কোন দেশ হয়ে এলে!’ সে হাত তুলে দেখায়: অষ্টাদশ শতাব্দী আর অন্নদামঙ্গলের ধারে বসে কে যেন স্মিত গান ধরেছে: ‘বিজলীতে বিজলীতে ময়ূর নাচাও হে’ … নাচো তবে
#
ওই দিকে কতদিন পর রাঢ়বঙ্গে কি পুরোনো এক বৃষ্টি নেমেছে! (শিরিন রঙের পটুয়াপাড়া/৮)
জানালা ও উনুনের গেরস্থালির সম্পর্ককে ছোট্ট ক-টি কথায় লেখে অভিষেক চক্রবর্তী,
জানলা একরকমের ধার নেওয়া চোখ, যে-দেখায় বাইরে একবাস ভিড়ের মধ্যে কীভাবে মেঘ আতরের মতো মিশে যাচ্ছে। জানলা জানে, তার উলটো পাড়ে রয়েছে এঁটো উনুন, যার আগাগোড়াটাই লোভ, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জানলাকে হিংসা করে সে (নির্জন নামের জানলা/১)
শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তীর ‘শিকারতত্ত্ব’ কবিতাটিও গদ্যকবিতা। এই কবিতাটি পড়তে গিয়ে বারবার কেঁপে উঠতে হয়। ফেলে আসা এক কোটি বছরের দিকে তাকাতে বাধ্য করে শুদ্ধেন্দু, সেখানে অনেক খাদক ও অনেক খাদ্য…
…অথবা অস্প্রে। বাগানের প্রথম আঙুর। শহরের আদুরে
ডানা ভরা পেশি আর কানায় কানায় ভরা আশ্চর্য মাদক…
মুহূর্ত শিকার, বেসামাল ঘরবাড়ি, বেওয়ারিশ, ভবঘুরে লাশকাটা—
উলটপুরাণ। বাবাকে সাবড়ে নেয় ছেলে, ছেলেকে সাবড়ে নেয় বাবা—
আর আমাদের ফেলে আসা এক কোটি মানুষবছর…
সব ব্যোমকেশ আর সত্যবতীর মাঝখানে অপেক্ষা করে থাকা একজন অজিত। সত্যবতীর সহজতার দিকে তাকিয়ে থেকে তরুণ কবি সুদক্ষিণা শ্বাসকষ্টের কথা লেখে,
এত বিদ্যাধরী হয়েও সে-সহজতা আজও আয়ত্ত হল না বলে গলার কাছ থেকে পাক দিয়ে ফের উঠে আসতে চায় অর্ধচর্বিত খাদ্যদ্রব্য আর কেবলই রক্তাল্পতাজনিত শ্বাসকষ্ট অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে ওঠে আমার…
এই কবিতাটিতেও লক্ষ করার বিষয়, এক আটপৌরে জীবনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে এই প্রজন্ম। সেটিও আজ ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির মতোই অলীক; কিন্তু তাকে ছুঁতে চাওয়ার এক অদম্য ইচ্ছা তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাদের।
এই ধারণার স্বপক্ষে আরেক তরুণ কবির গদ্যকবিতার দিকে চোখ ফেরানো যাক। সায়ন্তন ঠাকুর লিখছে,
সেদিন খুব বৃষ্টি হবে। জানলার রঙিন পর্দা ভেদ করে ছুটে আসবে জল। বাতাস বইবে অহেতুক। তোমার বাড়ির লাল মেঝের ওপর পেতে দেবে আসন, কাঁসার থালার ওপরে সাজিয়ে দেবে এক মুঠো ভাত। গন্ধরাজ লেবু। একটু গাওয়া ঘি আর কাঁচালঙ্কা। পাশের বাটি-ভরতি দু-হাতা গরম মুসুর ডাল। এলোমেলো বাতাসে ভেসে উঠবে আমার কতদিনের খিদে। কতদিনের অযত্ন। তোমার রান্নাঘরের পাঁচফোড়ন নুন তেল কালোজিরের কৌটোরা অবধি আনন্দে মেতে উঠবে। বাইরে তখন কালো মেঘ আরও কালো হয়ে আসবে।
#
শুধু তোমার এই নিমন্ত্রণের জন্যই তো বেঁচে থাকা যায় আরও কয়েকটা জন্মদিন। আফ্রোদিতি। খিদে নিয়ে হেঁটে আসা যায় কয়েকটা ছায়াপথ।
গন্ধরাজ লেবু, গাওয়া ঘি আর গরম মুসুর ডালের জীবন এক দূর ছায়াপথের মতো হয়ে উঠছে বলেই কি তার দিকে ঝুঁকে থাকা সমর্থন?
এই সময়ের তরুণ-তরুণতর কবিপৃথিবী জুড়ে যে-প্রত্নছত্রাক, তার সন্ধান পাওয়া যায় শুভম চক্রবর্তী, অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। গদ্যকবিতার ফর্মটিকে আশ্রয় করে শুভম লেখে,
শ্যাওলার রং সবুজই কেন? লাল বা বেগুনি কেন নয়? এইসব প্রশ্ন আর এখন শরীরে রোমাঞ্চ জাগায় না। ভেঙে যাক সব রোমাঞ্চের সেতু। তীব্র অপরাধবোধ এসে ঘিরে ধরুক আমায়। একটি দড়ি এসে ঝুলতে থাকুক, সর্বক্ষণ; মুখের সামনে। এবং সমস্ত ঝুলে যাওয়া মানুষের মতোই প্রথাগত বয়ান— ‘কোনোকিছুর জন্যই কেউ দায়ী নয়, কেউ দায়ী হয় না কোনোদিন!’ কারণ দায় নামক ধূমকেতু তিন-শো তেত্রিশ কোটি বছর আগে ঝরে গিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বালি। কোটি কোটি থুতু ছিটকে যাচ্ছে সমস্ত না ঘুমোনো তারাদের দিকে আর কেউ একটা আত্মহত্যার মহড়া নিচ্ছে।
অভিনন্দনের কবিতায় পাওয়া যায়,
ফলবতী মেঘের নিশ্বাস এল হে সুবর্ণরেখা। বহুদিন আসিনি অন্যের কিয়দংশ হতে। তবু আজ এত কাছ থেকে পরখ করার সুযোগ পেয়ে বাড়িয়ে দিলে না ত্রাণ। পেয়ারা বাগান দেখে ভেবেছি লীলাক্ষেত্র, তোমার বুক নয়। এ-আমার পাপবোধ, এ-আমার মরে যাওয়া ক্ষুধা। বুকের ভেতর ঢুকে যাওয়া লাল রাস্তা গর্জন করে। বারান্দা চুঁইয়ে পড়ে প্যাঁচার অন্ধত্ব। আমি শুয়ে পড়েছি উইয়ের কোটরে। একটি নিরামিষ কালসাপ এসে ঘিরে ধরছে কলম। তোমাকে লেখার কথা খেয়ে নিচ্ছে আর ঘাম দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সাদা চিঠির ব্যার্থতা, কুৎসিত শিরোনাম। (না লেখা ফার্ম হাউস)
শিল্পের যে-অমোঘ আকর্ষণে একদিন মাথায় বজ্রবিদ্যুৎ-ভরতি খাতা নিয়ে বিপদজনক পথে পা বাড়ায় শিল্পী, দিনান্তে সেই শিল্প তাকে এক ভয়ংকর জীবন যাপন করবার ভার দিয়ে যায়। অরিন্দম রায় এক বিখ্যাত নাটকের প্রেক্ষাপটকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করে লেখে,
এই তো জীবন কালীনাথ! নাছোড় হাড়ের মতো ভাঙা দাঁতের কোণে
আটকে গেছে কিছুতেই তোমাকে ছাড়ছে না!
তোমার সংলাপ চলে গেছে, কণ্ঠস্বর কাজ থেকে বসে যাওয়া
সার্কাসের সিংহের মতো হাঁ করছে— আওয়াজ বেরুচ্ছে না।
দর্শক তোমার লেজ মুচড়ে দিয়ে মশকরা করছে, তুমি
ক্ষয়ে যাওয়া নখগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস
ফেললে। গাছ থেকে একটাও পাতা ঝরে পড়ল না। (নানারঙের দিন)
একটি বালির কণায় বিশ্বকে দর্শন করার চেতনাকে আশ্রয় করে টাইম-স্পেসের জটিল সমীকরণটিকে ছুঁয়ে থাকে রাজদীপ রায়,
ওই তো চাষজমি বুজে যাওয়ার আওয়াজ ভারী দাঁত উপড়ে ফেলছে মাটি… মরচে উড়ে আসছে… উড়ে আসছে… চিত্রনাট্যে লেখা আছে ভিনগ্রহ পুড়ে যাওয়ার সংকেত এভাবেই পৃথিবীতে আসে… যখন অতীত বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। পিঁপড়ের চোখে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব দূর থেকে গোলাকার মিষ্টান্নের মতো হাতছানি দিচ্ছে খেলা ছেড়ে মাঠ ছেড়ে উঠে যাওয়া সেইসব তারাদের… (রামকৃষ্ণের মুখে গল্প/৫)
সুজিত দাসের গদ্যকবিতায় ঠাসা থাকে কৌণিক উচ্চারণ। একটি সাদা বাড়ির সামনে এনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয় সুজিত। এই সাদা বাড়ি নিছক প্রেমের অনুষঙ্গ বহন করে না আর। কারণ সুজিত লেখেন,
দক্ষিণ কোণে একটি মস্ত খাঁচা। খাঁচার ভেতর অচিন পাখি। খাঁচার ভেতর সবুজ তোতা। আলেকজান্দ্রিয়ান প্যারাকিট। তোতাটির গলায় চন্দ্রহার। একটা বাড়ির প্রেমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি আমি। (প্রভু, প্রেমে পড়ে যাই)
এই কবিতাটিতে চন্দ্রহার শব্দটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রহারও যে শেষ পর্যন্ত হার, একটি অনিবার্য বন্ধন, সেটার দিকেও আমাদের তাকাতে বাধ্য করে সুজিত।
এই দুটি দশকে গদ্যকবিতার সংখ্যা ও মান যেমন উল্লেখ্য, ঠিক তেমনই এই সময়ে এমন অতি শক্তিশালী কবিরাও রয়েছেন যাঁরা গদ্যকবিতা বিশেষ লিখলেন না।
এই লেখায় নিশ্চিতভাবেই ছুঁয়ে যাওয়া গেল না আরও অনেক কবির সার্থক গদ্যকবিতাকে। এই ধরনের যেকোনও লেখা অসম্পূর্ণ হবার জন্যই ডেসটাইনড।
এই লেখা শেষ করব, প্রায় দু-দশকের ব্যবধানে দুই কবির দুটি লেখা দিয়ে। নয়ের দশকের কবি অনিন্দ্য রায় মেধাবী। ইঙ্গিতময় ভাষায় তিনি লিখছেন,
পশুর চৈত্য আর ডুগডুগির স্বাধীনতা সংগ্রাম। রোপ ট্রিক। একটি সাক্ষাৎকার টেবিলে উলটে রাখছে আয়নাদের। রিয়ালিটির বুড়ো আঙুল রাখা যে-পুস্তিকা কিনতে পাই-এর মান হারিয়ে ফেলি। রাখালের গল্প এখানে চালিয়ে রাখি। চৈতন্য অব্দি হল না। তাও দন্তের ন মাজতে এত আনন্দ। বৃত্তের সম্ভাব্য খারাপ। তাকে ফেলার জল, মেলার স্থলের কীরম বাজছে। পদ্ম পাতার শিশির। শ্যাওলাদের পবিত্রতা এখনো প্রচার পাচ্ছে। এত যে ল্যাজ, ল্যাজারিন, ল্যাজাকুশ টানতে গিয়ে হাতের রেখাও বদলে গেল। লেখাও পুরুষতান্ত্রিক। যথারীতি ঘণ্টা বাজলে লালাদের জাগতে হয়েছে
তাৎক্ষণিকের আনন্দে উদ্বেল, রিয়েলিটি শো-এর খ্যাতিকে মোক্ষ করা কবিতাজগতের দিকে তীর্যক উচ্চারণ ছুড়ে দিয়েছেন অনিন্দ্য। ঘন ঘন থেমেছেন। যতিচিহ্নের ব্যবহার করেছেন। এবং কবিতাটি হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ।
এক অতিতরুণ কবি তার সমস্ত ঘোর, আত্মজৈবনিক উচ্চারণ কীভাবে কবিতায় ঢেলে দিতে পারে তার সার্থক উদাহরণ প্রগতী বৈরাগীর এই কবিতাটি,
কোমর অব্দি ভিজে উঠছে ঘর, মগ্ন দাঁড়াশের মতো সমস্ত দীঘল
ডুবিয়ে শান্ত হচ্ছে গল্পেরা, যেন বুক আর কোমরের খাঁজে আরেকটু
মেঘ নামালেই সমগ্র ঘেন্নাতত্ত্ব ভুলে এক্ষুনি দুলে উঠবে সনাতন
শঙ্খের মতো, চোখ বন্ধ করে শীৎ শীৎ জপ করতে করতে মাথা
ঢুকিয়ে দেবে আমার লীলায়িত হাঁ-মুখে। (মৎসকুমারী অথবা ছেঁড়া আঁশ)
প্রবল যৌনতাকেন্দ্রিক অনুষঙ্গকে অদ্ভুত সব ইমেজের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে এই তরুণ কবি।
‘সমস্ত দিঘল’-এর কথা লিখেছে প্রগতী। বাংলা কবিতা তার সামগ্রিকতা নিয়ে সেই দিঘলের সন্ধানেই রত। গদ্যকবিতা সেই সামগ্রিকের এক অনিবার্য অঙ্গ।
(প্রবন্ধ, শুধু বিঘে দুই, সপ্তম সংখ্যা-২০১৯)
*ছবি সৌজন্য: ‘শুধু বিঘে দুই’ পত্রিকার ফেসবুক পেজ
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।