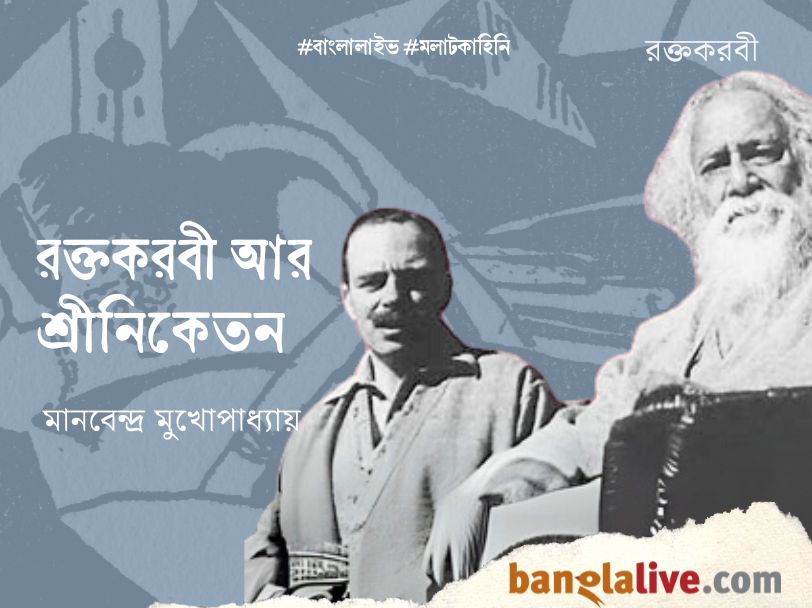(Raktakarabi)
রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকের সঙ্গে কি কবির কর্মকাণ্ডের মহানিরীক্ষাশালা শ্রীনিকেতনের কোনও যোগসূত্র আছে? শুধু কালগত যোগসূত্রের কথা না। সে যোগ আছে। রবিজীবনী-কার প্রশান্তকুমার পাল তাঁর রবিজীবনীর নবম খণ্ডে লিখেছেন, নাটকটির প্রথম খসড়াটির রচনা শুরু হয়েছিল ১৯২৩ সালের মে মাসের মাঝামাঝি। (পৃ.৭)। আর ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত সুরুলের পল্লি-পুনর্গঠন প্রকল্প ‘শ্রীনিকেতন’ নামে পরিচিতি পাবে ১৯২৩ সালেই, সে তথ্য আমরা সবাই জানি। (Raktakarabi)
তিনটি বছর ধরে নানা পাঠ-পাঠান্তরের পর রক্তকরবী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে ১৯২৬ সালে। মাঝের এই তিনটি বছরে পূর্ণায়ত রূপ পাচ্ছে নাটক রক্তকরবী, আর এইসময়েই একটু একটু করে নিজস্বতায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে কবি-কর্মীর ‘শ্রীনিকেতন’। কথা হচ্ছে, একটি প্রতিষ্ঠান আর একটি নাটকের মধ্যে অভিন্ন এক স্রষ্টার বিশেষ একটি দিকের ভাবনাগত সাযুজ্য নিয়ে। সামগ্রিক সাযুজ্য-প্রদর্শন ভ্রান্তিবিলাসমাত্র। তবু কেন কথাটা মনে আসছে, তা একটু খোলসা করে বলা যাক। (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী: বইয়ের শতবর্ষ, নাটকের নয়
রক্তকরবী নাটকের শুরুতে যেখানে অধ্যাপকের সঙ্গে নন্দিনীর প্রথম দীর্ঘ সংলাপটি পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে অধ্যাপক নন্দিনীকে একটি উপদেশ দেন। তিনি বলেন, ‘…পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকো গে।’ এই ‘দস্যুবৃত্তি করে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে’ ছেঁড়ার কথায় মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন-প্রকল্পের প্রধান বিদেশি সহযোগী লেনার্ড এলম্হার্স্টের একটি ভাষণ; কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরিতে যে-ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন ১৯২২ সালের ২৮ জুলাই। ‘দ্য রবারি অফ দ্য সয়েল’ শিরোনামের ওই ভাষণটি অবশ্য এলম্হার্স্ট তার আগেই দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, ওই বছরেরই ২২ ফেব্রুয়ারি। (Raktakarabi)

আশ্রমের মুখপত্র ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’য় সেই ভাষণের শিরোনামের বঙ্গীয় নামকরণ করা হয়— ‘ভূমিলক্ষ্মীর বিত্ত অপহরণ’। এলম্হার্স্টের কলকাতায় প্রদত্ত ভাষণটি প্রকাশিত হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ‘মর্ডান রিভিউ’ পত্রিকার অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়। পরে এলম্হার্স্ট তাঁর পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান বইতে জুড়ে দেন সেই ভাষণ। সঙ্গে ওই একই শিরোনামে জুড়ে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের একটি অভিভাষণ। ‘শান্তিনিকেতন পত্রিকা’র ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যায়; অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯২২ নাগাদ এলম্হার্স্টের ভাষণটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত। (Raktakarabi)
শিরোনাম ছিল ‘মাটির উপর দস্যুবৃত্তি’। এই শিরোনামটিই যেন অধ্যাপকের ওই সংলাপের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রায়-সমকালে রচিত রক্তকরবী নাটকে। তবে কি বক্তৃতার ওই ‘রবারি’ বা ‘দস্যুবৃত্তি’ শব্দটিই বছর-চারেকের মধ্যে উঠে এল রবীন্দ্রনাথের কলমে রক্তকরবীর নবম খসড়ায়? কিন্তু শুধু এইটুকুই নয়। ওই অভিভাষণের সঙ্গে শ্রীনিকেতন-প্রকল্পের সাযুজ্য আছে আরও। প্রসঙ্গত বলি, রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণটির আংশিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভূ-সম্পদের বিত্তহরণ নামের পুস্তিকায়, ২০০৬ সালে (প্রকাশক ‘মুক্তমন’)। (Raktakarabi)
“১৩৪৫ সালের কার্তিকে রবীন্দ্রনাথ ওই ভাষণে বলবেন, ‘বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।’ সরাসরি পরিবেশের উপর মানুষের দস্যুবৃত্তি নিয়ে শ্রীনিকেতন পর্বে কবির এরকম উদ্বিগ্ন ভাষণ আরও আছে।”
কী বলছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ? এককথায় বলতে গেলে সভ্যতার নামে আধুনিক যুগে যেভাবে পরিবেশের সীমাহীন দোহন চলছে, তার জন্য মানুষকে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের চেতাবনি শুনিয়েছেন কবি। এই যে যান্ত্রিক দোহনমার্গী সভ্যতা, তাতে নষ্ট হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক জীবন্ত সম্পর্ক। কবি বলছেন:
‘মানবদেহ বা সামাজিক সংগঠনের জীবন্ত সম্পর্ক তৈরি হয় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সদস্যদের পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা আর সহায়তার দ্বারা। …এই ঐক্যই হল [প্রকৃতির] চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য— তার সৃষ্টি হয়েছে নিজের জোরেই। …ক্ষমতার সংকীর্ণ আকাঙ্ক্ষা যখন জীবনের রিপাবলিকে আধিপত্য করতে থাকে, বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক বিনিময়ের ভেতর দিয়ে গড়ে-ওঠা স্বরসংগতি তখন ছন্দ হারাতে বাধ্য।’ (সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ)। রবীন্দ্রনাথের এইরকম উক্তি আরও পাওয়া যায়, যার মূল বক্তব্য হল: চতুষ্পার্শ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে জীবন্ত, সহানুভূতিপূর্ণ। তাদের আদান-প্রদানের মধ্যে থাকবে একটি ছন্দ, একটি সামঞ্জস্য। তা নাহলে জীবনের রিপাবলিকে ছন্দপতন হওয়া অনিবার্য। (Raktakarabi)

এলম্হার্স্টের ভাষণের ভূমিকা-স্বরূপ ওই অভিভাষণের অনেক পরের ‘অরণ্যদেবতা’ ভাষণ-নিবন্ধটিতেও প্রতিধ্বনিত হবে ওই একই সুর। ১৩৪৫ সালের কার্তিকে রবীন্দ্রনাথ ওই ভাষণে বলবেন, ‘বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।’ সরাসরি পরিবেশের উপর মানুষের দস্যুবৃত্তি নিয়ে শ্রীনিকেতন পর্বে কবির এরকম উদ্বিগ্ন ভাষণ আরও আছে। ১৯৩৯ সালে শ্রীনিকেতনের ‘হলকর্ষণ’ উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: ‘পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। …কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে।’ ‘অরণ্যদেবতা’ নিবন্ধে সভ্যতার নামে ক্ষমতাদর্পী রাষ্ট্রের পরিবেশ-লঙ্ঘনের নজির হিসেবে এসেছে আমেরিকার নাম। (Raktakarabi)
এ হল সেই জননী-বসুন্ধরার উপর মানুষের নিঃসীম দস্যুবৃত্তির নজির! ‘দস্যুবৃত্তি’ কথাটা সরাসরি পাওয়া যাচ্ছে ১৯৩৪-এর ‘পল্লীপ্রকৃতি’ নামের রচনাটিতেও। ‘আরণ্যক যুগের বর্বর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই প্রবল দেহ নিয়ে আজ দেখা দিল; আপন আপন ভোগের দুর্গ বেঁধে মানুষ অন্যকে শোষণ ও নিজেকে পোষণ করতে লাগল, তখনকার কালের দস্যুবৃত্তি দেহান্তর ধারণ করলে।’ পল্লীপ্রকৃতি বইটির প্রায় প্রত্যেকটি লেখাতেই রয়েছে কবির উদ্বিগ্ন স্বর। এর প্রতিপূরণ হবে কীভাবে? ১৯৩৯-এর পূর্বোল্লিখিত ওই ভাষণেই কবি বলছেন, ‘এই কথা মনে করে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ। অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ উৎসব।’ (Raktakarabi)
“সাম্রাজ্যবাদ আবার নামান্তরে জাতীয়তাবাদের মুখোশ পরে নেয়; উদ্দেশ্য যার অভিন্ন। ‘জাতীয়তাবাদ’ নামের আরোপিত এই ‘আইডেনটিটি’ মানুষের প্রাণের উত্তাপরিক্ত একটা বহিরঙ্গ যান্ত্রিক চুক্তির মতো।”
খেয়াল করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর উপর মানুষের এই নিঃসীম শোষণবৃত্তির কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ আজীবন দায়ী করেছেন সভ্যতার নামে মানুষের সীমাহীন লোভকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ তার লোভ নামক রিপুটিকে করে তুলেছে উত্তরোত্তর মর্মঘাতী। ভোগবাদ ও পণ্যরতির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। পল্লীপ্রকৃতি বইটির কোনও কোনও লেখায়, এবং অন্যত্র এই ভাবনারই প্রকাশ। প্রকাশ সেই নৈবেদ্য (১৯০১)কাব্য বা তারও আগে থেকে। ‘চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,…।’ (নৈবেদ্য ৯২)। রাষ্ট্র যে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে সেও মানুষের ওই লোভরিপুর কারণেই। (Raktakarabi)
সাম্রাজ্যবাদ আবার নামান্তরে জাতীয়তাবাদের মুখোশ পরে নেয়; উদ্দেশ্য যার অভিন্ন। ‘জাতীয়তাবাদ’ নামের আরোপিত এই ‘আইডেনটিটি’ মানুষের প্রাণের উত্তাপরিক্ত একটা বহিরঙ্গ যান্ত্রিক চুক্তির মতো। হাইড্রোলিক প্রেসের সঙ্গে তার তুলনা চলে, আর তার বিপরীতে থাকে একটি তরুশিশুর সপ্রাণ সত্তায় বেড়ে ওঠার উপমা। যাবতীয় যান্ত্রিক আধিপত্যকামী শক্তির ‘মরা ধন’-এর বিপ্রতীপে প্রাণশক্তির জগৎজোড়া জয়ঘোষণাই রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট। লোহালক্কড়ের মধ্যে চাপা-পড়া একটা করবী-চারা প্রাণের প্রবল উদ্যমে বুকে একফোঁটা রক্তের মতো ফুল ফুটিয়ে প্রাণের যে জয়গান গেয়েছিল, তারই প্রকাশ-বেদনায় রচিত হয়েছিল রক্তকরবী— একথা ক্ষিতিমোহন সেনকে বলেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। (Raktakarabi)
এই নাটকেও বসুন্ধরার উপর দস্যুবৃত্তি করে, তাকে ফোঁপরা করে করে তুলে আনা হয় তাল তাল সোনা। পৃথিবীর ‘মরা ধনে’ ভরে ওঠে রাজার কুবেরী ভাণ্ডার। শ্রমিকদের শোষণ করেই তা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ‘শহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপে নষ্ট হয় সকলেই জানেন।’ কথাটা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন রক্তকরবী নাটক রচনার ঢের দিন আগে, ফাল্গুন ১৩১৪ (১৯০৮) সালে পল্লীপ্রকৃতির অন্তর্গত প্রথম রচনাটিতে (‘সভাপতির অভিভাষণ’)। (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী: নব্যপুরাণ রক্তকরবী ও কিছু মেয়েলি ভাবনা
তার কিছুদিন আগেই তিনি রচনা করেছিলেন ‘স্বদেশী সমাজ’-এর কার্যক্রম; যা ফলিত রূপ পেয়েছে তাঁর পতিসরের জমিদারি এবং পরে শ্রীনিকেতনে। সেইজন্যই শুধু মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে রক্তকরবীর নাট্যঘটনার ব্যাখ্যা কিছুদূর পর্যন্ত সম্ভব হলেও রবীন্দ্রনাথের ওই নাটকের বিচার রবীন্দ্রজীবন ও চিন্তাধারার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রেখেই হওয়া কাম্য বলে মনে হয়। রক্তকরবীতে রাজা যে শেষপর্যন্ত তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠান নিজেই ধ্বংস করেন নন্দিনীর হাতে হাত রেখে তার ব্যাখ্যা মার্কসবাদে মেলা দুষ্কর। যদি শ্রেণিচেতনার আভাসও কেউ দেখতে পান নন্দিনীর নেতৃত্বে ফাগুলালদের যক্ষপুরী ভেঙে ফেলার সংগ্রামে, তবু মনে হয় ‘রাঙা আলোর মশাল’ নন্দিনী কেবলই একজন ভ্যানগার্ড নেত্রী নয়, সে মূলত অজেয় এক প্রাণশক্তির দূতী; যে প্রাণশক্তি ভূমিলগ্ন বলেই প্রকৃতির নিয়মে অজেয় ও সরল। ‘মরা ধন’-এর সঞ্চয়বাদী রাজার পক্ষে নন্দিনী তাই এত দুর্জ্ঞেয়। (Raktakarabi)
মার্কসবাদী বিচারধারায় বলা হয়েছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একশো বছরের শাসনে বুর্জোয়াশ্রেণি বুঝে নিয়েছিল তারা সব যুগের উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি বিশাল ও দানবাকার শক্তির জন্ম দিয়েছে। কমিউনিস্ট ইশতেহার থেকে উদ্ধৃত করে একালের মার্কস-তাত্ত্বিক পল সুইজি তাঁর ‘পুঁজিবাদ ও পরিবেশ’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘আগের কোনও শতক স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিল যে সামাজিক শ্রমের বুকে এমন শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে?’ (অনু: আশীষ লাহিড়ী, আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞান ও পরিবেশ, পৃ. ১৩)। পুঁজিবাদ তার স্বভাবগত দ্বন্দ্বের কারণেই একসময় ভেঙে পড়বে এই হল মার্কসীয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই নাটকে রাজা নিজের প্রতিষ্ঠান নিজেই ভেঙে ফেলছেন, তাও নন্দিনীর সাহচর্যের জাদুকরী প্রভাবে— তার ব্যাখ্যা মানুষের উত্তরণের রাবীন্দ্রিক প্রত্যয়ভূমি ছাড়া একরকম অসম্ভব। রবীন্দ্রভাবনায় অহং থেকে প্রেমে উত্তরণ হল ‘মুক্তি’। (Raktakarabi)
“রক্তকরবীতে ছিল মা-বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার প্রতাপী লোভতন্ত্রের দুঃশাসনীয় আস্ফালন নিয়ে উদ্বেগ। আর শ্রীনিকেতন-প্রকল্প হল তারই প্রতিষেধের রাবীন্দ্রিক উদ্যম।”
আবার অহং থেকে মুক্তির উপায়ও হল প্রেম। সেজন্যই কি যক্ষপুরীতে অজানা কোনও কারণে নন্দিনীর আবির্ভাব? তার পরিবর্তে প্রথমে খনিতে কাজের সূত্রে রঞ্জন এলে ঘটাতে পারত সমূহ বিপ্লব! কিন্তু এল নন্দিনী, যে খনির শ্রমিক নয়। তার সর্ব আভরণে, আচরণে প্রকৃতির সহজতার অমূল্য মাধুর্য। জড়পুরী যক্ষপুরীতে কেন প্রাণের প্রবর্তনার জন্য আসতে হয় একজন নারীকে? উত্তরটা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছেন রক্তকরবী রচনার প্রায়-সমকালে লেখা (১৯২৪)পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে। (Raktakarabi)
‘এমন সময় সেখানে [যক্ষপুরীতে] নারী এল, নন্দিনী এল: প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।’ প্রকৃতি আর নারীকে রবীন্দ্রনাথ সমীকৃত করে দেখেন, এমন দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে বিস্তর পাওয়া যায়। (Raktakarabi)

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মদমত্ত ক্ষমতাতন্ত্র ও সভ্যতাকে নেতিবাচক অর্থে মনে করতেন ‘ম্যাসকুলিন’। একালের নারীবাদীদের অনেকের সম্ভাব্য অনুযোগ উপেক্ষা করেই হয়তো তিনি ওই ডায়েরিতে বলবেন, ‘পুরুষের শক্তি তার অসমাপ্ত সাধনার ভার বহন করে চলবার সময় সুন্দরের প্রবর্তনার অপেক্ষা রাখে। সেই স্থিতির ফলই হচ্ছে নারীর মাধুর্য, সেই স্থিতির ফলই হচ্ছে নারীর মাঙ্গল্য, সেই স্থিতির সুরই হচ্ছে নারীর শ্রীসৌন্দর্য।’ এই ‘ম্যাসকুলিন’ আত্মঘাতী সভ্যতার চাঞ্চল্যকে শমিত করে নারী, তাকে শ্রীময়ী করে তোলে নন্দিনীরাই। (Raktakarabi)
‘শ্রী’ শব্দটির মধ্যেই রয়েছে ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাধুর্যের ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রিতি। কুবেরের সঙ্গে এখানেই ‘শ্রী’ অর্থাৎ লক্ষ্মীর তফাত। ‘শ্রী’ শব্দটি তাই রবীন্দ্রনাথের এত প্রিয়। এজন্যই তাঁর পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াসের নাম হয় ‘শ্রীনিকেতন’। বিশ্বভারতীর ছাত্রীনিবাসের নাম হয় ‘শ্রীভবন’ (এখন ’শ্রীসদন’)। সমবায়নীতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘লক্ষ্মী এইখানেই [পল্লির মধ্যেই] তাঁহার আসন সন্ধান করেন।… ধনপতি কুবের দেশের লোকের মনকে টানিয়াছে শহরের যক্ষপুরীতে। শ্রীকে তাঁহার অন্নক্ষেত্রে আবাহন করিতে আমরা বহুকাল ভুলিয়াছি।’ (Raktakarabi)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী’: বিগ ব্রাদার— The ‘Terrifying Bigness’
এই ভুলে-যাওয়া ‘শ্রী’-কেই প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি শ্রীনিকেতনে। কেননা জড়বাদী-ভোগবাদী সভ্যতার ম্যাসকুলিনিটির বিপরীতে আছে প্রকৃতির ফেমিনিনিটি। নন্দিনীকে রাজার মনে হয় সে ‘কোমল বলেই কঠিন।’ প্রকৃতির এই ধর্মই রক্ষণের ধর্ম, পালনের ধর্ম। এলম্হার্স্টের পোয়েট অ্যান্ড প্লাউম্যান বইয়ের ভূমিকাতেও গ্রামকে দেখা হয়েছে নারীপ্রতিমায়: ‘Villages are like woman…They are nearer to nature than the town and therefore in closer touch with the fountain of life. নাটক যেখানে শেষ হয়, সেখানে শোনা যায় ফসলকাটার গান, প্রফুল্ল প্রকৃতির ডালা ভরে উজাড় করা আশীর্বাদের স্মরণিকা-উৎসবের গান। আর শ্রীনিকেতনের মর্মকথা যে-গানে ব্যক্ত হয়েছে তা হল, ‘ফিরে চল্ ফিরে চল্ ফিরে চল্ মাটির টানে—/যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।’ (Raktakarabi)
রক্তকরবীতে ছিল মা-বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার প্রতাপী লোভতন্ত্রের দুঃশাসনীয় আস্ফালন নিয়ে উদ্বেগ। আর শ্রীনিকেতন-প্রকল্প হল তারই প্রতিষেধের রাবীন্দ্রিক উদ্যম। শ্রীনিকেতনের ওই মর্মগীতিটিতে মাটির ওই আঁচল পেতে অপেক্ষারই সম্পূরণ ঘটে যেন রক্তকরবীর অন্তিম সংগীতেও। সেখানে ‘ধুলার আঁচল’ ভরে ওঠে ‘পাকা ফসলে’। তাৎপর্যে এভাবেই একভাবে অভিন্ন সূত্রে গাঁথা পড়ে শ্রীনিকেতন আর রক্তকরবী। রক্তকরবীর ইংরেজি অনুবাদ রেড ওলিয়েন্ডার্স যে শ্রীনিকেতন-প্রকল্পের বিদেশি হোতা এলম্হার্স্ট সাহেবকেই উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেও বোধহয় নিতান্ত বন্ধুকৃত্য নয়! (Raktakarabi)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীতে বাংলার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ভবনের মুখ্য সমন্বয়ক। বেজিং ফরেন স্টাডিস ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রিত ভিজিটিং ফেলো হিসেবে ২০১৯ সালে তিনি চিন যান। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তাজগৎ এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর চর্চার বিশেষ ক্ষেত্র। 'বাকিরাত্রির ঘুম' (কাব্যগ্রন্থ), 'কোথায় আমার শেষ' (উপন্যাস), 'গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস' (আলোচনাগ্রন্থ ), 'উপন্যাসের যৎকিঞ্চিৎ' (প্রবন্ধ সংকলন), 'রবীন্দ্রনাথ: আশ্রয় ও আশ্রম' (প্রবন্ধ সংকলন) ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। বেশ কয়েকটি বইয়ের সম্পাদনাও করেছেন। বিচিত্র বিষয় নিয়ে পড়াশোনা তাঁর একমাত্র প্যাশন।