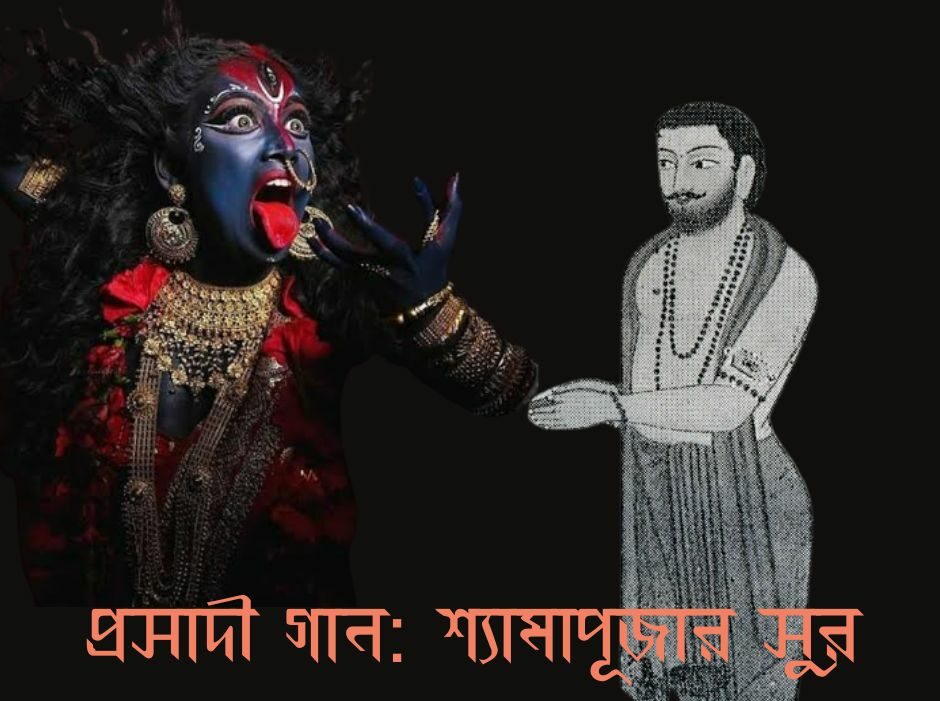ভারতের অধ্যাত্মসাধনায় সংগীতের মূল্য যে অপরিসীম ও অপরিহার্য তা তো জানাই আছে। এই উপমহাদেশের প্রতি পরতে যেভাবে সুরের উপস্থিতি, তার দৃষ্টান্ত বোধহয় পৃথিবীতে বিরল। এভাবেই কালীসাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হয়ে জুড়ে আছে সংগীত। মা কালীর কাছে ভক্তিপথে নিবেদিত গানের যে ধারা, তা ‘শ্যামাসংগীত’ নামে এক বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছে বাংলা গানে। এ গানের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে বিনা বাক্যব্যয়ে যাঁর নাম আসে, তিনি হলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন (Ramprasad Sen)। গভীর দর্শনজাত বাণীর সঙ্গে নিজস্ব সুরভাবনায় তৈরি শ্যামাপদে নিবেদিত এই সংগীতসাধকের গানগুলি ভক্তিপথে প্রকাশিত হয়ে এক অপূর্ব সাংগীতিক ভাবধারার জন্ম দিয়েছে।
শ্যামা-গানের যথার্থ পথিকৃৎ হিসেবে অবশ্যই বলতে হবে রামপ্রসাদের (Ramprasad Sen) নাম। তাঁর জন্মসাল নিয়ে যে বিভিন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয়, ১৭১৮ থেকে ১৭২০-র মধ্যে কোনও এক বছরে জন্ম তাঁর। বর্তমান হালিশহরকে তখন বলা হত কুমারহট্ট। সেখানেই জন্মেছিলেন এই প্রতিভাধর সাধক। তখন ধর্মীয় দিক থেকে ও রাজনৈতিকভাবে বাংলায় বেশ অরাজক সময় চলছে। চাষআবাদের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের ছিল না। আসলে, তখন থেকেই বাংলায় ছোটখাটো খাদ্যাভাব লেগেই থাকত। আমরা জানি, এই শতকের শেষের দিকেই ঘটেছিল সেই ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ), যা চাক্ষুষ করেছিলেন রামপ্রসাদ। যাই হোক, এরকম একটা অশান্ত সময়ে অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল এবং আজীবন তাঁকে চলতে হয়েছিল নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে। জন্মগত মেধা ও চিন্তাশীল সত্তা ছিল তাঁর। বাইরে চলা এইসব নানা ধরনের অশান্ত অবস্থা, তাঁর শিক্ষিত ও দার্শনিক মনকে এক আধ্যাত্মিক অন্বেষণে ছুটিয়ে বেড়াতো। যার দুটি ভিত্তিভূমি ছিল―কালীসাধনা ও সংগীতসাধনা।

রামপ্রসাদের বাবা রামরাম সেনের ছিল দুটি বিবাহ। রামপ্রসাদ ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষের চতুর্থ সন্তান। তখন বাংলায় সামগ্রিকভাবে অরাজক অবস্থা চললেও, কুমারহট্ট অঞ্চলে শিক্ষাচর্চার ভালোই চল ছিল। ঠিক যেমন একসময়ে ছিল শান্তিপুর-নবদ্বীপে। কুমারহট্টে টোল-মক্তব, সবই ছিল। অর্থাৎ, শিক্ষা-সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে সেই অর্থে কোনও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ছিল না। প্রসঙ্গত, তখন হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমদের যত না দ্বন্দ্ব ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি মতাদর্শগত সংঘাত ছিল হিন্দুধর্ম থেকে উৎসারিত নানা ধর্মীয় ভাবধারার মধ্যে। রামপ্রসাদের প্রথাগত শিক্ষা কিছুটা হয়েছিল। বাংলা তো বটেই, তার সঙ্গে সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, পার্সি ইত্যাদি ভাষাও শিখেছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই এইসব ভাষা শিখতে গিয়ে, বিভিন্ন মত ও পথের দর্শন, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। তবে তিনি প্রথামাফিক সংগীত শিক্ষা কারও কাছে নিয়েছিলেন কিনা, সেই সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।
বাবা রামরামের মৃত্যুর পর, রোজগারের দিকে মন দিতে হয় রামপ্রসাদকে। তখন থেকেই তাঁর মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়েছিল, যা প্রকাশ পেতে চাইত কাব্য ও সংগীতপথে। সেই ঘটনাই ঘটলো, কলকাতার ধনী পরিবারে তহবিলদারের চাকরি করতে করতে। হিসেবের খাতায় লিখে ফেললেন, “দে মা আমায় তবিলদারি/ আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী…”। এক কর্মচারী তা দেখে জমিদার মালিকের কাছে নালিশ করলেন রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে। বাবু কিন্তু গানটি পড়ে মোহিত হয়ে গেলেন। ভক্তি প্রেমে ভরা কী গভীর দর্শনানুভূতির বিচ্ছুরণ! শাস্তি দেওয়া তো দূর, রামপ্রসাদের মাইনে বাড়িয়ে দিলেন জমিদার। কিন্তু তাঁর মন ক্রমশ মা কালীর অন্বেষণে এতটাই তীব্র হচ্ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই চাকরিবাকরি ছেড়ে চলে এলেন হালিশহরে। শুরু হল তাঁর মাতৃসাধনা।

পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে তন্ত্রসাধনা করতেন রামপ্রসাদ— যার বহিঃপ্রকাশ ঘটত একের পর এক অপরূপ গানের মধ্যে দিয়ে। তন্ত্রসাধনা থেকে পাওয়া কুলকুণ্ডলিনী, ষটচক্র ইত্যাদি মন্ত্র ও দর্শনজ্ঞানের প্রতিফলন তাঁর অধিকাংশ গানের অন্তস্থলে বিরাজ করলেও, তা ছিল কালীচরণে সমর্পিত মন থেকে উৎসারিত ভক্তিরসের আচ্ছাদনে আবৃত। ফলে, গানগুলির সামগ্রিক রূপ হত এতটাই মনকাড়া যে, আজও তা সাধারণ মানুষের মনে নাড়া দিয়ে চলেছে।
রামপ্রসাদ তাঁর অধিকাংশ গানে এক বিশেষ ধরনের সুরের প্রয়োগ করেছিলেন, যাকে বলা হয় ‘রামপ্রসাদী সুর’। এ এমন এক মৌলিক সুরকাঠামো, যা গানের জগতে এক পৃথক সংগীতরীতির জায়গা অধিকার করেছে। তাঁর পরে আরও অনেক সংগীতকার এই সুরের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁদের গানে— যা আজও বহমান। সেদিক থেকে এই সংগীতসাধকের অবদান অপরিমেয়। এ বাদে তাঁর অনেক গানে বিভিন্ন রাগরাগিণী ও জটিল তালবিন্যাসের প্রয়োগও আছে। রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতো বিশিষ্ট সংগীত-জ্ঞানী ও গবেষক বলেছেন, রামপ্রসাদের রাগসংগীতের শিক্ষা ছিল। যদিও এর সপক্ষে নির্দিষ্ট তথ্য কিছু তিনি দেননি। তিনি এও লিখেছেন, বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা একবার নৌকো করে হালিশহরের পাশ দিয়ে যাবার সময়, ঘাটে বসা রামপ্রসাদের কণ্ঠ শুনে মুগ্ধ হন এবং সেখানে নেমে তাঁর গান শোনেন। রামপ্রসাদ নাকি “তাঁকে শুধু শ্যামাসঙ্গীত নয়―ধ্রুপদ, কাওয়ালি ও গজলও শুনিয়েছিলেন।” এ কথার পর রাজ্যেশ্বরবাবু লিখেছেন, “এই কাহিনী এত অধিক প্রচলিত যে, এর মধ্যে কিছু সত্যতা আছে বলেই মনে হয়।” রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন রামপ্রসাদের গুণমুগ্ধ। তিনি তাঁর দরবারে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সঙ্গে রামপ্রসাদকেও সভাকবির স্থান দিয়েছিলেন। রাজারই অনুরোধে এই দুই মহান কবি ‘বিদ্যাসুন্দর’ পালা রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের রচনায় ঘটেছিল আদিরসাত্মক মানবপ্রেমের প্রকাশ। রামপ্রসাদের ‘বিদ্যাসুন্দর’ থেকে ঝরে পড়েছিল ভক্তি ও ঐশ্বরিক প্রেম। দুটিই অসামান্য সৃষ্টি। শুধু দুই কবির দুরকম সত্তা থেকে উঠে আসা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের প্রতিফলন ঘটেছিল, একই বিষয়ে লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থে।

রামপ্রসাদের বেশিরভাগ গানে দেখা যায় বাউল, কীর্তন ইত্যাদি বাংলার মৃত্তিকাজাত সংগীতরীতির সুরপ্রভাব। তবে, কোনওকিছুই বোধহয় সচেতনভাবে করা নয়। সবটাই সহজাত প্রতিভাকে আশ্রয় করে, কালীপদে নিবেদিত ভক্তিমনের সংগীত-প্রকাশ। এ গানের বাণী এক উচ্চমার্গের ভক্তিসাহিত্য। যাতে সম্ভবত অজান্তেই এসে মিলে গেছে, সারা ভারতে জন্ম নেওয়া অসামান্য সাধকদের ভক্তিসাহিত্যের ধারা। এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ্ সর্বানন্দ চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, “কবির, নানক, ব্রহ্মানন্দ, মীরাবাই, সুরদাস এরকম আরো অন্যদের রচনার সঙ্গে রামপ্রসাদের রচনা মিলিয়ে পড়লে একটি ঐক্য স্পষ্ট অনুভব করা যায়। নামজপ, রিপুত্যাগ, বিষয়বৈরাগ্য, মায়া বা অবিদ্যা, কাল, কর্মজাল, ভক্তি, মুক্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গ রামপ্রসাদের গানে যেমন আছে, ওই সাধকদের গানেও প্রায় একইভাবে আছে। রামপ্রসাদের গানের ‘চক্র’, ‘সুষুম্না’― তন্ত্রের এইসব পরিভাষা কবিরের গানে পাওয়া যাবে।” সর্বানন্দবাবু বলেছেন, গুরু নানকের “ইহু তনু ধরতি…” গানের ভাবধারার সঙ্গে কীরকম সাদৃশ্য রয়েছে রামপ্রসাদের চিরবিখ্যাত “মন রে কৃষিকাজ জানো না…” গানটির, যেখানে দুটি ক্ষেত্রেই রূপক হিসেবে এসেছে ‘জমি’, ‘কৃষক’ ইত্যাদি। এখানে যা লক্ষ্যণীয়, দুই কৃষিপ্রধান অঞ্চল পঞ্জাব ও বাংলার দুই মহাসাধকের জীবনদর্শনচিন্তায় সংগীতের মধ্যে দিয়ে কীভাবে এসে পড়ছে কৃষি, জমি, কৃষক, ফসল ইত্যাদি। এ যেন এক অপূর্ব সাধন-সম্মিলন! সর্বানন্দ চৌধুরী আরও বলেছেন, “এছাড়াও রামপ্রসাদের গানের শ্যাম-শ্যামার যুগল রূপের বর্ণনা সুরদাসের গানে আছে।”
রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত মূলত গভীর বেদান্ত দর্শনের কথা বললেও, তা এমনই ভাবমাধুর্যে পরিপূর্ণ যে, আপামর বাঙালির হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে চিরকাল― “মন কেন মায়ের চরণছাড়া…”, “ডুব দে রে মন কালী বলে…”, “শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি/ এ ভবসংসার বাজারের মাঝে…”, “আয় মন বেড়াতে যাবি…”, “তিলেক দাঁড়া ওরে শমন…”, “ওরে সুরাপান করি নে আমি/ সুধা খাই জয় কালী বলে…”, “ভেবে দেখ্ মন কেউ কারও নয়…”, “আসার আশা ভবে আসা/ আসা মাত্র হল/ যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে/ ভ্রমর ভুলে র’ল…” ইত্যাদি আরও অনেক বলা যায়। প্রসঙ্গত, শ্যামা মায়ের গানের বাইরেও রামপ্রসাদ অল্পকিছু ভক্তিগীতি লিখেছিলেন। যেমন, মা দুর্গাকে নিয়ে রচনা করেছিলেন, “গিরিবর আর আমি পারি নে হে/ প্রবোধ দিতে উমা রে।” এভাবেই, অজস্র প্রসাদী গানে গভীর দর্শন ভক্তিরসে স্নাত হয়ে মনকাড়া শ্যামাসংগীতের রূপ নিয়েছে— তার মধ্যে যেমন আছে ভক্তি ও প্রেমের নিবেদন, তেমনই রয়েছে রিপুতাড়নাজনিত আত্মসমীক্ষার কথাও।

এছাড়াও, রামপ্রসাদের কিছু গানে প্রতিভাত হয়েছে চারপাশের সমাজ-চিত্র। ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখে তিনি গেয়ে উঠেছিলেন “অন্ন দে অন্ন দে অন্নদা…”, যে গান এর কয়েক শতক পর, ১৯৪৩-এর (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) আরেক ভয়ংকর আকালের পরিমণ্ডলে রেকর্ডে গেয়েছিলেন শিল্পী ভবানী দাস। একটি গানে রামপ্রসাদ তাঁর মায়ের কাছে ক্ষুধাতাড়নার কথা জানিয়েছিলেন এমনভাবে, যেখানে ‘জঠর যন্ত্রণা’ অনেক বিস্তৃত অর্থে প্রতিভাত হয়েছে― “মা মা বলে আর ডাকব না/তারা দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা/…রামপ্রসাদ মায়ের পুত্র/ মা হয়ে হলি মা ছেলের শত্রু/দিবানিশি ভাবি/ আর কি করিবি/ দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা…”
১৭৮১ সালে এই মহান সাধকের প্রয়াণ ঘটেছিল। বলা হয়, তিনি নাকি গান গাইতে গাইতে দেহত্যাগ করেছিলেন। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলা গানে শ্যামাসংগীত যুগের সূচনা হয়েছিল এই সংগীতসাধকের হাত ধরে এবং আজ পর্যন্ত তিনি এ গানের সৃষ্টিকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসে রয়েছেন। ‘রামপ্রসাদী সুর’ হিসেবে এক নতুন সংগীত-রীতির জন্ম তিনি দিয়েছেন বাংলা গানে। পরবর্তীতে নিজেদের গানে যে সুরের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সাধক কমলাকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ থেকে শুরু করে, পরবর্তীকালের আধুনিক বাংলা গানের সংগীতকারেরাও। যে ধারা আজও অব্যাহত। শুধু অন্য গানে তাঁর সুরের প্রয়োগই নয়, রামপ্রসাদের গান আজও গাইছেন বহু শিল্পী। একেই বোধহয় বলে শাশ্বত সৃষ্টি। তাই যুগের পর যুগ ধরে প্রসাদী সুর ও শ্যামাপূজা একাকার হয়ে থেকে গেছে সবার মনে।
তথ্যঋণ :
১) বাঙ্গালীর গান―দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৯০৫)
২) বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানাদিক― রাজ্যেশ্বর মিত্র (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)
৩) রামপ্রসাদী― সম্পাদনা : সর্বানন্দ চৌধুরী (সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭)
ছবি সৌজন্য: Getarchive, Wikipedia, Facebook
জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।