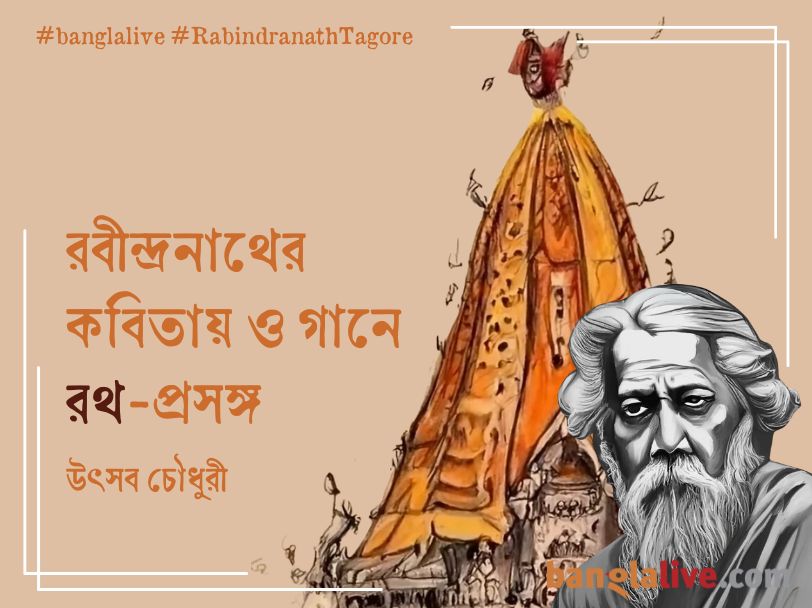রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মেছিলেন, কলকাতায় তখন রথ দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে সচল ছিল না। অশ্বচালিত নানারকম যানবাহন তখনও রাজধানীর রাস্তায় পুরোদমে চলছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাগাধুনিক রথের সেই রাজকীয় গাম্ভীর্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রথ তার রাজত্ব বজায় রেখেছিল একটিমাত্র বাৎসরিক পার্বণে… আষাঢ় মাসে জগন্নাথের রথযাত্রায়। রবীন্দ্রনাথ (Rabindranath Tagore) নিজে ব্রাহ্ম পরিবারের মানুষ, ছোটোবেলায় ভাইবোনেদের সঙ্গে খুদে রথ টানার আনন্দ কিংবা বড়োবেলায় রথারূঢ় জগন্নাথকে ভক্তিনম্র দর্শন, কোনও অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ বলে তাঁর জীবনী, বা আত্মজীবনীগুতে দৃঢ় সাক্ষ্য আমরা পাইনি। অথচ রথের চিত্রকল্প তাঁর কবিতায়, তাঁর গানে ভরপুর। এবং সেই সমস্ত রথোল্লেখ বাঙালির সর্বজনীন রথযাত্রার আমেজ থেকে শুরু করে মহাকাব্যিক চিরন্তনতা অবধি বিপুল পরিসর জুড়ে সুবিস্তৃত। আসুন, তারই কয়েকটি নিদর্শন আরেকবার ফিরে পড়া যাক।
রবীন্দ্রনাথের কবিতার শিশু কথক এবং শিশু চরিত্রদের স্বল্পজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে রথ এবং রথযাত্রা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। সেই অভিজ্ঞতায় ভক্তির আবেগ কিংবা ব্যায়বাহুল্যের আড়ম্বর নেই, আছে সরল আনন্দের অনাবিল উচ্ছ্বাস।
‘পুতুল ভাঙা’ কবিতার সেই শিশুটির কথন… “মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায় এবার রথের দিনে/ সেই যে রঙিন পুতুলখানি আপনি দিলে কিনে…”। রথের মেলা থেকে মায়ের সেই স্বল্পমূল্যে কেনা উপহারটি তার কাছে বিষম দামি, গুরুমশাইয়ের কোপে পড়ে সেটি নষ্ট হয়েছে, মায়ের কাছে তাই শিশু এসেছে কাতর অভিযোগ নিয়ে।
‘ছোটোবড়ো’ কবিতার যে শিশু বড় হয়ে বাবার মতো হতে চায়, এবং শৈশবের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে চায়, তার বিভিন্ন স্বপ্ন-সংকল্পের একটি হল, “রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়/ একলা যাব, করব না তো ভয়–“। শিশুটি বলছে, সেই সময়ে মামা যদি ছুটে এসে বলেন, “হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো…” তক্ষুনি সে মামাকে বলে দেবে, সে বাবার মতো বড় হয়ে গিয়েছে, রথের মেলার মতো জনাকীর্ণ স্থানে একা একা গেলেও এখন আর তার কোনও ভয় নেই। কিংবা ‘পুতুল ভাঙা’ কবিতার সেই শিশুটির কথন… “মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায় এবার রথের দিনে/ সেই যে রঙিন পুতুলখানি আপনি দিলে কিনে…”। রথের মেলা থেকে মায়ের সেই স্বল্পমূল্যে কেনা উপহারটি তার কাছে বিষম দামি, গুরুমশাইয়ের কোপে পড়ে সেটি নষ্ট হয়েছে, মায়ের কাছে তাই শিশু এসেছে কাতর অভিযোগ নিয়ে। ‘রাজা ও রানী’ কবিতার শিশু কথকটি অবাধ্যতার জন্য রাজ-প্রতিম পুরুষ অভিভাবকের কাছে শাস্তি পেয়েছে, পেয়ারা পেড়ে আনা এবং চিঁড়ের পুলি খাওয়ার পাশাপাশি “রথ দেখতে যাওয়া”-র ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন কঠোর অভিভাবক৷ এইভাবে, ‘শিশু’ এবং ‘শিশু ভোলানাথ’ দুটি কাব্যগ্রন্থেই বারংবার ফিরে এসেছে রথ এবং রথযাত্রা-কেন্দ্রিক উচ্ছ্বাস, অথবা সেই আমোদ থেকে বঞ্চিত হবার খেদ।
বড়দের চোখ দিয়ে শিশুদের দেখা হচ্ছে, এমন কবিতাতেও এসেছে রথের প্রসঙ্গ। ‘ক্ষণিকা’ বইয়ের ‘সুখদু:খ’ কবিতা শুরু হচ্ছে এইভাবে… “বসেছে আজ রথের তলায়/ স্নানযাত্রার মেলা–“। সেই মেলায় এক পয়সা দিয়ে তালপাতার বাঁশি কিনে বাজাচ্ছে যে মেয়েটি… তার হাসিটিই কবি-কথকের চোখে সবচেয়ে আনন্দময় হয়ে ধরা দিয়েছে।
আবার, বড়দের চোখ দিয়ে শিশুদের দেখা হচ্ছে, এমন কবিতাতেও এসেছে রথের প্রসঙ্গ। ‘ক্ষণিকা’ বইয়ের ‘সুখদু:খ’ কবিতা শুরু হচ্ছে এইভাবে… “বসেছে আজ রথের তলায়/ স্নানযাত্রার মেলা–“। সেই মেলায় এক পয়সা দিয়ে তালপাতার বাঁশি কিনে বাজাচ্ছে যে মেয়েটি… তার হাসিটিই কবি-কথকের চোখে সবচেয়ে আনন্দময় হয়ে ধরা দিয়েছে। আবার, এর বিপ্রতীপে যে ছেলেটি একটি রাঙা লাঠি কেনার পয়সাও জোগাড় করে উঠতে পারেনি, তার কারুণ্যভরা চোখদুটিও কবির নজর এড়িয়ে যায়নি৷
ছোটোদের নিয়ে কবিতার পর, এবার বড়দের নিয়ে কবিতার পরিসরে প্রবেশ করা যাক। রবীন্দ্রনাথের ভক্তিরুচ্ছ্বসিত কবিতা এবং গানগুলির দিকে তাকালে সহজেই নজরে পড়বে, তাঁর চেতনায় ঈশ্বর প্রায়শই হয়ে উঠেছেন এক রথারূঢ় রাজাধিরাজ। যেমন, ভীষণ পরিচিত ‘কৃপণ’ কবিতাটির ভিক্ষুক-কথক লীলারহস্যময় ঈশ্বরকে “স্বর্ণরথে”-র আরোহী-রূপেই দেখেছে, এবং প্রত্যাশা করেছে যে রাজার ছড়িয়ে দেওয়া ধনধান্য মুঠো-মুঠো কুড়িয়ে নেবার সৌভাগ্য বুঝি দূরে নেই! কিন্তু তাকে বিস্মিত করে, রাজার রথ তারই সামনে এসে থেমেছে, রাজা স্বয়ং হাত পেতেছেন তার কাছে ভিক্ষা নেবেন বলে। হতচকিত, বিভ্রান্ত ভিক্ষুক রাজাকে একটি ছোটো শস্যকণা ভিন্ন আর কিছু দিতে পারেনি। পরে, ঘরে এসে ভিক্ষার ঝুলিতে একখণ্ড স্বর্ণকণা দেখে সে নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। (অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য বলে রাখা ভাল, এই কবিতার সম্ভাব্য অনুপ্রেরণা হল ভাগবতের শিশুকৃষ্ণ ও ফলওয়ালির গল্প। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের এতই প্রিয় ছিল যে, ‘পদরত্নাবলী’-র ছোট্ট পরিসরের মধ্যেও তিনি এই কাহিনি-ভিত্তিক একাধিক পদ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।)
রবীন্দ্রচেতনায় যে আনন্দময় দেবপুরুষের দেখা মিলছে না, যিনি আসবেন বলে আশা, অথবা এসেও ফিরে গেলেন বলে দেখা হল না… তাঁদের সামান্য বৈশিষ্ট্য এই স্বর্ণরথ।
এই রাজকীয় স্বর্ণরথ রবীন্দ্রনাথের রচনায় ফিরে ফিরে এসেছে৷ “সব দিবি কে” গানের আসন্ন বসন্তপুরুষ স্বর্ণরথারূঢ়, ‘উৎসর্গ’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় আসন্ন সূর্যদেবতা… তিনিও স্বর্ণরথারূঢ়। ‘গীতাঞ্জলি’-র ৬৭ নং কবিতায় যে “সুন্দর” পারিজাত-হাতে কবি-কথকের সাথে প্রাত:কালীন সাক্ষাতে এসেছিলেন, কিন্তু কথকের দেখা না পেয়ে একাই ফিরে গেলেন, তাঁর গতায়াতও “সোনার রথে”। অর্থাৎ, রবীন্দ্রচেতনায় যে আনন্দময় দেবপুরুষের দেখা মিলছে না, যিনি আসবেন বলে আশা, অথবা এসেও ফিরে গেলেন বলে দেখা হল না… তাঁদের সামান্য বৈশিষ্ট্য এই স্বর্ণরথ। এই সুবর্ণরথের মধ্যে সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকা দৈব ঐশ্বর্যের প্রকাশ আছে তো বটেই। সেইসঙ্গে, অন্ধকারবিদারী সূর্যের তীব্র স্বর্ণাভ আলোকছটার প্রাকৃতিক অনুপ্রেরণাও নিশ্চয়ই আছে। এবং, আছেন সেই ঔপনিষদিক ব্রহ্ম, যিনি একইসঙ্গে “আদিত্যবর্ণং” এবং “রুক্মবর্ণং”… সূর্যাভ এবং স্বর্ণাভ।
সাধারণের দেখা-শোনার আড়ালে থাকা এই রথচারী সৌরদেবতার কল্পনা তুঙ্গে উঠেছে ‘লিপিকা’-র ‘রথযাত্রা’ কবিতায়। জগন্নাথের বার্ষিক রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা যে সূর্যায়নের প্রতীক… এ নিয়ে গবেষকেরা বহু কথাই বলেছেন। ‘রথযাত্রা’ কবিতায় দেখা যাচ্ছে… রাজা-রানীর সাড়ম্বর রথদর্শনের উদ্যোগে এক দু:খী অংশ নেয়নি, মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলছে “ঠাকুর তো রথে করেই আমার দুয়ারে আসেন।” তাই যদি হবে, তো রথের চিহ্ন নেই কেন?
সাধারণের দেখা-শোনার আড়ালে থাকা এই রথচারী সৌরদেবতার কল্পনা তুঙ্গে উঠেছে ‘লিপিকা’-র ‘রথযাত্রা’ কবিতায়। জগন্নাথের বার্ষিক রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা যে সূর্যায়নের প্রতীক… এ নিয়ে গবেষকেরা বহু কথাই বলেছেন। ‘রথযাত্রা’ কবিতায় দেখা যাচ্ছে… রাজা-রানীর সাড়ম্বর রথদর্শনের উদ্যোগে এক দু:খী অংশ নেয়নি, মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলছে “ঠাকুর তো রথে করেই আমার দুয়ারে আসেন।” তাই যদি হবে, তো রথের চিহ্ন নেই কেন? দু:খীর উত্তর “তিনি যে আসেন পুষ্পকরথে।” এই গগনচারী পুষ্পকরথারূঢ় ঠাকুরটির মধ্যে বাল্মীকি-বাহিত রামকথার পুষ্পকরথারূঢ় সপার্ষদ রামচন্দ্রের অনুপ্রেরণা অনুমান করা দুষ্কর নয়। আর যদি কবির সমকালীন ইতিহাস থেকে এর সূত্র খুঁজতে হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কলকাতায় রানি রাসমণি প্রবর্তিত রঘুবীরের রথযাত্রার দৃষ্টান্তটি তো আছেই! তবে, কবিতাটি এখানেই থামছে না। মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে দু:খী দেখিয়ে দিচ্ছে তার দুয়ারের দুইপাশে দুটি সূর্যমুখী। অর্থাৎ, সূর্যবংশজ রাম থেকে দু:খীর ‘ঠাকুর’ হয়ে উঠছেন স্বয়ং সৌরদেবতা, গগনপথে তাঁর নিত্য রথযাত্রা, মর্ত্যপৃথিবীর সূর্যমুখীর দল তাঁর সেই পথের দিকেই এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে রোজ। সেই সূর্যের অন্তর্যামী পুরুষের উদ্দেশেই উপনিষদ-নিষ্ঠ কবি উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি করে বলেন, “করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,/ তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি/ আপনার আত্মার স্বরূপ।”
অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, বৈদিক সূর্যরথ আর সাম্প্রতিক জগন্নাথ-রথের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ কি কেবল রথারূঢ় দেবপুরুষের ছবিই আঁকলেন? রথারোহিণী দেবীর ছবি কই? আছে, তাও আছে। বৈদিক শ্রীসূক্তের অধিদেবতা যে লক্ষ্মী, তিনি “রথমধ্যাং”। সেই রথারোহিণী শ্রীদেবীর ছায়াপাত ঘটেছে কবির গানে। কাশের গুচ্ছ, শেফালিমালা আর নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে ডালা সাজিয়ে দেবীর আবাহন “এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে… “।
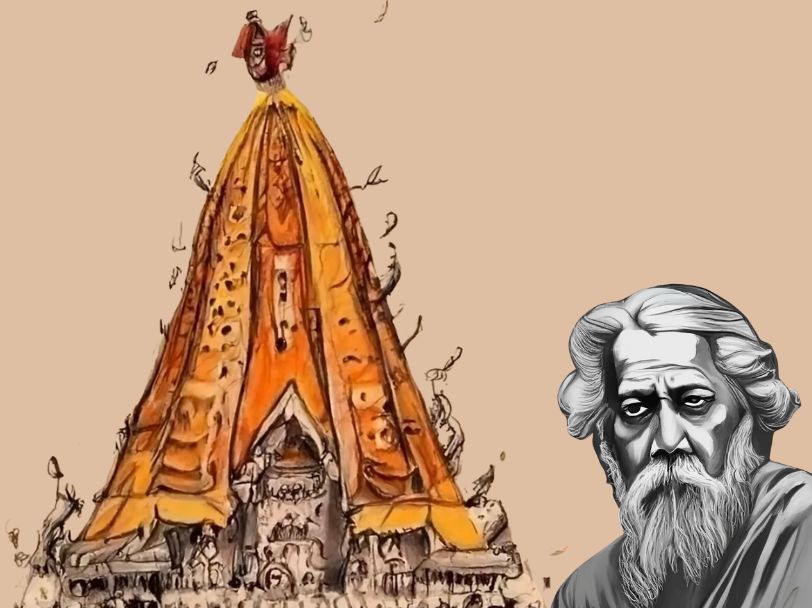
রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিচিন্তার মধ্যেও রথের আনাগোনা চলেছে। ‘রথের রশি’ একটি রূপক নাটক… সেখানে রথারূঢ় দেবতার নাম ‘মহাকাল’ তথা ‘মহাকালনাথ’। ইনি অনন্ত সময়ের প্রতিভূ। তাঁর রথের দড়ি টানতে ব্যর্থ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের দল; শেষত রথ চলল শ্রমজীবী শূদ্রদের টানে। আধুনিক বিশ্বে প্রোলেতারিয়েত অথবা সাব-অল্টার্ন শ্রেণী-বিষয়ক সচেতনতা, বিপ্লব ও অভ্যুত্থানের একটি ভারতীয়কৃত রূপক আমরা এই নাটকে দেখতে পেলাম রথ-চিত্রকল্পের মাধ্যমে।
আর, স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতের তৃতীয় স্তবকেও আমরা পাচ্ছি রথ-প্রসঙ্গ। পরমেশ্বর তথা ‘ভারতভাগ্যবিধাতা’ এখানে রথী নন, সারথী। স্পষ্টতই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পাঞ্চজন্য-নিনাদী গীতা-বক্তা পার্থসারথীর ছায়া পড়েছে এই গানে, শ্রীকৃষ্ণই হয়ে উঠেছেন রথারূঢ় ভারতেশ্বর…
“পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥”
তথ্যসূত্র: ‘শিশু’, ‘শিশু ভোলানাথ’, ‘ক্ষণিকা’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘খেয়া’, ‘উৎসর্গ’, ‘লিপিকা’, ‘গীতবিতান’, ‘রথের রশি’ ইত্যাদি।
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সাম্মানিক বাংলা সহ স্নাতক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও এম ফিল, বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতায় পিএইচডি গবেষণারত।