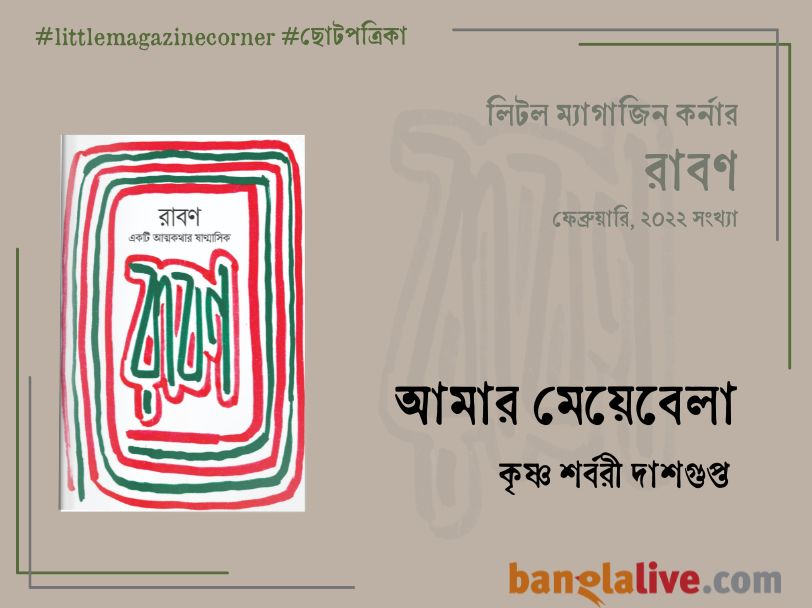বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয়তনগত ধারণা বা বোধগুলোও কী বদলে যায়? নাহলে ছোটোবেলায় যে খেলার মাঠটাকে বিশাল মনে হত, এখন সেটাকে আর তত বড় তো লাগেনা। কিংবা খেলতে খেলতে টুনুদের বাড়ির যে দালানে একদিন হারিয়েই গেছিলাম প্রায়, তার পরিসরও আর চোখ ধাঁধায় না দেখি ইদানীং। আমাদের পুরনো বাড়ির সেগুন কাঠের আখাম্বা সদর দরজাটাকে ও সেসময়ে রূপকথার বইতে দেখা দুর্গের তোরণ বলে ভাবতাম। লোহার পাত বসানো দরজার ইয়াব্বড় লোহার কড়া ছোটো আঙুলে নাড়াই অসাধ্য। একমাত্র গভীর রাতে ছাড়া সে দরজা কখনও বন্ধ হয়না, দিনে-দুপুরে হাট করে খোলাই থাকে অষ্টপ্রহর। (Little Magazine)
সারাদিনে কত লোক যে আসে যায়, কে-ই বা অতবার খোলাবন্ধ করে। কলকাতা শহরেও ঘরে ঘরে কলিং বেলের চল হয়নি তখন, বাড়িতে কেউ এলে দরজায় কড়া নাড়ত। সে নাড়ারও আবার কত কায়দা! কড়ার শব্দ শুনে গৃহস্থ অনেক সময়ে বুঝে যেতেন, কে এল। সদর পেরোলে ‘এল’ আকৃতির লম্বা করিডোর, আমরা বলতাম ‘দেউড়ি’। একা কখনো ওই দেউড়ি পেরোতে হলে টেনে ছুট লাগাতাম। তার কারণ আর কিছুই না দেওয়ালে ঝোলানো একটা কুমিরের হাঁ-মুখ। বাঁকানো হরিণের শিংও ছিল, তবে ওই ভয়ানক দাঁতওয়ালা কুমিরের বিশ্রী মুখটা ওখানে কী যে শোভা বৃদ্ধি করত কে জানে! বড়দাদুর অমন সাজানো বসার ঘরে মাথাসুদ্ধু ভালুকের চামড়াটা যেমন। ও ঘরে পারতপক্ষে ঢুকতাম না, ঢুকলেও আড়ষ্ট হয়ে আড়চোখে তাকাতাম মাথাটার দিকে। মনে হত এই বুঝি ভালুকটা গা-ঝাড়া দিয়ে তেড়ে আসবে। তখন ভয় করত, বড় হবার পর সেটা বদলে গেল ঘেন্নায়, যখন বুঝতে শিখলাম প্রাণহীন প্রাণীশরীর যত্ন করে সাজিয়ে রাখাও বলদর্পী মানুষের একধরনের অহমিকা।
একতলাতেই বৈঠকখানা। বাবা-কাকাদের আড্ডাঘর। বৈষয়িক বা অন্য জরুরি কাজে যাঁরা আসেন, তাঁরাও ওই ঘরেই বসেন। বাড়ির লাইব্রেরি বলতেও এটাই। দেওয়ালজোড়া আলমারিগুলোতে আইনের বই ছাড়াও নানান বিষয়ের বই, পত্রপত্রিকা। বৈঠকখানার বাইরের দেওয়াল ঘেঁষে কাঠের বেঞ্চি পাতা। বারুইপুর, রামনগর থেকে প্রজারা এলে, কিংবা কেউ চাকরি-বাকরি বা অন্য কাজের সুপারিশ নিয়ে এলে ওখানে বসে। অপরিচিত বা অল্পপরিচিত মানুষ, কারা যে বৈঠকখানার টিকিট পাবেন আর কারা বেঞ্চির, বাড়ির অভিজ্ঞ পরিচারকদের সেটা নখদর্পণে। অতিথিকুলে কুলীন বিবেচিত হতেন অতি নিকট আত্মীয়-পরিজন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবেরা। নৈকট্যের মাত্রা বুঝে তাঁদের কেউ যাবেন দোতলার নাচঘরে, চাই কী গৃহকর্তার অন্দরমহলেও। একতলার দেউড়ি যেখানে দেওয়ালে ধাক্কা খায়, তার বাঁ দিকেই দোতলায় ওঠার শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। সে সিঁড়ি বার দুই বাঁক ঘুরে পৌঁছে গেছে নাচঘরের দরজায়। সিঁড়ির মুখে ঢাল তরোয়ালের দেওয়াল সজ্জা, আর তার পর থেকে দু’ধারের দেওয়ালে পরিবারের সদস্যদেরই সাদা-কালো ফটোগ্রাফ পরপর সাজানো। এই নাচঘরের সঙ্গে নাচের কোনো সংযোগ আমরা তো দূরস্থান, আমাদের ঠাকুরদা বা তস্য পিতার আমলেও ছিল বলে জানা নেই। মূল বাড়ি ভাগ হবার সময়ে সবুজ ইতালিয়ান মার্বেল পাতা লম্বাটে আকৃতির বিরাট এই সুসজ্জিত ঘরখানিও দু’ভাগ হয়ে যায়। সামনের অর্থাৎ উত্তরের অংশটা পায় চার নম্বর বাড়ি আর দক্ষিণ দিকটা আমরা।
দু’প্রান্তের দেওয়ালে বাহারি ফ্রেমে বেলজিয়ান কাচের বিশাল বিশাল আয়না থাকায় ঘরটাকে আরও যেন দীর্ঘ মনে হত। উঁচু কড়ি-বর্গা থেকে ঝোলা ঝাড়বাতি আর রুচিশীল আসবাবের আভিজাত্যে এটি ছিল বাড়ির সবচেয়ে সেরা ঘর। পুজোর ঠিক পরে পরে কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে ঠাকুমার নারায়ণের ‘পালা’ পড়ত। তাঁর বাপের বাড়ির নারায়ণ শিলা। সারা বছর ঠাকুর শরিকদের বাড়ি বাড়ি ঘোরেন। এবাড়িতে দু’মাসের জন্যে তাঁর ঠিকানা ছিল ওই নাচঘর। এই দুটো মাস বাড়িতে উৎসবের আমেজ। পুজো উপলক্ষ্যে লোকসমাগমের একটা আলাদা মজা তো ছিলই, তাছাড়া আমাদের কাছে বড় আকর্ষণ ছিল প্রসাদের গুজিয়া, নকুলদানা আর সন্ধেবেলা আরতির সময়ে ঘন্টা বাজানোর প্রতিযোগিতা। খেলতে খেলতে একদিন নাচঘরের বাইরের দালানে চৌকাঠের ঠিক পাশেই একটা ছোটো গর্ত দেখেছিলাম, যার চারপাশটা পিতল দিয়ে বাঁধানো। গর্তে চোখ রাখলে নীচের তলাটা দেখা যায়। পরে শুনেছি, টানা পাখার মোটা দড়ি নামত ওর মধ্যে দিয়ে। আর নীচের তলায় বসে সেই পাখা টেনে ঘর ঠান্ডা রাখত মাইনে করা ‘পাঙ্খা পুলার’।
নাচঘরের কোল ঘেঁষে রাস্তার দিকের লম্বা টানা বারান্দাটা ছিল আমাদের চোর-পুলিশ খেলার জন্যে খুব জরুরি। আমরা যেতাম বটে, কিন্তু একটু বড়ো কোনো দিদি বা মা-কাকিমাদের সেখানে যাওয়া নিষেধ। দোতলা পর্যন্ত বাড়িটা বেশ গমগম করে, তারপরই তেতলাটা কেমন একটু একলা মতো। অভ্র মেশানো লাল সিমেন্টের সিঁড়ি উধাও হয়ে যায় তেতলার ঘর-দুয়ার পেরিয়ে ছাদের প্রসারতায়। বড়ো রাস্তার মুখ থেকে গলির ভিতর বেশ কিছুটা অব্দি ছড়িয়ে থাকা বাড়িটা ভাগ হতে হতে যেমন ছোট হয়েছে, ছাদটাও টুকরো হয়েছে ততবারই। তবু তার চিলছাদ, চিলেকোঠার ঘর আর মোটা মোটা শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের গায়ে লেগে থাকে অজানা কত না রহস্যের গন্ধ। দেউড়ি থেকে ওপরে না-এসে ডানদিকে চলে গেলে যে ঘরগুলো, সেখানে তখন কেউ থাকেনা। পরিত্যক্ত ঘরে হঠাৎ ঢুকলে একঝাঁক পায়রা ডানা ঝটপট করে উড়ে যায়। একুশ ইঞ্চি দেওয়ালের এই ঘরগুলোতে ভীষণ ড্যাম্প। গরমকালের দুপুরে আমরা বহুদিনই বালিশ বগলে করে শুতে যেতাম সেই ঠান্ডাঘরে। স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে হাত রেখে ঠাকুমা বলতেন, এ তোমাদের পূর্বপুরুষের চোখের জল। ব্যর্থতা, বঞ্চনা আর হতাশার গল্প কোন পরিবারেই বা না থাকে, ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম সেকালের বড়ো পরিবারে অন্তঃপুরের এক চিরকালীন আত্মশ্লাঘার কথা। এককালে বাড়ির মেয়েকে বিয়ের পরেও বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য ছাড়া তখন শ্বশুরবাড়ি যেতে দেওয়া হত না। জামাই শুধু মাঝেমধ্যে আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়িতেই জীবন কেটে যেত বিবাহিতা কন্যাটির। বিবাহ, মাতৃত্ব, বৈধব্য— সবটাই পিতৃগৃহে, স্বামীর ঘর করার সাধ মনেই গুমরে মরত। অথচ চোখের সামনেই সে বাড়ির ছেলেদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসারধর্ম পালন করতে দেখত। এই মানসিক যন্ত্রণা যাঁরা নিতে পারেননি, অনেকেই তাঁরা জীবন থেকে সরে গেছেন, বয়সের ধর্মে কেউ হয়তো ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন। সমাজ সংসারের চোখের আড়ালে পরিবারই বিচার করেছে তার। পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্যে এমন ঘটনা আজ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তা আগুনের তেজে ছড়িয়ে পড়ে। কুসংস্কারে ডুবে থাকা সমাজে সেদিন সে স্বচ্ছতা ছিল না। একদিকে যাদের এতো উন্নাসিকতা অন্যদিকে তাদের লৌকিকতার ধরণটি বড়ো বেশি ফর্মাল, আনুষ্ঠানিক। আমার ছোটোবেলায় মনে আছে, বিবাহিত পিসি কোনোদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে তাকে বাইরের লোকের মতো আনিয়ে দেওয়া জলখাবারে আপ্যায়ন করা হবে। কিন্তু আগে থেকে না জানিয়ে, অথবা নিমন্ত্রিত হয়ে না এলে সে বাড়ির সকলের সঙ্গে দুপুরের বা রাতের খাবার খেতে পারবে না। পরবর্তীকালে আমার যেসব বন্ধুদের আদি বাস পুব বাংলায়, তাদের বাড়িতে দেখেছি, দুপুরে ভাত খাওয়ার সময়ে কেউ এলে, বাড়িতে সেদিন যা রান্না হয়েছে, তা যত সামান্যই হোক, সেটাই ভাগাভাগি করে অতিথিকে খেতে বলার ভারি সুন্দর আর মানবিক একটি প্রথা আছে।
পুরোনো বাড়ির গোলগোল মোটা মোটা থামের আড়ালে আর ছাদ, বারান্দা, অলিগলির আনাচকানাচে ছাড়িয়ে থাকে ভয়ের শিকড়। দিনের আলো নিবে আসার পর ঘরের বাইরে বেরোতে গেলেই পায়ে পায়ে যেন বেধে যায়। দুষ্টু ছেলেমেয়েকে পড়তে বসাতে, খাওয়াতে কিংবা শোওয়াতে বড়োরা বাধ্য হন গায়ে কাঁটা দেওয়া সব কল্পকাহিনি আমদানি করতে। লোডশেডিং হলে পড়ার টেবিলে কেরোসিনের সেজবাতি জ্বেলে দেওয়া হত। ম্লান আলোয় পড়ার বইয়ের অক্ষরগুলো আরও যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠত, নজর চলে যেত সেজের আলোয় দেওয়ালের গায়ে হেঁটে বেড়ানো আমাদেরই তালঢ্যাঙ্গা ছায়াগুলির দিকে। ভয় পাবার একটা গা-শিরশিরানো মজা আছে। আছে বলেই তো আমরা বর্ষাদিনে বাজ-বিদ্যুতের আবহে ভূতের গল্প শুনতে চাই। তেমনি আবার ভয় দেখানোটাও একরকমের বিনোদন। আমাদের বাড়িতে আসতেন ছোটো পিসিমার দেওর রতুকাকা। একটু মেয়েলি হাবভাবের জন্যে এমনিতেই তিনি সকলের হাসির খোরাক হতেন, তার ওপরে তাঁর ছিল অসম্ভব ভূতের ভয়। অনেক পরিবারেই এরকম এক-আধজন মেয়েলি পুরুষ চিরকালই থাকেন, যাঁরা পুরুষের শরীরেও ঠিক পুরুষোচিত নন। ঘরে-বাইরে এঁদের নানারকম ঠাট্টা, অপমান সহ্য করতে হয়। এঁরা বাড়ির ফাইফরমাশ খাটেন, শাড়ির ফুল বসানো, রিফু করা জাতীয় নারীসুলভ কাজে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখনও এদেশে এল জি বি টি-র ভাবনাটাই অঙ্কুরিত . হয়নি। কিন্তু এঁদের নিয়ে সমাজ তেমন উচ্চকিতও ছিল না। স্বভাবতই এঁরা রোজগারপাতি করতেন না, এঁদের বিয়ে-থাও হত না, তবু যৌথ পরিবারে এঁরা কাকা, জ্যাঠা বা দাদা হয়ে মোটামুটি স্বাভাবিকভাবেই দিনাতিপাত করতেন। কোনোদিন বোঝা বলেও পরিগণিত হতেন না, আজীবন একজন স্নেহশীল রতুকাকাও এইরকমই একজন ছিলেন। সন্ধেবেলা কোনোদিন আমাদের বাড়িতে এলে, সদর দরজা দিয়ে বের হওয়া পর্যন্ত যাঁকে ভূতের ভয় দেখিয়ে সবাই বীভৎস আমোদ পেতেন। একবার তো তেলের টিনে দড়ি বেঁধে আংটায় ফুলিয়ে অন্য প্রান্তের দড়ি হবে পরজার ফুটোয় চোখ রেখে লাইব্রেরি ঘরে বসে রইলেন জেবু, রহুকাকার অপেক্ষায়। যেই না রতু নীচের ল্যান্ডিঙে পা রেখেছেন, বিদ্যুৎগতিতে মাথার ওপর নেমে এল তেলের টিন। আমরা তখন রুক্ষশ্বাসে অপেক্ষা করছি আর ভয় পাচ্ছি, পাছে রতুকাকা অজ্ঞান হয়ে যান! কিন্তু আশ্চর্য, তেমন কিছুই হলনা। যেটা দেখে মনে হয়েছিল, এভাবে ঠাট্টার পাত্র হয়েও বেবহয় এই রকাকারা গুরুত্ব পাওয়াটাকে উপভোগ করেন।
ভরের মতো, নিয়ম কানুন, অনুশাসন দুর্বলের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে কষ্ট ভোগ করতে দেখার মধ্যে একধরনের আনন্দ আছে। এইসব পুরনো পরিবার ছিল সেই বিকৃতির সুতিকাগৃহ। ঠাকুমা যখন এগারো বছরে এবাড়িতে সবে বউ হয়ে এসেছেন, তখনকার একটা ঘটনা শুনেছিলাম তাঁর কাছেই। বলিক বন্ধুটি গঙ্গাস্নানে চলেছেন পালকিতে, সঙ্গে তাঁর শাশুড়ি। ঘাটে গিয়ে জালে নেমে হুটোপুটি করবেন, মনোগত ইচ্ছেটা এরকমই। হঠাৎ যখন দেখলেন পালকি দিয়ে জাল ঢুকছে, ভয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। শাশুড়ি বুঝিয়ে বলেছিলেন, ঘাট যতই পারিবারিক হোক, বউ-মানুষ পর পুরুষের সামনে নেমে স্নান করতে তো পারে না, তাই পালকিসুদ্ধু জলে ডুবিয়ে গঙ্গার পবিত্র জল গায়ে লাগানো হচ্ছে। প্রতিবাদ যেদিক থেকে আসা উচিত, শুরুতেই সেই স্বরটাকে যদি দিগভ্রান্ত করে দেওয়া যায়, শাসকের আর কোন ভয় থাকে না। ছ’ক্লাসে পড়তে পড়তে উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়িতে বিয়ে হয়ে গেছিল আমার ঠাকুমার। পড়ার খিদেটা তখন গনগনে। বাবা মেয়ের শখের কথাটা বিলক্ষণ জানলেও তাঁর আর্থিক অবস্থা সেসময়ে বেশ কমজোর। এত ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া করতে সাহসে কুলোয়নি। তবে কলকাতায় তখন বিবাহিত মেয়েরাও অনেকে স্কুলে যাচ্ছে। সেই ভরসার সাহস করে ম্যাজিস্ট্রেট বেয়াইয়ের কাছে বলেও কোরেছিলেন কথাটা।
তখন ডিরোজিও সাহেব আর সশরীরে না থাকলেও গলি থেকে রাজপথে বইছে তাঁর নবযুগের হওয়া। শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে আলোকপ্রাপ্তা স্ত্রী পাওয়ার ইচ্ছেটি শাখা মেলছে। কাজেই জামাইয়ের প্রচ্ছন্ন সম্মতি থাকার প্রস্তাব পেশ হতেও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু বিধি বাম! সে প্রস্তাবে জল ঢেলে দিতে কর্তামশাইয়ের একটুকু দেরি হল না। বেশ স্পষ্ট করেই তিনি বলে দিলেন, “বৌমা যদি ইংরেজি শিখতে চার তো মেমসাহেব রেখে দিচ্ছি। বাসা, তার, সংস্কৃত শিক্ষনে পণ্ডিতমশাইকে খবর পাঠাব। বইপত্র যা লাগে শুনি আনিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু তাবলে পাঁচটা লোকের চোখের সামনে দিয়ে এবাড়ির বউ ইস্কুল যাবে লেখাপড়া শিখতে, এতবড় অনাচারটা তো আর ঘটতে দেওয়া যায় না।” অতএব…। মেমসাহেব কিংবা টিকিওলা পণ্ডিতমশাইকে বহাল করতে অবশ্য তিনি একটুও দেরি করেননি, তবে সে আর ক’দিন ? পরপর বড় পিসিমা আর জ্যেঠু জন্মাবার পর পড়ার সে তাগিদটা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলেছিল বালিকা বধূটি। যদিও তার স্বামী কিন্তু হাল ছাড়েননি। বাবার সিদ্ধান্তের কোন নাটকীয় প্রতিবাদ না করলেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজে যতটুকু পারেন আলো যুগিয়েছেন স্ত্রীকে। তার কর্মহীন অলস দুপুরগুলো ভরিয়ে দিয়েছেন ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘সবুজপত্রের’ ছায়ায়। ইস্কুলে দিদিমনির কাছে যা শেখা হল না, ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই তা সস্নেহে শিখিয়ে দিলেন রবিবাবু, বঙ্কিমবাবু। শেক্সপিয়ার বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে পরিচয় না- হোক, কাজ চালাবার মতো ইংরেজিটাও শেখা হল অমৃতবাজার পত্রিকার পাতায় রং পেন্সিলের দাগ দিয়ে।
ঠাকুমা নিজে যা পারেননি, চেয়েছিলেন নিজের মেয়েরা সেটা পারুক। কিন্তু মেয়েদের স্কুলপর্বটা ভালোয় ভালোয় কাটলেও তার পরের ধাপে পৌঁছে দিতে আর পারেননি। জাঁদরেল শ্বশুরমশাই না থাকলেও পরিবারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখনও ঘাপটি মেরে থেকে গেছে রক্ষণশীলতার ভ্রান্ত সংস্কারগুলি। যতদিন পরের ঘরে না যাচ্ছ, ঘরে বসে পড় না যত খুশি, কেউ বাধা দেবে না, প্রাইভেটে বি এ /এম এ পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার পরাকাষ্ঠা দেখাও, কিন্তু ওই পর্যন্তই। যুগ যুগ ধরে জমিয়ে তোলা অন্ধকার কি আর একবারে কাটে? লাফ দিয়ে ওঠা যায়, গাছের মগডালে? তবে খুব একটা টের পাওয়া না গেলেও, ততদিনে তলায় তলায় শুরু হয়ে গেছে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার, ওপরে ওঠার কাজ।
আমার মায়ের প্রথম সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়। সেটি ছিল পুত্রসন্তান। তারপরে আমার আবির্ভাবটা গোটা পরিবারের কাছেই বোধহয় তেমন অভিপ্রেত ছিলনা। এমনিতেই তো এ বাড়িতে মেয়েসন্তান জন্মালে শাঁখ বাজে না, অন্নপ্রাশন ও হয়না, শুধু বড়দিদা, মানে বাবার বড় জ্যেঠিমা, শুনেছি ঠাকুরবাড়িতে কুলদেবতা গোপীনাথের সামনে খবরটি জানিয়ে ঝুড়ি করে আনন্দনাড়ু বিলিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, পরিবারে যে নতুন মানুষটি ঈশ্বরের ইচ্ছায় এসেছে, তাকে সানন্দে আবাহন করে না নিলে ঈশ্বরকেই অপমান করা হয়। ব্যারিস্টার স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসন্তান এই ব্যক্তিত্বশালিনী রমণী তাঁর নিজের বিশাল বাড়িতে সম্পূর্ণ একা থাকতেন। সচরাচর কোন ব্যাপারে অন্যের শরণাপন্ন হতেন না। তবে দু’বাড়ির মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত এবং যোগাযোগ ছিল। পাড়া প্রতিবেশী অনেকেই সমস্যায় পড়লে তাঁর পরামর্শ নিতে আসত। কলকাতার বাড়ির শৈশব স্মৃতি আমার বাবা-মা ছাড়া আর যে একটিমাত্র মানুষ তাঁর অপার স্নেহে নাকি উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন, তিনি এই বড়োদিদা।
বাবা বদলি হয়ে কলকাতায় আসার পর আমি ভরতি হলাম বেথুন স্কুলে। আমাদের গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বেশি ছিল না, বড়জোর মিনিট পনেরো। দিব্যি টানা রিক্সায় মা’র সঙ্গে গল্প করতে করতে যেতাম। ভাড়া সেই সাতের দশকে যতদূর মনে পড়ে বারো আনা। হঠাৎ একদিন কানে এল, এবার থেকে নাকি স্কুলবাসে যাব। বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করতে করতে যাবার উত্তেজনায় সেদিন আর ভেবে দেখা হয়নি, নিয়মটা পাল্টালো কেন? পরে বুঝেছিলাম, আমাদের পরিবারের আদ্যিকালের মানসিকতায় ঘরের বউ দুবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেয়েকে পৌঁছতে যাচ্ছে, এটা সকলের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ হয়নি। মা’কে দেখতাম বাড়ি থেকে মাথায় ঘোমটা দিয়েই বেরোত, পাড়া ছেড়ে বড়ো রাস্তায় পড়ার পর কোনো কোনোদিন মাথার কাপড় নামিয়ে দিত, নামাতে ভুলেও যেত মাঝে মাঝে। আমার সেই মা, যার রাইফেল কাঁধে পাখি শিকারের ছবি দেখেছি মামারবাড়ির অ্যালবামে।
তা বাসে যেতে শুরু করার পর ঠাকুমা একদিন বললেন, “কাল সকালে তোমাকে আমি বাসে তুলে দিয়ে আসবো’খন।” আমার তো চোখ কপালে উঠেছে, “তুমি যাবে?” ঠাকুমাকে কখনও রাস্তায় নেমে একা কোথাও হেঁটে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বাবাও খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। কিন্তু গুরুজনের মুখের ওপর প্রতিবাদ করাকে তখন অসভ্যতা বলে মনে করা হত। অতএব পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় গলির মোড়ে শিবুদার মনিহারি দোকানের সামনে বাহাত্তর বছরের সম্ভ্রান্ত চেহারার সেই বৃদ্ধাকে অনেকেই ছেলে এবং নাতনির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। দেখে একটু অবাকও হলেন চেনা দু’একজন। তাঁরা তো আর জানেন না, এককালে বেথুন স্কুলের এই গাড়ি যখন ঘোড়ায় টানত, পর্দানশীন ছাত্রীদের পাছে পথে কেউ দেখে ফেলে, তার জন্যে সেই কালো গাড়ির জানলা রাখা হত শক্ত করে এঁটে, সেই আমলে ওই গাড়িতে চড়ে ইস্কুল যাবার স্বপ্ন দেখেছিল যে ফুটফুটে মেয়েটি, আজ ঠাকুমা হয়ে সে-ই এসেছে, তার সে স্বপ্নকে সাকার হতে দেখতে।
বাড়িতে মায়ের কাছে পড়তাম। আমার পড়াশোনাটাকে মা বেশি গুরুত্ব দিত বলে যৌথ পরিবারে ঠেস দিয়ে কথাও কম শোনেনি। “ওই তো কালো কুচ্ছিত মেয়ে, পড়িয়ে তাকে একেবারে জজ ম্যাজিস্ট্রেট করবে”, এ কথা আকছার
কানে আসত, কিন্তু মা খুব কানে নিত বলে মনে হয়না। আসলে যৌথ পরিবার বলতে যে সুন্দর ছবিটা গল্প উপন্যাসে পড়েছি, আমার নিজের জীবনে সেটা ফ্যান্টাসিই থেকে গেছে। ছোটবেলায় বাবা চাকরিসূত্রে মুম্বাইতে থাকতেন, মাঝেমাঝে লম্বা ছুটি নিয়ে কলকাতা আসা হত। সেসময়ে পারিবারিক অশান্তি অপরিণত মনে ভারি একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করত। ‘অশান্তি’ শব্দটাও সম্ভবত সেই তখনি আমার বাংলা ভোকাবুলারিতে যোগ হয়। নিজের চেহারা নিয়ে একটা হীনমন্যতাবোধ ওই ছোটোবেলাতেই সেই যে মনে গেঁথে গিয়েছিল, সারাজীবনে তার থেকে আর বেরোতে পারলামনা। যে বয়সে সব মেয়েরাই সাজে, আয়নার সামনে দাঁড়াতে গেলেই তখন ওই ‘কুচ্ছিত’ বিশেষণটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত। মা ছাড়া আর কেউ সেটা জানত না। হয়ত সেইজন্যেই মা চাইত শিক্ষা দিয়ে সে খামতিটাকে ঢেকে দিতে। শোভাবাজারে আমাদের বিরাট পরিবারের মিলনক্ষেত্র ছিল ঠাকুরবাড়ি। সেখানে কেউ বড়ো একটা চিনত না আমায়। মাধ্যমিকের রেজাল্ট ভালো হবার পর নামটা এক আধটু জানল কেউ কেউ, পরে যখন ‘বর্তমান’ কাগজে কাজ করি, একবার ঠাকুরদালানে বাবার সঙ্গে কারুর দেখা হয়েছিল, যিনি আমার লেখা কাগজে পড়েছেন। পরিচয় জেনে তিনি নাকি বলেছিলেন, “আপনি বুঝি ওর বাবা?” মেয়ের পরিচয়ে বাবাকে পরিচিত হতে দেখে মা সেদিন খুশি হয়েছিল খুব । আমার সমস্ত সত্ত্বার সঙ্গে কলকাতা শহর এবং শোভাবাজারের বাড়ি যতোখানি সম্পৃক্ত, ঠিক ততটা না হলেও ছোটোবেলার দিনগুলোর গায়ে এখনও কিছুটা লেগে আছে মুম্বাই শহরের গন্ধ। তখন অবশ্য মুম্বাই নামটা চালু হয়নি, বম্বে-ই বলা হত। নেপিয়েন্সি রোডে বাবাদের অফিসের ফ্ল্যাটে যাবার আগে আমরা কোলবা দেবী আর বান্দ্রা অঞ্চলে ভাড়া থেকেছি কয়েক দফায়। প্রথম যখন সবাই মিলে বম্বে যাওয়া হল তখন নতুন জায়গায় আমাদের সংসার গুছিয়ে দিতে গেছিলেন আমার দাদা, অর্থাৎ দাদামশাই আর দিদিমা। দাদা ছিলেন খুব হাসিখুশি আর খুবই কর্মঠ। কোন অসুখবিসুখ ছিলনা। ওখানে যাবার দিন কয়েকের মধ্যে দাদার স্ট্রোক হল। ডাক্তার বললেন, হাসপাতালে যাবার দরকার নেই, বাড়িতেই রেস্টে থাকুন। তার অল্পদিন পরেই বম্বেতে শুরু হচ্ছে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ। আমার খেলা পাগল দাদা ডাক্তারকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, “মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে পারব তো?” ডাক্তারও হাসতে হাসতেই উত্তর দিয়েছিলেন, “নিশ্চয়ই।” এর দুদিনের মধ্যেই সেই ডাক্তারকে 96 আবার আসতে হয়েছিল আমাদের ফ্ল্যাটে, দাদার ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে। নতুন ফ্ল্যুটি তখনও ঠিকমতো গোছানোই হয়নি, আচমকা ধাক্কায় তার নতুন বাসিন্দাদের জীবনটাও অগোছালো হয়ে গেল। আমাকে পাশের বাড়িতে রেখে বাবা-মা, দিদ উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে গেল দাদাকে নিয়ে। আমি বারান্দা থেকে টা-টা করলাম। কিন্তু দাদা চোখ খুললই না। সকালে যখন মিছিমিছি চা করে নিয়ে দানার ঘুম ভাঙাতে গেছিলাম, তখন থেকেই দাদা আর চোখ খোলেনি। আড়াই বছরের জীবনে সেই আমার প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। স্নেহের উৎসমুখগুলো শুকিয়ে যাবার শুরু। যথানিয়মে যথাসময়ে শুরু হল পড়াশোনা। মিশনারি স্কুল। সুন্দর সাজানো ক্লাসরুমে ছোটো ছোটো রঙিন চেয়ার টেবিল। আমি বসি একটু পিছনের সিটে। ভাষাটা রপ্ত না হওয়ায় শিশুমনে অদ্ভূত এক হীনমন্যতাবোধ কাজ করে। ‘প্রেজেন্ট প্লিজ’ ছাড়া সারাদিনে আর কোন কথা নেই। ইংরেজি বা হিন্দি যা জানি তাতে কাজ চলে যায়, কিন্তু বন্ধু পাতানো হয় না। মুখচোরা বলে কেউ কথাও বলেনা। বাবা যেদিন পৌঁছতে যায়, ক্লাসের বাকি বালখিল্যদের সঙ্গে বেশ একটু হৈ-চৈ করে আসে। এইভাবে দু’দিনেই বাবা খুব পপুলার হয়ে গেল। বারা আমাকে মোটেই চেনেনা তারাও বাবা গেলেই ঘিরে ধরে। একদিন এদেরই কেউ বলল, “তোমার বাবা কী সুন্দর দেখতে!” বাবার সুন্দর চেহারা আমার ব্যক্তিগত শ্লাঘার জায়গা। তবে এ ব্যাপারে আমার একটা কথা সকলকে জানাতে ইচ্ছে করল। ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম, বাবার বয়স যখন বছর বারো, সব ভাইবোনদের একবার মারাত্মক গুটি বসন্ত হয়। একটি বোন তাতে মারাও যায়। সুস্থ হবার পর প্রথম আয়নায় মুখ দেখে বাবা নাকি ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কেঁদেছিল, “আমি কেন ব্রাউন হয়ে গেছি” বলে। এটা শুনে আমি বোঝার চেষ্টা করতাম, এই যদি ব্রাউন হয়, তবে তার আগের রংটা কী থাকতে পারে। কিন্তু এই গোটা আখ্যানটি ইংরেজি বা হিন্দিতে বুঝিয়ে বলার এলেম তখনও হয়নি আমার, তাই ব্যাপারটাকে অতি সরলীকরণ করে সগর্বে ঘোষণা করে দিই, “এ আর কী এমন সুন্দর দেখছ তোমরা! আমার বাবা তো আরও সুন্দর” বালখিল্য বাহিনী থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করে, “ওমা, যে এসেছিল সে তোমার বাবা নয়?” আমি অকুতোভয়ে বলি, “না না, ও তো আমার কাকা, বাবা আরও কত সুন্দর!” ঈশ্বর জানেন, এই অনৃতভাষণটির মূলে বিন্দুমাত্র অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। কথাটা কিছুদিনের মধ্যেই কীভাবে যেন, পড়বি তো পড় খোদ বাবার কানেই পৌঁছে যায়। এবং বাড়িতে এই নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি হয়। অতি সাধারণ চেহারার ভীতু ভীতু এই বাঙালি মেয়েটার ঝুঁকে পড়া মেরুদণ্ড পনেরোই আগস্ট। স্বাধীনতা দিবস। সকালে রোলকলের সময়েই ক্লাস টিচার সেই প্রবাসে এক ধাক্কায় সিধে হয়ে গিয়েছিল একদিনের ঘটনায়। সেদিনটা ছিল প্যারেড হবে, তারপর টিফিন প্যাকেট দেওয়া হবে। প্যাকেট নিয়ে সবাই যে যার বলে দিলেন, আজ আর ক্লাস হবেনা। সবাই লাইন করে মাঠে যাবে, ওখানে ক্লাসে এসে বসেছি। সারা ঘরে খচমচ আওয়াজ। এর মধ্যে এক হাসিখুশি দিদিমণি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, “এতক্ষণ যে গানটা শুনলে, জানো, সেটাকে কি বলে ?” ক্লাসশুদ্ধু সব্বাই একসঙ্গে বলে উঠলো, “জাতীয় সংগীত।
ন্যাশনাল অ্যানথেম।”
– “বাহ্! এ গানের ভাষাটা কী, জানো কেউ ? ”
কচি গলাগুলি জানা সব ভাষার নাম একাদিক্রমে বলতে থাকে, – হিন্দি,
মারাঠি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি…
আমার তখন বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। সিনেমা দেখতে গিয়ে হলে শুনেছিলাম এই গান। বাবা বলেছিলেন এ গানের গল্প। এরা কেউ সেটা মনে হয় জানেনা। খুব দ্বিধা নিয়ে ডান হাতটা আধখানা তুলি। “ইয়েস পনিটেল?” চেয়ারের নীচে পা-কাঁপছে বুঝেও উঠে দাঁড়াই— “বাংলা, সিস্টার, বেঙ্গলি।” বলেই প্রবল উত্তেজনায় বসে পড়ি। “অ্যান্ড হু রোট দি সং?” সবাই একটু চুপচাপ। তারপর আবার শুরু হয় নামের মিছিল। “নো-নো-নো”— এবার দিদিমণিরও বোধহয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। “অ্যান্ড ইউ?” এবারে তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াই, দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চারণ করি আপামর বাঙালির সেই প্রিয়নাম— “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।” দিদিমনি উচ্ছ্বসিত, “ভে-এ রি গু-উড!” এবার ক্লাসে অন্যরকমের কথা শুরু হয়ে যায়। পাশের ডেস্ক থেকে একটি ছাত্র অভিমানে গাল ফুলিয়ে বলার চেষ্টা করে, “শি নোজ, বিকজ শি ইজ
ফ্রম বেঙ্গল।”
“ইউ শুড অল নো, বিকজ ইউ অল আর ফ্রম ইন্ডিয়া।” দিদিমণি হাসিমুখে দু’দিকে দু’হাত ছড়িয়ে বলেন। স্কুল ছুটি হয়ে যায়। সবাই বেরোবার জন্যে হুটোপুটি লাগায় । আমিও গেটের দিকে এগিয়ে চলি। মা আসবে নিতে। তারই মধ্যে টের পাই, পা-দুটো আর কাঁপছেনা। পরবাসে এক বাঙালি মেয়ের আত্মবিশ্বাস কখন অজান্তে আকাশ ছুঁয়ে ফেলে এক বাঙালি কবির প্রসাদে।
ক্লাস টু-তে একদিন অ্যাসেম্বলিতে শুনলাম মানুষ নাকি চাঁদে নেমে পড়েছে আগের দিনই, উঁচু ক্লাসের দাদাদিদিদের সেদিন কী উত্তেজনা! বছর খানেকের মধ্যেই যে চাঁদে গিয়ে থাকা যাবে, এ ব্যাপারে দেখা গেল অনেকেই মোটামুটি নিশ্চিত। রাতে বাড়ির ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে পড়ে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, সেই রুপোলি থালাটার ওপরে হাঁটছে নাকি কেউ। রাগে অগ্নিশর্মা সুয্যিমামার চেয়ে ঠান্ডা সুস্থির চাঁদ চিরকালই সবার আপনজন। কলকাতায় সন্ধেবেলা লোডশেডিং হলে অনেকদিনই ধোয়া ছাদে মাদুর বা শতরঞ্চি পেতে আমরা আকাশমুখো হয়ে শুয়ে থাকতাম। ছাদের এমাথা থেকে ওমাথা হাঁটলে চাঁদবাবাজীও তারা বসানো মেঘের সমুদ্দুর সাঁতরে চলতে
থাকত সঙ্গে সঙ্গে।
সেই স্বপ্নরাজ্যে বসবাসের ভাবনাটা আমার একা দুপুরগুলোয় অনন্ত এক কল্পনার দরজা খুলে দেয়। ছোটোবেলায় কোনোদিন, বাড়ির বাইরে কোথাও কারো সঙ্গে খেলতে যাবার অনুমতি ছিল না। বন্ধুদের বাড়িতেও না। বাড়ির বাইরে থেকে কেউ যে খেলতে আসবে সেটাও না-মঞ্জুর। সারাটাদিন নিজের সঙ্গেই কথা বলি। কখনো সোচ্চারে, কখনো আবার মনে মনে। ড্রেসিং টেবিলের নীচে পা ছড়িয়ে বসে আয়নার আমিটার সঙ্গে কত গল্পই যে করি! সেখানে কোনো ভাষার পাঁচিল নেই, কথা হয় প্রাণের ভাষায়। দুপুরবেলা মা সাধারণত শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ত, মাঝে মাঝে মাটিতে বসে ছবি আঁকত। আমি তখন খাটের ওপর উপুড় হয়ে মার-ই দেওয়া অঙ্কের টাস্ক করছি। লোহার গরাদ ওয়ালা কাঠের জানলার খড়খড়ির পাল্লা ফাঁক করা আছে আলো আসার জন্যে । অঙ্ক থামিয়ে ঝুঁকে পড়ে মা’র ছবি আঁকাও দেখছি মুগ্ধ হয়ে। “ও মা, আমাকে শেখাবে?” মা ছবি থেকে চোখ না সরিয়ে বলত, “ছবি আঁকা কাউকে শেখানো যায়না। যেটা দেখে তোমার ভালো লাগল, খারাপও লাগে যদি, সেই ভালো লাগা বা খারাপ লাগাটাকে তোমার মতো করে ফোটাতে পারলেই তো ছবি হয়ে গেল। তুমিও তো স্কুলের খাতায় কী সুন্দর গ্রামের ছবি এঁকেছ। তবে যখন সত্যিকার গ্রাম দেখবে, ছবিটাও বদলে যাবে, দেখো।” মানিকতলায় মামার বাড়িতে মায়ের ক্যানভাস লাগানো ইজেল দেখেছিলাম। সেটা কেন আনেনি, জানতে চাইলে মা বলত, মাটিতে বসে আঁকতে নাকি বেশি সুবিধে। কখনো বলেনি, এ বাড়িতে ওটা কালচারাল শক হবে, তাই। হাসিমুখে নিজেকে যে কতটা বদলে নেওয়া যায়, মা ছিল তার জ্যান্ত উদাহরণ। দুপুর রোদে খালি পায়ে যে ঠাকুরবাড়ি যাচ্ছে অশোক ষষ্ঠী করতে, রাতে ছোট্ট টাইপ রাইটারে বসে সে-ই আবার বাবার উকিলের চিঠির ড্রাফট করছে। বাবা যে মাঝে মাঝে অফিসের পার্টিতে মা’কে নিয়ে যেত, এটা নিয়ে বাড়িতে প্রবল অশান্তি হত।
সত্যি বলতে কী আমি নিজেও সেটা মন থেকে ঠিক মানতে পারতাম না, একটু বড়ো হওয়ার পর। তবে এই মা-ই যখন বিজয়ার দিন দালানের এক প্রান্ত থেকে গলবস্ত্র হয়ে জ্যেঠুকে প্রণাম করার সময়ে আমাকে বলতে পাঠাত আর আমি লাফাতে লাফাতে গিয়ে চিৎকার জুড়তাম, “ও জ্যেঠু, মা তোমাকে প্রণাম করল”, তখন ভাবতাম মায়ের কোন চেহারাটা আসল! আমাদের পরিবারে তখনও পর্যন্ত ভাসুর ঠাকুরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা বা কোনো আদানপ্রদান চলত না।
পাছে বাংলা না শিখি, তাই মা কলকাতায় এলেই পাঁজা করে শিশুপাঠ্য সব বই নিয়ে যেত। ‘শুকতারা’, ‘শিশুসাথী’, দেবসাহিত্য কুটিরের ‘উপহার’, ‘দেবদেউল’, ‘মণিহার’; ঘনাদা আর টেনিদার বই। প্রথাগত ধারায় বর্ণপরিচয় পড়া হয়নি বটে, কিন্তু এই সাধারণ বইগুলোই ছিল আমার সাহিত্যশিক্ষার সোপান। বাবা সময় পেলে, রাতে খাওয়ার পর বা ছুটির দিনে বই পড়ে শোনাতেন। যে গল্পটা শেষ হল না, তার বাকিটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতাম অধীর আগ্রহে। হয়ত পরের দু’একদিন বাবার ফিরতে দেরি হল, বা কাজে ব্যস্ত থাকতে হল, কৌতূহল ধরে রাখতে না পারলে বাধ্য হয়ে নিজেই পড়তে চেষ্টা করতাম। ঠেকে ঠেকে গোঁত্তা খেতে খেতে কবে আস্তে আস্তে সড়গড় হয়ে গেল পড়াটা। এখন মনে হয়, ওই পড়ে না দেওয়াটা বোধহয় কায়দা ছিল আমাকে পড়তে শেখাবার। আজকাল বাংলায় থেকেও অনেক ছোটোরা দেখি বাংলা পড়তে বা লিখতে একেবারেই শেখে না। স্কুলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসেবেও বাংলা পড়ানোর নাকি ‘যৌক্তিকতা’ খুঁজে পান না তাদের বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন বাবা-মা। আমার নিজের বাংলার আনন্দপাঠের কথা তাদের খুব বলতে ইচ্ছে করে, সাহসে কুলোয়না। কলকাতায় এসে দেখলাম সমবয়সী বন্ধুরা অনেকেই আমার থেকে অনেক বেশি পড়ে ফেলেছে এর মধ্যেই। আমার দৌড় তখনও ‘শিশু’ বা ‘সোনার তরী’র কিছু কবিতা, ‘গল্পগুচ্ছের’ গুটিকয় গল্প, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত’, ‘দত্তা’ আর বড়জোর বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’। সিরিয়াস প্রবন্ধে তো দন্তস্ফুট করতেই পারিনা। এদের সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সব বিষয় বাংলায় পড়তে হবে জেনেও মা কিন্তু আমাকে কলকাতায় এসে কোনো ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ভরতি করেনি। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হলেও পরে বুঝেছি মায়ের এই সিদ্ধান্তটি কতখানি সঠিক ছিল। জীবনে যেটুকু যা শিখতে পেরেছি, তার জন্যে স্কুলের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।
বছরখানেকের মধ্যে পাকিস্তানের মুঠো থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে লড়াই বাধল ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের। শুধু মাতৃভাষায় কথা বলতে চেয়ে কীভাবে রক্তস্নান করে ওঠে এক দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্র, পুরোপুরি না বুঝলেও রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। কলকাতায় বসে সেটা যতখানি টের পাওয়া যায়, বাংলার বাইরে থেকে তার ছিটেফোঁটাও যায় না। যখন কলকাতায় আসি, চারদিকে একটা চাপা উত্তেজনা। শুনতে পাই ‘ব্ল্যাক আউট’ চলছে— নিষ্প্রদীপ। বাড়ির সব জানলার কাচের শার্সিতে যোগ চিহ্নের মতো করে খবরের কাগজ সাঁটা। হ্যারিকেন বা সেজবাতির চিমনির গায়েও কাগজ জড়ানো যাতে বাইরে আলো বেশি না ছড়ায়। সন্ধেবেলা কোনো কোনো দিন সাইরেন বেজে উঠত। পটপট করে নিভে যেত সব বাড়ির আলো। বোমারু বিমান নাকি আকাশে চক্কর দিচ্ছে। যতক্ষণ না ‘অল ক্লিয়ার’ সাইরেন বাজছে, ততক্ষণ সবাই জড়সড় হয়ে বসে। রোজ রাতে রেডিয়োতে বেজে ওঠে দ্রুতলয়ের বাজনা, এক সুললিত গম্ভীর গলায় শুরু হয় ‘সংবাদ পরিক্রমা’। কী আশ্চর্য তার ভাষা! বাংলাদেশের মানুষের যন্ত্রণা এপারের মানুষ যে কতখানি অনুভব করছেন, বাড়িয়ে দিচ্ছেন সহানুভূতি, সহমর্মিতার হাত, সেটা আজ যেভাবে বলছি, ঠিক সেভাবে সেদিন উপলব্ধি করতে না পারলেও রাতের খাওয়ার পর বড়োদের সঙ্গে বসে শুনতাম মনযোগ দিয়ে, এ ছবিটা বেশ মনে পড়ে। রেডিয়োতে মুজিবর রহমানের বক্তৃতা শোনা যায় কোনো কোনোদিন। একটা গোটা জাতিকে উজ্জীবিত করে চলেছেন একজন মানুষ, এটা যেটুকু বুঝতাম, ততই মনে মনে যেন শরিক হয়ে উঠলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের। আর সেইসঙ্গে অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠলাম ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর। বাংলাদেশ স্বাধীন হল, মনে হল বুঝি আমরাই মুক্তি পেলাম।ইতিমধ্যে এপার বাংলায় আর এক অশান্তি ছাইচাপা আগুনের মতো ধুইয়ে উঠেছে। সমাজকে বদলে দিতে অস্ত্র ধরেছে প্রতিবাদী তরুণের দল। তাদের বিপ্লবের ভাবনাকে মন থেকে সমর্থন করলেও নাশকতার আতঙ্কে তটস্থ হয়ে আছেন সাধারণ মানুষ। সেটা মোবাইল ফোন, মেসেজ বা হোয়াটস অ্যাপের যুগ নয়, টেলিভিশন পর্যন্ত আসেনি, কাজেই অনেক দেরিতে খবর বহন করে আনে পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড। সর্বহারার ক্ষমতায়নের রাজনীতি সেই নদশ বছর বয়সে স্পষ্ট বোঝার কথা নয়, কিন্তু সকালে কাগজ খুললেই হত্যা আর সংহারের সংবাদে বাবা-মায়ের বিচলিত হওয়াটা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হত।
যদিও স্থানীয় কাগজ সুরে বাংলার ভয়াবহতা নিয়ে স্বভাবতই কেমন না। ইতিমধ্যে শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা কলকাতার ফিরে যাব। বাবার সহকর্মী এবং জ্ঞাতি ভাই ব্যাংকের কো-অপ যাওয়ার পর থেকে বাবাকে বারবার বলছিলেন সেখানে চলে আসতে, কিন্তু বাবা কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে, পারিবারিক পাড়া ছেড়ে আসবে না। আমাদের পুরোনো বাড়ি আবার ভাগ হল, বদলে গেল সদর দরজা। পাঁচিল উঠে এল দেউড়ি আর উঠোনের মাঝে। ছোটো হয়ে গেল আমার মুক্তির আকাশ, আমর প্রিয় ছাদ। বাবা যেহেতু চাকরি করতেন এবং বাবার যেহেতু ছেলে নেই, ত বাবার বরাদ্দ হয়েছিল বাড়ির পিছনের পুরনো, পরিত্যক্ত অংশ। করচের কথা কেউ কান দেয়নি। তোমার তো চাকরি আছে। চাকরির জোরে লোন নেওয়ার সুযোগও আছে। বরচ নিয়ে ভাবনা কী? পরে শুনেছি, বাবার অভিমান হয়েছিল বুব, অভিমান থেকে জেদ। আর সেই জেদের জোরেই সাহস করে বুদ্ধি বাটিতে বাবা-মা তিলে তিলে গড়ে নিতে পেরেছিল নিজেদের স্বপ্নসৌধ।
মানুষের মন বড়ো বিচিত্র। যাকে চিরটাকাল ভেবে এসেছি পর, বিদাে মুহূর্তে সেই কীভাবে যেন ‘যেতে নাহি দিব’ বলে দুই হাতে গলাটি জড়িয়ে ধরে। ক্লাসে যেদিন জানালাম চলে যাব, সবাই ভারি অবাক হল। বাড়ি বাছি বলায় একজন চোখ পাকিয়ে বলল, “বাড়ি তো এটাই, ওখানেই বরং বেড়াতে যাও।” তা বটে। এতদিন সেরকমই ঘটেছে। তাদের চাপাচাপিতে শেষ অব্দি কথা দিতে বাধ্য হলাম যে খুব শিগগিরই ফিরে আসব আবার। রাখা যাবেনা জেনেও এমন কত কথাই না দিই, দিয়েই চলি আমরা গোটা জীবন জুড়ে। ভালোবাসার উপহারে দু’হাত ভরিয়ে ঘরে ফিরেছি সেদিন। কেউ দিয়েছে পেন্সিল, কেউ তার প্রিয় সুগন্ধি ইরেজার, রুমাল, টফি, কমিকস— সেই সেকালে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে যেটুকু হত আরকি। কলকাতায় এসে ভরতি হলাম যে ইস্কুলে তার উঁচু পাঁচিল বাইরের জগৎটা থেকে যেন আলাদা করে ঘিরে রাখে, আগলে রাখে তার সযত্নে ফোটানো কোরক গুলিকে। বিরাট সবুজ খেলার মাঠের ধরে তার মস্ত ড্রিল শেড। সকালে স্কুল শুরুর আগে সেখানে প্রার্থনা হয়। উপনিষদের মন্ত্র— ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেহস্ত মা মা হিংসী। বিশ্বানী দেব সবিতদুরিতানি পরাসুব, যন্ত্রদ্রং তন্ন আসুব। নমঃ সম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ, ময়স্করায় চ, নমঃ শিবায় শিবতরায় চ। সবাই মিলে এক লয়ে উচ্চারণ করে চলেছে। অচেনা সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ যত দিন রপ্ত না হয়েছে মাথা নীচু করে থাকতাম। কিন্তু আশ্চর্য, আমার অজান্তেই আমার গভীরতম বোধের মধ্যে কোথাও উচ্চারিত হত আমার শিশুকাল থেকে বলে আসা ধ্যানমন্ত্র, ‘Our Father, which art in Haven, / Hallowed be thy name, / Thy kingdom come / Thy will be done in Earth, as it is in Heaven./ Give us this day our daily bread / And forgive us our trespasses, / As we forgive them/ those who trespass against us./ And lead us not into temptation, /But deliver us from evil./ For Thine is the kingdom, / And the power, and the glory, / For ever and Ever. Amen.’ কেমন এক রকমে যেন টের পেতাম, মিশে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে সব। এর অনেক বছর পরে উপনিষদের ওই মন্ত্রটির রবীন্দ্রনাথকৃত বঙ্গানুবাদটি চোখে পড়ে। এই বৈদিক মন্ত্র কবির নিজেরও খুব প্রিয় ছিল। ‘তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা ব’লে যেন জানি, তোমায় নত হয়ে যেন মানি, তুমি কোরো না কোরো না রোষ। হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও যত পাপ যত দোষ। যাহা ভালো তাই দাও আমাদের, যাহাতে তোমার তোষ….।’ সেদিন সত্যিই নিজের ততদিনে পরিণত বোধের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র এবং খ্রিস্টিয় প্রার্থনা একাকার হয়ে যায় অর্থে, অনুভবে। ধর্মের উত্তরণ ঘটে চিরায়ত মানবতায়। প্রিয় শহর কোল পেতে নেয় তার ফিরে আসা কন্যাটিকে।
কৃষ্ণ শর্বরী দাশগুপ্ত: জন্ম ১৯৬২, উত্তর কলকাতার একটি রক্ষণশীল পরিবারে। বাবার কর্মসূত্রে শৈশব কেটেছে মুম্বই শহরে। কলকাতায় ফিরে বেথুন স্কুলে ভর্তি হওয়া। কিছুটা অনিচ্ছায় কলেজের পড়াশোনা বাণিজ্য শাখায়, তারপর পথ বদলে স্নাতকোত্তরে সাংবাদিকতা। এম এ পড়তে পড়তে ‘বর্তমান’ দৈনিকে চাকরি এবং সেখান থেকে ইউপিএসসি-র মাধ্যমে আকাশবাণীর বৃহত্তর পরিমণ্ডলে। কাজের পাশাপাশি চলেছে আংশিক সময়ের অধ্যাপনা এবং শখের লেখালিখি।
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।