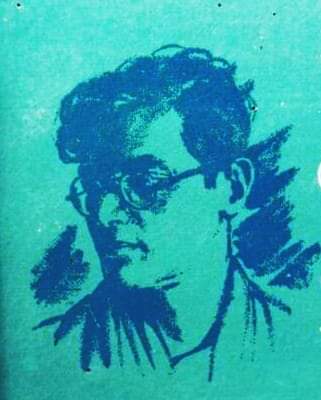তখন সদ্য এমএ পাশ করেছি, কলকাতার এ কলেজ ও কলেজে মাথা গলানোর চেষ্টা করছি। কেন না, নেট এবং সেট পরীক্ষার দৌলতে আমার দুই প্রিয় কথাসাহিত্যিকের একজন─ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন বিভূতিভূষণ─ ক্রমেই ধূসর হওয়ার পথে। নেট পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে গেছে, ‘ময়নাদ্বীপের পরিসীমা কত?’ আর সেট পরীক্ষা বুঝিয়েছে হোসেন মিয়াঁ সম্পর্কে মোটে ত্রিশটি শব্দ লেখাই যথেষ্ট। সেই সব গলিঘুঁজি থেকে মুখ ফিরিয়ে অতিথি হিসাবে পৌঁছেছি কলকাতার একটি নামকরা কলেজের ইন্টারভিউ বোর্ডে৷ এক্সটারনাল এক্সপার্টকে ধরলে মোট চারজন ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা‘-র উপর ডেমনস্ট্রেশন দিতে বলা হয়েছিল আমাকে। আমি বলে চলেছি আমার সাধ্যমতো। হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে একজন অধ্যাপক জানতে চাইলেন: ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’-য় কোন পাশ্চাত্য উপন্যাসের প্রভাব আছে?’ সত্যি কথা, বলতে পারিনি। তাতে সেই অধ্যাপকই আমায় নিজের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, আমি কি অ্যালবেয়ার কাম্যু-র ‘দ্য প্লেগ’ উপন্যাসের নাম শুনিনি? অবাক হয়ে বলে ফেলেছিলাম, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত কোনও উপন্যাসের উপর ১৯৩৬-এ প্রকাশিত ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’-র প্রভাব কী করে থাকা সম্ভব? বলাই বাহুল্য, চাকরিটা না-হলেও বাঙালির তুলনাত্মক ভ্রম সম্পর্কে প্রতীতি জন্মেছিল আমার। এরপর যখন টিউশনি পড়াই, তখন দেখি বিভিন্ন কলেজে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ সম্পর্কে অধ্যাপকরা পড়ান, ওটি নাকি নিয়তিবাদ-কেন্দ্রিক উপন্যাস। অবাক হয়ে ভাবি, ‘মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি’─এই বাক্যটিকে কী নির্মম ঔদাসীন্যে বাইপাস করে যাওয়া চলে। ঠিক যেমন ময়নাদ্বীপ আমাদের নিবিড় পাঠনির্ভর সমালোচনায় হয়ে যায় উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রতীক।
আজ মানিকের জন্মদিন। এইসব ক্যালেন্ডারে-দাগ-মারা দিনগুলো এলেই বাঙালির অননুকরণীয় আদেখলাপনা বেরিয়ে আসে। সামাজিক মাধ্যম জুড়ে তাঁর কিংবা তাঁর বইয়ের ছবি। অথচ আলোচনা নেই কোনও। আলাপের সুর সেখানে অনুপস্থিত। আমরা প্রশ্ন করি না যে, কেন শুনব ‘হলুদপোড়া’ অতিপ্রাকৃত গল্প? ‘দিবারাত্রির কাব্য’ বা ‘চতুষ্কোণ’ নিয়ে কথা হয় না কেন? বাজারে মানেবই নেই বলে? নাকি ‘দিনের কবিতা’ শুরু হওয়ার আগে ওই ছোট্ট ভূমিকায় সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন স্বয়ং মানিক, সেইজন্য? ‘মানুষ নয়─আসলে মানুষেরই Projection’! অধিকাংশ বাঙালি বিশ্বাস করেন যে, ‘পদ্মানদীর মাঝি’ লিখতে গিয়ে মানিক পদ্মার চরে মাঝিদের সঙ্গে দিন গুজরান করেছেন, ‘ভাগাভাগি করে বিড়ি খেয়েছেন’ পর্যন্ত। বিষয়টা অনেকটা ওই ঈশ্বরের প্রগলভ নদী সাঁতরে পারাপারের অতুল মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠার মতোই। যে ভাবে মিথ্যা একটা সময় পর মিথ হয়ে যায়, মানিকের পদ্মা-লাগোয়া এই কিসসাটাও তেমন।
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ান। মাঝেমধ্যেই বিকেলের দিকে পায়ে-পায়ে পৌঁছে যেতেন ‘পরিচয়’ পত্রিকার দপ্তরে। ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে উঠে গিয়েছে সরকারি নিষেধাজ্ঞা। ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে ঠিকানা বদলে গিয়ে হ্যারিসন রোডে এসে থিতু হয়েছে পত্রিকাদপ্তর। এমনই এক সন্ধ্যায় পত্রিকার দপ্তরে জোর আড্ডা: তারকনাথের প্রশ্নের জবাবে মানিক জানান যে, ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে দু’-একবার পদ্মায় গিয়েছিলেন। তা বাদে আর নয়। তারকনাথ জবাবে যা বলেছিলেন, তা অবশ্য এখানে অপ্রাসঙ্গিক। অন্য ঘটনাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন চিন্মোহন সেহানবীশ। চিন্মোহন তখন জেলে। মানিক দেখা করতে গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে। বড়া কমলাপুর তখন উত্তাল, আগুন জ্বলছে সেখানে। চিন্মোহন মানিককে ওখানে গিয়ে, সবটা নিজের চোখে দেখে, লিখতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে মানিক জানিয়েছিলেন যে, তিনি অবশ্যই লিখবেন, কিন্তু তার জন্য ওই নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে হবে না। আফ্রিকা না-গিয়েও তো একটা ‘চাঁদের পাহাড়’ লেখা যায়─ যদি মনে কল্পনা আর কলমে জোর থাকে। উল্লেখ থাক, বড়া কমলাপুর না-গিয়েও সেখানকার তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে যে-গল্পটি লিখেছিলেন মানিক, সেটি ‘ছোটবকুলপুরের যাত্রী’।
কাউকে খাটো করতে চাই না, কিন্তু বিশ্বাস করুন, গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে জানতে গেলে সবার আগে খবরের কাগজের ফিচারিস্ট লেখাগুলো পড়া এবং সেগুলো বিশ্বাস করা বন্ধ করা উচিত। গবেষণার জন্য মানিকের সাহিত্যের পাশাপাশি যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত ওঁর ডায়রি আর চিঠিপত্র পড়তে হয়, ওঁর সময়ের মানুষজনের স্মৃতিকথা পড়তে হয়, সন্দেহ হলে কাটাকুটি খেলে নিতে হয় খানিক। অনেকেই বলেন মানিকের প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘অতসীমামী’। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ‘প্রবাসী’-তে প্রকাশিত ‘ম্যাজিক’ গল্পটি ওঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প, যা ‘বিচিত্রা’-য় ‘অতসীমামী’ প্রকাশের মাস খানেক আগেই বেরোয়। প্রকৃত গবেষক/জ্ঞানপিপাসু এই লাইব্রেরি থেকে ওই লাইব্রেরি ছুটে বেড়ান, পুরোনো বইয়ের দোকানিকে পাগল করে ছাড়েন, আর তারপর হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে জানতে গিয়ে কোনও একদিন হাতে পেয়ে যান শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের ‘পরিচয়ের আড্ডা’ কিংবা হিরণকুমার সান্যালের ‘পরিচয়ের কুড়ি বছর’। জরাজীর্ণ, তবু খুঁজে পাওয়া মহার্ঘ্য লেফাফা-বই।
বাঙালি অধিকাংশই লার্জার দ্যান লাইফে মজে বেশি। ফলত ব্যক্তি-মানিক বড় হয়ে ওঠে তার চোখে এবং অকাতরে চলতে থাকে তাঁর সাহিত্যের অপব্যাখ্যা। একদা ‘পরিচয়’ পত্রিকার দপ্তরে বসেছিলেন সম্পাদক গোপাল হালদার, মানিক উদ্ভ্রান্তের মতো এসে তাঁর কাছে এসে কুড়িটা টাকা চান। গোপাল হালদারের থেকে টাকা পেয়ে পরমুহূর্তেই যেমন এসেছিলেন, সে ভাবেই বেরিয়ে যান। সিরিয়ালের দৌলতে যেমন আমরা জানি, সব পরিবারেই একজন-না-একজন খলচরিত্র থাকে, তেমনই একজন, গোটা ঘটনাটা দেখে গোপাল হালদারকে বলেছিলেন, সে নিশ্চিত যে টাকা ক’টা নিয়ে মানিক হাড়কাটা কিংবা খালাসিটোলায় যাবে। গোপাল হালদারের জবাব ছিল : মানিক ‘পরিচয়’-কে যা দিয়েছে, সেটা ফেরতযোগ্য নয়। বাংলার বিদ্বৎসমাজে এই দুই ধরনের মানুষেরই বড় আকাল এখন; আর সেটা আরও প্রকট হয় মানিকের মৃত্যুর বছর চারেক আগের একটি ঘটনায়।
১৯৫২ সালে এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথ উত্তাল। প্রেসিডেন্সি কলেজের, হালফিলে বিশ্ববিদ্যালয়, সামনে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাঁচ নম্বরের একটি ট্রাম। অবরোধ চলছে, আর সেই ভিড়ে-ভরা পদাতিকদের মাঝখানে, পিচরাস্তায় বসে, ট্রামলাইনের মাঝখানে, খড়ি দিয়ে অবিকল লিখে দিয়েছিলেন মানিক: ‘ট্রামমজুর, ভাষামজুরের সেলাম নাও’। এই শিরদাঁড়াটার, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনামতো ‘বাংলাদেশ ভয় পেত’ যে-চোখকে, আজ বিগবাজারে দেশ বিক্রির দিনে, মজবুর মজদুরদের দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের বারবেলায় সেই রাগের বড়ো প্রয়োজন ছিল। সবাই যখন নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার খেলায় মত্ত, তখন মনে পড়ে, এই লোকটাই প্রথমবার বারণ করে দেওয়ার বহু বছর পর, যখন অন্য সিনেমা কোম্পানির সঙ্গে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’-র চুক্তিতে সই করেন, চুক্তিপত্রে একটি বাক্য যোগ করেছিলেন: ‘কোনওমতেই সস্তা করা চলবে না।’ অমেরুদণ্ডী সরীসৃপের তাঁর জন্মদিন পালনের কোনও এক্তিয়ার নেই, থাকতে পারে না।
জন্ম ১৯৮৫। গল্প লেখার চেষ্টা করেন। কবিতা লিখতে পারেন না একদম, তাই কবিদের প্রতি সম্ভ্রম নিয়ে দূরে-দূরে থাকেন। প্রকাশিত গল্প সংকলনের সংখ্যা দুই, উপন্যাসের সংখ্যা এক।