টিভিএফের প্রতিষ্ঠাতারা যে আইআইটির প্রাক্তনী, তা জানতুম না। জানার পর থেকে নিজে সেখানে পড়ার সুযোগ না-পাওয়ার জন্য আইআইটির প্রতি যে ‘দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা’ গোছের একটা মনোভাব ছিল, সেটা অনেকটা কাটল। আরও কাটল সদ্য তাদের প্রযোজিত ওয়েব সিরিজ ‘পঞ্চায়েত’ দেখার দৌলতে।
২০১০ সালে বানানো ছবি ‘পিপলি লাইভ’ মনে পড়ে? নির্মাণের আধুনিকতার নিরিখে সেটার সঙ্গে ‘পঞ্চায়েত’-এর অনেকটা মিল থাকলেও মূল একটা জায়গায় তফাৎ রয়েছে। সেটা হল, পিপলিতে একটা খুব স্পষ্ট, শক্তিশালী গল্প ছিল। পঞ্চায়েত-এ যে শুধু সেই অর্থে কোনও প্লট নেই তা-ই নয়, এই সিরিজের মেজাজটাই এমন, যে প্লটের প্রয়োজনীয়তাটাই বাহুল্য মনে হয়। অনুভূতিটা অনেকটা খোলা নৌকায় শুয়ে দোল খেতে খেতে মাঝিদের গানের ফিরে ফিরে আসা সুরে বুঁদ হয়ে যাবার মতো। মাঝে মাঝেই ‘মালগুড়ি ডেজ’-এর কথা মনে পড়ে যায়। আলস্য আর অনায়াস যে খলবলে কইমাছের মতো নির্মেদ আর শাণিত হতে পারে, এর আগে আমার ধারণা ছিল না।
যাই হোক, এসব প্যাচাল ছেড়ে আসা যাক সিরিজের কথায়। পটভূমিকাটা যাঁরা আমাজন প্রাইমে প্রোমো দেখেছেন, তাঁরা মোটামুটি জানেন। পরিস্থিতি আর ভাগ্যের ফেরে একটি আদ্যন্ত শহুরে যুবক ফুলেরা বলে উত্তর প্রদেশের একটি প্রত্যন্ত, কিন্তু মোটামুটি সমৃদ্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব হয়ে চাকরি করতে যায়। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, খানিকটা বাধ্য হয়েই। সেখানে তার অভিজ্ঞতা নিয়েই সিরিজ। আগেই বললাম, গপ্পো বলতে সে রকম কিছুই নেই। অতি পরিচিত কিছু ঘটনাই পর্বগুলোর উপজীব্য। কিন্তু এগুলোই যে মরসুমি কাশ্মিরি আঙুরের মত সরস হয়ে ওঠে, তার পিছনে কারণ মূলতঃ তিনটে।
প্রথমতঃ, নির্মাতাদের রসবোধের সূক্ষ্মতা। এরকম বুদ্ধিদীপ্ত, পরিমিত অথচ লাগসই রসবোধ সত্যিই বিরল। কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর চেষ্টা তো নয়ই, হাহা করে হাসারও কোনও অবকাশই নেই চিত্রনাট্য জুড়ে। দর্শকদের বুদ্ধির প্রতি এমন বিশ্বাস যে পরিচালক রাখতে পারেন, তাঁর সম্মানের মর্যাদা রাখতেই দর্শকের নিজেকে বিবর্তিত করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, অত্যন্ত যত্ন করে সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন্ত সব চরিত্র এবং তাদের অভিনয়। পঞ্চায়েত প্রধানের ভূমিকায় নীনা গুপ্তা এবং তাঁর স্বামীর ভূমিকায় রঘুবীর যাদব যে অনবদ্য অভিনয় করবেন, সে তো জানা কথাই। কিন্তু অন্য তিনটি প্রধান চরিত্রে জীতেন্দ্র কুমার, ফয়জল মালিক এবং চন্দন রায় – তিনজনেই এমন মেদুর সজীবতা দিয়েছেন, যে চরিত্রগুলো যেন ছুঁয়ে দেখা যায়। বিশেষ করে বলতেই হয় প্রধান চরিত্রে জীতেন্দ্র কুমারের কথা। এর আগেও কিছু অভিনয় তিনি করেছেন, তবে তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু এই সিরিজে তিনি সত্যিই মুগ্ধ করেছেন। শহুরে মধ্যবিত্ত যুবকের গ্রাম সম্বন্ধে যে একটা ধাতুগত বিরক্তি, বিতৃষ্ণা এবং খানিকটা ভয় মিশ্রিত অবজ্ঞা, সেটা যে রকম অনায়াসে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন… এক কথায় দুর্দান্ত।
তৃতীয় কারণটা অবশ্য খুব সহজেই অনুমেয়। আলস্যকে নির্মেদ ভাবে পরিবেশন করতে হলে যে সম্পাদনা আর ক্যামেরার কাজ বিশ্বমানের হওয়া প্রয়োজন, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্পাদক অমিত কুলকার্নি একটা অদ্ভুত ব্যাপার করেছেন এখানে, যেটা তলিয়ে ভাবলে অবাক না-হয়ে উপায় থাকে না। সিরিজে ক্কচিৎ কদাচিৎ জাম্পকাট বা সেই অর্থে অ্যাব্রাপ্ট কাট চোখে পড়ে। অথচ গোটা সিরিজে কোনও বাড়তি মুহূর্ত পাওয়া ভার। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, যেখানে সিরিজের মূল মেজাজটাই আয়েসের, সেখানে এ কাজটা কতটা কঠিন। আর এটা সম্ভব হয়েছে চিত্রগ্রাহক অমিতাভ সিংহের সঙ্গে সম্পাদকের সমঝোতার জন্য। সিরিজের প্রধান মুডটা তৈরি করতে বাইরের অধিকাংশ শটে পিছনে খোলা মাঠ এবং খেতকে যে মুন্সিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা এই সমঝোতা ছাড়া সম্ভব নয়।

তবে এই কারণগুলোর বাইরেও একটা হোলিস্টিক কারণ আছে, যেটা সিরিজটাকে হাতে-ধরলেই-গুঁড়ো-হয়ে-যাওয়া গ্রামের শুকনো মাটির মত বাস্তব, মুচমুচে করে তোলে। আমরা যারা শহুরে, তাদের গ্রামের জীবন সম্বন্ধে ধারণাটা এতটাই অস্পষ্ট, যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামের জীবন ফুটিয়ে তুলতে গেলে সে চেষ্টা অন্ধের হস্তিদর্শনের মত হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে। হয় অর্থ আর শিক্ষার অহঙ্কারের জায়গায় বসে একটা অতি সরল, সমস্ত প্রযুক্তিবর্জিত মোটা দাগের চেহারা আঁকা হয়। সম্ভবত সেটা আসে একটা ভিত্তিহীন অনুকম্পা থেকে। আর না-হলে অজানার প্রতি ভীতিবশতঃ একটা অসম্ভব ধান্দাবাজ, হিংস্র, সাম্প্রদায়িক বারুদের স্তুপ হিসেবে গ্রামীণ রাজনীতির কল্পিত ছবি আঁকা হয়।
কিন্তু ‘পঞ্চায়েত’ এইখানেই আলাদা হয়ে যায়। চন্দন কুমারের চিত্রনাট্য, আকবর খানের শিল্প নির্দেশনা আর তর্পণ শ্রীবাস্তবের প্রোডাকশন ডিজাইন পঞ্চায়েত-কে একটা অন্য স্তরে তুলে নিয়ে যায়। প্রচুর পরিশ্রম ও গবেষণা করে এবং সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টিতে তাঁরা একটা যথাসম্ভব বাস্তব চিত্র ফোটানোর চেষ্টা করেন। এবং সেই জন্যেই চরিত্রগুলো এত জীবন্ত। ফুলেরাবাসীরা বাড়িতে দু’খানা শৌচালয় সত্ত্বেও ‘মাঠে যাওয়া’ পছন্দ করেন, আবার হোয়াটস্যাপ গ্রুপে দিশি মদের পার্টিও প্ল্যান করেন। মনিটর আর কম্পিউটার তাদের কাছে সমার্থক, এদিকে একখানা গদিমোড়া রিভলভিং চেয়ারের জন্য গ্রামের প্রধানের প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ হবার জোগাড়।
সেখানে নামে মহিলা প্রধান হলেও ক্ষমতা ভোগ করেন অত্যন্ত ধূর্ত প্রধান-পতি। তিনি গ্রামের মাতব্বর, গরিব চাষির বিপাকের সুযোগ নিয়ে তার জমি সস্তায় কেনেন। আবার তিনিই বাড়িতে স্ত্রীর ভয়ে কেঁচো। নবাগত সচিবের প্রতি দয়াবশতঃ তাকে বিনা পয়সায় দুধ দেন। কখনও বা তার ঝামেলা সামলাতে বন্দুক নিয়ে ছুটে যান ভিন গাঁয়ে। এবং এই সিকোয়েন্সগুলো যে শুধু চিত্রনাট্যের কারণে বাস্তব হয়ে ওঠে, তা কিন্তু নয়। পারিপার্শ্বিকের সাজসজ্জা, ক্যামেরার কাজ, পোশাকের ডিটেলিং, প্রতিটি জিনিস একসঙ্গে মিলেই গড়ে তোলে ফুলেরা আর তার বাসিন্দাদের।
তবে একটা ব্যাপার আছে। হয়তো অন্যান্য বিষয়ে এত ভালো বলেই সংলাপটা কিছু কিছু জায়গায় একটু বেমানান লাগে। মনে হয় শহুরে বুদ্ধি বা পালিশ যেন একটু কম হলে ভাল হত। বিশেষত যে দৃশ্যে নীনা গুপ্তা আর রঘুবীর যাদবের মধ্যে মেয়ের সম্ভাব্য স্বামী নিয়ে কথাবার্তা হয়, বা নীনা গুপ্তা এদেশে মহিলা হয়ে জন্মানোর জন্য চাপা উপেক্ষা উপলব্ধি করেন– দৃশ্যগুলো মর্মস্পর্শী হলেও সংলাপ জায়গায় জায়গায় একটু আরোপিত মনে হয়।
হয়তো অন্যান্য বিষয়ে এত ভালো বলেই সংলাপটা কিছু কিছু জায়গায়
একটু বেমানান লাগে।
যাই হোক, শেষমেশ মোদ্দা কথায় জিনিসটা দাঁড়ায় এরকম– স্মার্ট বা আধুনিক – দু’টো কথাই বহুব্যবহারে নিজেদের কৌলীন্য হারিয়েছে বহুকাল হল। তবু বলব, সত্যিই স্মার্টনেস বা আধুনিকতা যে থাকে শিল্পের নির্মাণশৈলীতে, তার বিষয়ে নয়, সেটা যদি বুঝতে হয়, একবার ঢুঁ মেরে আসতেই হবে ফুলেরার গ্রাম পঞ্চায়েতের দফতরে।
পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তিতিবিরক্ত হতে হতেও আইটি শিল্পতালুকে মজদুরি করতে বাধ্য হন। কিন্তু সবচেয়ে পছন্দের কাজ হাতে মোবাইলটি নিয়ে আলসেমি করে শুয়ে থাকা। চেহারাছবি নিরীহ হলেও হেব্বি ভালোবাসেন অ্যাকশন ফিলিম, সুপারহিরো আর সাই ফাই। সঙ্গে চাই সুরেশের রাবড়ি, চিত্তরঞ্জনের রসগোল্লা-পান্তুয়া, কেষ্টনগরের সরভাজা ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টান্ন।



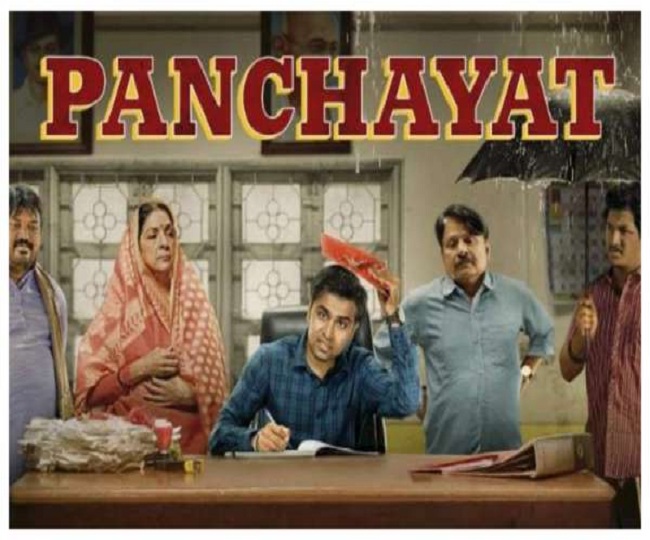




















2 Responses
বেডডা রিভিউটি ও সিরিজের মতনই নিঁখুত সুন্দর ! অনেকদিন পর তোমার লেখা পেয়ে দিল বাগ বাগ হয়ে গেল!
পঞ্চায়ত সিরিজটা যেমন উপভোগ করেছি তার রিভিউটাও ততধিক্ উপভোগ করলাম। খুব সুন্দর লেখা।