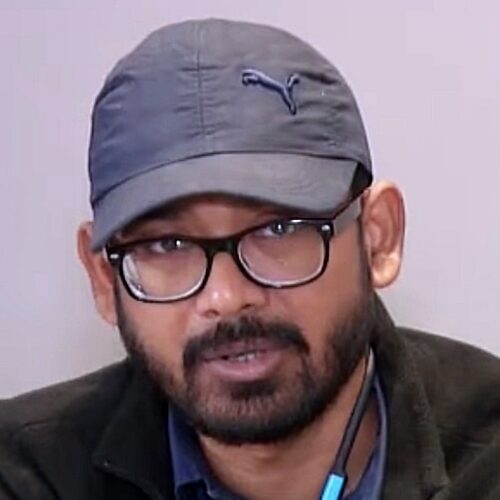এই পর্বে আপনাদের একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হব। সাম্পানের মতো ঘটনার পরম্পরা তরতর করে এগোবে না। আড্ডার তরী এই ঘাটে সেই ঘাটে থেমে থেমে এগোবে। এমনটি করতাম না যদি আপনারা মোমবাতির শিখা দেখে সূর্য কল্পনা করতে পারতেন। যেহেতু পারা অসম্ভব, অতএব টাঙ্গুয়ার হাওরের লুকনো কলকব্জা, মানুষজনের ইতিউতি জীবন, মাছেদের ঘাই মারা সশব্দ রাত্তিরের বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বৈকি। যে সুনামগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে তাকে বলা হয় ‘হাওরকন্যা’। সুনামগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে তাহিরপুর ও ধর্মপাশা, এই দুই উপজেলা নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওরের অবস্থান। তাহিরপুর উপজেলার দুই ইউনিয়ন অর্থাৎ উত্তর শ্রীপুর ও দক্ষিণ শ্রীপুর এবং ধর্মপাশা উপজেলার উত্তর বংশীকুন্ডা ও দক্ষিণ বংশীকুন্ডা ইউনিয়ন নিয়ে এই হাওর অঞ্চল গঠিত হয়েছে। সর্বমোট ১০টি মৌজা মিলে হাওরের আয়তন ৪ হাজার ৮৬০ হেক্টর। এর মধ্যে ২৮০২.৩৬ হেক্টর জলাভূমি। গ্রাম রয়েছে ৪৬টি। টাঙ্গুয়ার হাওরে ছোট বড় ১২০টি বিল আছে। তবে প্রধান বিল ৫৪টি। ভরা বর্ষায় এর আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে ওঠে।
হাওরের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক জলধারা। নদী হিসেবে রয়েছে সোমেশ্বরী, রক্তি, পাটলাই, কংশ, ধামলাই, বৌলাই, ধনু ও অবশ্যই সুরমা। নদীগুলির সঙ্গে অসংখ্য খাল ও নালা বর্ষাকালে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তখন হাওর প্রকৃত অর্থে সাগর। হাওরের উত্তর দিকে মেঘালয় পাহাড়। এই পাহাড় থেকে ৩৮টি ঝরনা নেমে এসে মিশেছে টাঙ্গুয়ার হাওরে। টাঙ্গুয়ার হাওর মূলত ‘মাদার ফিশারিজ’ এবং একইসঙ্গে গ্রুপ ফিশারিজ। অন্যান্য হাওর থেকে এখানকার মাছ ও পাখি আয়তনে বড় বলে দাবি করা হয়। এই হাওরে ১৫০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৪১ প্রজাতির মাছ, ১১ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ৬ প্রজাতির কচ্ছপ, ৭ প্রজাতির গিরগিটি ও ২১ প্রজাতির সাপ দেখা যায়। এমন বিপুল ও কিছু ক্ষেত্রে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণকে ধারণ করেছে হিজল, করচ, নলখাগড়া, দুধিলতা, সিঙরা, চাইল্যা, বইল্যা, উকল, গুইজ্জাকাঁটা, নীল শাপলা, পানিফল, শোলা, হেলেঞ্চা, শীতলপাটি, শতমূলী, স্বর্ণলতা, বনতুলসী প্রভৃতি দু’শো প্রজাতি গাছের সবুজ আচ্ছাদন। তবে চূড়ান্ত আর্থিক দুর্দশা ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারনে স্থানীয় অধিবাসীরা নির্বিচারে এদের কেটে সাফ করে দিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই জীববৈচিত্র্যের ওপর এর ভয়ঙ্কর প্রভাব বাংলাদেশ সরকারকে দুশ্চিন্তায় রেখেছে।

আমি আদ্যোপান্ত কলকাতা শহরের মানুষ। তবে কাজের প্রয়োজনে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বেশকিছু গ্রামীণ মাছ বাজার ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। অচেনা মাছ দেখামাত্র থলেবন্দি করে বাড়ি নিয়ে এসেছি রসাস্বাদনের জন্য। তবে টাঙ্গুয়ার হাওরে এসে যে সব মাছেদের নাম শুনেছি তা একেবারেই আশ্চর্য রকম সুন্দর ও অশ্রুত। এতদিনের ওঠানো জামার কলার মিইয়ে পড়তে বেশি সময় নেয়নি। কিছু মাছের নাম লিখে ফেলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না– আইড়, বোয়াল, রুই, কাতলা, কালিবাউশ, শোল, চিতল, ফলি, মাগুর, বেলে, মৌরলা, মৃগেল, বাচা, কৈ, বাটা, ট্যাংরা, খলশে, শিং তো আছেই। সঙ্গে আছে চাপিলা, গজার, ছেলা, লাউয়াবাইম, তারাবাইম, চিরকাবাইম, গছিবাইম, গুতুম, টাকি, সরপুঁটি, জাতপুঁটি, চান্দা, নামচান্দা, ছোট চিংড়ি, ডেরা, মেনি, বুজুরি, নাপতানি, পটকা, একঠুটা, মধুপাবদা, বোয়ালিপাবদা, ঘাউড়া, ভাগনা, বাঘাইর, রিটা, পোয়া, শ্রীরাইল, কেচকি, পাতামাছ, পাথরচাটা, বাতাসি, কাশখাউরি, গুলশা, তিতনা, ঘনিয়া, বেতগুতুম, কাকিয়া, কানপনা, চেকা, ঘোড়ামুখো, লবনচোরা, শিরাইল, রাগা, কাজুলি, বালুচাটা, মহাশোল ইত্যাদি।

প্রথম সারিতে উল্লেখিত অনেক মাছ হয়তো আমাদের বেশ পরিচিত কিন্তু বাকি নাম একেবারেই অচেনা। তবে পাতামাছ পেয়েছিলাম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোনও এক বাজার থেকে। যাইহোক, টাঙ্গুয়ার হাওরে ফিরে আসি। এই হাওরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ না করলে এই পর্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটি হল, দেশি ও বিদেশি পাখিদের আবাসস্থল টাঙ্গুয়ার। প্রায় ২০৮ প্রজাতির পাখি এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রধান আকর্ষণ হল পরিযায়ী পাখিরা। সুদূর রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়া থেকে আগত অতিথি পাখিদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। পাখি শিকার বন্ধের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৬৬-৬৭ সালে ‘শাহজালাল পক্ষী নিবাস’ নামে একটি অভয়াশ্রম তৈরি করেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাখিদের আবাস স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের সঙ্গে পর্যটন শিল্প গড়ে তোলা। তবে এত বছর পর সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল, তা নিয়ে আমার মতো অনেকেই সন্দিহান। অক্টোবর থেকে পুরো মার্চ মাস পর্যন্ত হাওরের জলে পাখিদের সঙ্গে চোরাশিকারিদের সংখ্যাও চোখে পড়বার মতো। তবে এই সমস্যা শুধুমাত্র যে বাংলাদেশেই রয়েছে এমনটি নয়। ভারতের বিভিন্ন জলাভূমিতে পরিযায়ী পাখি শিকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পুর্ণরূপে বন্ধ করা যায়নি। আমি গিয়েছিলাম ভরা বর্ষায়, তবে শীত এলে জল সরে যখন মাটির দেখা পাওয়া যায়, তখন শুরু হয় ধান চাষের কাজ। মূলত বোরো ধানের চাষ হয়। তবে খুব অল্প পরিমাণে আমন ধানের চাষও করা হয়ে থাকে। উঁচু জমিতে চাষ করা হয় বাদাম। সামান্য রসুন, পেঁয়াজ, সর্ষে আর শাক-সবজির চাষ হয়।
হাওরের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক জলধারা। নদী হিসেবে রয়েছে সোমেশ্বরী, রক্তি, পাটলাই, কংশ, ধামলাই, বৌলাই, ধনু ও অবশ্যই সুরমা। নদীগুলির সঙ্গে অসংখ্য খাল ও নালা বর্ষাকালে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তখন হাওর প্রকৃত অর্থে সাগর। হাওরের উত্তর দিকে মেঘালয় পাহাড়। এই পাহাড় থেকে ৩৮টি ঝরনা নেমে এসে মিশেছে টাঙ্গুয়ার হাওরে।
তথ্যের ভিড়ে হাওর ভেজা মন হারিয়ে যাওয়ার আগেই চলুন নতুন উদ্যমে টেকেরঘাটে পৌঁছে কী দেখলাম, কী বুঝলাম সে গল্পে ফিরে যাই। বোট এতক্ষণে এগিয়ে গিয়েছে বেশ খানিকটা। আকাশ যথারীতি কালো মুখ করেই ভয় দেখাচ্ছে। শনির হাওর যথেষ্ট ভয় দেখিয়েছে। তার গল্প না হয় অন্য কোনও সময়ে বলা যাবে। টেকেরঘাট পৌঁছনোর খানিক আগেই জলের উপর ভাসতে থাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা চোখে পড়বার মতো। কাশ্মীরের ডাল লেকের বসতির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মেঘালয় পাহাড় তার বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। ওপারের কিচ্ছুটি দেখতে দেবে না। যতই সুন্দর হোক না কেন, এমন প্রাচীর আমার না-পসন্দ। তবে রহস্য তৈরির জন্য অন্তরাল বড় প্রয়োজন। খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের রহস্য বিনা আয়াসে সবার চোখে ধরা দিক, এটি বোধহয় প্রকৃতিরও না পসন্দ। দুপুরের খাবার তড়িঘড়ি শেষ করে যখন হাত মুখ ধুচ্ছি, আমাদের বোট ‘সাম্পান’ ঘাটে ভিড়বার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অপরূপ সবুজ এই টেকেরঘাট। ঢেউ তোলা সবুজ কার্পেটের টিলা হাওরকে আলাদা করেছে পাহাড়ের সঙ্গে। আরও একটি অপরূপ বিউটি স্পট রয়েছে এদের মাঝখানে। সে হল নীলাদ্রি লেক। চুনাপাথরের খাদান ছিল। সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সিমেন্ট কোম্পানি খাদানকে একা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। মেঘালয়ের ঢলের পানি তার মতো করে একটা সুন্দর বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এখন গভীর খাদানের বুকে রুপালি রঙের জল খেলে বেড়ায়। আমি সম্মোহিত হয়ে ওর ধার ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছি। তরুণ পর্যটকের দল ডানদিকের সবুজ মখমলের টিলায় চড়ে বসেছে। কেউ হয়তো গিটারের তারে সুর বেঁধে গান ধরেছে। দূর থেকে সেই গান মনের আরাম দেয়। ‘হইয়া আমি দেশান্তরী/ দেশ বিদেশে ভিড়াই তরী রে..’ আমিও এক বিদেশি লোক ঘাটে তরী ভিড়িয়েছি। এখানে আমাকে কেউ চেনে না। কোনও অতীতের সম্পর্ক আমার কাছে পাওনাগন্ডা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য হাজির হবে না। তাই হয়তো অপার শান্তিতে মুহূর্তেই ডুবে যাওয়া যায়। তবে নীলাদ্রি, সে তো অপরিচিত নয়। নাম ভিন্ন হলেও ওকে দেশ ও দেশের সীমানার বাইরে যেন কতবার দেখেছি, কথা বলেছি। প্রকৃতি আমাদের চেনা ভাষায় কথা বলে না। চেনা সরগমে মূর্ছনা তোলে না। মহাবিশ্ব যেমন নিঃশব্দ, ঠিক তেমনই এই নিঃশব্দ আলাচারিতায় ব্যস্ত হতে হয় গভীর বোধ দিয়ে।

গোধূলির রং আকাশে লেগেছে। খানিক পরেই নামবে চরাচর জুড়ে নিখাদ অন্ধকার। সেই আঁধারে আমার দৃষ্টি অসহায় হয়ে পড়বে। তাই হাঁটতে হাঁটতে একটি সাইনবোর্ডের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সাবধান করে দিয়ে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ লিখেছে ‘সামনেই আন্তর্জাতিক সীমানা– সাবধান’। আমি ভয় পেয়ে নোটিশ টাঙানো বোর্ডের কাছেই যে কংক্রিটের তৈরি চেয়ার আছে তাতে বসে পড়লাম। হাওরের জল বন্যার সময়ও এইখানে উঠে আসে না। তবে হাওরের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায় নীলাদ্রির বুকে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর মানুষজন সেই দীর্ঘশ্বাসে বেঁচে থাকার অক্সিজেন খুঁজে পায়। এত সংঘর্ষ, এত বেমানান মনুষ্যজীবন, তবু এদের হাসিমাখা মুখ বুঝিয়ে দেয়, সন্ধানী না হলে অমরত্বের খোঁজ মেলে না। আমিও প্রান্তিক মানুষের দলে নাম লিখিয়েছি অমৃতভাগের আশায়। পাব কিনা, সে মহাকাল জানে।
এই পর্বে আর কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না। মনের জগতে আলোড়ন হলে শব্দ জব্দ হয়ে যায়। অতএব আগামী পর্বগুলিতে বাকিটুকু লিখব। আপনারাও আমার সঙ্গে নীলাদ্রির ধারে বসে অপেক্ষা করুন। রাত হলে বৃষ্টি নামবে। তাতে ভিজে যেতে যেতে হাওর মহলের ঘুমন্ত রাজকন্যা-রাজকুমারের অভিলাসে দিব্য স্বপ্ন দেখুন। আজ তবে বিদায়। (চলবে)
ছবি সৌজন্য: লেখক
সম্রাট মৌলিক পেশাদার কর্পোরেট জগতকে বিদায় জানিয়ে কাজ করছেন নদীর সঙ্গে। জল ও নদী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঘুরে দেখছেন ভারত-সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নদীব্যবস্থা, জানছেন ব্যবহারযোগ্য জলের সুষম বন্টনের পরিস্থিতি। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও রাশিয়া- পাঁচটি দেশে এখন পর্যন্ত প্রায় পনেরো হাজার কিলোমিটার একা ভ্রমণ করেছেন দু চাকায় সওয়ার হয়ে। এছাড়াও প্রায় দু দশক ধরে হেঁটেছেন অনেক শহর, প্রত্যন্ত গ্রাম,অজানা পাহাড় ও জঙ্গল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের স্নাতক সম্রাটের শখ প্রজাপতি ও পোকামাকড়ের ছবি তোলা। প্রথম প্রকাশিত বই 'দাগ'।