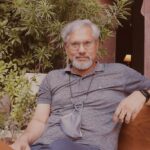নিজের পিতৃদেবকে লেখা চিঠি ‘প্রিয়তম বাবা’তে ফ্রানজ কাফকা লেখেন -“তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেলে ভীষণ খুশি হতাম, বস্ হিসেবে, কাকা হিসেবে কিংবা ঠাকুরদা, এমনকি শ্বশুর হিসেবেও । কেবলমাত্র বাবা হিসেবেই তুমি আমার প্রতি অসম্ভব কড়া।” নভেম্বর ১৯১৯-এ চেক প্রজাতন্ত্রের একটি স্যানেটোরিয়ামে চিকিৎসা চলাকালীন টিবি রোগী কাফকার লেখা এই চিঠি কোনওদিন তাঁর বাবার কাছে পৌঁছয়নি । কাফকাই দিয়ে উঠতে পারেননি কখনও, চার বছর পর তাঁর মৃত্যুর আগে অবধি। বাবার সঙ্গে এক অনতিক্রম্য দূরত্বে কাফকার সংবেদনশীল মন। ঠিক একই ভাবে আন্দ্রেই তারকোভস্কি নিজের পিতা কবি আর্সেনি তারকোভস্কির থেকে পৃথক জমিতে বিচরণ করেন । ১৯৭০ সালের ডায়েরিতে ৩৮ বছর বয়সী তারকোভস্কি লিখছেন – ” বাবাকে অনেক যুগ দেখিনি । তাঁকে না দেখা যত দীর্ঘায়িত হয় তত তাঁর কাছে পৌঁছনোর বিষয়টি উত্তেজনাপ্রবণ অথচ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে । এ নিয়ে কোনও সংশয়ই নেই যে আমার মধ্যে বাবা-মা’র সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে একটা হীনম্মন্যতাবোধ কাজ করে । বাবার সঙ্গে থাকলে আমার নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে হয় না । আমার ধারণা বাবা-মা’ও আমাকে প্রাপ্তবয়স্ক বলে মান্যতা দেন না । আমাদের সম্পর্ক ভঙ্গুর, মূক । আমি তাঁদের খুব ভালোবাসি, কিন্তু কখনঔই তাঁদের উপস্থিতিতে আমি স্বাভাবিক হতে পারি না…আমি কি তাহলে একটা চিঠি লিখব? কিন্তু একটা সামান্য চিঠি কোনও মীমাংসা করতে পারে না। পরবর্তীকালে যখনই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হবে আমরা এমন ভাব করব যেন চিঠিটা ছিলই না কখনও। আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসি কিন্তু সেটা স্বীকার করতে আমরা লজ্জা বা ভয় পাই। আমার পক্ষে তাই সম্পূর্ণ অপরিচিত কারও সঙ্গে আলাপ করা অনেক সহজ, সাবলীল।” অর্ধশতকেরও বেশি ব্যবধানের এই দুই দিকপালের ব্যক্তিজীবনের মানসিক এই ভারসাম্যহীনতা প্রকাশিত হয় তাঁদের কাজের আঙিনায়ও। ঠিক যেভাবে এই যন্ত্রণা ডানা মেলে ইংমার বার্গম্যানের চলচ্চিত্রাকাশেও।
কাফকার মতই তারকোভস্কির বাবাকেও দেখে যেতে হয় নিজের সন্তানের মৃত্যু। তারকোভস্কির বাবার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘তুষারপাতের আগে‘ প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে যেবছর মুক্তি পায় তারকোভস্কির প্রথম ফিচার ফিল্ম ‘ইভান্স চাইল্ডহুড‘। তারকোভস্কির ছোটবেলাতেই তাঁর বাবা বাড়ি ছেড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে যান, যুদ্ধ শেষ হলে তিনি এই পরিবারে আর ফেরত আসেন না সেভাবে, ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন নিজের স্বতন্ত্র দাম্পত্য জীবন। মানসিক স্তরে বাবার সঙ্গে দূরত্ব, শারীরিক অ–নৈকট্য/আশ্বাস ‘৩০-‘৪০র দশকের অনেক বালক–কিশোরের মতোই তারকোভস্কিকেও করে তোলে বিষণ্ণ। যে বয়সে বাবার সাহচর্য, পথপ্রদর্শন, সময় কাম্য তা না পাওয়ার শূন্যতা অবধারিত প্রতিফলিত হয় তারকোভস্কির ছবিটির আখ্যানে। হয়তো সেকারণেই ইভান পিতৃহারা। যুদ্ধের সে বিষফল, অনাথ, অনিশ্চয়, হিংসায় মত্ত, নিষ্করুণ, শৈশবহীন । তার স্বপ্নদৃশ্যে মা আসেন একাধিকবার, কিন্তু স্বপ্নেও জায়গা হয় না বাবার।
সেই যুগের অন্যান্য অনেক যুদ্ধস্থিত থিমের চলচ্চিত্রের তুলনায় ‘ইভান্স চাইল্ডহুড‘এর বৈশিষ্ট্য হল এই যে নেহাতই একটি যুদ্ধের ছবি থেকে এটা মেটাফিজিকাল চলচ্চিত্রে উন্নীত হতে সক্ষম হয় তার স্বপ্ন–দুঃস্বপ্নের প্রায় সুররিয়্যাল বৈপরীত্যের জন্য । এখানে পূর্বজীবনের স্মৃতি আসে স্বপ্নের রূপে, রূপকে। অর্থাৎ, সেই অবচেতন যা একমাত্র জাগ্রত হয় যখন ইভান নিদ্রিত অথবা মৃত। স্বতন্ত্র আখ্যান হিসেবে দীর্ঘ স্বপ্নের অনুক্রমের উপস্থাপনায় তারকোভস্কি গঠন করেন এক ভগ্নচৈতন্য – এক দ্বান্দ্বিক চরিত্রায়ণ যা ইভানের বিভক্ত ব্যক্তিত্বের স্বরূপকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। এক অপরিবর্তনীয় বৈপরীত্য, এক অনতিক্রম্য বৈরিতা – অতীতের সুখী ইভান বনাম ফিল্মবাস্তব সময়ের কঠিন, নির্মম ইভান।
ছবির শুরু থেকে তারকোভস্কি ব্যবহার করেন শক্তিশালী ভিস্যুয়াল এবং আকর্ষণীয় শব্দগ্রাম – স্বপ্নমুহূর্ত ও বাস্তবের দ্বন্দ্বকে চিত্রায়িত করতে। যে কারণে স্বপ্নদৃশ্যগুলি (সব মিলিয়ে চারটি) সবসময়ই অতি–উজ্জ্বল, ছায়াহীন, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল, প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্য। অন্যদিকে ইভানের বাস্তবজীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন, নোংরা, গাঢ় ছায়াময়, বিকৃত। বিস্তীর্ণ প্রান্তর সেখানে মৃত, বাঙময় নয়। অথচ পুরো ছবিতে তারকোভস্কি কখনওই যুদ্ধের দৃশ্য সেভাবে দেখান না। নেপথ্যে মেশিনগানের আওয়াজ শোনা যায়, কখনও কখনও গুলিবৃষ্টির ঝলকানি ক্ষণিকের জন্য রাতের আকাশকে আলোকিত করে দেয়। ছবি শুরুই হয় স্বপ্নদৃশ্যের মাধ্যমে – একটি মাকড়সার জাল, তার ভিতর দিয়ে ইভানের রৌদ্রোজ্জ্বল, শান্ত, সমাহিত মুখশ্রী; একটি কোকিলের ডাক শোনা যায়, একটি প্রজাপতিও দেখি আমরা। ইভান গাছগাছালির মাথার ওপর দিয়ে প্রায় উড়তে উড়তে এগিয়ে যায় (যা দর্শক হিসাবে আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে এটা আদতে একটা স্বপ্নদৃশ্যই), নেমে এসে দেখে তার মা এক বালতি জল নিয়ে যাচ্ছে, ইভান সেই বালতিতে মুখ ডুবিয়ে জল খায়। পরমুহূর্তেই মেশিনগানের শব্দে ইভানের সেই সুকোমল স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়, সে বাস্তবে জেগে ওঠে এক ঘর অন্ধকারের মধ্যে। এর পরের কিছু শটেই ইভানের বাস্তব কালিমালিপ্ত জীবনযাত্রা, পরিপার্শ্ব, মৃত্যু উপত্যকা, অনমনীয় দীর্ঘ মরা গাছের সারি, অন্ধকার জলাশয় (যার বরফ শীতলতা দেখলেই অনুমান করা যায়) দেখতে পাই । বাস্তব এবং স্বপ্নের বিপরীতধর্মিতা কখনো মেলানো হয় না, উপরন্তু ছবির অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্য আরও ঘনীভূত হয় । পরবর্তী স্বপ্নদৃশ্যগুলোয় আমরা দেখতে পাই স্বচ্ছ কুয়োর জল, আপেলভর্তি লরি (পূর্ণ উর্বরতার প্রতীক হয়তো), চারটি ক্লাসিকাল এলিমেন্টস–এর মধ্যে অন্ততঃ তিনটি – জল, মাটি এবং বাতাস আমরা দেখতে বা বুঝতে পারি; সমুদ্রতট, ছোট ছেলেমেয়েরা যাদের সঙ্গে ইভান খেলা করে, বৃষ্টি (যা তারকোভস্কির ছবির এক পৌনঃপুনিক সিম্বল), আলো। আলোকের এই ঝর্ণাতলায় ইভান কিশোর, মায়াময়; পক্ষান্তরে বাস্তবের ইভান চিন্তাক্লিষ্ট, নির্দয় এবং কৈশোর–অতিক্রান্ত এক প্রাপ্তবয়স্ক মন। কারণ, ইভান এক জ্বলন্ত অসঙ্গতি – যেখানে স্বপ্ন রূপান্তরিত হয় দুঃস্বপ্নে বাস্তবের চোরাগলিতে।
তারকোভস্কির অসামান্য মুন্সিয়ানা ছবির শেষ স্বপ্নদৃশ্যে। ইভান তো তখন মৃত, তাহলে সেই স্বপ্নটা আসলে কার? শৈশব, এর আগে সবসময় এসেছে অতীত হিসেবে, স্বপ্নকল্পে। তবে কি শৈশব আসলে মরণোত্তর এক বিভ্রম? তারকোভস্কিরই ‘সোলারিস‘ ছবির শেষে ক্রিসের ঘরে ফেরা এক অবাস্তব বাস্তব, সাধারণ বাস্তবে সেও হয়তো মৃতই। ‘সোলারিস‘এর পরে ‘মিরর‘এও নায়কের মৃত্যুর পর আমরা তাকে দেখি একটি ছোট শিশুরূপে বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে হেঁটে যেতে, এমনকি ‘নস্টালজিয়া‘ও শেষ হয় একটি স্বপ্নদৃশ্যে যেখানে মৃত্যুর কিয়ৎ পরেও আমরা গোরচকভকে দেখতে পাই ইতালীয় ল্যান্ডস্কেপের ভিতর তার রুশ বাড়ির সামনে বসে থাকতে। প্রখ্যাত দার্শনিক জিজেকের কথাকে বিস্তার করে বলা যায় তারকোভস্কির ছবির স্বপ্নদৃশ্য কোনও ব্যক্তির শারীরিক স্বপ্নযাপন থাকেনা আর, তা সেই ব্যক্তির ঊর্দ্ধে এক অন্য চেতনার অভিঘাতে অভিজ্ঞাপিত হয়। দর্শক হিসেবে সেই অভিজ্ঞতা এক চেতনাতীত কনশাসনেস, তাকে মানুষের ব্যবহারিক যুক্তির বাটখারায় মাপা যায় না। এই ভার্চুয়াল স্মৃতিছেঁচা দৃশ্যকল্প তাই সময়ের অনুঘটক হয়ে যায়, ব্যক্তির একক উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ থাকে না আর।
এখানে যেটা বলা দরকার তা হল আরও কিছু দৃশ্য যাদের স্বপ্ন–বাস্তবের মধ্যবর্তী ভিস্যুয়াল ইন্টারলিউড বলা যেতে পারে। মোরগ হাতে বৃদ্ধ সেরকমই একটি দৃশ্য। কিন্তু তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ হয়তো ছবির শেষ দিকে যখন ইভানকে বাকি অফিসারেরা রেখে যান এবং তার একটা হ্যালুসিনেশনের সূত্রপাত হয় – একটি চার্চবেল যাকে দড়ি দিয়ে ওপরে তুলে রাখে ইভান; ক্রমশঃ একটা ছুরি হাতে সারা ঘর হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায় সে, নিজের সঙ্গেই কথা বলে যায়, আমরা অন্য মানুষদেরও গলার আওয়াজ পাই – গুঞ্জন, ফিসফিস। ইভান উত্তেজিত হয়, এক অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে তার যেন বোঝাপড়া, সে ক্রমেই রেগে যেতে যেতে এক সময় ভেঙে পড়ে। দৃশ্য এগোলে আমরা ইভানের মৃত্যুর দৃশ্যকল্প দেখে বুঝি এ বাস্তবই, ইভানের দৃষ্টিকোণে যা দেখা অসম্ভব। ডিসলভের মাধ্যমে আমরা অচিরেই ছবির শেষ দৃশ্যে (যা স্বপ্নদৃশ্যই) ঢুকে পড়ি – বাস্তব, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন আমাদের মানসিক চেতনায় ওতপ্রোত মিশে যায়, স্নায়ুর ওপর আঘাত করে। এই ভিস্যুয়াল ইন্টারলিউড আমাদের মনে করতে বাধ্য করে ১৯৪৮সালের রসোলিনির ‘জার্মানি ইয়ার জিরো‘ ছবিটির শেষদৃশ্যকে । সেখানে ইভানের সমবয়সী এডমুন্ডকে দেখতে পাই যে যুদ্ধোত্তর বার্লিনের এক বিভ্রান্ত কিশোর। ইভান এবং এডমুন্ড যুদ্ধের দুই মুখ, মুদ্রার দুই পিঠ, বিশ্বযুদ্ধের দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ অথচ দুজনের হাহাকারই কী অপরিসীম । দুজনেই ‘ফাদার ফিগার‘ প্রত্যাশী, আকাঙ্ক্ষী। ইভানের বাবা নেই, এডমুন্ডের বাবা আছেন কিন্তু তিনি অসহায়, অসুস্থ, দুর্বল। এবং ইভানের সেই হ্যালুসিনেশন দৃশ্যের মতো এডমুন্ডকেও আমরা দেখি একা, নিজেই কিছু কাল্পনিক প্রতিপক্ষ সাজিয়ে ক্রীড়ারত। ইভানকে বিশ্বাস করানো হয় যে শক্তিমান, সেই যুদ্ধে যায়, ইভান আপ্রাণ চেষ্টা করে ভেঙে না পড়ে সুঠাম থাকতে। অন্যদিকে এডমুন্ডকে শেখানো হয় যুদ্ধোত্তর ধ্বস্ত জার্মানিতে দুর্বলদের জায়গা নেই, তারা সরে না গেলে সবলেরা ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারবে না। ১২ বছরের এডমুন্ড শেষমেশ তার বাবার খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয় এবং শেষ দৃশ্যের অন্তে আত্মহত্যা করে পরিত্রাণ পায়।
শুরু থেকে শেষ
‘ইভান্স চাইল্ডহুড‘ শুরু হয় একটি গাছ ধরে ক্যামেরার আরোহণের মাধ্যমে । ছবির শেষ স্বপ্নদৃশ্যেও একটি ন্যাড়া, পোড়া গাছ দেখে আমাদের মনে পড়ে শুরুর সেই গাছটাকে । গাছের মোটিফ তারকোভস্কির ছবিতে বারংবার আসে । শেষ ছবি ‘দ্যা স্যাক্রিফাইস‘এও শুরুতেই লিওনার্দো দাভিঞ্চির ‘এডরেশন অফ মেজাই‘এর ‘ট্রি অফ লাইফ‘ বেয়ে ক্যামেরার উড়ান যা পরের দৃশ্যে সমুদ্রতটে গাছ পোঁতার দৃশ্য হয়ে যায়। শেষ চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে, তারকোভস্কির সমগ্র চলচ্চিত্র ভান্ডারের শেষ দৃশ্যকল্পেও ক্যামেরা বেয়ে ওঠে সেই গাছটিকে যা বাবা ও ছেলে অতীতে পুঁতেছিল । সেটা তখনও অপুষ্ট, পাতাহীন তবুও তা প্রাণহীন নয় । ঘোড়া, আপেল, মাটি, জল, আগুন, ওড়ার রূপক – এই সব চিহ্নই তারকোভস্কির প্রথম ছবি থেকেই পরিলক্ষিত । নিজের ছেলে এবং পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি আশা থাকে আলেকজান্ডারের, তারকোভস্কিরও, প্রথম থেকে শেষ ছবিতে ‘ট্রি অফ লাইফ‘ এভাবেই বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। আরএকভাবে দেখলে, ১৯৬২র তারকোভস্কির মনোজগতে পিতার প্রতি অনীহা, বিরাগ, অধোবদন ইভানকে পিতৃহীন করে রাখে। ১৯৭০-এ পুত্রের পিতা হওয়ার সুবাদেই কি তবে ১৯৮৬র শেষ ছবিতে পুত্রের প্রতি পিতার এই আশাবাদ? ভাগ্যের কী পরিহাস, জীবনের শেষ পাঁচ বছরে পুত্র আন্দ্রেউসকার থেকে অন্য মহাদেশে নির্বাসিত থাকতে বাধ্য হন স্নেহশীল তারকোভস্কি। এবং, পুত্র হিসেবে পিতাকে চিঠি দেওয়ার বিষয়ে দ্বিধান্বিত থাকলেও শেষ বছর কয়েক অনর্গল চিঠি লেখেন ছেলেকে যাকে তিনি চিঠিতে ত্যাপা বলে উল্লেখ করেন – “তোমার বাবা তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, তোমায় মিস্ করে এবং সবসময়ই তোমায় মনে করে ভালোবাসায়। ভেঙে পড় না, সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন।” ইভান, এডমুন্ডের মতো ঠিক বারো বছর বয়স থেকেই আন্দ্রেউসকা তার বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, পরের পাঁচ বছরের জন্য । ফুসফুসের ক্যান্সারে মৃতপ্রায় তারকোভস্কির সঙ্গে শেষপ্রহরে প্যারিসে দেখা হয় আন্দ্রেউসকার । তারকোভস্কির ডায়েরির একদম শেষ দিকের এন্ট্রিতে আমরা দেখি – “আমায় আন্দ্রেউসকাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে সে সিনেমা এবং সাহিত্য বিষয়ে কী জানে।” প্রথম ছবির প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ ছবির শেষাবধি কিশোর ছেলে এবং গাছের আশ্রয় তারকোভস্কির যাত্রাকে আলোকরেখায় নির্ণীত করে রাখে।
শেষেরও শেষ
ইতালিতে থাকাকালীন ডায়েরিতে তারকোভস্কি লেখেন – “একটি কমবয়সি ছেলে পাহাড়ি রাস্তায়। সে হাত তুলে গাড়ি থামাতে চায়, কেউ থামে না। তার মুখ বিষণ্ণ, সাদা, ক্ষয়াটে চুল। আমার ত্যাপার কথা মনে পড়ে। সেও একদিন বড় হয়ে যাবে, পূর্ণবয়স্ক, এরকমই বিষণ্ণ, দুঃখী।” আমারও, বাড়িতে এক বারোবছরিয়া ছেলেকে দেখতে দেখতে মনে আসে বাড়িতে বাবা থাকলেও একদিন বড় হতে হতে সেও এক বিষণ্ণ, একাকী, বাবা হয়ে যাবে ।
পেশাগতভাবে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। নেশায় সিনেমাপ্রেমী। চলচ্চিত্র বিষয়ক একাধিক বই লিখেছেন বাংলা ও ইংরেজিতে। স্মৃতি সত্তা ও সিনেমা, কিছুটা সিঁদুর বাকিটা গোলাপ, সত্যজিত রে'জ হিরোজ অ্যান্ড হিরোইনজ, সিক্সটিন ফ্রেমজ এই লেখকের কিছু পূর্ব প্রকাশিত বই।