ক্ষীরোদ ঘোষ বাজারের ওই বাড়ির কিছু আশ্চর্য ব্যাপার স্যাপার ছিল, যা তখন বুঝতে পারতাম না, এখন পারি। সময় তৈরি করেছে এক দীর্ঘ সাঁকো। সাঁকোর এপার থেকে একটা প্রেক্ষিত পাওয়া যায়, যা কাছ থেকে পেতাম না। রাস্তার উপর তিন তিনটে বড় গেট, ওপরে যাবার তিনটে ঢাউস সিঁড়ি এবং গন্তব্যে পৌঁছনোর বাধা অসংখ্য গলিঘুঁজি। একতলার সিঁড়ির আলো প্রায়ই খারাপ থাকত, ফলে আকাশ থেকে ল্যান্ডিংয়ে এসে পড়া আলোর স্বাদ পাওয়ার জন্য হোঁচট খেতে খেতে উঠতে হত দোতলায়। আনাড়ি নবাগতের গড়িয়ে পড়ে একতলায় ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত ষোলো আনা। কিন্তু একশোর বেশি ফ্ল্যাটের মধ্যে বাঙালি বাসিন্দা ছিল হাতে গোনা। আমাদের নিয়ে বড়জোর চার পাঁচটি পরিবার। বাকিরা শিখ, মারোয়াড়ি, গুজরাতি, দক্ষিণী। আমাদের দু’পাশের দুই প্রতিবেশী শিখ ও মারোয়াড়ি। নানা ধরনের ফোড়ন ও মশলার গন্ধ ছাড়াও গলি ও সিঁড়িতে ভেসে বেড়াত হিন্দি, গুর্মুখি, তামিল ইত্যাদি ভাষার টুকরো। এখন আমার আবছা সন্দেহ হয়, আমার লেখার যে ভারতীয়ত্ব নিয়ে ঈষৎ গর্ব অনুভব করি, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই ‘বাজারে’র বাড়িতেই। যাই হোক, আমাদের ভালমানুষ প্রতিবেশীরা যখন দেখলেন,আমাকে স্কুলে পাঠাবার জন্য অভিভাবকদের কোনওই উদ্যোগ নেই, তখন তারা এসে উঁকিঝুকি মেরে নানা কৌতূহল ব্যক্ত করতে লাগলেন, খুকি কি স্কুলে যাবে না? এমন মুখ্যু সুখ্যু হয়েই থাকবে?
[the_ad id=”266918″]
আমি নিজের বইয়ের বাক্স এবং স্বরচিত গান কবিতা ইত্যাদি নিয়েই মগ্ন ছিলাম। এর মধ্যে কোথায় স্কুল, কোথায় কী? এবার বাবা-মাকে কিছু বিচলিত মনে হল। কলকাতায় বসে বাঙালি অভিভাবক সন্তানের শিক্ষা নিয়ে ভারতের অন্য ভাষাভাষীদের (যাদের একটি হোমোজিনাস কমন নামে – নন বেঙ্গলি বা অবাঙালি ডাকা হয়) দ্বারা উদ্ভাষিত হতে রাজি হবেন কেন? মা কিছু একটা প্ল্যান করেছিলেন। বাড়ির কাছে হাঁটাপথে বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়। সেখানে পড়ত আমাদের চেয়ে বড় এক পিসতুতো দিদি। অনেক উঁচু ক্লাস। ইলেভেন। একদিন বেণী দুলিয়ে হাসতে হাসতে এসে আমাকে বলল, চল, তোকে স্কুল দেখিয়ে নিয়ে আসি। হাত ধরে বড় রাস্তা পারও করিয়ে দিল সে। ইতুদি। স্কুলের গেট সবুজ। পাঁচিল গোলাপি। সবুজ পাতা ও সাদা গোলাপি ফুলে ভরা মাধবীলতা নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে সেই পাঁচিলের উপর। ভিতরে খেলার মাঠ, ঝাঁকড়া পুরনো বটগাছের নীচে শিবমন্দির, সেকেন্ডারি বিভাগের মস্ত বিল্ডিং, সব দেখেশুনে পছন্দ হয়ে গেল।
[the_ad id=”266919″]
ভর্তির ফর্ম ভরলেন বাবা। অ্যাডমিশনের পরীক্ষা দিতে গেলাম সেজেগুজে। তাতে এমন কিছু গন্ডগোল করে এলাম, যাতে বাবা মার মুখ চুন। পরীক্ষায় পাশ না করলে বাড়িতে বসে থাকতে হবে এবং শুনতে হবে প্রতিবেশীদের মন্তব্য। আরও একটি বছর। কেন যে ভুলভাল লিখে এলাম, ছেড়ে এলাম প্রশ্ন। ইংরাজিতে নিজের নাম লিখতে বলা হয়েছিল, আমার মনে হল ওটা ঠাট্টা। আমার নাম তো ওরা জানেই। স্কুলের নামও লিখলাম না। স্কুল তো জানেই নিজের নাম। একটা প্রশ্ন ছিল, রিক্সাগাড়ির কয়টি চাকা। আমার মনে হল, এটা নিশ্চয়ই সাইকেল রিক্সা। কাজেই চাকা তিনটে। হাতে টানা রিক্সাকে গাড়ি বলে না তো! এত প্রশ্ন ছেড়ে ও ভুল করে আসার কারণে অ্যাডমিশন টেস্টে ফেল করা অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তবু শেষে ভর্তির ডাক পেলাম। পরিবারের মান বাঁচল।

পরবর্তীকালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবার পর দেখেছি, শহুরে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সহযোগীদের অভিভাবকরা তাদের ইংরাজি মিডিয়াম, নইলে অন্তত সরকারি স্কুলে ভর্তি করেছেন, ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের কথা ভেবে। আমাদের বাড়িতে কেরিয়ার চিন্তার চেয়ে বড় ছিল স্কুলে পৌঁছবার ভাবনা। পায়ে-হাঁটা দূরত্বে হতে হবে স্কুল। তাছাড়া পড়াশুনো শেখার জন্য স্কুলের কিছু ভূমিকা আছে, তবে তা আহামরি কিছু নয়, এই মনোভাব মা-বাবা প্রায়ই ব্যক্ত করতেন। কাজেই আমি হাঁটাপথে স্কুল চললাম। সকাল সকাল ভাত খেয়ে, গোল কৌটোয় টিফিন নিয়ে। পিচবোর্ডের উপর রেক্সিন দিয়ে মোড়া সুটকেসে বইখাতা। হাজরার মোড় পেরিয়ে, রাধাকৃষ্ণ মন্দির পার হয়ে, পুরকর্মীদের কোয়ার্টারের বাইরে মেলা হলুদ-গোলাপি শাড়ির উড়ন্ত ঝাপট নাকে মুখে মেখে স্কুলের দিকে বাঁক নেওয়া। বেলতলা রোডের দিকে বাঁক নিলেই হঠাৎ চোখে পড়ত অনেকটা নীল আকাশ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আর নীলে লিপ্ত হয়ে থাকা সবুজ গাছেরা যেন কোনও জাপানি পটের ছবি।
***
ক্লাস টু-তে সোজা ভর্তি হয়েছি। ক্লাস ওয়ানদের মনে হয় দুগ্ধপোষ্য শিশু। মনখারাপের একটা কারণ , ওই সুন্দর গোলাপি তিনতলা সেকেন্ডারি বিল্ডিংয়ে আমাদের ঢুকতেই দেবে না। প্রাইমারির বাড়িটা একটা ময়লাটে হলুদ ঘুপচি মতো বাড়ি, দেওয়ালগুলো নোনাধরা। একতলায় ভাল আলো আসে না।বাড়িতে পড়ি সঞ্চয়িতা থেকে ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’। আর এখানে সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ। কদিনের মধ্যেই স্কুলের পড়ায় বিরক্তি ধরে গেল। কিছুটা আনন্দ ছিল আঁকার ক্লাসে, রং পেনসিল আর কল্পনা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে ছবি আঁকা যেত। একটা মেঘের বিকেলে ড্রইং দিদিমণি ছবি আঁকছেন, ঘর অন্ধকার। আলো নেই বাইরে মেঘ। সাদা কাগজের উপর পেনসিলের আঁচড়ে ফুটে উঠছে একখানা সোনা ব্যাং, তার পাশে বড় বড় ঘাস। প্রাইমারির বাইরে যে এঁদো চৌবাচ্চা ছিল, তাতে নাকি ভূত বসে থাকত। দিনের বেলা দলবল নিয়ে টিনের ঢাকা খুলে দেখেছি, ভিতরে গঙ্গামাটি মাখা শ্যাওলার পরত, স্থবির জল ও ব্যাঙাচি। কিন্তু আসা যাওয়ার পথে কেউ যদি ‘ভূত ভূত’ বলে চেঁচিয়ে উঠত, ছুট্টে পালাতাম। চোখে চশমার জন্য কাছ-দূর ঠিক আন্দাজ করতে পারতাম না। ওইভাবে ছুটতে গিয়ে একবার ভূগোল দিদিমণির পেটে মাথা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে একটি সলিড চড় খেয়েছিলাম।

সমুদ্রের মতন দুস্তর আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের মোড় পার হওয়ার জন্য প্রথম প্রথম সাহায্য নিতে হত মোক্ষদা নাম্নী এক ‘খরখরে’ মহিলার, যে কাছাকাছি বাড়ি থেকে কয়েকজন নাবালিকাকে পশুপালকের মতন তাড়না করে রাস্তা পার করাত। তার অতি প্রশস্ত কপাল, পিঠে ছড়ানো কোঁকড়ানো চুল, পানে রাঙানো ঠোঁট মনে পড়ে, আর তার সাদা খোলের তাঁতের শাড়ির নকশা পাড়। সাদার উপর কালো আর নীল লতাপাতার নকশা আমার মনের মধ্যে ধরা আছে। রাস্তা পার করানোর বন্দোবস্তের মধ্যে একটা ছোট দুর্নীতি ছিল। আমাদের স্কুল ব্যাগগুলি হাতে কাঁধে ধারণ করত মোক্ষদা। এর জন্য প্রত্যেক বাড়ি থেকে সে পেত দু’টাকা করে মাসে। স্কুলে পৌঁছবার কিছু আগে, ছাত্রীর দল ভারী হতে থাকত আর সুটকেস-বাহিনী মোক্ষদাকে দেখাত সারা অঙ্গে কাঁঠাল গজানো একটি বুড়ো গাছের মতো। একদিন হঠাৎ স্কুলের অফিসে আমাদের ডাক পড়ল। অফিসের কেরানিবাবুরা জানতে চাইলেন মোক্ষদাকে ব্যাগ বওয়ার জন্য কোনও টাকা আলাদা করে দিই কিনা। মোক্ষদা যদিও উত্তরটা আগেভাগে শিখিয়ে রেখেছিল আমাদের, এশট্যাবলিশমেন্টের জেরার মুখে আমাদের বাক্য হরে গেল। দুর্নীতি স্বীকার করলাম না, কিন্তু নীরব রইলাম। এর ফল, পরের দিন থেকে সুটকেস হাতে একা রাস্তা পেরনো। মোক্ষদা সঙ্গে থাকত, কিন্তু দূরে দূরে আর বিড়বিড়িয়ে বকত আমাদের সত্যনিষ্ঠার নিন্দে করে। অবশ্য ক্লাস থ্রি থেকে আর রাস্তা পারাপারের জন্য মোক্ষদার দরকার রইল না। একই রাস্তা দিনে দু’বার করে একবছর পেরচ্ছি। মা-বাবা দেখতাম এই সব ব্যাপার নিয়ে অযথা উদ্বেগ দেখাতেন না।
আমাদের বাড়িতে কেরিয়ার চিন্তার চেয়ে বড় ছিল স্কুলে পৌঁছবার ভাবনা। পায়ে-হাঁটা দূরত্বে হতে হবে স্কুল। তাছাড়া পড়াশুনো শেখার জন্য স্কুলের কিছু ভূমিকা আছে, তবে তা আহামরি কিছু নয়, এই মনোভাব মা-বাবা প্রায়ই ব্যক্ত করতেন। কাজেই আমি হাঁটাপথে স্কুল চললাম। সকাল সকাল ভাত খেয়ে, গোল কৌটোয় টিফিন নিয়ে।
ক্লাস থ্রি-তে উঠে স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা জমা দিতে গেলাম। ভাগ্যিস সঙ্গে ক্লাসের এক বন্ধু ছিল। ক্লাসটিচার ভুরু কুচকে বললেন, তোমার নিজের লেখা? না, মা-বাবা লিখে দিয়েছেন? আমার কান লাল হয়ে উঠেছে। এমন অপমানজনক প্রশ্ন কেউ করতে পারে আমাকে? বন্ধু বলল, না দিদিমণি, ওর খাতা আছে, ও কবিতা লেখে। কোনও সম্পাদকীয় পরিমার্জনা ছাড়াই আমার কবিতা বেরল সেবার। তারপর আর ফিরে তাকাইনি। স্কুল ম্যাগাজিনে আমার লেখা একটি স্থায়ী চিহ্ন হয়ে গেল। আরও একটি পাতায় যেত আমার চাইনিজ কালি ও কলমে আঁকা একটি গান-পাগল কোলাব্যাঙের ছবি, যে বসে আছে ব্যাঙের, মানে, নিজেরই ছাতার নীচে। ড্রইং দিদিমণির পছন্দের। প্রথম দিকে নাম, ক্লাস-সহ যেত। পরে নাম টাম থাকতনা। কেবল ছবিটা। সবাই জানত আমারই আঁকা ওটা।
[the_ad id=”270084″]
স্কুলে যাওয়ার চেয়েও বেশি ভাল লাগত স্কুল থেকে ফেরা। বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে মায়ের হাতের জলখাবার। লুচি আলুভাজা বা পরোটা আর সুজির পায়েস। খুঁটে খুঁটে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া। সঙ্গে বই। লীলা মজুমদার, সুকুমার রায়, বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। বই ঠাসা কাঠের তাক থেকে কোনও একটা তুলে নেওয়া। ঝুঁকে বসে, সামনে খালি প্লেট, অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত পড়া। সেই সময় সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতেও থাকত অজস্র বইয়ের সম্পদ। আমার ভিতরকার শিশু কবিকে তৈরি করছিল আমার নিজস্ব পাঠের পৃথিবী।
পরবর্তী পর্ব ৩ জানুয়ারি ২০২১
লিখতে লিখতে অথৈ দূর: পর্ব ২ – প্রকৃতির পাঠশালায়
কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।




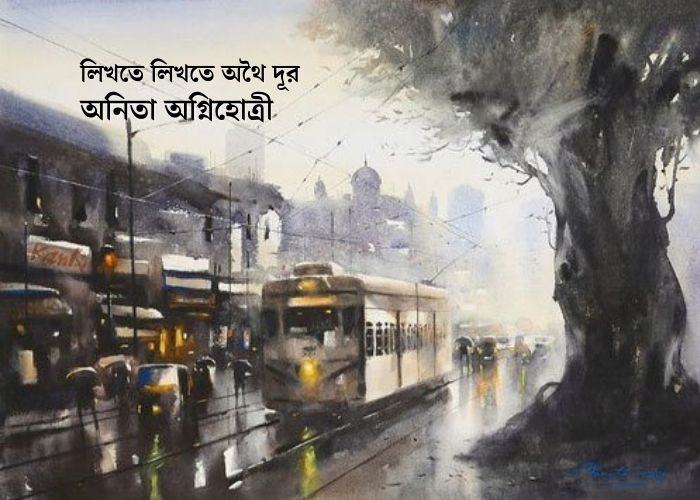





















4 Responses
প্রনাম দিদিভাই।
ভালো লাগছে পড়তে। একটা ছবি আঁকা সময় যেন।
khub bhalo lagche. chobir moto lagche.
যেন কেউ খুব আত্মমগ্ন ভাবে নিজের সঙ্গেই কথা কইছে। কেউ শুনছে কিনা তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনই মনে হয় পাঠশেষে।