উত্তমকুমারের প্রয়াণের পরে তাঁর স্মরণে প্রকাশিত একটি লং প্লেয়িং রেকর্ডের ভাষ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শুরুতেই বলেছিলেন “উত্তমকুমার নায়ক”; বলেই যেন তাঁর মনে হল, ঠিকমতো হল না। তাই পরক্ষণেই বললেন― “মহানায়ক”। ঠিকই তো। আপামর বাঙালির কাছে মহানায়ক বলতে তো একজনই। তাঁর অকস্মাৎ চলে যাওয়া সবার কাছে বজ্রপাতের আঘাত হেনেছিল। স্বভাবতই উত্তমকুমারের প্রসঙ্গ এলে, কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন ছবিতে তাঁর যে উজ্জ্বল বিচরণ, সেটাই উঠে আসে অধিকাংশ আলোচনায়। কিন্তু এর বাইরেও তাঁকে নিয়ে বলবার বেশ কিছু দিক আছে। যা এক অন্য উত্তমকুমারের (Uttam Kumar) সন্ধান দেয়।
মহানায়ক যে খুব ভালো গান গাইতেন, তা মোটামুটিভাবে সবারই জানা। জীবনের শুরুর দিকে তিনি নিষ্ঠাভরে গান শিখেছিলেন পণ্ডিত নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এক অসামান্য সংগীতগুণীর কাছে। নিদানবন্ধুবাবু ছিলেন ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরি ইত্যাদি রীতির শাস্ত্রীয় সংগীতে একজন দক্ষ শিল্পী ও গুণী শিক্ষক। বিভিন্ন ঘরানায় তাঁর তালিম ছিল। এরকম একজন গুরু নির্বাচন দেখেই বোঝা যায়, কতটা গভীরভাবে গান শিখতে চেয়েছিলেন উত্তম। তাঁর পাড়ার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ডা.লালমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখায় পাওয়া যায়, ১৯৪৬-৪৭ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সময়, নিজেই একটি গান লিখে ও সুর করে, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গাইতেন উত্তম। গানটি ছিল― “হিন্দুস্থান মে কেয়া হ্যায় তুমহারা/ও ব্রিটিশ বেচারা/ আভি চলা যাও ইংল্যান্ড বাজা কর ব্যান্ড/ মন্দির মসজিদ মে পূজা আরতি সে শুনো আজান পুকারতি/ দিলকো দিলাও মিল হিন্দু মুসলমান/সারি হিন্দুস্থান মে আয়ি তুফান/ গরিবোঁ কি দুখো কি হোগি আসান।” শুধু গান নয়, এ থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর সমাজ সচেতনতার দিকটিও।

যিনি সংগীতে এতটা সম্পৃক্ত ছিলেন, ছবির জগতে সেই উত্তমকুমারের সংগীত-কণ্ঠ আমরা সেভাবে শুনতেই পেলাম না। শুধুমাত্র দেবকীকুমার বসু পরিচালিত নবজন্ম’ (১৯৫৬) ছবিতে সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ, বৈষ্ণব পদাবলীর সাতটি ছোট ছোট পদ গাইয়েছিলেন তাঁকে দিয়ে। এছাড়া, কোনও এক ঘরোয়া পরিবেশে উত্তমের গাওয়া, আরতি মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় গান “এই মোম জোছনায়…” রেকর্ডে বের করেছিল মেগাফোন কোম্পানি। আমরা জানি, পরবর্তীতে কিছু অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে মণ্টু বসু আয়োজিত ‘বসুশ্রী’-র পয়লা বৈশাখের জলসায় উত্তম গান করতেন। এরকম অনুষ্ঠানে গাওয়া তাঁর কিছু গান সিডি বা সোশ্যাল মিডিয়ায় শোনা যায়। আর কিছু নাটকে অভিনয় করে উত্তম গেয়েছিলেন গান। যার মধ্যে ‘শিল্পী সংসদ’ প্রযোজিত ‘অলীকবাবু’ বা ‘অভিসার’ নাটকের কথা বলা যায়। অথচ, ছবিতে গান গাইতে তিনি যে চাইতেন, তার প্রমাণ আছে উত্তম-লিখিত ‘হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর’ বইতে। একজায়গায় তাঁর গান শেখার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন, “হায়, তখন কী জানতাম ফিল্মে গান গাইবার জন্য প্রযোজকরা কোনোদিনই আমাকে সুযোগ দেবেন না। ক্যামেরার সামনে অপরের গাওয়া গানের সঙ্গে ঠোঁট নাড়াই সার হবে। আর ঐ জায়গাটায় শ্রোতারা শুনবেন অন্য কোনো সুগায়কের কণ্ঠস্বর।” প্রসঙ্গত, গান একবারের বেশি গাইতে না পারলেও, দুটি ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন উত্তমকুমার। যার মধ্যে ‘কাল তুমি আলেয়া’ (১৯৬৬) ছবিতে আশা ভোঁসলের গাওয়া ‘পাতা কেটে চুল বেঁধেছি…’ ও ‘একটু বেশি রাতে…’ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ‘আমি যাই চলে যাই…’ দারুণ জনপ্রিয় এবং অসাধারণ কম্পোজিশন। আর ‘সব্যসাচী’ ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবে, কাহিনি অনুযায়ী উত্তম ব্যবহার করেছিলেন বেশ কিছু বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান। শুধুমাত্র শিপ্রা বসুর একটি গান ছিল তাঁর সুরে। চলচ্চিত্রে সংগীতের সঙ্গে উত্তমকুমারের সরাসরি সম্পর্ক বলতে এটুকুই।
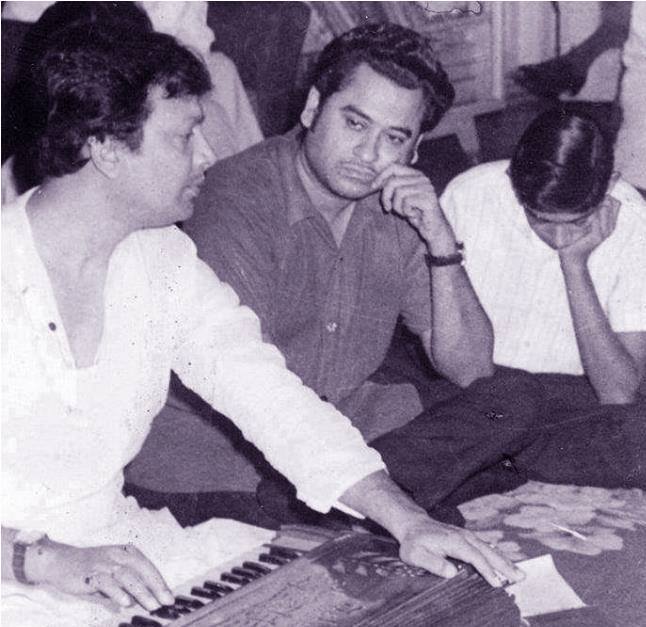
খুব ভালো গান জানতেন বলেই বোধহয়, গানের সঙ্গে ঠোঁট মেলানোর ক্ষেত্রে উত্তম অসাধারণ হয়ে উঠতেন। এ ব্যাপারে যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম, তা নিশ্চয়ই সবাই মানবেন। তাঁর এই দিকটি প্রথম নজরে আসে চিত্রপরিচালক নির্মল দে-র। যাঁকে ‘উত্তমকুমার’-এর জন্মদাতা বলা যায়। কেন?
উত্তমের ছবি-জীবনের শুরুটা ছিল প্রতিকূলতায় ভরা। ১৯৪৭-এ প্রথমবার সুযোগ হিন্দি ‘মায়াডোর’-এ। কিন্তু ছবি মুক্তি পেল না। এরপর, ১৯৪৮-এর ‘দৃষ্টিদান’ থেকে ‘সঞ্জীবনী’ (১৯৫২) অবধি পরপর সাতটি ছবি মুখ থুবড়ে পড়ল তাঁর। চারিদিকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ছড়াছড়ি। ইন্ডাস্ট্রিতে নাম হয়ে গেল ‘ফ্লপ মাস্টার জেনারেল’। এসব দেখেও, পরিচালক নির্মল দে তাঁর ‘বসু পরিবার’ (১৯৫২) ছবিতে বড়ভাই ‘সুখেন’-এর চরিত্রে নিলেন উত্তমকে এবং এই ছবি থেকেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর থেকে শুধুই উত্তরণ। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে এরকম অসফল একজন অভিনেতাকে কেন নিলেন নির্মলবাবু? সেই ঘটনায় আসা যাক…
উত্তমের ছবি-জীবনের শুরুটা ছিল প্রতিকূলতায় ভরা। ১৯৪৭-এ প্রথমবার সুযোগ হিন্দি ‘মায়াডোর’-এ। কিন্তু ছবি মুক্তি পেল না। এরপর, ১৯৪৮-এর ‘দৃষ্টিদান’ থেকে ‘সঞ্জীবনী’ (১৯৫২) অবধি পরপর সাতটি ছবি মুখ থুবড়ে পড়ল তাঁর। চারিদিকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ছড়াছড়ি। ইন্ডাস্ট্রিতে নাম হয়ে গেল ‘ফ্লপ মাস্টার জেনারেল’।
এম. পি.প্রোডাকশন-এর ‘সঞ্জীবনী’-র কাজ তখন চলছে। উত্তম হিরো। এম্.পি-র তিনি চুক্তিবদ্ধ শিল্পী। অন্যদিকে নির্মল দে-ও যুক্ত ঐ সংস্থায়। একদিন নির্মলবাবু দেখলেন, উত্তম স্টুডিওতে বসে গাইছেন, “চাঁদের বেণু বাজবে এবার…”। গানটি ‘সঞ্জীবনী’-তে শৈলেন রায়ের কথায় ও অনুপম ঘটকের সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া একটি গান। সেদিন গানটি গাইবার সময় উত্তমের সুন্দর গায়কির সঙ্গে তাঁর নাটকীয় অভিব্যক্তি ও আত্মমগ্নতার রূপটি নজরে এল নির্মল দে-র। সেই দেখে সলিল সেনকে নির্মলবাবু বলেছিলেন, “ও যখন গাইছিল, সুর, ছন্দ আর কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর অভিব্যক্তি বদলাচ্ছিল― আমি সেটাই লক্ষ্য করছিলাম। যার অনুভূতি এত তীক্ষ্ণ, ভাব স্বতঃউৎসারী, তার পক্ষে সব রোলই করা সম্ভব। ওকে আমি গ্রাম্য চরিত্র দেব― দেখবে ও তাও সুন্দর করবে।… আমি বলছি দেখো―হি উইল স্কোর। কাব্যের রসে যে সঞ্জীবিত হতে পারে―তার অভিনেতা হিসেবে ভয় কী? অবশ্য সঞ্জীবনী-র গান না শুনলে আমিও এতটা বুঝতাম না।”
ঠিক তাই হল। ‘বসু পরিবার’ উত্তমের ভাগ্যকে ঘুরিয়ে দিল। নির্মল দে-র পরের দুটো ছবিতেও নায়ক ছিলেন উত্তম। যার মধ্যে ১৯৫৩-র ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এ প্রথম সুচিত্রার সঙ্গে সংযোগ এবং ছবি মেগা হিট। এরপর, ‘চাঁপাডাঙার বউ’-এ (১৯৫৪) দেখা গেল উত্তমের জীবনের অন্যতম সেরা অভিনয়।

উত্তম বরাবর ছিলেন খেলা পাগল। বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হয়ে খেলা-পাগলামি থাকবে না, তা কি হয়? রাইট ব্যাক পজিশনে একসময় নিয়মিত ফুটবল খেলেছেন তিনি পাড়ার লুনার ক্লাবের হয়ে। বক্সিং শিখতেন ভবানী দাসের কাছে। উত্তমের কৈশোর থেকে যৌবনে পা রাখার সময়টা ছিল উত্তাল চল্লিশের দশক। স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাব, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, দেশভাগ, শরণার্থী সমস্যা এবং এর মধ্যেই আসা স্বাধীনতা ইত্যাদি সবমিলিয়ে গোটা ১৯৪০-এর দশক এবং তার পরেও বেশ কয়েক বছর ছিল চূড়ান্ত ঘটনাবহুল। এরকম দীর্ঘ অশান্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে উত্তমের মতো যাঁরা সেইসময়ে বড় হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের মানসিক দৃঢ়তা গড়ে উঠত বোধহয়, যা থেকে জন্ম নিত অসম্ভব জীবন সংগ্রামের ক্ষমতা। ছবির জগতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লক্ষ্যে শুরুর দিকে উত্তমের যে লড়াই, সেটাই এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে কিছুটা। তাছাড়া, সেই বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই পরাধীনতার প্রভাবে যুবকদের মধ্যে শারীরিকভাবে নিজেদের বলশালী করে তোলার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। যার রেশ চলেছিল স্বাধীনতার পরেও বেশ কয়েক দশক। সম্ভবত সেই প্রভাব থেকেই উত্তমেরও শারীরিক কসরত জাতীয় খেলার দিকে ঝোঁক এসেছিল। তিনি বিভিন্ন সময়ে রোয়িং, টেবিল টেনিস, টেনিস খেলেছেন। ভবানীপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনে নিয়মিত সাঁতার কাটতেন। আর ক্রিকেট তো খেলতেনই। ম্যাটিনি আইডল হবার পরেও, বিভিন্ন মহৎ উদ্দেশ্যে আয়োজিত চিত্রতারকাদের ক্রিকেট ম্যাচে তাঁকে দেখা গেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৬২ সালে ইডেন উদ্যানে হওয়া ‘হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একাদশ’ বনাম ‘কানন দেবী একাদশ’-এর চ্যারিটি ক্রিকেট ম্যাচ। যেখানে চিত্রজগতের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে ভিনু মানকড়, মুস্তাক আলির মতো প্রথিতযশা ক্রিকেটারেরাও মাঠে নেমেছিলেন।

ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবলের নেশাও পুরো মাত্রায় ছিল। মোহনবাগানের অন্ধ সমর্থক ছিলেন উত্তমকুমার। ১৯৭৭ সালে মুম্বাইয়ের ‘রোভার্স কাপ’ ফাইনালে উঠেছিল মোহনবাগান। তখন উত্তমকুমারও শক্তি সামন্তের ‘আনন্দ আশ্রম’ ছবির শুটিংয়ের জন্যে মুম্বাইতে। ফাইনালের আগের দিন, কয়েকজন মোহনবাগান ফুটবলার গিয়েছিলেন উত্তমের সঙ্গে দেখা করতে। মহানায়ক তাঁদের বলেছিলেন, “কালকে না তোদের রোভার্স ফাইনাল? রোভার্স জিতে আসবি। নয়তো আসিস না।” মোহনবাগান কথা রেখেছিল। ঐ ১৯৭৭-এই আমেরিকার কসমস ক্লাবের হয়ে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন ফুটবল সম্রাট পেলে। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইডেন উদ্যানে খেলেছিলেন তিনি। পেলেকে ঘিরে সেইসময় উন্মাদনা ছিল বাঁধনহারা। এই খেলার উদ্যোক্তা ছিল মোহনবাগান ক্লাব। উত্তমকুমার ক্লাবের সেক্রেটারি ধীরেন দে-কে কয়েকটি টিকিটের জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। অত চাহিদার মধ্যেও ধীরেনবাবু বেশ কয়েকটি টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মহানায়ককে। প্রসঙ্গত, ‘ধন্যি মেয়ে’ ছবিতে ‘কালীবাবু’রূপী উত্তমকুমার, তাঁর ফুটবল দল ‘সর্বমঙ্গলা স্পোর্টিং ক্লাব’-কে মোহনবাগানের মতো সবুজ মেরুন জার্সি পরিয়েছিলেন। অবশ্য এই ভাবনাটা ছিল ছবির পরিচালক, যিনি নিজেও একজন কট্টর মোহনবাগানি, সেই অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের। আবার, ‘সপ্তপদী’-তে যে দৃশ্যে ‘কৃষ্ণেন্দু’-রূপী উত্তমকুমার ফুটবল খেলেন, সেখানে তাঁকে পরতে হয়েছিল লাল হলুদ জার্সি। কারণ, শুটিং হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল মাঠে, যার আয়োজন করেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের নামকরা কর্মকর্তা ও ‘বসুশ্রী’ সিনেমার মালিক মণ্টু বসু। ফলে, তাঁর ইচ্ছে অনুসারেই জার্সির রং নির্ধারিত হয়েছিল। ‘সপ্তপদী’ ছাড়াও আরও কয়েকটি ছবিতে উত্তমকুমারকে নানা ধরনের খেলার দৃশ্যে দেখা গেছে।

উত্তমকুমারের গ্রহণযোগ্যতার পরিসর যে কতটা বিস্তৃত ছিল, তা ভাবাই যায় না। যার উজ্জ্বলতা তাঁর প্রয়াণের ৪৩ বছর পরে, আজও এতটুকু ফিকে হয়নি। চিত্রসাংবাদিক রবি বসু ‘আনন্দলোক’ পত্রিকাতে একটি লেখায় লেখেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র একবার তাঁকে বলেছিলেন— “উত্তম যে কত বড় অ্যাক্টর তার পরিমাপ আমাদের দেশের অ্যাক্টরদের পাশে দাঁড় করিয়ে করা যাবে না। ভারতের বাইরের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে যদি ও অভিনয় করতো তাহলে বুঝতে পারতে ও কত বড় শিল্পী।” বুদ্ধদেব বসুও যে ভালোরকম উত্তম-অনুরক্ত ছিলেন, সে কথাও আছে রবিবাবুর লেখায়। তাঁর কাছে মাঝেমধ্যেই উত্তমকুমারের খোঁজ নিতেন ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’-র রচনাকার। রবি বসু সম্পাদিত একটি চলচ্চিত্র পত্রিকায় ‘পাতাল থেকে আলাপ’ নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। উপন্যাসের মূল চরিত্রটি এক রোমান্টিক জনপ্রিয় চিত্রতারকার। যিনি বৃদ্ধ বয়সে দূরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত হয়ে স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন। রবি বসুর বক্তব্য অনুযায়ী, চরিত্রটি উত্তমকুমারের কথা মাথায় রেখেই লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। উপন্যাসটি পড়ে রবি বসুকে উত্তম বলেছিলেন― “আমাকেও কি শেষ বয়সে ওই অবস্থায় পড়তে হবে নাকি! না বাবা, সে আমি সহ্য করতে পারবো না। দেখবেন আমি কোনোদিন বুড়ো হব না।” তার কথা যে এরকম মর্মান্তিকভাবে সত্যি হবে, কে জানত!
সত্যিই তো উত্তমকুমার কোনওদিনই ‘বুড়ো’ হলেন না। আজও তিনি জীবন্ত এক চিরকুমার। মহানায়ক।
তথ্যঋণ :
১) হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর― উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা: অভীক চট্টোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি প্রকাশন)
২) নায়কের কলমে― উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা: অভীক চট্টোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি প্রকাশন)
৩) আমার আমি― উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় (অনুলেখক : গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং)
৪) বিমল চক্রবর্তী সম্পাদিত “চিরদিনের উত্তমকুমার”
এছাড়া, ‘উল্টোরথ’, ‘ঘরোয়া’, ‘প্রসাদ’ ইত্যাদি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।
ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Facebook, Twitter
জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

























