২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন (Ishwarchandra Vidyasagar birthday)। শুধু একটি নির্দিষ্ট দিনই নয়। প্রতিনিয়ত, একটু একটু করে জন্ম নিয়েছেন তিনি। জন্ম নিয়েছেন নিজেরই অতীত থেকে এক সংস্কারমুক্ত এবং আধুনিক ভবিষ্যতের দিকে। আর নিজের জীবনের শেষ পর্বে এসে তিনি অদ্ভুত ভাবে ইতি টানলেন তাঁর সেই চেনা যাত্রাপথে। থেমে গেলেন এক অন্যরকম যাপনের শর্তে। ফলে এবার তিনি সমূলে উপড়ে আনলেন নিজেকে এমন এক জীবনের আয়োজনে যাকে বলা যায় পুনর্বাসন। এমনটা কেউ কখনও ভাবেনি। সম্ভবত দেখেওনি অন্য কারও ক্ষেত্রে। কারণ প্রবুদ্ধ সমাজের একজন অন্যতম পুরোধা হয়েও কেউ কি আর এমন সিদ্ধান্ত নেয়! তাহলে আর তিনি কোথায় এবং কীভাবে বাস্তববাদী! তাই, কেউ বললেন এ হল তাঁর পলায়নী-মন। হাল ভেঙে পালিয়ে যাচ্ছেন, প্রভাব হারাবার ভয়ে। কেউ বললেন ঋণ এবং অপমানের বোঝা– কতদিন আর সহ্য করবেন এইভাবে! কারও মনে হল তাঁর পক্ষে এঁটে ওঠা শক্ত এই নব্য ইংরেজিয়ানা এবং চালচলনের সঙ্গে। আসলে এই সবক’টি প্রেক্ষিতই ভীষণ সত্যি এবং বিচ্ছিন্নভাবে তা হয়তো টুকরো টুকরো কারণও। কিন্তু এগুলি একযোগে জড়ো হতে হতে বিদ্যাসাগরের মনে যা সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল, তা হল সিদ্ধান্ত। আ-যৌবন অনেকভাবে অনেক কিছুর মীমাংসা করেছেন তিনি। সূত্র, আইন, পদ্ধতি, ব্যবহার, লোকাচার, অনাচার, রুচি, নিপুণতা, শাস্ত্র, ব্যকরণ, স্বদেশিয়ানা, সংস্কার, মনুষ্যত্ব– এ সবের। এবার এক নতুন মীমাংসা এবং নতুন সিদ্ধান্ত । আর তা মুখোমুখি দু’জন বিদ্যাসাগরের মধ্যেই। এখানে তাঁরা যে একে অন্যের প্রতিপক্ষ তা কিন্তু নয়। প্রতিষ্ঠিত, বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠানসম বিদ্যাসাগরকে স্বেচ্ছায় বাতিল করে, ভিন্ন পরিবেশে একেবারে অনামা, অচেনা এক অন্য বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠা। হয়ে ওঠা এক আসল মানুষ।

এক বিদ্যাসাগরের অবস্থান যদি হয় গতি, প্রতিবাদ, উপার্জন, সংস্কার, গোষ্ঠী, সংগঠন এবং নাগরিক চিহ্ন, তবে অন্য বিদ্যাসাগর তখন এক বিপরীত অবস্থানে। ভিন্ন চিহ্নে তিনি তখন উন্মুখ তাঁর নিজের পুনর্বাসনে। এবং আরও একবার এক কঠিন পথ তিনি রচনা করলেন এক তরুণ উদীয়মান এবং প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর থেকে বৃদ্ধ অসুস্থ এবং বান্ধবহীন সেই অন্য বিদ্যাসাগরে পৌঁছতে। এটা কোনও পারাপার নয়। উপরন্তু একবারে পেরিয়ে চলে যাওয়া সেই কোনওভাবেই আর না ফিরে আসার সিদ্ধান্তে। দুই বিদ্যাসাগরের মধ্যে সমতা পেল পণ্ডিতের গোঁ বা সাধু ভাষায় দৃঢ়তা, আর ওই ‘বিদ্যাসাগর’ খেতাবটি।
না, এ কোনও সন্ন্যাস নয়। নয় সন্ন্যাসীর মতো একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়া অজ্ঞাতের পরিচয়ে। নয় অভিমানে নিজেকে ব্রাত্য মনে করাও। এমনকি হেয়-জ্ঞানে অন্যদের তুচ্ছ করে বিদেশ যাত্রাও নয়। নয় নতুন করে কোনও অর্থকরী প্রকল্পে যুক্ত হওয়া। এ হল জীবনের মোড় অন্যদিকে ঘোরানো। নিজের মধ্যে যেটুকু সতেজ এবং অনাঘ্রাত শুভবোধ আছে সেটুকুই সম্বল করে এগিয়ে এসে হাত ধরলেন ওই দ্বিতীয় বিদ্যাসাগরের।
এই দ্বিতীয় প্রতিবাদী পথের চিহ্নে আমরা পেলাম তাঁর কিছু অনড় অথচ অনায়াস সিদ্ধান্ত। কলকাতায় বাদুড়বাগানের তাঁর সেই প্রিয় বাড়ি, বৈঠকখানা, বইয়ের সংগ্রহ কিছুই বিক্রি করলেন না। এ সবই কিন্তু তাঁর স্ব-উপার্জনের নিরিখ। কারও সঙ্গে কোনও আলোচনার অবকাশ না রেখে, নিজ সিদ্ধান্তে এক মেমসাহেবের ছেড়ে যাওয়া একটি একতলা বাংলো কিনলেন। কিনলেন এক বিস্তৃত সংলগ্ন জমিও। পুনর্বাসনের স্বপ্নকে বাস্তব করতে এই তাঁর শেষ বিনিয়োগ। বাংলা থেকে বহুদূরে তৎকালীন বিহারের কর্মাটাঁড় নামে সাঁতাল-অধ্যুষিত এক এলাকা। সুবিধা শুধু রেল-সংযোগ। বাদবাকি আর সবই নতুন, অচেনা, ধূসর, রুক্ষ এবং প্রায় জনমানবহীন। বীরসিংহ থেকে কলকাতা আসার সময় সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা ঠাকুরদাস। আর এবারের এই যাত্রায় তিনি নিজেই নিজের অভিভাবক। এমনকি পরিত্যাগ করে এসেছেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদেরও। যে পরিণতির কথা ভেবেই মানুষ কাতর হয়ে পড়ে , আশঙ্কা করেই ভয়ে শিউরে ওঠে, তাকেই তিনি গ্রহণ করলেন স্বেচ্ছায়। শাস্তি না শান্তি – কী দিতে চাইলেন নিজেকে! নাকি এর কোনওটাই না ভেবে আরও এক নতুন উদ্যমে মেতে উঠতে চাইলেন তিনি। এবারে প্রত্যক্ষত আর সমাজ সংস্কার নয় কিন্তু সংস্কার তাঁর নিজের। অর্থাৎ ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের পুনর্বাসন এবং আনন্দের সঙ্গে সসম্মানে বেঁচে থাকা।

নিজের পছন্দমতো একটি বসতের ব্যবস্থা করেই যে পাট গুটিয়ে চলে এলেন তা নয়। নিজের বয়ানেই একটি উইলও লিখলেন। যাকে যেমন মাসোহারা দিতেন, তার হিসেব এবং তাদের কাছে ওই অর্থ সময়মতো পৌঁছে যাবার বাস্তব ব্যবস্থাও। নিজের স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়, পরিজন, পরিচারিকা, দুস্থ এবং সাহায্যপ্রার্থী কেউই বাদ গেল না সেই নিখুঁত হিসেব থেকে। এ যেন বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁদের আমৃত্যু প্রাপ্য বা পেয়ে যাবার অধিকার। তিনিও রেহাই চাইলেন না তাঁর এই দায় থেকে।
এই সঙ্গে, প্রত্যেকটি আপনজনকে বিদায়ী চিঠি লিখে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন তাঁর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি। মনের দূরত্বকে, বুকের মধ্যে চেপে না রেখে তিনি তাঁর জীবনের এই শেষ সিদ্ধান্তটি নিলেন। এই চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায় যে নিজের জীবনের নতুন দায়িত্বের শর্তগুলো আঁকতে তিনি তাঁর দায় থেকে সরে দাঁড়াননি। দায়ও যে দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে এই বাস্তববোধের সূচনা করলেন বিদ্যাসাগর তাঁর এই পুনর্বাসনের মধ্যে দিয়ে।
আরও একটি কাজ যা তিনি একই সঙ্গে করলেন তা হল, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বঞ্চিত করা। এও এক নজিরবিহীন প্রয়াস। তাঁর মৃত্যুর পরে নারায়ণচন্দ্র অবশ্য বিদ্যাসাগরের মতো প্রথিতযশা বাবার সই জাল করে সেই সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং যথেচ্ছাচারে তা বিক্রি করে দেন। বিদ্যাসাগরের অসীম সৌভাগ্য এবং সাধারণ মানুষের ভালোবাসার জোরে অন্যের অর্থব্যয়ে আবার তার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করা যায়। তিনি বুঝেছিলেন যে নারায়ণচন্দ্রের মতো পরজীবিদের সমূলে উপড়ে না ফেললে এ সমাজের শুদ্ধি হবে না। ঠিক যেমন করে উপড়ে ফেলেছিলেন সংস্কৃত কলেজের অশিক্ষক অধ্যক্ষ রসময় দত্তকে। যেমন করে উৎপাটন করেছিলেন বাল্য বিবাহ এবং কুলীনদের বহুবিবাহের মতো কু-প্রথা । ঠিক সেইভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে উত্তরাধিকারী হতেও যোগ্যতা লাগে।

নিজের সংসার, পরিজন, ঘরবাড়ি, নগর জীবনের সুবিধে এবং কলকাতার সুধী সমাজ ছেড়ে এই যে তিনি চলে এলেন – তা ঠিক কীসের টানে! কোন প্রত্যাশায় এত বড়ো এক তোলপাড় ডেকে আনলেন নিজের জীবনে! যাঁর হাত ধরে আমাদের জীবনে পেশাদারিত্ব, উচ্চাশা, উপার্জন, নাগরিকায়ণ এমন সব ভাবনা ক্রমে সহজভাবে ধরা দিতে লাগল, তিনিই কিনা হেঁটে গেলেন এসবের বিপ্রতীপে!
আদতে বিপ্রতীপ হাঁটলেন কি! না। হাঁটলেন বা জবরদস্ত হয়ে বসলেন মানুষের ধর্ম যে কী তা বুঝতে। প্রকৃতি এবং প্রান্তিক মানুষকে এক করে দেখে এমন এক নতুন ভূখণ্ড বানাতে যেখানে মনুষ্যত্ব বোধই রাজা হয়ে বসবে আমাদের চেতন ও অচেতনের সাম্রাজ্যে। তাঁর বাস্তব চেতনার ঐশ্বর্য দিয়ে বুঝতে চাইলেন দারিদ্র্য, উপায়হীনতা আর স্বনির্ভরতার সূত্রগুলি।
আরও একটি কাজ যা তিনি একই সঙ্গে করলেন তা হল, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বঞ্চিত করা। এও এক নজিরবিহীন প্রয়াস। তাঁর মৃত্যুর পরে নারায়ণচন্দ্র অবশ্য বিদ্যাসাগরের মতো প্রথিতযশা বাবার সই জাল করে সেই সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং যথেচ্ছাচারে তা বিক্রি করে দেন। বিদ্যাসাগরের অসীম সৌভাগ্য এবং সাধারণ মানুষের ভালোবাসার জোরে অন্যের অর্থব্যয়ে আবার তার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করা যায়। তিনি বুঝেছিলেন যে নারায়ণচন্দ্রের মতো পরজীবিদের সমূলে উপড়ে না ফেললে এ সমাজের শুদ্ধি হবে না।
তাঁর চেনা পৃথিবীর ধাপগুলি একে একে সাজিয়েই এই প্রত্যন্ত এলাকায় গড়ে তুললেন প্রাইমারি স্কুল, দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি এবং ওই পোড়ো জমিতে উচ্চ ফলন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষি– এই তিনের সমন্বয় আবার ঘটল তাঁর কর্মকাণ্ডে। বাদ গেল তর্ক-বিতর্ক, সুপারিশ, এবং সুবিধাভোগীদের যাতায়াত। কুৎসিতের পাশে এসে বসল সুন্দর। এল লাবণ্য আর আশাবাদ। আর এল মানুষের সঙ্গে সরাসরি এক স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগ। জমি ভর্তি ভুট্টা চাষ করিয়ে সেগুলিই আবার বিলিয়ে দিলেন সেই তাদের মধ্যে, যারা ওই ফসল ফলিয়েছে। কাছ থেকে তারাও দেখল তাঁর উদার মন, নিয়মানুবর্তিতা, উদ্যোগ এবং আড়ম্বরহীন এক পরিচ্ছন্ন জীবন। তিনি বন্ধু হলেন এমন এক দল মানুষের যাদের কাছে শহুরে সংস্কার একেবারেই মূল্যহীন। কারণ জঙ্গল আর রুক্ষ জমিই তাদের জীবনধারণের উপায়। শিক্ষার আলোই যেখানে পড়েনি সেখানে কী বা সংস্কৃত, কিইবা বাংলা! আর ইংরেজি তো দূরস্থান। একমাত্র যা কাজে লাগল তা হল মানুষের প্রতি তাঁর নিবিড় ভালোবাসা। যার বিনিময়ে সভা, সমিতি বা সংগঠন এসব কিছুই লাগে না।

এই দ্বিতীয় চেতনার উদ্ভাসেই পুনর্বাসন ঘটল তাঁর। উপবিতধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিসেবে দ্বিজ তো তিনি ছিলেনই। এবার হলেন ‘দ্বিগুণ জীবিত’। একদিন তাঁর পায়ে পায়ে মাইল ফলক দেখতে দেখতেই বীরসিংহ গ্রামটি কলকাতা পৌঁছেছিল। এবার যে যাত্রা তা আর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নয়। এক ব্যক্তিত্ব থেকে আর এক ব্যক্তিত্বে এসে দাঁড়ানো। যার ফলে আমরা দেখলাম যে মেমসাহেবের সেই বাংলোটকে কী করে অ আ উ ঊ করে নিতে হয়! দেখলাম বিস্তীর্ণ জমির মধ্যে ছিমছাম বাড়ি। কোনও জমিদার বা রাজার নয় – একজন পণ্ডিতের। আজ যাঁর নামে রেল ইস্টিশন। Subaltern Studies -এর বহু আগে যা ধরা ছিল তাঁর জীবনযাপনে। এই স্বেচ্ছা নির্বাসনে তিনি পেলেন স্বাধীনতা আর মননের আনন্দ। পেলেন স্বজনচিহ্নে এক নতুন ভূখণ্ড- যা তিনি বার বার চেয়েছিলেন তাঁর ফেলে আসা জীবনে। আর দেখলেন যে এই নতুন মানুষগুলি কেউ তাঁর কৃপা বা সাহায্যপ্রার্থী নয়। বরং সকলেই সহযোগী এবং তাঁর দিন যাপনের আশ্রয়। এখানে মাটি রুক্ষ কিন্তু তা এক ছায়াঘেরা নিবিড় বনাঞ্চল ……………….
“এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত”।
প্রণাম এই ‘দ্বিগুণ জীবিত’ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যিনি নির্বাসনকে সম্ভাষণ করলেন– পুনর্বাসন এই নতুন নামে।
ছবি লেখকের সৌজন্যে পাওয়া।
আড্ডা আর একা থাকা,দুটোই খুব ভাল লাগে।
লিখতে লিখতে শেখা আর ভাবতে ভাবতেই খেই হারানো।ভালোবাসি পদ্য গান আর পিছুটান। ও হ্যাঁ আর মনের মতো সাজ,অবশ্যই খোঁপায় একটা সতেজ ফুল।




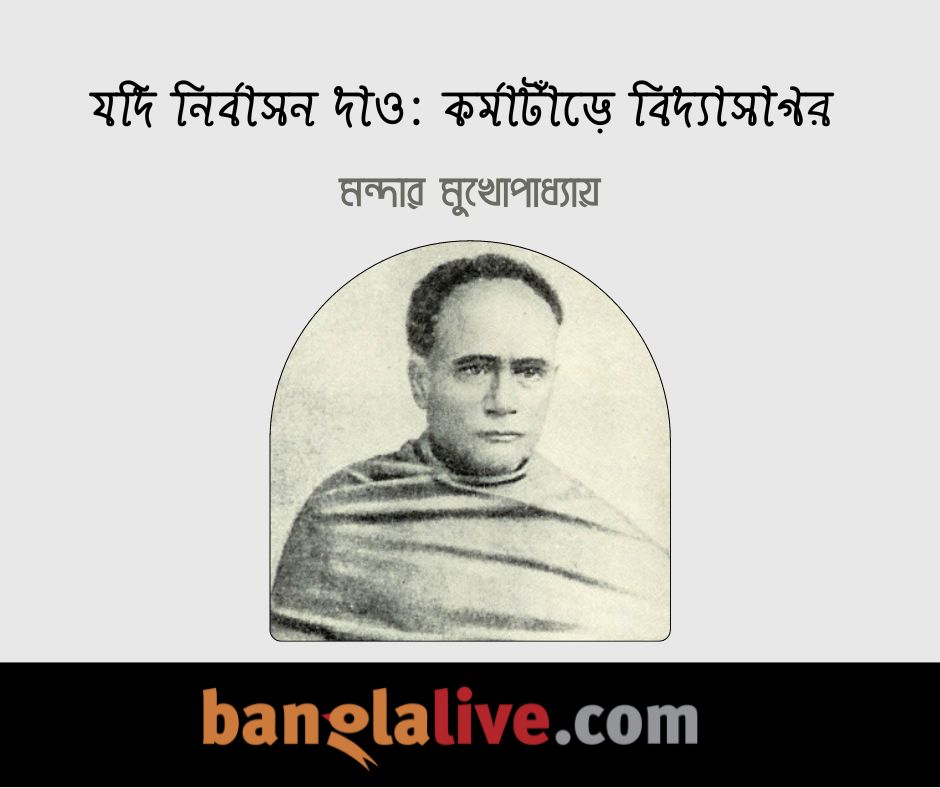





















5 Responses
“তুমি কাহার সন্ধানে সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন আকুল করে কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাসো”
সেই তো! এমন আকুল আর কে করে!
উচ্চমানের লেখা।
ধন্যবাদ
উচ্চমানের লেখা