বাংলা সিনেমার ইতিহাস সুদীর্ঘ, কালোত্তীর্ণ। প্রায় একশো বছরের ইতিহাসে বহু ঘাটের জল পেরিয়ে সাবালক হয়েছে বাংলা সিনেমা। বাংলা সিনে সঙ্গীতের জগৎ তারই সমসাময়িক। তবে শুধু বাংলাই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও সিনেমার সূচনাপর্ব থেকে সঙ্গীতের ব্যবহার হয়ে এসেছে৷ এমনকি নির্বাক যুগেও সরাসরি প্লেব্যাক না এলেও আবহসঙ্গীতের ব্যবহার ছিল৷ সে সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বাদ্যযন্ত্রী, গায়ক-গায়িকারা এসে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। অনেকক্ষেত্রে ছবির নির্দেশকই সঙ্গীত পরিচালনার কাজ সামলাতেন। পরবর্তী কালে অবশ্য আলাদা করে সঙ্গীত পরিচালক নিয়োগ করা হত।
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলা সিনেমার আদিপর্ব থেকে সঙ্গীত পরিচালকদের দীর্ঘ তালিকায় কোনও মহিলার নাম নেই। তাহলে কি সত্যিই মহিলা সঙ্গীত পরিচালক বা সুরকার ছিল সে যুগে বিরল? কণ্ঠ বা নেপথ্যসঙ্গীতে বহু প্রতিভাময়ী নারীদের পাওয়া গেলেও সঙ্গীত পরিচালনা বা সুরারোপ নিয়ে কোথাও যেন দেখা গেছে মহিলাদের প্রতি অদ্ভুত অনাস্থা, অবিশ্বাস ও অদূরদর্শিতার আবহ।
আর সেই জন্যই পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মতোই বাংলা সিনেমার সুরের জগৎ হয়ে উঠেছিল পুরুষশাসিত। সেখানে মহিলারা ছিলেন একপ্রকার ব্রাত্য। অথচ ভীষণভাবেই ‘ছিলেন’ তাঁরা। আমরাই পারিনি চিনে নিতে। নইলে ক’জনই বা নাম শুনেছেন সেই সব বিরল প্রতিভার অধিকারিনীদের? ক’জন জানেন বাংলা চলচ্চিত্র সঙ্গীতে তাঁদের অবদানের কথা? ক’জন মনে রেখেছেন নীতা সেন, অসীমা মুখোপাধ্যায়, বাঁশরী লাহিড়ী, বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, অরুন্ধতী দেবী-দের ‘অশ্রুত’ আখ্যান…
কথায় আছে, প্রথা থাকলে প্রথাভাঙার রীতিও থাকবে৷ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সুর সংযোজন বা পরিচালনার ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। দীর্ঘ একশো বছরের ইতিহাসে উঠে আসেন হাতে-গোনা কিছু অসামান্যা বিদূষী, যাঁরা সিনে-সঙ্গীত জগতে রাতারাতি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। অথচ রয়ে গেছেন অনালোচিত, অপ্রাসঙ্গিকতার ঘেরাটোপে। সময় এসেছে সেই সব ছকভাঙা, প্রতিভাময়ীদের কথা তুলে ধরার।
বাংলা সিনেমায় মহিলা সুরকারদের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যার নাম মনে পড়ছে তিনি বাঁশরী লাহিড়ী। বাঙালি সুরকার, গায়ক ও বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক অপরেশ লাহিড়ীর স্ত্রী। বাপ্পি লাহিড়ীর মা। বাঁশরী নিজে একজন দক্ষ গায়িকা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারঙ্গম। ডোভার লেন মিউক কনফারেন্সে খেয়ালে প্রথম হয়েছিলেন। স্বামী-পুত্রের পরিচয়ে তিনি আদৌ আলোকিত নন। মার্গ সঙ্গীতের পাশাপাশি ঠুমরী ও শ্যামাসঙ্গীতেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৬৬ সালে ‘সুভাষচন্দ্র’ (হিন্দি) সিনেমায় অপরেশ লাহিড়ীর সুরে বাঁশরীর গাওয়া ঠুমরি ‘নেহি মানে জিয়ারা হমার’ অনবদ্য এক সৃষ্টি। ছেলে বাপি লাহিড়ীর সুরেও গেয়েছেন বাঁশরী৷ ১৯৭৬ সালে ‘তেরে প্যায়ার মে’ সিনেমায় শৈলেন্দ্রর কথায় ভুপেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে তাঁর ডুয়েট ‘ভুল গয়ে হাম’ এক অনন্যসাধারণ গজল।

অথচ শুধু প্লে ব্যাক বা ভোকালেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বাঁশরী। করেছেন সঙ্গীত পরিচালনাও। ১৯৬২ সালে সুশীল ঘোষ পরিচালিত ‘দিল্লি থেকে কলকাতা’ সিনেমায় সুর দেন তিনি। সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয় এই সিনেমার গান।
বাঁশরীর প্রায় সমসাময়িক ছিলেন অরুন্ধতী দেবী৷ সুঅভিনেত্রী, পরিচালক, লেখক আবার সুগায়িকাও ছিলেন তিনি। বিশ্বভারতীতে পড়ার সময় আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে গানের তালিম। চল্লিশের দশকে অরুন্ধতী রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন রেডিওতেও। কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ সিনেমার সূত্র ধরে তিনি ঢুকে পড়েন টলিউডে। এরপর একে একে ‘নবজন্ম’, ‘পঞ্চতপা’, ‘বিচারক’, ‘মা’, ‘ছেলে কার’, ‘ঝিন্দের বন্দী’, ‘জতুগৃহ’তে তাঁর অসামান্য অভিনয় দাগ কেটে যায়।

তবে শুধু অভিনয় বা গান নয়, সিনেমাতে সুরও দিয়েছেন অরুন্ধতী দেবী। একটি নয়, পাঁচ পাঁচটি সিনেমায় সুর দিয়েছেন অরুন্ধতী। ১৯৬২ সালে পীযুষ বসুর ‘শিউলি বাড়ি’ ছবিতে সুরকার হিসেবে ডেবিউ করেন তিনি। তাঁর সুরে মৃণাল চক্রবর্তীর গাওয়া ‘রাই জাগো রাই জাগো’ গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়। এর পর ১৯৬৭-তে ‘ছুটি’, ১৯৭০ সালে ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ১৯৭২-এ ‘পদিপিসির বর্মীবাক্স’ ও ১৯৮৪-তে ‘দীপার প্রেম’ চলচ্চিত্রে সুর দেন তিনি।
আধুনিক ও ভক্তিমূলক গানের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার। অসম্ভব সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী বিজনবালা বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষাতেই ছিলেন স্বচ্ছন্দ। ৪০-৫০-এর দশকে তুমুল জনপ্রিয়তা পান তিনি। ছিল অসংখ্য রেকর্ড। নজরুল ইসলামের বহু গানে বিজনবালা সুর দিয়েছেন৷
চল্লিশের দশকে বিজনবালা এক অভাবনীয় ও ব্যতিক্রমী কাণ্ড ঘটান। গান গাইবার জন্য পারিশ্রমিক, সোজা ভাষায় রয়্যালটির দাবি করে এক সংস্থার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে জেতেন। সাম্প্রতিককালে গানের জন্য যে রয়্যালটির প্রচলন, বিজনবালা-ই ছিলেন তার পুরোধা। গান গাইবার পাশাপাশি সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনাও করেন তিনি। ১৯৭০-এ ‘মহাকবি কৃত্তিবাস’ ও ১৯৭৬-এ কালিকা সেনের সঙ্গে যৌথ পরিচালনায় ‘যুগমানব কবীর’ চলচ্চিত্রে সুরারোপ করেন বিজনবালা।
টলিউডে নীতা সেনের পা রাখা অনেকটা ‘ভিনি ভিডি ভিসি’র মতো। অর্থাৎ তিনি এলেন, দেখলেন ও জয় করলেন। পাঁচের দশকের শেষে, যে বছর বাঁশরি লাহিড়ী ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পান, সে বছরই সেই একই অনুষ্ঠানে রাগাশ্রয়ী গানের জন্য পুরস্কার জেতেন নীতা। কেউই ভাবেননি পরবর্তীকালে বাংলা সিনে-সঙ্গীতের জগতে দাপিয়ে বেড়াবেন এই দুই কৃতি শিল্পী। দু’জনের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিসরেও ছিল সুসম্পর্ক।
রেডিওতে কাজ করার সময়ে একাধিক আধুনিক বাংলা গানে সুর দেন নীতা। ১৯৭৭ সালে আসে প্রথম ব্রেক। অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ‘বাবা তারকনাথ’ ছবিতে সুর দিলেন নীতা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় সুর দিয়ে গোটা বাংলা মাতিয়ে তোলেন নীতা। কেদার রাগে মান্না দে-র গাওয়া ‘শিব শম্ভু ত্রিপুরারি’, বা আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান’, আশা ভোঁসলের ‘তুমি সূর্য তুমি চন্দ্র’ গানগুলি লোকের মুখে মুখে ফেরে। ছবি ও ছবির গান দুইই হিট। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে মাইলফলক গড়েছিল সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি অভিনীত ‘বাবা তারকনাথ’।

এর পর আর পিছু ফিরে দেখতে হয়নি নীতাকে। গোলাপ বউ (১৯৭৭), নন্দন (১৯৭৯), সীতা (১৯৮০), সোনার বাংলা-র (১৯৮২) মতো একের পর এক হিট ছবিতে সুর দেন নীতা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায় থেকে অনুরাধা পড়োওয়াল পর্যন্ত অসংখ্য শিল্পীরা গান গেয়েছেন তাঁর সুরে। তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় ‘রক্তজবা’ (১৯৭৮) ছবি মুক্তি না-পেলেও পরে ১৯৮২ সালে তার রেকর্ড বেরয়। এবং এই ছবির সূত্র ধরেই বাংলা গানের দগতে পা রাখেন অনুপ জালোটা। মৃদুভাষী, লাজুক ও নম্র স্বভাবের নীতা সবমহলেই কুড়িয়ে নেন সমাদর ও শ্রদ্ধা। কোনও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া নীতা-ই প্রথম স্বতন্ত্র ও একক প্রতিভার জোরে টলিউডে নিজের পৃথক স্থান পাকা করে নেন। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে পরবর্তী কালে পেয়েছিলেন ‘মেন্টর’- রূপে৷ শেষদিন পর্যন্ত বহাল ছিল সেই সম্পর্ক।
নীতার পাশাপাশি আরও এক মহিলা তখন দ্রুত গতিতে উঠে এসেছিলেন বাংলা সিনেমার সঙ্গীতজগতে। তিনি অসীমা মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল মাল্টিস্টারার ছবি ‘চৌরঙ্গী’। সাহিত্যিক শংকরের উপন্যাস অবলম্বনে এই ছবি পরিচালনা করেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, উৎপল দত্ত, বিশ্বজিৎ, অঞ্জনা ভৌমিক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়… কে নেই তাতে।
ছবি মুক্তি পেলে লোকের মুখে মুখে ঘুরেছিল মান্না দে-র কণ্ঠে ও মহানায়কের লিপে সেই গান ‘বড় একা লাগে এই আঁধারে’। কেউ প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাননি এই গানের সুরকার এক মহিলা- অসীমা মুখোপাধ্যায়। দেশ রাগে নিবদ্ধ বিরহ পর্যায়ের এই গান আলোড়ন ফেলেছিল তামাম বঙ্গদেশে।

কী করে ‘চৌরঙ্গী’-তে ব্রেক পান অসীমা, তা-ও এক মজার ঘটনা। অসীমা দেবী জানান, ছবিতে সুর দেওয়ার কথা ছিল কিংবদন্তী শচীন দেববর্মণের। সে সময় প্রায় ৫০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিতেন তিনি। এদিকে ছবিটি অসীমা দেবীরই পারিবারিক প্রোডাকশন। বিপুল অঙ্কের সেই টাকা দিতে না পারায় নিজের কাঁধে তুলে নেন সঙ্গীত পরিচালনার ভার৷ সে সময় ইন্ডাস্ট্রিতে বাঘা বাঘা সুরকারদের উপস্থিতি৷ তাঁদের সঙ্গে কীভাবে পাল্লা দেবেন, তা নিয়ে অসীমার মনেও ছিল দ্বিধা। কিন্ত হাল ছাড়েননি পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও পঙ্কজ মল্লিকের এই ছাত্রী। বাকিটা ইতিহাস।
এর পর আর থামতে হয়নি তাঁকে। একে একে মুক্তি পায় ‘আজকের নায়ক’, ‘শুভ রজনী’, ‘তনয়া’, ‘নিশান্তে’, ‘দাবার চাল’, ‘মেমসাহেব’-এর মতো হিট ছবি। ‘মেমসাহেব’ ছবিতে তাঁর নিজের সুরে মান্না দে-র সঙ্গে তিনি গেয়েছেন ‘আজ বুঝি পাখিরা’। টলিউড ইন্ডাস্ট্রির কৃতি মহিলা সঙ্গীত পরিচালকের পাশাপাশি সুগায়িকা রূপেও অসীমা পরিচিত। খুব কম লোকই জানেন পঙ্কজ মল্লিক ও বাণীকুমারের পরিচালনায় মহালয়ার ভোরে হওয়া কালজয়ী অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী’তেও রয়েছে অসীমার গাওয়া একটি গান ‘শুভ্র শঙ্খ রবে’।
ষাটের দশকে এইচএমভি থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডও বেরিয়েছিল অসীমার। ‘মেমসাহেব’ ছবিতে অপর্ণা সেনের লিপে তাঁর গাওয়া ‘বঁধূ এমন বাদল দিনে’ আজও শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে। বাংলার প্রায় সব প্রথিতযশা শিল্পীরাই তাঁর সুরে গান গেয়েছেন। তবু আজও অসীমার আক্ষেপ, লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কখনও তাঁকে দিয়ে গান গাওয়ানোর সুযোগ হয়নি। এই আক্ষেপ বুকে নিয়ে আজও নিভৃতে দিনযাপন করছেন স্বর্ণযুগের এই কালজয়ী সুরকার।
আশির দশকের পর, অসীমাদেবী ছাড়া তেমন দাপুটে মহিলা সঙ্গীত পরিচালক পায়নি বাংলা ইন্ডাস্ট্রি। তবে ব্যতিক্রমী কিছু শিল্পী স্বল্প পরিসরে নিজের প্রতিভার পরিচয় রেখেছিলেন। ১৯৮০ তে ‘সীতা’ ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন নীলা সেন। ২০০৩ সালে তরুণ মজুমদারের জাতীয় পুরস্কারজয়ী ‘আলো’ ছায়াছবি’তে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, আর এক প্রথিতযশা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শিবাজি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে৷ ঠিক যেমন ২০০৮ সালে অতনু বসুর ‘সেদিন দুজনে’-তে চন্দন রায়চৌধুরীর সঙ্গে জুটি বাঁধেন রীতা রায়।
২০০৮ সালেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘সাধুবাবার লাঠি’তে সুর দেন সলিল-দুহিতা অন্তরা চৌধুরী। চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যালও এক সময় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। ২০০০ সালে ‘আততায়ী’ ও ২০০৪ সালে ‘কালো চিতা’ এই দু’টি ছবিতে নির্দেশনার পাশাপাশি সুরারোপের দায়িত্বও সামলেছেন। এছাড়া ২০০০ সালে ‘পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম’ ছবিতে সুমিত্রা কুন্ডু ও ঠিক দশ বছর আগে ১৯৯০ সালে ‘ভাগ্যলিপি’তে সুমিত্রা লাহিড়ী সামলেছিলেন সঙ্গীত পরিচালনার কাজ।
টলিউডের মতো বলিউডেও সঙ্গীত পরিচালনার জগতে একসময় দাপিয়ে বেড়িয়েছেন বহু অসামান্যা। ১৯৩৪ সালে ‘অদল এ জাহাঙ্গীর’ ছবিতে সুরকার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন বেগম ইশরত সুলতানা (১৯০৬-১৯৭২)। বলিউডে তিনিই প্রথম মহিলা সুরকার। ১৯৩৭-এ ‘কাজ়াখ কি লড়কি’ সিনেমায় তার সঙ্গীত অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা পায়৷ ১৯৩৫-এ ‘তালাশ এ হক’ সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করেন অভিনেত্রী নার্গিসের মা জদ্দনবাঈ (১৮৯২-১৯৪৯)৷

বলিউডের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মহিলা সুরকার রূপে উঠে আসেন সরস্বতী দেবী (১৯১২-১৯৮০)। ‘ঝুলা’, ‘অচ্ছুত কন্যা’, ‘জীবন নাইয়া’র মতো একাধিক ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন তিনি। বলিউডে সঙ্গীত পরিচালনার জগতে আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ঊষা খান্না (১৯৪১)। ‘দিল দেকে দেখো’, ‘হম হিন্দুস্তানী’, ‘হবস’, ‘আও প্যায়ার করে’, ‘সৌতন’-এর মতো অসংখ্য ছায়াছবিতে সুর দিয়েছেন ঊষা। ১৯৮১-তে বাংলা ছবি ‘অবিচারে’ও সুরারোপ করেন তিনি।
দক্ষিণী সিনেমাতেও পাওয়া যায় একঝাঁক মহিলা সুরকারদের। এঁদের মধ্যে ভানুমতি রামকৃষ্ণ-সহ ভবতারিণী (ইলায়ারাজার কন্যা), এ আর রেহানা (সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমানের বোন) অন্যতম। নতুনদের মধ্যে স্নেহা খানওয়ালকর (গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর), অলকানন্দা দাশগুপ্ত (পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের মেয়ে), রচিতা অরোরা, জসলীন রয়াল, পরম্পরা ঠাকুর, শ্রুতি হাসন বিশেষভাবে উল্লেখ্য।
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী কিশোরী আমোনকরও তিনটি সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। সঙ্গীত পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন স্বয়ং ‘সুরসম্রাজ্ঞী’ লতা মঙ্গেশকরও। ১৯৫৫ সালে মারাঠি সিনেমা ‘রাম রাম পহনে’তে সুর দিয়ে মাত করেছিলেন লতা। এ ছাড়াও তিনি সুর দিয়েছেন একাধিক মারাঠি ছবিতে।
দুর্ভাগ্যের বিষয়, তুলনামূলক বিচারে বলিউডের মহিলা সুরকাররা টলিউড বা অন্যান্য আঞ্চলিক ছায়াছবিতে সক্রিয়ভাবে কর্মরত মহিলা সঙ্গীত পরিচালকদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে৷ সবচেয়ে বড় কথা, এখনও বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাননি তাঁরা। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সে তুলনায় ভাগ্যহীন। এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে বাঙালি দর্শক ক্রমে ভুলতে বসেছে তাঁদের ‘ঘরের মেয়ে’দের।

সেই জন্য অসীমা মুখোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তি সুরকার আক্ষেপ করে বলেন, “আজকাল আর কেউ ডাকে না। খোঁজ নেয় না। মহিলা বলেই বুঝি আমরা প্রাপ্য সমাদর পেলাম না।” এই প্রজন্মের আরেক নবীন সঙ্গীত পরিচালক উপালি চট্টোপাধ্যায় বলেন, “আজও বাংলার মহিলা সুরকারদের লিঙ্গ বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় নানা প্রতিকূলতার। তবুও আশার কথা বহু মেয়েরা আজও এগিয়ে এসে সুর করছেন, নিজের মতো করে লিখছেন গান।”
দিনের শেষে এই আশাটুকু নিয়েই বেঁচে থাকা, ফের ঘুরে দাঁড়ানো। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আজও লড়ে যাচ্ছেন বাংলার প্রমীলা সুরকারের দল। নিজের ও পূর্বসূরীদের অবহেলা ও বিস্মৃতির আড়াল ভেঙে তাঁরা উঠে এসে দাঁড়াচ্ছেন সামনে, সুরের আলোকজ্জ্বল পথের উৎস সন্ধানে।
*ছবি সৌজন্য: youtube, facebook, wikimedia
*ঋণ স্বীকার:
১. রাজীব চক্রবর্তী, সংগ্রাহক ও সঙ্গীত গবেষক
২. জয়দীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ও গবেষক
৩. দেবজ্যোতি মিশ্র, বিশিষ্ট সুরকার ও শিল্পী
৪. সুখেন্দুশেখর রায়, সাংসদ ও আলোচক
৫. চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহার, অমৃতা চ্যাটার্জি (মুখার্জি) ও ড. সুজয়কুমার পাল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
পেশায় সাংবাদিক প্রসেনজিতের জন্ম ১৯৮১-তে। লেখালেখির শুরু কবিতা দিয়েই। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ফেলো, প্রসেনজিতের গবেষণার বিষয় রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও সঙ্গীততত্ত্ব। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে লেখা। অবসরে ভালোবাসেন সরোদ বাজাতে, পুরনো চিঠি ও বই পড়তে।




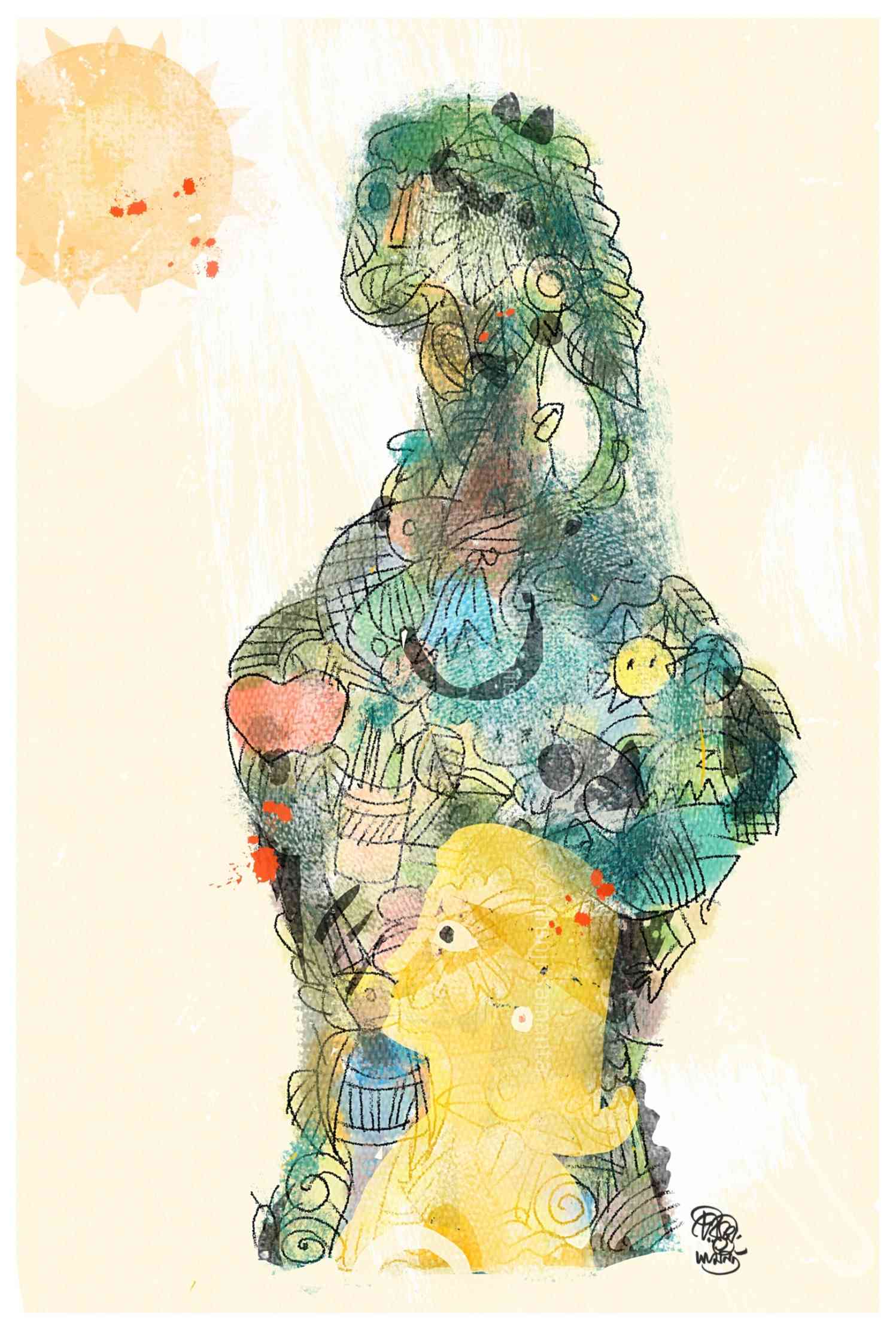





















5 Responses
ঋদ্ধ হলাম।
খুব ভালো আর্টিকল
ঋদ্ধ হলাম।
খুব ভালো আর্টিকল।
প্রসেনজিৎ, লেখা ভালো লাগল। এই বিষয়ে তো আর কারও লেখা চোখে পড়েনি আগে। এরকমই আর-একটি প্রায় অনালোচিত অধ্যায় হল মহিলা যন্ত্রশিল্পীদের কথা। আলাদা করে কেউ কেউ আলোচনার কেন্দ্রে এসেছেন, কিন্তু সার্বিক আলোচনা হয়নি। এই কদিন আগেই প্রায়াত শিশিরকণাদির কথা মনে পড়তেই এমন একটা ভাবনা মনে এল। দেখো সে বিষয়ে কোনও লেখা তৈরি করা যায় কিনা!
তথ্যসমৃদ্ধ লেখা অত্যন্ত ভালো লাগলো
Atyanta proyojoniyo ebang asambhab bhalo lekha Prasenjitda. 🌻