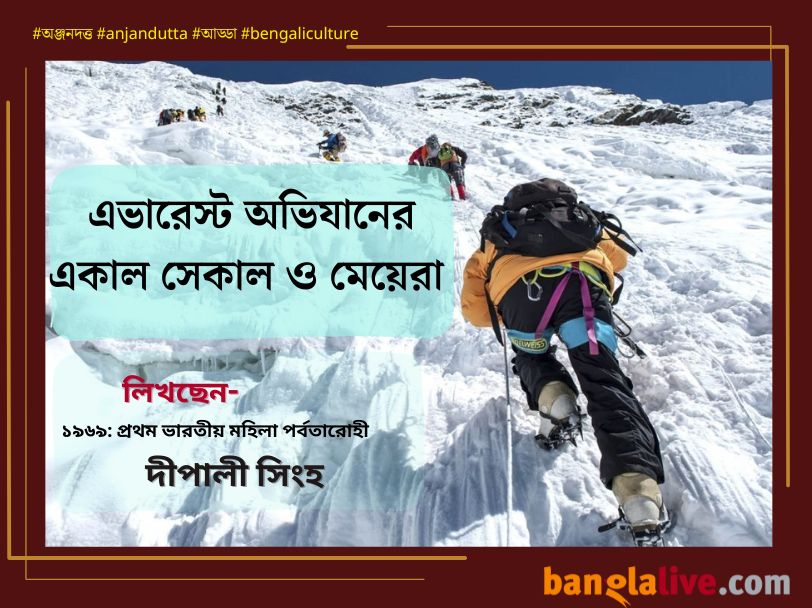হিমালয় (himalaya) নামটার মধ্যেই নিহিত রয়েছে কত অজানা রহস্য ও অচেনা রোমাঞ্চের ছোঁয়া। ভারতবর্ষে আমরা পাহাড় বলতে হিমালয়কেই বুঝি। বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হলেও এই হিমালয় সবদিক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বরমাল্য। কী দৈর্ঘ্যে, কী উচ্চতায়, কী বিরাটত্বে, কী মহিমায়, কী সৌন্দর্যে হিমালয় অনন্য। এই পর্বতমালা ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার এক জীবন্ত বিগ্রহ। এছাড়া হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখররাজি, তার ভয়াল সৌন্দর্য, তার অজানা রহস্যের হাতছানি চিরদিনই আকর্ষণ করে চলেছে রোমাঞ্চ পিপাসু অভিযাত্রীদের। হিমালয়ের গহন কন্দরে তাই অবিরত চলেছে মৃত্যুকে পায়ে মাড়িয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলার অবিরত সংগ্রাম, যার নাম পর্বতারোহণ।
পর্বতারোহণ ভারতবর্ষে খুব বেশিদিন শুরু না হলেও, ভারতীয় পর্বতারোহীরা বিভিন্ন দুরূহ অভিযানে অংশ নিয়েছে এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর শৃঙ্গ এভারেস্ট (Everest) জয়েও সফল হয়েছে আমাদের পুরুষ ও মহিলা অভিযাত্রীরা। একসময় এভাবেই আরোহণের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি রেকর্ড ছিল আমাদের সংগ্রহে। মেয়েদের মধ্যে একজন তো দু’বার পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট আরোহণ করে ফেলেছে। তা ছাড়াও প্রায় ১৫ জন এভারেস্ট বিজয়ীনির দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। ‘এভারেস্ট’—চারটি অক্ষরের একটি ছোট্ট শব্দ। কিন্তু এই ছোট্ট শব্দটির যে কী বিশাল ব্যপ্তি, কী গভীর ব্যঞ্জনা, কী মহিমান্বিত গৌরব, তা বোধহয় কমবেশি আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারি।
আরও পড়ুন: এভারেস্ট অভিযান: এক রূপকথা
পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ পর্বতমালা হিমালয়—যা কিনা পাঁচটি দেশের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। সেই হিমালয়ের তথা বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ—এভারেস্ট। যদিও ভারতের মধ্যে হিমালয়ের একটি বড় অংশ রয়েছে, তবুও পর্বতারোহণ যে একটা স্পোর্ট কিংবা অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় খেলা হতে পারে, সেটা কিন্তু আমরা শিখেছি অনেক পরে। আমরা এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার অনেক আগে থেকেই বিদেশিরা এসে ভারতীয় হিমালয়ে নানান অভিযান চালিয়েছে।
ভারতীয়দের টনক নড়ল সেদিন, যেদিন তেনজিং নোরগে নামক এক পর্বতপুত্র নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী এডমন্ড হিলারির সঙ্গে পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট-এ ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করল। দিনটি ছিল ইংলন্ডের রাণীর অভিষেকের দিন। সারা বিশ্ব-কাঁপানো এই সংবাদ সমস্ত যুব সমাজকে উদ্বেলিত করেছিল। তেনজিং ততদিনে পশ্চিমবাংলার দার্জিলিং-এর অধিবাসী। তাই এই সাফল্য সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত ভারতীয়দের থেকেও পশ্চিমবাংলার অধিবাসীদের কাছে একান্ত আপন বলে মনে হল। আপামর যুবক-যুবতী এক নতুন উন্মাদনায় মেতে উঠল। এমনকী প্রশাসনও নড়েচড়ে বসল। পাহাড়ে চড়া বা পর্বতারোহণ যে একটা অন্যতম স্পোর্ট বা দুঃসাহসিক খেলা হিসেবে গণ্য হতে পারে, সেই ধারণাকে মান্যতা দিয়ে তৈরি হল ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র—হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট—আমাদেরই শৈলশহর দার্জিলিং-এ। সেই শিক্ষাকেন্দ্রে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হল ১৯৫৪ থেকে।
ভারতীয়দের টনক নড়ল সেদিন, যেদিন তেনজিং নোরগে নামক এক পর্বতপুত্র নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী এডমন্ড হিলারির সঙ্গে পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট-এ বৃটিশ পতাকা উত্তোলন করল। দিনটি ছিল ইংলন্ডের রাণীর অভিষেকের দিন। সারা বিশ্ব-কাঁপানো এই সংবাদ সমস্ত যুব সমাজকে উদ্বেলিত করেছিল। তেনজিং ততদিনে পশ্চিমবাংলার দার্জিলিং-এর অধিবাসী।
এখানেই বোধহয় বীজ বপন হল এভারেস্ট নামক সেই রোমহর্ষক, ভয়াল সৌন্দর্যের অধিকারী, অজানা রহস্যে ভরা উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে অভিযানের অদম্য বাসনার। যদিও সময় লেগেছে অনেকদিন, গঙ্গা দিয়ে জল বয়ে গেছে অনেক, তবুও আমরা পেরেছি। পশ্চিমবাংলার প্রথম এভারেস্ট অভিযান সংগঠিত হয় ১৯৯১ সালে প্রাণেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তিব্বতের গ্রেট ক্যুলুয়ার রুট দিয়ে। সমস্ত পুরুষ সদস্য, একজনই মহিলা রীতা চক্রবর্তী। সে অভিযান অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়েও সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। কিন্তু তাদের অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও মনোবলের জয় হয়েছে ১০০%।
এরপর আরও দু-একটি প্রচেষ্টার পর সাফল্য এল ২০১০-এ বসন্ত সিংহরায় ও দেবাশীস বিশ্বাসের হাত ধরে। ২০১০-এর মে মাসের ১৭ তারিখে সকাল ৭টায় ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করল এই দুই বাঙালি, এভারেস্ট শীর্ষে, এ এক পরম প্রাপ্তি পুরো পর্বতারোহী সমাজের। যে কোনও ফুটবলারের কাছে যেমন অলিম্পিকে যাওয়ার একটা স্বপ্ন থাকে, যে কোনও ক্রিকেটার যেমন ওয়ার্ল্ড কাপে খেলার ইচ্ছা পোষণ করে, ঠিক তেমনই যে কোনও পর্বতারোহীর কাছে এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণ এক স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সমস্ত পর্বতারোহীরা এই পরম আকাঙ্ক্ষিত শৃঙ্গ আরোহণের ইচ্ছা সযত্নে লালন করে। তাই দুই বঙ্গসন্তানের এই কৃতিত্ব বঙ্গবাসীর কাছে এক উন্মাদনা হয়ে রইল।

মেয়েদের মধ্যে ভারতীয় হিসাবে প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করে বচেন্দ্রী পাল ১৯৮৪ সালে। উত্তরকাশীর এই কন্যার সাফল্য মহিলাদের পর্বতারোহণে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। ভারত তথা পশ্চিমবাংলার মেয়েদের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল এবং মহিলাদের সাফল্যের প্রতি সবার মনোযোগও বাড়ল।
বাঙালি মেয়েদের এভারেস্ট আরোহণের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসবে কুঙ্গা ভুটিয়ার নাম। নাম শুনে অবাক লাগছে তো। তা একটু লাগবেই। জন্মসূত্রে বাঙালি না হলেও কুঙ্গার জন্ম পশ্চিমবাংলায়। এই বাংলায়ই তার বেড়ে ওঠা। কর্মজীবন, সংসার-জীবন সবই এখানে। তাই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী কুঙ্গা ভুটিয়া ১৯৯৪ সালে বাংলা থেকে প্রথম এভারেস্ট চূড়ায় পা রাখা মহিলা অভিযাত্রী। কুঙ্গার এই কৃতিত্বে অন্য আরোহী মেয়েদের উত্তেজনার পারদ আরও তুঙ্গে উঠল। তারা একটা আশার আলো দেখতে পেল।
কিন্তু যতটা ভাবা যায়, প্রকৃত কাজে এগোনো তার থেকে অনেক বেশি কঠিন হয়ে ওঠে। প্রথম বাধা অর্থের—সেটা এক চরম বাধা। বাঙালির এভারেস্ট আরোহণের প্রথম দিকে খরচ লাগত ১৫ লাখ টাকা। এখন সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ গুণ।
১৯৯৪-এর পর অনেকটা সময় ফাঁকা গেছে। শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতি থাকলেও অন্যান্য বাধার সম্মুখীন হয়ে বাংলার মেয়েরা এভারেস্টের পথে পা বাড়াতে অপারগ ছিল।

টাকার যোগাড়, শরীরকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা, অনুশীলন, পারিবারিক অবস্থা—সব কিছু নিয়ে এক ধরনের অসহায়তা গ্রাস করেছিল। কিন্তু যারা পাহাড়ে যায় তাদের দমিয়ে রাখা দুঃসাধ্য। সমস্ত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে একমাত্র দৃঢ় মনোবল এবং অদম্য সাহস ও এভারেস্টের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ নিয়ে নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছাপোষা মেয়ে ছন্দা গায়েন, ২০১৩ সালে বেরিয়েছিল তার স্বপ্নের অভিযানে। দুর্গম হিমালয়ের বরফে আবৃত পথ, শীতল হিমবাহ, আগ্রাসী ফ্রিডাম, বরফের চোরাবালি পেরিয়ে বাধা-বিপত্তি দু’পায়ে মাড়িয়ে বাঙালি কন্যা ছন্দা গায়েন ২০১৩ সালের ২০শে মে যখন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পা রাখল, সেই দিনই বাংলার মহিলা পর্বতারোহণের আরেক গৌরবময় অধ্যায় শুরু হল। ওই একই বছরে একেবারেই নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে টুসি দাস ওই একই পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল এভারেস্ট শিখরে। ছন্দা ও টুসি একেবারেই আমাদের ঘরের মেয়ে। তাদের এই সাফল্যের কৃতিত্ব আমাদের আবারও মনে করিয়ে দিল যে বাঙালি মেয়েরাও পারে। তারপর সুনীতা হাজরা—শীর্ষের কাছাকাছি পৌঁছেও আবহাওয়া এবং অসুস্থতার কারণে শিখর আরোহণের সফলতা পায়নি। কিন্তু তার প্রচেষ্টা পুরোপুরিই ছিল। এরপর আবারও সুনীতা হাজরা এবং লিপিকা বিশ্বাস এক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু নানান কারণে সে অভিযান সম্ভব হয়নি।
এরপর এল ২০২২। যখন পিয়ালী বসাক স্বপ্নশিখরে পৌঁছে বাঙালি মেয়েদের আরোহণের পথে আরও খানিকটা অনুপ্রাণিত করল। এখানে বলতেই হবে যে, এভারেস্ট আরোহণের যে দুর্গমতা, যে ভয়াল পথ, যে দুস্তর হিমবাহ, যে ফুটিফাটা ক্রীভাসের ফাঁদ আর -৪৫ ডিগ্রির ঠাণ্ডা, তা কিন্তু পুরুষ-মহিলা বিচার করে না। ওই একই পথে যেমন লম্বা-চওড়া সুঠাম দেহধারী, রোজ গাদা গাদা মাংস খাওয়া, ইউরোপ, আমেরিকার অধিবাসীরাও যায় তেমনই এই বাংলার নরম-সরম বাঙালি মেয়ে, সাড়ে চার পাঁচ ফুট হাইটের, ৪০ কেজি ওজনের, সর্বদা পুষ্টিকর খাবার না খেতে পাওয়া বাঙালি মেয়েদেরও যেতে হয়। একই প্রতিকূলতা, একই তুষার-ঝঞ্ঝা, হিমবাহের তুষারাবৃত পথে চলতে হয়। সেখানে কিন্তু পুরুষ, মহিলা বা এদেশ-ওদেশ বা বাঙালি-অবাঙালি কোনও ভেদাভেদ নেই। একমাত্র শারীরিক ক্ষমতা, মানসিক প্রস্তুতি আর প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে জেতার সাইসটাই দরকার।

এই মুহূর্তে আর এক বাঙালি কন্যা, তারকেশ্বরের সবিতা মাহাতো এভারেস্টের পথে বেসক্যাম্পে পৌঁছে গেছে। এই বাংলা থেকে টাকার যোগাড় করতে না পেরে বিহার সরকারের সহায়তায় সে অভিযানে এগিয়েছে।
এটাই হচ্ছে আসল কথা। টাকার অভাবে কী পুরুষ কী মহিলা কোনও এভারেস্ট অভিযানই দলগতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না এই বাংলা থেকে। বড়জোর দু’জন কী তিনজন অথবা একক প্রচেষ্টায় এখন এভারেস্ট অভিযান হচ্ছে।
পশ্চিমবাংলায় মেয়েদের পর্বতারোহণ শুরু হয় আমারই উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে। ১৯৬৭ সালের প্রথম সেই মহিলা রন্টি অভিযান থেকে আজ আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। অনেকটাই এগিয়েছি, তবে যতটা অগ্রগতি হওয়া দরকার ছিল ততটা হয়তো হয়নি। তার কিছু কারণও আছে।
আমাদের সময় অভাব ছিল উপযুক্ত পোশাক-আসাক, সাজসরঞ্জাম, পারিবারিক বাধা, সামাজিক পরিবেশ, প্রযুক্তির অভাব, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং আরও অনেক অনেক অসুবিধা। তখন চাইলেও বা পুরোপুরি সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও মেয়ে দুর্গম পাহাড়ের পথে বেরিয়ে পড়তে পারত না। এখন সে বাধা অনেকটা দূর হয়েছে বটে, কিন্তু এখন সময়াভাব, উপযুক্ত আগ্রহের অভাব, অত্যধিক প্রতিকূল পরিবেশকে মানিয়ে নেওয়ার শক্তির অভাব। এখন পর্বতারোহণ অনেকটা প্যাশনের চেয়ে বরং ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে, তথ্য পাওয়া যায় মোবাইলের এক ক্লিকের মাথায়, সাজসরঞ্জামের কমতি নেই, তবুও মেয়েদের আরোহণের স্বপ্ন তো আমাকে ভাবায়। অন্যান্য যে কোনও খেলায় যখন দেখি মেয়েদের দুনির্বার অগ্রগতি এবং অজস্র সাফল্য, তখন মনখারাপ লাগে।
এই মুহূর্তে আর এক বাঙালি কন্যা, তারকেশ্বরের সবিতা মাহাতো এভারেস্টের পথে বেসক্যাম্পে পৌঁছে গেছে। এই বাংলা থেকে টাকার যোগাড় করতে না পেরে বিহার সরকারের সহায়তায় সে অভিযানে এগিয়েছে।
এটাই হচ্ছে আসল কথা। টাকার অভাবে কী পুরুষ কী মহিলা কোনও এভারেস্ট অভিযানই দলগতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না এই বাংলা থেকে। বড়জোর দু’জন কী তিনজন অথবা একক প্রচেষ্টায় এখন এভারেস্ট অভিযান হচ্ছে।
পশ্চিমবাংলায় মেয়েদের পর্বতারোহণ শুরু হয় আমারই উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে। ১৯৬৭ সালের প্রথম সেই মহিলা রন্টি অভিযান থেকে আজ আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। অনেকটাই এগিয়েছি, তবে যতটা অগ্রগতি হওয়া দরকার ছিল ততটা হয়তো হয়নি। তার কিছু কারণও আছে।
আমাদের সময় অভাব ছিল উপযুক্ত পোশাক-আসাক, সাজসরঞ্জাম, পারিবারিক বাধা, সামাজিক পরিবেশ, প্রযুক্তির অভাব, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং আরও অনেক অনেক অসুবিধা। তখন চাইলেও বা পুরোপুরি সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও কোনও মেয়ে দুর্গম পাহাড়ের পথে বেরিয়ে পড়তে পারত না। এখন সে বাধা অনেকটা দূর হয়েছে বটে, কিন্তু এখন সময়াভাব, উপযুক্ত আগ্রহের অভাব, অত্যধিক প্রতিকূল পরিবেশকে মানিয়ে নেওয়ার শক্তির অভাব। এখন পর্বতারোহণ অনেকটা প্যাশনের চেয়ে বরং ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রযুক্তি অনেক এগিয়েছে, তথ্য পাওয়া যায় মোবাইলের এক ক্লিকের মাথায়, সাজসরঞ্জামের কমতি নেই, তবুও মেয়েদের আরোহণের স্বপ্ন তো আমাকে ভাবায়। অন্যান্য যে কোনও খেলায় যখন দেখি মেয়েদের দুনির্বার অগ্রগতি এবং অজস্র সাফল্য, তখন মনখারাপ লাগে।

মেয়েদের পর্বতাভিযানে যাওয়ার প্রাথমিক কারণগুলি দূর করতে না পারলে এই যাত্রা কতদূর এগোবে বলা মুশকিল। এক্ষেত্রে শারীরিক বাধার চেয়েও সামাজিক চেতনা বা পারিবারিক উৎসাহের ভূমিকা অনেক বেশি। হিমালয় সচেতনতা এবং অ্যাডভেঞ্চার স্পিরিট জাগিয়ে তুলতে হবে ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে। এর জন্য প্রয়াসী হতে হবে পর্বতপ্রেমী ও পর্বত অভিযাত্রীদেরই। আশা রাখি ভবিষ্যতের চিত্রটা উজ্জ্বল হয়ে উঠবেই।
ছবি সৌজন্য: roar media, Pinterest, wikipedia
কোলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি। পূর্বভারতের প্রথম মহিলা পর্বতাভিযাত্রী দলের সংগঠক ও দলনেত্রী। মোট বারোটি অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়াও ট্রেকিং, রক ক্লাইম্বি্ং ও অন্যন্য নানা এ্যডভেঞ্চারের আঙিনায় তাঁর অনায়াস বিচরণ। অর্জনে আছে প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্সও। গান, কবিতা ও নাটক তাঁর শখ। ৭২ বছর বয়সে ১৪০০০ ফুট উচ্চতার 'চন্দ্রতাল'-এ গিয়ে প্রথম অভিযানের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছেন। ৭৫ বছর বয়সে দিদি নং ওয়ান হয়েছেন। যুবদপ্তরের অধীনে পর্বতারোহন ও অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের অন্যতম কার্যকরী সদস্য। তেনজিং নোরগে এওয়ার্ড সহ নানা সম্মানে ভূষিত। নিজের একটি ফাউন্ডেশন আছে যা পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে কাজ করে।