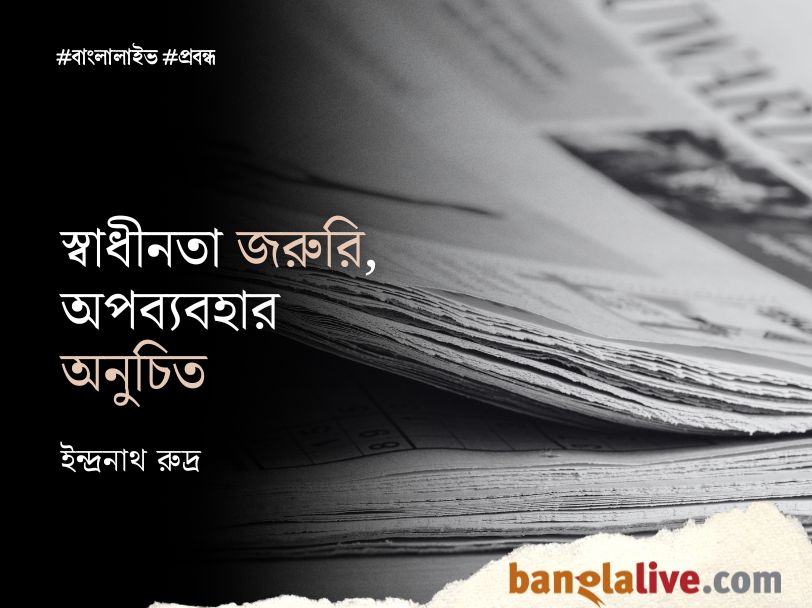(World Press Freedom Day)
ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর প্রথম সার্বিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সরকারি ও সরাসরি কোপ পড়ে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে। এই কোপ এতই মারাত্মক ছিল যে, সে বছর ২৫ জুন রাত ১২টার মিনিট কয়েক আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকরউদ্দিন আলি আহমেদ ‘ইমারজেন্সি অর্ডার প্রোক্লেমেশন’-এ সই করলেও পর দিন সকালে দিল্লি থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়নি। সেই সময়ে শেষ রাতে, এমনকী ভোরেও বহু খবরের কাগজ ছাপা শুরু হত। কাজেই, খবর সময় মতো ধরানো যায়নি বলে দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার খবর বেরোয়নি, বিষয়টি আদৌ তা নয়। (World Press Freedom Day)
ভাজা মাছের উলটো পিঠ: ইন্দ্রনাথ রুদ্র
আসলে অধিকাংশ সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের অফিস ও ছাপাখানা দিল্লির যে তল্লাটে ছিল, সেই বাহাদুর শাহ জ়াফর মার্গে বিদ্যুৎ সরবরাহই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে। (World Press Freedom Day)
‘হিন্দুস্তান টাইমস’, ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এর মতো যে গুটি কতক ন্যাশনাল নিউজ়পেপারের অফিস বাহাদুর শাহ জ়াফর মার্গে্ ছিল না, কেবল সে সব সংবাপত্রই এই জরুরি অবস্থার খবর ছাপতে সক্ষম হয় ২৬ জুন। তৎকালীন মাদ্রাজ থেকে (পরে যা চেন্নাই হয়েছে), প্রকাশিত ‘দ্য হিন্দু’-র লিড নিউজ়ের হেজলাইন ছিল: ‘প্রেসিডেন্ট প্রোক্লেমস ন্যাশনাল ইমারজেন্সি: প্রেস সেন্সরশিপ ইম্পোজ়ড’। তবে এই সেন্সরশিপ বা খবরে সরকারি নজরদারি, কাটাছেঁড়া ও খবর বাতিল করা ২৬ জুন শুরু হলেও, তার আগের রাতেই বাহাদুর শাহ জ়াফর মার্গের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মধ্যে দিয়েই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব বা কণ্ঠরোধ করা শুরু হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চেয়েও অভিযোগের আঙুল বেশি ওঠে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কোনও কিছু না-হয়েও সব কিছু হয়ে ওঠা সঞ্জয় গান্ধীর দিকে। (World Press Freedom Day)
সিদ্ধার্থশঙ্করকে খোদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বাহাদুর শাহ জ়াফর মার্গে বিদ্যুৎ থাকবে
জরুরি অবস্থার অন্যতম প্রধান কারিগর, ইন্দিরা-ঘনিষ্ঠ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল তাবড় সংবাদিকদের অনেকের। সিদ্ধার্থশঙ্করকে খোদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বাহাদুর শাহ জ়াফর মার্গে বিদ্যুৎ থাকবে। তা সত্ত্বেও সংবাদপত্র অফিসগুলোয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর ক্ষুব্ধ সিদ্ধার্থশঙ্কর প্রশ্ন করেন, ‘এ সব কী অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার চলছে? এর মানে কী?’ সঞ্জয় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ‘এটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনারা জানেন না, দেশটা কী ভাবে চালাতে হয়।’ (World Press Freedom Day)
বিদ্যে কমলভোজনে:ইন্দ্রনাথ রুদ্র
ভারতে আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস বা ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে উদযাপনের সময়ে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ মনে পড়তে বাধ্য। তবে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার সময়ে ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে’ নামে কিছু ছিল না। এই দিনটা পালিত হয়ে আসছে ১৯৯৪-এর ৩ মে থেকে। ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৩-এর ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ বা জেনারেল অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক বছরের ৩ মে-কে ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে’ হিসেবে উদযাপনের কথা ঘোষণা করেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণা অনুযায়ী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার তাৎপর্য এবং গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও মানবাধিকারের রক্ষক হিসেবে সাংবাদিকতার গুরুত্বের কথা স্মরণ করাবে প্রতি বছর এই দিনটির উদযাপন। কিন্তু বেছে বেছে ৩ মে তারিখটিই কেন? ১৯৯১ সালের ৩ মে নামিবিয়ার রাজধানী উইন্ডহোকেই হয়েছিল আফ্রিকান সাংবাদিকদের ঘোষণা, যা বিখ্যাত ‘উইন্ডহোক ডিক্লারেশন’ নামে পরিচিত। ওই ঘোষণাকে দুনিয়া জুড়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং মুক্ত ও স্বাধীন সাংবাদিকতা ভাবনার ক্ষেত্রে মানদণ্ড ধরা হয়। (World Press Freedom Day)
এখন কেবল সংবাদপত্র নয়, নিউজ় চ্যানেল, রেডিয়ো, নিউজ় পোর্টাল এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমও হয়ে উঠেছে সংবাদের উৎস। তাই, ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে’-র নাম পাল্টে ‘ওয়ার্ল্ড মিডিয়া ডে’ রাখলে বোধহয় ঠিক হবে।
কিন্তু সংবাদপত্র বা সার্বিকভাবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা মানেটা কী? এখন তো কেবল সংবাদপত্র নয়, নিউজ় চ্যানেল, রেডিয়ো, নিউজ় পোর্টাল এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমও হয়ে উঠেছে সংবাদের উৎস। তাই, ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে’-র নাম পাল্টে ‘ওয়ার্ল্ড মিডিয়া ডে’ রাখলে বোধহয় ঠিক হবে। (World Press Freedom Day)

কোনও কারিকুরি বা ভাষার চাতুর্য না-করে সহজ ভাবে বলা যায়, যেটা সত্য, যেটা ঘটনা, সেটা ঠিকভাবে, কোনওরকম বিকৃত না-করে এবং কারও প্রভাবে প্রভাবিত না-হয়ে পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরাই সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা। কিন্তু এখন চারপাশে যা চলছে, তাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার এহেন সংজ্ঞাকে নেহাতই মশকরা বলে মনে হতে পারে অনেকেরই। প্রতিটি মিডিয়া হাউজ়েরই রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সম্পাদকীয় নীতি, যা কখনও স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান আবার কখনও সূক্ষ্মতায় ঢাকা, যা কখনও রাজনৈতিক কারণে তৈরি আবার কখনও ব্যবসায়িক স্বার্থে চালিত। সেই সম্পাদকীয় নীতি প্রতিফলিত হয় সংবাদ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে, সংবাদকে বেশি গুরুত্ব বা কম গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে। কোনও ঘটনাকে কীভাবে দেখা হচ্ছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এমনও হয়েছে যে, গোটা কলকাতা ঘুরে সার্বিক বনধ পালিত হচ্ছে দেখে এসেও সাংবাদিক সেটা লিখতে পারেননি। তাঁকে ফলাও করে লিখতে হয়েছে, যে গুটি কতক দোকানপাট ও অফিস খোলা ছিল, তার কথা। প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাংবাদিককে বোঝাতে হয়েছে যে, বনধ ব্যর্থ। কারণ, তাঁর সম্পাদক ও সম্পাদকীয় নীতির চাহিদা ছিল সেরকমই। (World Press Freedom Day)
বোরোলির অলিগলি:ইন্দ্রনাথ রুদ্র
তবে অবস্থা বুঝে সেই সম্পাদকীয় নীতির পরিবর্তনও ঘটানো হয় সময়ে সময়ে। কী রকম? একবার একটি শিল্পবাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে কোনও রাজ্য সরকারের গোলমাল পেকেছে। বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্রের মালিক-সম্পাদক সেই ব্যসায়ীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তাঁর সংবাদপত্রগুলো এবং টিভি চ্যানেল সেই ব্যবসায়িক সংস্থার কাছ থেকে বিপুল টাকার বিজ্ঞাপন পায়। মালিক-সম্পাদক সেই ব্যবসায়িক সংস্থা ও রাজ্য সরকারের মধ্যে মিটমাট করানোর চেষ্টা করতে, মধ্যস্থতা করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী অনড়, উল্টে তাঁর কাছে দু’কথা শুনতে হল মালিক-সম্পাদককে। ঠিক তার পরেই তাঁর সব কাগজ ও চ্যানেল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগল। অথচ তারাই তার আগে, সাত-আট মাস ধরে রাজ্য সরকারের কোনও খুঁত দেখতেই পাচ্ছিল না। সরকার-বিরোধী নীতির জেরে আবার ওই মিডিয়া হাউজ়ে সরকারি বিজ্ঞাপন আসা বন্ধ হয়ে গেল। (World Press Freedom Day)
পাঠক বা দর্শক কী চাইছেন, সেটা ঠাহর করেই সংবাদ পরিবেশন করতে বাধ্য হয় বহু সংবাদপত্র ও নিউজ় চ্যানেল।
পাঠক বা দর্শকের মনোভাব বুঝেও সম্পাদকীয় লাইন পরিবর্তনের নজির কম নেই। বিজ্ঞাপন লক্ষ্মী এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সংবাদপত্রের সার্কুলেশন কমে গেলে, চ্যানেলের টিআরপি পড়ে গেলে, নিউজ় পোর্টালের ভিউয়ার ও সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা গোত্তা খেয়ে পড়লে, পড়তেই থাকলে বিজ্ঞাপন কিন্তু একটা সময়ের পর আসবে না। তখন পাঠক বা দর্শক কী চাইছেন, সেটা ঠাহর করেই সংবাদ পরিবেশন করতে বাধ্য হয় বহু সংবাদপত্র ও নিউজ় চ্যানেল। (World Press Freedom Day)
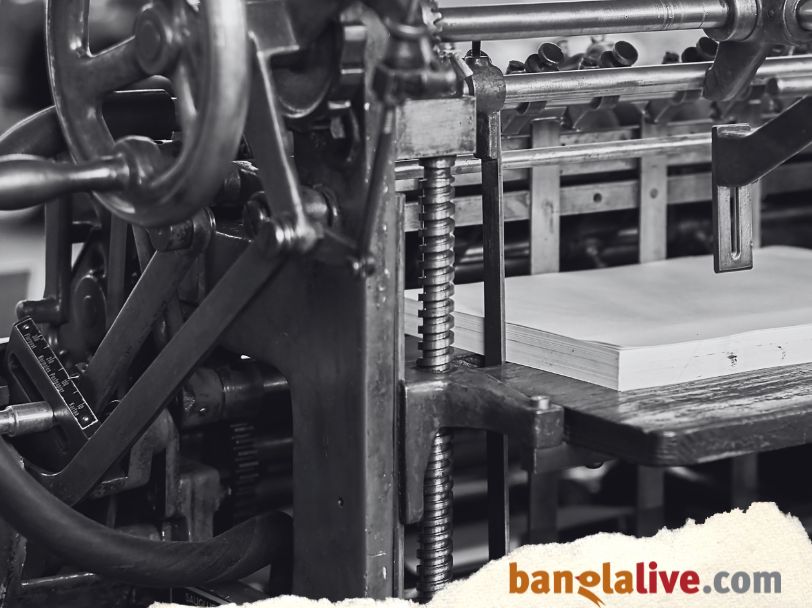
কেবল জরুরি অবস্থার সময়েই সংবাদপত্রে সত্য লেখা যায়নি, তা কিন্তু নয়। এই যেমন এক প্রবীণ সাংবাদিক সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর আত্মকথায় এ যাবৎ চাপা পড়ে থাকা দু’টো ঘটনা সামনে এনেছেন। প্রথম ঘটনাটা ১৯৭০ সালের। বর্ধমানে সাঁইবাড়ি কমিশন চলাকালীন, সাংবাদিকের সঙ্গে একই গাড়িতে বসে থাকা মামলার প্রধান সাক্ষীকে খুন হতে দেখে, খুনির রাজনৈতিক পরিচয় জেনেও সাংবাদিক সত্যটা লিখতে পারেননি। খুনি যে রাজনৈতিক দলের, সেই দল সরাসরি হুমকি দিয়েছিল সাংবাদিকের অফিস কর্তৃপক্ষকে। দ্বিতীয় ঘটনা ১৯৭৬ সালের। লিগের বড় ম্যাচ শুরু হওয়ার ১৭ সেকেন্ডের মাথায় আকবরের দেওয়া গোলে মোহন বাগান হারিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গলকে। তবে খেলা শেষ হওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে যান আকবর। চিকিৎসায় ধরা পড়ে যে, আকবরকে খেলার আগে ডোপ করানো হয়েছিল অর্থাৎ খাওয়ানো হয়েছিল নিষিদ্ধ উত্তেজক ওষুধ— এখনকার পরিভাষায় পারফরম্যান্স এনহান্সিং ড্রাগ। সেই সত্যটাও তখন সামনে আনা যায়নি। কারণ, সাংবাদিকের কর্মস্থল সেই সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল মোহন বাগান ক্লাবের। (World Press Freedom Day)
সত্য ধামাচাপা দেওয়ার এ সব ঘটনা অবশ্য সার্বিকভাবে কোনও সরকারি নিষেধাজ্ঞার পরিণাম নয়। জরুরি অবস্থার সঙ্গে এগুলোর তফাত এখানেই। (World Press Freedom Day)
তাঁদের বক্তব্য ছিল, ‘হাতে কলম আছে বলে যে কোনও কারও বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তা-ই লেখা ও ছাপা যায় না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই জরুরি, তা বলে স্বাধীনতার অপব্যবহার করাও উচিত নয়।’
এখন আবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষকে এমন আক্রমণ করা হচ্ছে, যা কিন্তু আখেরে তাঁর সম্মানহানি ছাড়া কিছু নয়। একটি রাজনৈতিক দলের নেতা বা নেত্রী অন্য কোনও দলের নেতা বা নেত্রীকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করছেন বা মন্তব্য করছেন শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। একটা সময়ে সংবাদমাধ্যমগুলো এসব জিনিসকে খবর বলেই মনে করত না। কিন্তু এখন সে সবই খবর। ডাল-ভাত-মাছের ঝোল সযত্নে পরিহার করে তার পরিবর্তে চানাচুর-ফুচকা-ডালমুটকে মেজর মিল-এর স্টেপল ফুড করার মতো। ১৯৮৮ সালের অগস্ট মাসে কেন্দ্রের তৎকালীন সরকার, রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকার ‘মানহানি বিল’ এনেছিল, যা লোকসভায় পাশও হয়ে যায়। সেই বিলের উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষের মানহানি ঠেকানো। অপরাধ প্রমাণ হলে এক মাস থেকে দু’বছর পর্যন্ত জেলের সংস্থান ছিল ওই বিলে। সেই সময়ে কোনও কোনও সাংবাদিক কিন্তু ওই বিলকে সমর্থনও করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ‘হাতে কলম আছে বলে যে কোনও কারও বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তা-ই লেখা ও ছাপা যায় না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই জরুরি, তা বলে স্বাধীনতার অপব্যবহার করাও উচিত নয়।’ তবে সেই সাংবাদিকরা ছিলেন সংখ্যালঘু। সার্বিকভাবে গোটা দেশের প্রায় সমস্ত সংবাদমাধ্যম এবং বিরোধী দলগুলো ওই বিলকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধের উদ্যোগ হিসেবেই দেখে তার বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে সরব হয়েছিল। মানহানি বিলের বিরুদ্ধে ১৯৮৮-র ৫ অগস্ট ইন্ডিয়া গেট থেকে দিল্লি বোট ক্লাব পর্যন্ত একটি বিশাল মিছিল বেরোয়। প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার শেষমেশ বিলটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। তবে এই সময়ে দাঁড়িয়ে মনে হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার আটকাতে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মানহানির বিলের মতো কিছুর। (World Press Freedom Day)

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এখন সম্পূর্ণ অন্য রকম একটা চ্যালেঞ্জের কথা স্বীকার করছে রাষ্ট্রপুঞ্জও। তা হল, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের আকছার ব্যবহারে সত্য ও অসত্যর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চ্যালেঞ্জ। এআইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, সেটা যুগধর্ম, কিন্তু সেটা দিয়ে মিথ্যে কিছু ছড়ানো হলে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর। বছর কয়েক আগে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল। একটি হাতি ও সিংহী পাশাপাশি হেঁটে আসছে এবং সিংহশাবকের যাতে হাঁটতে কষ্ট না-হয়, তার জন্য তাকে শুঁড়ে তুলে হাতি হাঁটছে। প্রাণিজগতে কী রকম প্রশংসনীয় সম্প্রীতি, মানুষের শেখা উচিত— এ সব কথা প্রচার করা হয়েছিল ছবিটির মাধ্যমে। ছবিটি কিন্তু তৈরি করেছিল এআই— ফোটোগ্রাফ ছিল না সেটি। ছবির উৎসব যে ওয়েবসাইট, সেটা যে ফেক, ঝট করে তা বোঝার উপায় ছিল না। কারণ, বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত আসল ওয়েবসাইটের কেবল একটি অক্ষর পাল্টে ফেক ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছিল। কোনও কোনও সংবাদমাধ্যম সেই ছবি প্রকাশ করেছিল, পরে তারা ভুল স্বীকার করে নেয়। (World Press Freedom Day)
এআইয়ের তৈরি অনলাইন হেটস্পিচ যেভাবে বাড়ছে ও ছড়াচ্ছে, তাতে তো আগুন জ্বলে যেতে পারে। এবং জ্বলছে না বা ইতিমধ্যেই জ্বলেনি, তা কিন্তু নয়।
তা-ও তো এটা একরকম নিরীহ বিষয়। এআইয়ের তৈরি অনলাইন হেটস্পিচ যেভাবে বাড়ছে ও ছড়াচ্ছে, তাতে তো আগুন জ্বলে যেতে পারে। এবং জ্বলছে না বা ইতিমধ্যেই জ্বলেনি, তা কিন্তু নয়। (World Press Freedom Day)
সব মিলিয়ে, এ বছরের ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে’-র চিন্তাভাবনা এবং দুশ্চিন্তা ও চ্যালেঞ্জের বিষয় অনেক কিছু হলেও সে সবের কেন্দ্রবিন্দুতে এআই। প্রধান সত্য এটাই। (World Press Freedom Day)
খাওয়ার জন্য বাঁচেন। চোখ বেঁধে খেতে দিলেও রুই ও কাতলা মাছের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন অনায়াসে। আর চোখ খোলা থাকলে? মুখে না-তুলে রান্না করা খাবারের রং দেখেই বুঝতে পারেন, নুন বেশি বয়েছে নাকি কম।