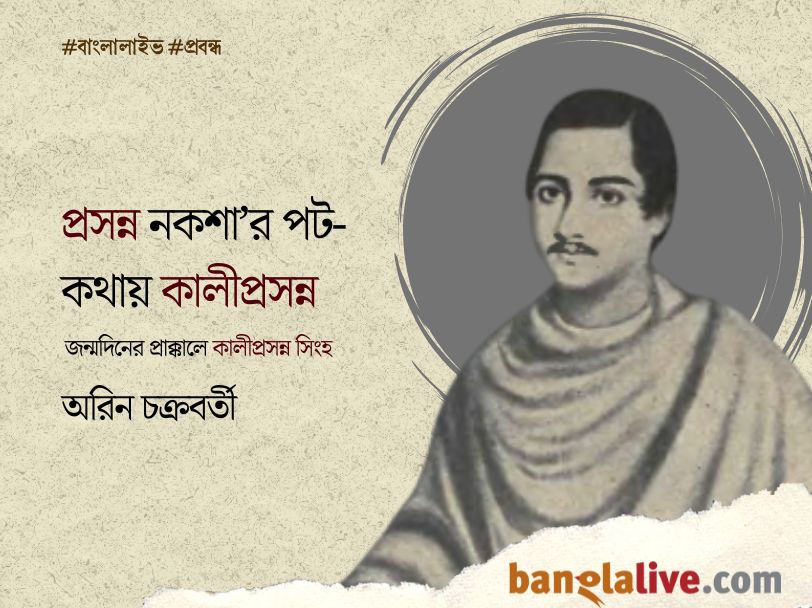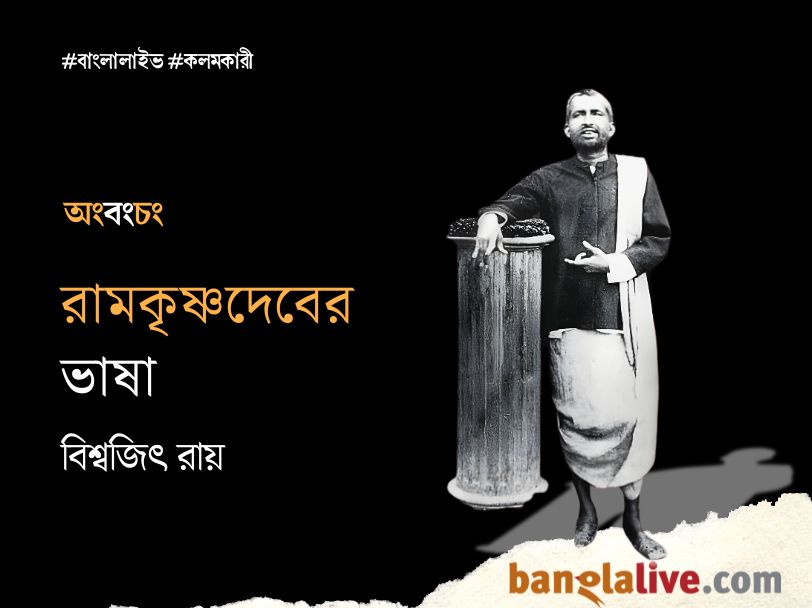দমনপুর যেন একটা সীমান্ত। নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে আরণ্যক জীবনের। একদিকে শহর আলিপুদুয়ার। অন্য তিনদিকে শুধুই সবুজ। জনবসত কিছু আছে বটে, তাকে ছাপিয়ে আছে গাছ, চা-বাগান, বন। আর আছে নোনাই। ক্ষীণকায়া এক নদী। দমনপুর জঙ্গলের মাঝে নীরবে বয়ে যায়। কালজানি, তোর্সা, জলঢাকার মতো তার কৌলীন্য নেই। কিন্তু জীববৈচিত্র্য ধারণ করে আছে নোনাই। এই জলধারা পার হওয়া হাতির বাঁয় পায় কি খেল। দু’কদম হাঁটলেই নদী পার হওয়া যায়। এ নদীর এপার-ওপার করা তাই হাতির কাছে খেলার শামিল। অন্যদিকে, ডিমা যেন নোনাইয়ের সহোদরা। দুই লাফে পার হতে পারে দামাল কিশোর।
ইচ্ছে হলে তাই হাতির যখন তখন অনায়াস পারাপার। নোনাই-ডিমা ডিঙিয়ে হাতি আসে যায়। তবে এখনও কোনওদিন আলিপুরদুয়ারের নাগরিক জীবনে হানাদারির রেকর্ড নেই। অথচ দমনপুর হাটটা পার হলেই তো রেল কলোনি। মানুষ,আলো, রাজপথ, বাজার, সিনেমাহল, শপিংমল। হাতির তাতে আকর্ষণ নেই। বড়জোর দমনপুরে রানা বসুর বাদল-বীনা রিসর্টের পিছনের গাছটায় গা ঘষে চলে যায় হাতি। জানালা দিয়ে দেখা সেই দৃশ্যে পর্যটকের ভয়মিশ্রিত মনোরঞ্জন হয় বটে, হাতিরও বিনোদন হয়। এ তল্লাটে কাঠের উঁচু পাটাতনের বাড়ি তো বিশেষ আর নেই, যা দেখে অভ্যস্ত ছিল হাতির চোখ। ওরকম বাড়িকে যেন নিজের মনে হয় হাতির। এখন অবশ্য সব কংক্রিট।
সংবাদপত্রে টেলিভিশনে হাতি মাঝে মাঝে খবর হয়। ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর জন্য অথবা হাতি-মানুষ সংঘাতের জন্য। প্রায়ই খবরে আসে হাতির দৌরাত্ম্য খুব বেড়েছে। তারা মানুষ মেরে ফেলছে পায়ে পিষে, কিংবা শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মেরে। মাঠের পাকা ধান-ভুট্টা খেয়ে সর্বস্বান্ত করছে বন-লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের। দেখে শুনে মনে হবে, হাতি আসলে মূর্তিমান যম। সাক্ষাৎ শয়তান। কিন্তু আমরা বাইরে থেকে ভাবলে কী হবে, এ তল্লাটে বাস্তবে ভগবানের আর এক অবতার হাতি। মহাকাল! গণেশ বাবা। হাতি মরে পড়ে থাকলেও লাশের ওপর ফুল ছেটানো এখানকার বাসিন্দাদের রীতি। শুধু ভয়ে নয়। ভক্তিতে।
ভুটানঘাট লাগোয়া কাইজালি বস্তি হোক, কিংবা জলদাপাড়ার পাশে মাদারিহাট বা ধৈধৈ ঘাট, স্থানীয়দের পাকা ফসলে কার্যত মই দেয় হাতি। কখনও একা বা দোকা আবার কখনও পালে। দল বেঁধে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, এটুকু গণেশ বাবার প্রাপ্য। জঙ্গলের পাশে থাকব, অথচ মহাকালবাবাকে লেভি দেব না, তা আবার হয় নাকি?

ডুয়ার্স-তরাইয়ের এ তল্লাট, অসম সীমানার সংকোশ নদী ও নেপাল সীমান্তের মেচি নদীর মাঝের এই ভূভাগ তো হাতিরই আপন দেশ। মানুষ এখানে অনুপ্রবেশ করেছে। একসময় সাহেবরা চা-বাগান বানানোর জন্য শ্রমিকের কাজ করাতে রাঁচি, ছোটনাগপুর থেকে আড়কাঠি লাগিয়ে ওরাওঁ-মুণ্ডা,-খরিয়া-বড়াইক-মহালি-নাগেশিয়া-লোহারদের নিয়ে এসেছিল। দেশভাগের কারণে পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু স্রোত আছড়ে পড়েছিল এখানে। স্রোত না হলেও সেই আসার বিরাম নেই এখনও। আবার নেপাল থেকেও বহু লোক আসেন। এখানেই থেকে যান। আদিম অধিবাসী বোরো-রাভা-টোটোরা তো আছেনই। এত লোককে জায়গা দিতে গেলে যে কারও জমিজিরেত চলে যায়। হাতিরও গেছে। জমিজিরেত গেলে আপনার, আমারও মাথাগরম হয়। হাতির দোষ কী? কারও হাত-পা ছড়িয়ে থাকার পরিসর কেড়ে নিলে সে তো ক্রুদ্ধ হবেই! তবে মহাকালবাবা কিন্তু শুধু ক্রুদ্ধ হন না, মানুষকে আগলেও রাখেন!
আশির দশকের শেষের দিকের একটা ঘটনা বলি। হাতি কী ভাবে এক শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছিল। জলদাপাড়া লাগোয়া উত্তর মাদারিহাট গ্রামে বিকেল বিকেল এক বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল বিশালকায় এক হাতি। ও অঞ্চলে এটা নিয়মিত। স্বাভাবিক ঘটনাই বলা চলে। এরকম হলে প্রচলিত প্রথা হল চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ওই পরিবারের গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রী তাই করেছিলেন। কোলের শিশুটিকে নিয়ে ছুট লাগিয়েছিলেন দু’জনে। ছুট ছুট ছুট। প্রাণ হাতে করে। পিছনে ছুটে আসছে দশাসই মূর্তিমান। দম্পতির লক্ষ্য, কোনওক্রমে জঙ্গলের কোনও গাছে উঠে হাতির নাগাল এড়ানো। এই কৌশলে যে হাতিকে এড়ানো যাবে, তেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।
শিশু কোলে দৌড়চ্ছেন মহিলা। আগে আগে তাঁর স্বামী। দৌড়চ্ছে গজরাজও। কিছুটা পিছনে। কিন্তু ধরে ফেলতে কতক্ষণ? অমন বিশাল বপু হলে কী হবে, হাতির সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় মানুষের হার অবধারিত। মৃত্যুভয়ে প্রাণপনে দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন মহিলা। হাত থেকে ছিটকে গেল কোলের শিশু। কোনওরকমে মহিলা উঠলেন বটে, কিন্তু শিশুকে আর হাত বাড়িয়ে তুলতে পারলেন না। হাতি কাছাকাছি এসে পড়েছে। নিজের প্রাণের দুর্ভাবনায় এরকম সময়ে হয়তো সন্তানের অগ্রাধিকার আর মনে আসে না। জীবন-মৃত্যু সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো এটাই স্বাভাবিক।
দম্পতি যতক্ষণে জঙ্গলের কাছাকাছি ততক্ষণে শুঁড় উঁচিয়ে গজরাজ পৌঁছে গিয়েছে যেখানে শিশুটি পড়ে গিয়ে আছাড়িপিছাড়ি কাঁদছে সেইখানে। মৃত্যু চেতনা তার নেই বটে। কিন্তু মা হারিয়ে গেলে শিশু বিপন্ন বোধ করবেই। হাতি দৌড়তে দৌড়তে এসে দাঁড়িয়ে গেল শিশুর কাছে। শিশু তখন কাঁদতে কাঁদতে ধুলোমাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর ইষ্টনাম জপছেন বাবা-মা। নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ায় তাঁদের তখন বোধ ফিরেছে। উৎকণ্ঠায় দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। এই বুঝি পায়ে পিষে সন্তানের ভবলীলা সাঙ্গ করে হাতি। নাহলে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় তো অবধারিত। নিজেরা প্রাণে বাঁচলেও আতঙ্কে তাঁরা গাছে ওঠার কথা ভুলে ঝোপের আড়াল থেকে নজর রাখছেন সন্তানের দিকে। এরপর যা হল, সেটাই হাতি-মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চরম নিদর্শন, যেমন ঘটনা অনেক লুকিয়ে আছে এই এলাকায়। হাতি শিশুকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে তুলল বটে, কিন্তু আছাড় মারল না। বরং আলতো করে শুঁড়ে বসিয়ে গজেন্দ্রগমনে রওনা দিল দম্পতির বাড়ির দিকে।
পিছন পিছন দূরত্ব রেখে শিশুর বাপ-মা। তখন আর হাতির বৃংহন নেই। বরং যেন শান্ত-সৌম্য রূপ। শিশুকে শুঁড়ে নিয়ে হাতি পৌঁছল বাড়িতে। দাওয়ায় বসিয়ে দিল আলতো করে। তারপর যখন কাছাকাছি মানুষের উপস্থিতি টের পেল, তখন নীরবে জঙ্গলের পথ ধরল। ততক্ষণে হাতি বোধহয় বুঝে গিয়েছিল, আশপাশে শিশুর স্বজনরা এসে গিয়েছে। ওর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না। তাই নিশ্চিন্তে সে জঙ্গলে ফিরে গেল। সেই রাতেই আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শিশুটিকে। খবর পেয়ে পেশাগত ঔৎসুক্যে আমিও হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলাম। শুঁড়ে পেঁচিয়ে থাকায় শিশুটির চামড়া লাল লাল হয়ে উঠেছিল মাত্র, কিন্তু সারা দেহে কোথাও একটিও ক্ষতচিহ্ন ছিল না!
পরম মমতায় শিশুটিকে সযত্নে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে সেই প্রাণী যাকে দেখলে ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়। সাধে কী আর হাতিকে আদি বাসিন্দারা দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করে! হাতির অপত্য স্নেহের আরও একটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে এখনও টাটকা। ঘটনাস্থল কৈলাশপুর চা বাগান। জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তির কাছে। সময়টা আশির দশকের শুরু। বাউণ্ডুলে জীবনে ঘুরতে ঘুরতে আমি সেদিন সকালে ক্রান্তি পৌঁছেছি। বাস থেকে নেমেই শুনলাম চায়ের দোকানে জোর আলোচনা। আগের দিন রাতে কৈলাশপুরে দুই শিশুর জীবন বাঁচিয়েছে দুই হাতি। দৌড়ে গেলাম কৈলাশপুরে। দেখলাম, শিশু দুটি সম্পর্কে দুই ভাই।

আগের দিন সন্ধ্যায় চা-শ্রমিক মায়ের সঙ্গে হাট থেকে বাড়ি ফিরছিল তারা। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। গাছে ছাওয়া চা-বাগানের পথ আঁধার। শিশু দু’টির মায়ের হাতে ছিল লালটিন। সাদরিভাষী চা-শ্রমিকরা হ্যারিকেনকে লালটিন বলেন। সেই লালটিনের আলোয় ওই মহিলা দেখলেন, তাঁদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে বিরাট সাইজের দুই মহাকাল। অতঃপর চিৎকার এবং দৌড়। পড়ে রইল লালটিন। হারিয়ে গেল দুই বালক। কোনওরকমে শ্রমিক মহল্লায় পৌঁছে কাঁদতে কাঁদতে মহিলা সবিস্তারে জানালেন সব। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে খুঁজতে বের হল দু’ভাইকে। কিন্তু সারা রাত ঘুরেও না পাওয়া গেল হাতিদের, না মিলল দুই ভাইয়ের হদিস।
উৎকণ্ঠায় রাত জাগল গোটা কৈলাশপুর চা বাগানের লেবার লাইন। ভোরের আলো ফোটার পর যে দৃশ্য দেখল তারা, তা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। সবাই ভেবেছিল, হয়তো এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে থাকবে দুই শিশুর থ্যাঁতলানো, দলাপাকানো দেহ। তার বদলে সকলের চোখে পড়ল এক অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য। দুই ভাই চা-বাগানের ফাঁকে কাদা মাখা গায়ে পাশাপাশি বসে। এবং অক্ষত। ভয়ের লেশমাত্র নেই অবয়বে। আর ওদের মাথার ওপর দিয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দুই হাতি।
কিন্তু বাচ্চাদের পেটের তলায় বসিয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকার কী কারণ? কারণ হল, বৃষ্টিতে ভিজে যেন ওদের কষ্ট না হয়। সেই জন্য ওই ভাবে নিজেদের শরীর দিয়ে ছাতা তৈরি করে পরম অপত্য স্নেহে দাঁড়িয়ে ছিল দুই হাতি। লোকজনের সাড়া পেয়ে, শিশু দুটি নিরাপদ বুঝে ধীরে ধীরে হাতিরা মিলিয়ে যায় লাগোয়া জঙ্গলে।
হাতিরা কখনও কখনও মানুষ মেরে ফেলে বটে, কিন্তু মানুষের প্রতিবেশী হিসাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতেই ওদের বিশ্বাস। হক কথাটা বলেন মাহাতি মুণ্ডা। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া পানবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। সম্প্রতি তাঁর কথা লিখেছেন আমার স্নেহভাজন সাংবাদিক রাজু সাহা। লেখাটা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। রাজুকে মাহাতি বলেছেন ‘বাবুকে (এ অঞ্চলে আদিবাসীরা হাতিকে বাবু বলেও সম্বোধন করেন) আমরা দেখলে বাবুও আমাদের দেখে। আমরা ওদের বাসস্থান কেড়ে নিয়েছি, খাবারের বনভূমি ধ্বংস করেছি। ওরা তো রেগে যাবেই। খাবার ছিনিয়ে নিতে আসে ওই কারণেই।’ কিন্তু মাহাতির কোনও ক্ষতি করে না তাঁর আদরের বাবুরা। তিনি ধান হোক, ভুট্টা হোক কিংবা গাছের কাঁঠাল, পুরোটা ঘরে তোলেন না। কিছুটা রেখে দেন বাবুদের জন্য। ওরা সময় মতো এসে খেয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের বন ও বনাঞ্চল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা একে তামাশার ছলে বলেন, হাতির প্রাপ্য লেভি রেখে দেওয়া। লেভি পেলে খুশি থাকে হাতি। ক্ষতি দূরের কথা, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।
কর্মসূত্রে কলকাতায় দীর্ঘদিন বসবাসের পর থিতু শিলিগুড়ি শহরে। নিজেকে ডুয়ার্সের সন্তান বলতে ভালোবাসেন। গ্রামের আদি বাড়ির একপাশে বোড়ো আদিবাসী বসত, অন্যপাশে সাঁওতাল মহল্লা। বক্সার রায়ডাক জঙ্গল গ্রামের কাছেই। শৈশব, কৈশোরে বাড়ির উঠোনে চলে আসতে দেখেছেন হাতি, চিতাবাঘ, হরিণ। জঙ্গলে কুল কুড়োতে কুড়োতে আর নদীতে ঝাঁপিয়ে বড় হওয়া। প্রকৃতি আর উপজাতিরাই প্রতিবেশী। যৌবনে এই পরিবেশে কিছুকাল বাউন্ডুলে জীবনের পর সিদ্ধান্ত, সাংবাদিকতা ছাড়া আর কোন কাজ নয়।