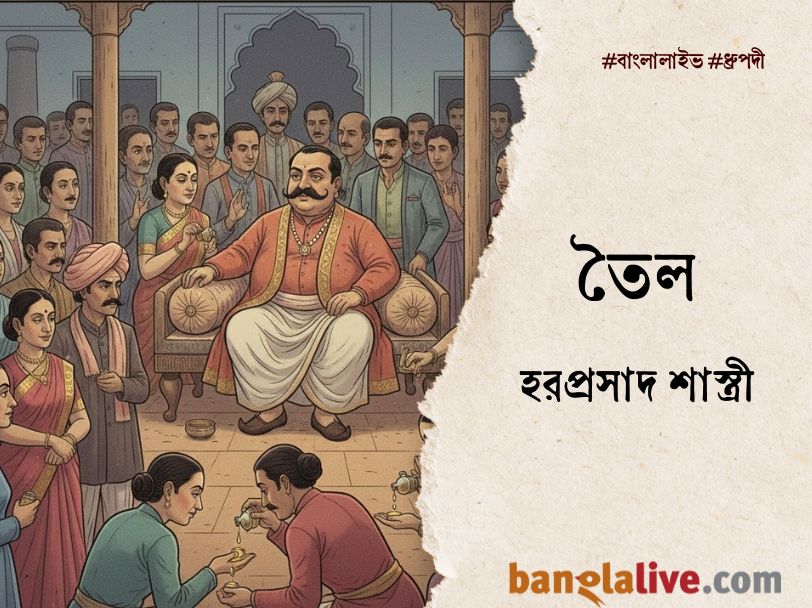চায়ের প্রচারে বাংলায় যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত তা এরকম-
যাহাতে নাহি মাদকতা দোষ,
কিন্তু পান করে চিত্ত পরিতোষ।
বিজ্ঞাপনে লেখা হত: ইহা নিম্নলিখিত রোগ হইতে রক্ষা করে, ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয়, প্লেগ ইত্যাদি। তাছাড়া বাংলায় এসে রামসুক তেওয়ারির চা-পানের নেশা করে কী দুর্দশা হয়েছিল, তার বর্ণনা তো কুমুদরঞ্জন মল্লিক দিয়ে গিয়েছেন-
“বাংলায় কাটাইয়া গোটা দুই বর্ষা
রামসুক তেওয়ারীর পরকাল ফর্সা।
প্রাতে আর সন্ধ্যায় চা ধরেছে নিত্য
আজ বাড়ে অম্বল কাল বাড়ে পিত্ত।”
রোগ প্রতিরোধের যে বিজ্ঞাপন, তার একেবারে বিপরীত চিত্র। রামসুক অবশ্য চা বাগানের শ্রমিক হয়ে বাংলায় আসেনি, সে এ মুলুকে এসে চা-খোর হয়ে পড়েছিল কেবল। তাছাড়া, সে ছিল পুরুষমানুষ। কিন্তু যে সমস্ত মহিলা চা-বাগানে শ্রমিক হিসেবে এসে পড়েছিলেন, তাঁদের গল্প ছিল আরও ভয়াবহ। তাঁদের জীবন জন্ম জন্মান্তরের দুষ্টচক্রে ছিল বাঁধা। চা-বাগানে চা গাছ রক্ষনাবেক্ষন, পরিচর্যা এবং সবচেয়ে জরুরি কাজ– চা গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ, নারী শ্রমিকদের। পাতা তোলার কাজ তাঁরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি যত্নের সঙ্গে করতে পারেন, তাঁদের হাতের আঙুলের গঠনই এরকম। চা পাতা পরিবহন, ওজন সংক্রান্ত কাজ, কারখানায় উৎপাদনের কাজ, সাহেব ও বাবুদের বাড়ির মালির কাজ ইত্যাদি কাজ পুরুষ শ্রমিকের জন্য।
মহিলা শ্রমিকরাই বস্তুত চা শিল্পের মেরুদণ্ড। অথচ চা-বাগান সৃষ্টির প্রথম লগ্নে এঁরাই ছিলেন সবচেয়ে অত্যাচারিত। ইংরেজদের ভারতীয় সম্পদ শোষণের দুটি উপায়ের মধ্যে প্রথমটি ছিল কল-কারখানায় (তখন মূলত টেক্সটাইল) শোষণ, আর দ্বিতীয়টি হল প্ল্যান্টেশন। প্ল্যান্টেশনের প্রথম পর্বে ছিল নীল চাষ। তারপর চা ও কফি, শেষে রাবার। আমাদের উৎসাহ চা শিল্পে।

১৮১৫ সাল নাগাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চায়ের ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি লাভ করছিল- তাদেরই ছিল একচেটিয়া কারবার। ১৯৩৩ সাল নাগাদ তাদের এই একচেটিয়া কারবার আর স্থায়ী হল না। এরপরেই ভারতে চা উৎপাদনের কথা ইংরেজ শাসকেরা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে থাকে। ভারতে চা ব্যবসায় মূলত উদ্যোগ নিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্তারা। এদের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলি ইংল্যান্ডে রেজিস্ট্রিকৃত হলেও কলকাতায় এইসব কোম্পানির এজেন্টরা উপস্থিত থাকত। প্রথম দিকে তো, বিশেষত আসামে, শ্রমিকদের অবস্থা ছিল দাস প্রথাভুক্ত নির্যাতিত মানুষের মতো। তখন অত্যাচারের চরম সীমায় পৌঁছেও কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাবার উপায়টুকুও তাদের ছিল না। কেননা পালিয়ে যেতে গেলে তাদের বেত্রাঘাত, এমনকী গ্রেপ্তার করার অধিকারও মালিকের ছিল।
১৯২০ সালে সিলেটর শ্রমিকেরা এই দুঃসহ অবস্থা সইতে না পেরে ‘মুলুক চল’ এই নামে এক আন্দোলনের ডাক দেয়। তারপর জন্মভূমিতে ফেরার জন্যে তারা দলে দলে চা-বাগান ছেড়ে রওনা হয়। চাঁদপুরের ঘাটের কাছে পৌঁছোলে তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চলে। কিছু শ্রমিক মারা যায়, বাকিরা কর্মক্ষেত্র চা-বাগানে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।
চা-শিল্প শ্রমিক-নির্ভর। এই শিল্পে মুনাফা করতে গেলে দুটি সহজ পন্থা রয়েছে। এক, উৎপাদন খরচ কমাও এবং দুই, শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে যথাসম্ভব স্বল্প শ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন বাড়িয়ে নিয়ে চল। চা-বাগানে সারাবছর ধরে একই সংখ্যার শ্রমিক প্রয়োজন হয় না। ঋতু অনুসারে তা বাড়ে কমে। যেমন বর্ষা নামলে চা পাতা তোলার জন্য অনেক বেশি শ্রমিক প্রয়োজন হয়। নতুন পাতার আগমন মানেই এখুনি তা তুলে নিতে হবে, বিলম্ব চলবে না। বিলম্ব মানেই লোকসান। মন্দার সিজনে, যখন উৎপাদনের চাপ নেই, তখন যে পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তাদের নামই শুধু বেতনের খাতায় তোলা থাকে। তাদেরই শুধু মাইনে দিলে চলে। কিন্তু যখন চা গাছে পাতা গজাবার ধুম লাগে বর্ষায়, তখন বাকি শ্রমিক মিলবে কী করে?
সেটা খুব কঠিন কাজ না, কেননা শ্রমিকেরা তো চা-বাগানের মধ্যেই থাকে, কুলি লাইনে। তাই শ্রমিক পরিবারের উদ্বৃত্ত নারী-পুরুষদের মধ্যে থেকে অতিরিক্ত শ্রমিকের যোগান আসে। যে শ্রমিকেরা এই পাতা উদ্গমের রমরমার সময়ে কাজে যোগ দেয়, তারা কখনও স্থায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে পারে না। স্থায়ী শ্রমিকের মর্যাদা পেতে তাদের কখনও খুব জোরদার লড়াই-আন্দোলনেও যেতে দেখা যায়নি। মজা হল, স্থায়ী শ্রমিকেরাই চাইত না যে এরা স্থায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত হোক। কারণ, চা-বাগানে একজন চা-পাতা তোলায় নিয়োজিত শ্রমিককে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তুলতেই হয়। সেটা তোলার পর বাড়তি যা সে তুলতে পারবে, তার জন্যে সে পায় উদ্বৃত্ত মজুরি। সুতরাং অতিরিক্ত হাত যদি কাজ করে, তবে স্থায়ী শ্রমিকটির মজুরি কমে যায়। একারণে স্থায়ী শ্রকিকেরা চাইত না, পিক সিজনে নিয়োজিত শ্রমিকেরা স্থায়ী হোক।

তবে ঘোর বর্ষায় এই ভয় নেই। কেননা যে পরিমাণ পাতার উদ্গম তখন হয়, সামান্য পরিমান স্থায়ী শ্রমিকদের পক্ষে সেই চা-পাতা তুলে ফেলা অসম্ভব। অর্থাৎ পিক সিজনে অস্থায়ী শ্রমিকেরা স্থায়ী শ্রমিকদের উপার্জনে ভাগ বসাতে পারে না। কিন্তু এটা বোঝা গেল যে, স্থায়ী শ্রমিকদের সামনে এই অস্থায়ী শ্রমিকেরা সবসময়ই একটা ভীতির কারণ, যতই তারা নিজ পরিবারের মানুষ হোক না কেন।
স্বাধীনতার আগে চা-শ্রমিকদের বেতনের বিষয়ে সামঞ্জস্য এবং সাম্য থাকবে না এটা তো অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, বয়স ও লিঙ্গভেদে মজুরির হেরফের এবং কোনও ‘স্কেল অফ পে’ না থাকা। এইসব বিষয়গুলি স্বাধীনতার পরেও বজায় ছিল বহুদিন। স্বাধীন দেশের ‘ওয়েজ বোর্ড’ এ সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। এই যে বয়সভেদে কিংবা লিঙ্গভেদে মজুরির হেরফের, এককালে হয়তো এর পেছনে যুক্তি ছিল। পুরনো দিনে গাছ কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার করার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজ পুরুষদের করতে হত, তাই তাদের বেশি মজুরি পাওয়া খারাপ দেখাত না। কিন্তু পরে চা-শিল্পে যখন মহিলা শ্রমিকদের শ্রম অধিক জরুরি হয়ে পড়ল, যখন দেখা গেল যে চা পাতা তোলার কাজে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে এবং মোট শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি, তখনও তারা কম বেতন পেতে থাকল। ফলে সমান কাজে সমবেতন নীতি কিন্তু বজায় থাকল না। এই বৈষম্য বজায় ছিল ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। এই বিভাজন বজায় থাকলে একদিকে যেমন কোম্পানির মজুরির খাতায় অনেক টাকা বেঁচে যেত, তেমনি আবার শ্রমিকদের জোটবদ্ধ হওয়ার বিষয়টাও থাকত ঢিলেঢালা।
জোটবদ্ধ হওয়ার কথায় মনে হল, ডুয়ার্সের চা-শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ইতিহাস দু’এক কথায় বলা যেতে পারে। সেই কবে ১৮৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে চা-শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অথচ সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ শুরু হতে হতে প্রায় আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় এসে গিয়েছিল। আসলে চা-শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন অন্দোলন গড়ে ওঠার উপযুক্ত পরিবেশই এই দীর্ঘ সময় জুড়ে ছিল না। একে তো শ্রমিকদের পরিবারশুদ্ধ দূর দেশ থেকে টেনে এনে চা-বাগানের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাদের অন্যত্র আর কোথাও কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল না। চা-বাগানের বাইরে যাবার সুযোগ কিংবা অধিকারও ছিল না। তার উপর বাইরের কোনও মানুষকে চা-বাগানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। চৌকিদারদের নিরন্তর পাহারা ছিল। ফলে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে তারা নির্বাসিত হয়ে থাকতে বাধ্য হত।
তদুপরি শিক্ষার সঙ্গে তাদের কোনও সংযোগ ঘটেনি। নিরক্ষর এই মানুষদের মজুরি বা কাজের শর্ত নিয়ে দর কষাকষির অবস্থা ছিল না। সে সময়ে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো। তাছাড়া, ভৌগোলিক প্রেক্ষিতে ডুয়ার্স ছিল বহিঃপৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন। এই অবস্থায় পাওনাগন্ডা নিয়ে কোনও অসন্তোষ দেখা দিলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা মালিকদের পক্ষে কঠিন ছিল না। এদিকে দেশের প্রথম পর্বের ইংরেজি জানা উঁচুজাতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব কুলি-কামিনদের সমস্যায় খুব নাক গলাতে উৎসাহীও ছিলেন না। বাঙালি মালিকানাধীন চা-বাগানেও তাই কোনও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের দেখা মেলেনি।
চা-বাগানে সারাবছর ধরে একই সংখ্যার শ্রমিক প্রয়োজন হয় না। ঋতু অনুসারে তা বাড়ে কমে। যেমন বর্ষা নামলে চা পাতা তোলার জন্য অনেক বেশি শ্রমিক প্রয়োজন হয়। নতুন পাতার আগমন মানেই এখুনি তা তুলে নিতে হবে, বিলম্ব চলবে না। বিলম্ব মানেই লোকসান। মন্দার সিজনে, যখন উৎপাদনের চাপ নেই, তখন যে পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তাদের নামই শুধু বেতনের খাতায় তোলা থাকে। তাদেরই শুধু মাইনে দিলে চলে। কিন্তু যখন চা গাছে পাতা গজাবার ধুম লাগে বর্ষায়, তখন বাকি শ্রমিক মিলবে কী করে?
তাবলে অসন্তোষ একেবারে দানা বাঁধত না, এমন নয়। ১৮৯৫ সাল থেকে ডুয়ার্সের নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন শ্রমিক অসন্তোষের খবর পাওয়া যায়। ১৯০৩ সাল নাগাদ আলিপুরদুয়ারের আশেপাশের কয়েকটি চা-বাগানে শ্রমিকেরা মজুরি নিয়ে প্রতিবাদ করেছে। দলসিংপাড়ায় সাহেব-ম্যানেজার আক্রান্ত হয়েছে শ্রমিকদের হাতে। রেশনে অতিরিক্ত চালের দাবিতেও ১৯০৬ সালে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল শ্রমিকেরা। সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও উপজাতির শ্রমিকেরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তবে এইসব অন্দোলন কঠোর হাতেই মালিকেরা দমন করতে পেরেছিল।
১৯১৬ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, যা ‘টানা ভগৎ’ অন্দোলন হিসেবে খ্যাত। ডুয়ার্সের ওঁরাও উপজাতির মানুষেরা ভেবেছিল তাদের এই সীমাহীন দুর্দশার পেছনে রয়েছে কোন অশুভ আত্মা কিংবা ভূতপ্রেতের কারসাজি। তারা বিশ্বাস করত, কোনও ত্রাতা এসে তাদের এই কঠিন সময় থেকে উদ্ধার করবে। তারা স্বজাতির মানুষদের কাছে আবেদন রেখেছিল যে তারা যেন শুদ্ধ জীবনযাপন করে এবং অন্য কোনও জাতের অধীনে কুলি বা শ্রমিকের কাজ না করে।
আধুনিক অর্থে ট্রেড-ইউনিয়ন দার্জিলিং জেলায় তাদের কাজকর্ম শুরু করে ১৯৪৬ সাল নাগাদ। ১৯৪৬ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দার্জিলিং অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে সাম্যের ও স্বাধীনতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল, গঠিত হয়েছিল দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট টি গার্ডেন ওয়ারকার্স ইউনিয়ন। ১৯৪৬ সালে ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি, মজুরিবৃদ্ধি, স্বল্পমূল্যে রেশন ইত্যাদি দাবিতে হরতালের নোটিস দেওয়া হয়। শ্রমিক অধ্যুষিত দার্জিলিং অঞ্চল থেকে রতনলাল ব্রাহ্মিণের নির্বাচনে জয়লাভ জলপাইগুড়ির শ্রমিক আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। বেঙ্গল অসম রেল রোড ওয়ার্কারর্স ইউনিয়ন-এর কর্মীরাও ডুয়ার্সের চা-বাগানের শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিল।
*ছবি সৌজন্য: idronline, Indian Express, insidene.com
অপূর্ব দাশগুপ্ত 'পুরোগামী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের অবসরপাপ্ত বিশেষ রাজস্ব আধিকারিক।