মলুটী থেকে মল্লেশ্বর যেতে গিয়ে বেশ কিছুটা খারাপ রাস্তা। গাড়ির গতি কমে গেল। গুগল ম্যাপও ফেল করে যায় মাঝেমধ্যে। গ্রামের মধ্যে এক ওকে তাকে জিজ্ঞেস করে নিয়ে চলতে হয়। তার মধ্যে গাড়ির রিয়ার ভিউ মিররে সায়ন যা দেখল তা চমকে ওঠার মতোই। গাড়ি থামিয়ে সায়ন বাইরে এসে দেখল ছিদাম বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে আবারও তাদের লালগাড়ি ধাওয়া করেছে। কিছুতেই সঙ্গ ছাড়বে না তাহলে ছেলেটা!
“কী রে তুই?” বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে সীমা বলে ওঠে।
“ভাবলাম তুমরা এতক্ষণে ঠিক মল্লেশ্বরের দিকে যাচ্ছ নিশ্চয়ই। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।”
সায়ন ভাবল, দুটো বেশি পয়সা হাতে পেয়ে ছেলেটার বুঝি মল্লেশ্বর না দেখাতে পেরে গিল্ট ফিলিং হচ্ছে। তাই দৌড়ে দৌড়ে আবার এসেছে পেছন পেছন। একেই বলে ভ্যালুজ। নিশ্চয়ই ভালো বংশের ছেলে। শিক্ষাদীক্ষাও ভালো।
এদিকে কখন যে সম্ভ্রমের দূরের ‘আপনি’ ডাক থেকে অবলীলায় ছিদামের কাছের ‘তুমি’ হয়ে গেছে দু’পক্ষ তা টেরও পায়নি।
সীমার চোখে খুশির ঝলক। “আয়, আয়। তুই বরং সামনে বসে পড়” বলে নিজেই পেছনের সিটে গিয়ে বসে পড়ে সে। ড্রাইভার সায়নের পাশের সিটে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হয়ে বসতে পেরে এবার যেন শান্তি হল ছিদামের। আবার সেই আলো আলো ভালোমানুষের প্রাণ জুড়নো মুখ। কে জানে হয়ত এই প্রথম চারচাকা গাড়িতে চড়ল ছিদাম।
সায়ন বলল, “হ্যাঁ রে, বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছিস তো কিছু?”
“হ্যাঁ গো। ভাত খেয়েই তো দৌড়েছি। মা ভাত বেড়ে বসে ছিল। না গেলে চিন্তা করত।”
বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়ল সায়ন, “দেখলি? কেমন বুঝতে পারি আমি? ঠিক সময়েই ঘর পাঠিয়েছি তোকে।”
ছিদামের নিষ্পাপ সারল্য আবারও চোখ টানল সীমার। বাড়ি ফিরে নেয়েধুয়ে, দুটো খেয়েদেয়ে এসেছে। এখন বেশ ফ্রেশ লাগছে ছেলেটাকে।
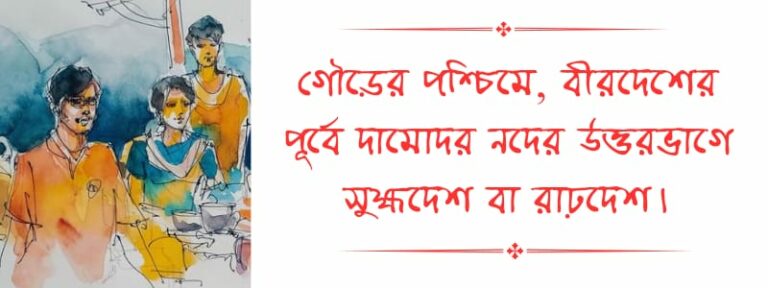
উন্মুক্ত বিশাল মাঠ। আভূমি ঝুরি নামা যুগ যুগ আগের প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় লালগাড়িটা পার্ক করে গুগলম্যাপের নিশানা দেখে মল্লেশ্বর শিবগঞ্জে এসে হাজির হল ওরা। ছিদামই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সায়ন ভাবে, ছিদাম এল বলে অনেকটাই সুবিধে হল। যতই ভরসা থাকুক গুগল ম্যাপে, মাঝেমধ্যে সেও উলটোপালটা রাস্তা দেখায়। মল্লেশ্বর যাবার পথে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যেত ওদের। ছিদাম এসে পড়ল তাই রক্ষে। ততক্ষণে দুপু্রের সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমের দিগন্তে। গাড়ির দরজা খুলে ছিদামকে নামিয়ে ওরাও নামলো একে একে। এই গোটা গ্রামটারই নাম ‘শিববাড়ি’।
“গাড়ি থেকে নামতে নামতে কী বিড়বিড় করছিলি রে?” কৌতূহল চাপতে পারে না সীমা।
ছিদাম বলে, “নেপালদাদুর শেখানো শ্লোকটা তোমাদের বলব তো, তাই আওড়ে নিলাম একবার।”
“তাই! তাহলে বল দেখি, শুনি।”
ছিদাম বলতে থাকে—
“গৌড়স্য পশ্চিমভাগে বীরদেশস্য পূর্বতঃ
দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশ প্রকীর্ত্তিতঃ
মহাভারত থেকে শুরু করে কালিদাস, সব পুরনো বইতেই সুহ্মদেশের উল্লেখ আছে। আমাদের নেপালদাদুই তো এই শ্লোকটা উদ্ধার করেছেন।
আবার কেউ কেউ বলে,
গৌড়স্য পশ্চিমভাগে বীরদেশস্য পূর্বতঃ
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশ প্রকীর্ত্তিতঃ।।
সায়ন বলল, “তার মানে সুহ্মদেশ আর রাঢ়দেশ শব্দ দুটো অদলবদল হয়েছে মাত্র। শ্লোকের মূল অর্থ একই রইল।”
“মহাভারত আছে তুমাদের ঘরে? মহাভারতের সভা পর্বে না কী আছে, সুহ্ম এবং রাঢ়দেশ একই এলাকার দুটো নাম!” ছিদাম হাসতে হাসতে বলে।
“তুই এই শ্লোকটার মানে জানিস?” সীমা বলে
“হ্যাঁ। জানি তো। গৌড়ের পশ্চিমে, বীরদেশের পূর্বে, দামোদর নদের উত্তরভাগে সুহ্মদেশ বা রাঢ়দেশ। এখানকার আদি বাসিন্দা রায়দের সুমু বলে তো। সেই সুহ্ম থেকেই এসেছে এই শব্দ। ব্রাহ্মণ যেমন বামুন হয়েছে, ঠিক তেমনই।” প্রায় মুখস্থের মতো গড়গড় করে বলে যায় ছিদাম।
সায়ন মাথা নাড়ে, “ঠিক। বীরভূমকে তো বীরভূমিও বলা হত একসময়। আদিবাসী শব্দে বীর মানে তো জঙ্গল। খুব সম্ভবত, এই মলুটী গ্রাম গড়ে ওঠার সময় তা অবিভক্ত বৃহত্তর বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলে ছিল।”
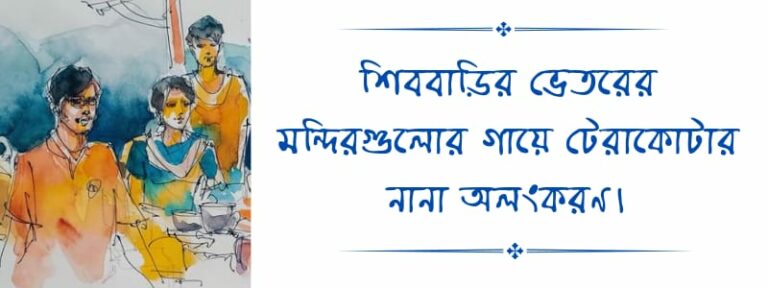
সায়নের ব্যাখ্যা শুনে খুশি হয়ে ওঠে সীমা।
ছিদাম বলে, “ওই যে মহাভারতের কথা উঠল না! মহাভারতের কত গল্প যে পাবে এই মল্লেশ্বরে! এবার চল, বলব তুমাদের।”
মল্লেশ্বর শিবগঞ্জের মন্দিরপল্লিতে ঢুকেই ছিদাম যেন আবার প্রফেশানাল গাইড বনে গেল। আগের মতোই। গলগল করে বকবক শুরু করে দেয় সে। সায়ন আর সীমা মোহিত হয়ে পড়ে ওইটুকু ছেলের আগ্রহ আর এনার্জি দেখে। এইটুকু বয়সেই কী ম্যাচিওরড ছেলেটা!
ছিদাম আবার এসে পড়ায় ওরা দুজনেই আহ্লাদে আটখানা তখন। নিজেদের মধ্যেই বলাকওয়া করে, ছিদামের বংশ ভালো। গ্রুমিংও ভালো।
সায়ন বলে, “ওই যে বুড়ো ভদ্রলোক! শুনলে না? নেপালবাবু! ওঁর গাইডেন্স পাচ্ছে তো… তবে পেডিগ্রিও ভালো ছেলেটার।”
প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক বিরাট চৌহদ্দির মধ্যে মল্লেশ্বর শিব মন্দির ছাড়াও গ্রামের চারিদিকে রয়েছে লাইন করে মন্দির। বেশিরভাগই ছোট, বাংলার চারচালা রীতিতে তৈরি। উত্তর দিকে দোতলা প্রধান তোরণটি দেখিয়ে ছিদাম বলল, “এই দেখ বাবু, তোরণদ্বারের ওপর নহবতখানা। আগে বোধহয় সানাই বাজত।”
শিববাড়ির ভেতরের মন্দিরগুলোর গায়ে টেরাকোটার নানা অলংকরণ। একের পর এক ছবি তুলতে থাকে সায়ন। অজস্র দেবদেবীর মূর্তি। এখনও অক্ষত। ঘুরতে ঘুরতেই সীমা বলে, “ছিদাম! তুই জানিস কতকাল আগেকার এই শিবপল্লি?”
“নেপাল দাদু তো বলেছিল দ্বাদশ শতাব্দীর। এই দেখ, এটা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর শিলামূর্তি।”
সীমা প্রণাম করে দেখতে পায় সিঁদুরে লেপা সেই পাথরের দেবীর মুখমণ্ডলে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে ত্রিনয়ন। খানিকটা আপন বলেই বিড়বিড় করে সে, “বুঝলাম। সব শক্তি মন্দিরেই যেমন একজন পুরুষ আর একজন প্রকৃতি থাকেন, তেমন এখানে এই সিদ্ধেশ্বরী দেবীই বুঝি মল্লেশ্বর শিবের শক্তিস্বরূপা!”
“ঠিক বলেছ দিদিমণি!” ঘাড় নেড়ে সায় দেয় নেপাল— “নেপালদাদুও ঠিক তোমার মতোই বলত।”
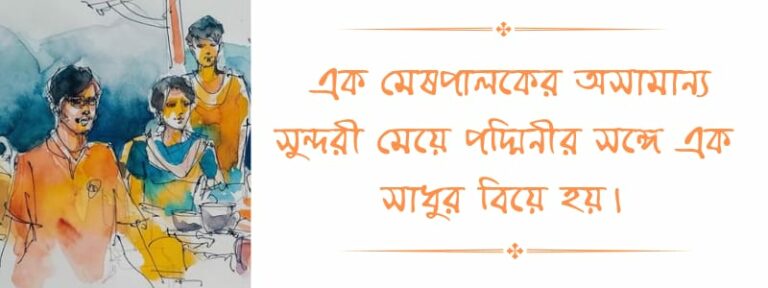
“জানো? মল্লেশ্বর শিব নিয়ে এ অঞ্চলে অনেকে অনেক কথা বলে।”
সীমা বলে, “হ্যাঁ রে। পড়ছিলাম আসতে আসতে ফোনে। মল্লারপুরের ঘন জঙ্গলে এক মেষপালকের অসামান্য সুন্দরী মেয়ে পদ্মিনীর সঙ্গে এক সাধুর বিয়ে হয়। তাঁদের সন্তান মল্লনাথ।” সীমা অবশ্য নিজের ভাষা বদলেছে ছিদামের সামনে।
আসলে সীমা যা পড়েছে তার একটা লাগসই ব্যাখ্যাও খুঁজে নিয়েছে নিজের মনে। সে ভাবে, হয়তো সেই সন্ন্যাসীকে সিডিউস করেছিল পদ্মিনী নামের এক রূপসী কন্যা। কিংবা উল্টোটাও হতে পারে। মানে সন্ন্যাসীও পদ্মিনীর প্রেমে আকুল হয়ে তাকে হয়ত ভোগ করার লোভ সামলাতে পারেনি। সবই তো লোকায়ত ঘটনা। মানুষ নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে আসছে।
“আরও ঘটনা আছে…” ছিদাম বলে, “একদিন গভীর বনের মধ্যে গোরু চরাতে গিয়ে মল্লনাথ চমকে ওঠে। দেখে, একটা দলছুট গরু বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দুধ দিচ্ছে আপনা আপনি। সেই যে বটগাছটার নীচে তুমি গাড়ি রাখলে? সবাই বলে ওই গাছটাই। কয়েক দিন পরপর একই জিনিস ঘটতে দেখে মল্লনাথ তার সেই সন্ন্যাসী বাবাকে নিয়ে সেখানে হাজির হল। তার বাবা বলল গ্রামের আরও লোকজন নিয়ে জায়গাটা খুঁড়তে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে উদ্ধার হল ঘড়া ঘড়া গুপ্তধন…”
“একদম ঠিক বলছিস। প্লিজ ক্যারি অন ছিদাম।” সীমা বলে ওঠে।
“কী বললে ওটা?”
সায়ন হেসে ওঠে— “মানে, তুই চালিয়ে যা। থামিস না। খুব ভালো লাগছে এ গল্প আমাদের।”
ছিদাম আবারও শুরু করে—
“মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তার কিছু পরেই কোদাল আর পাথরের ঘষায় বিশাল শব্দ। হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠতেই চমকে উঠল সবাই। মল্লনাথ নাকি দৈববাণী শুনতে পেয়েছিল তখনই। মাটির নীচে ছিল মহাভারতের রাজা জয়দ্রথের পূজিত শিব, বাবা সিদ্ধিনাথ। বাবা সিদ্ধিনাথই এখানকার এই মল্লেশ্বর শিব। পাথরের শিলায় এখনও সেই কোদালের ক্ষতচিহ্ন আছে, দেখে নাও গিয়ে। মাটির নীচ থেকে পাওয়া সেই গুপ্তধনের মালিক হয়েছিল মল্লনাথ। আর সেই মল্লনাথের নামেই এই জায়গার নাম মল্লারপুর।
মহারাজ মল্লনাথ সিংহ এই জনপদের উন্নয়ন করে রাজধানী নির্মাণ করান। শিব মন্দিরের সংস্কার করেন, তাই জনপদের নাম মল্লারপুর এবং শিবের নাম ‘মল্লেশ্বর’ হয়েছে।
পাশের ফতেপুর গ্রামে অনেক প্রাচীনকালে এক জনজাতির বাস ছিল। এই দেখ না পড়ে! মল্লনাথের জন্মের কথা সব লেখা আছে পাথরে।”
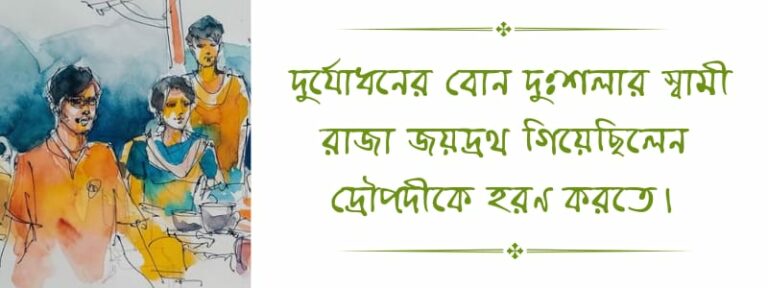
মোট ২৩টা মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখায় ছিদাম। তার মধ্যে একটি মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি, বাকি সব শিব মন্দির।
সীমা বলল, “এইবার বুঝলাম মল্লারপুর নামের সূত্র। তুই আবার না ফিরে এলে কি আর এতসব জানা হত আমাদের? ব্লেস ইউ ডিয়ার।”
“কী বললে দিদিমণি? ও কথার মানে কী?” বিস্ময়ের রেশ ছিদামের গলায়…
সায়ন বলে, “দিদিমণি তোকে আশীর্বাদ করল।”
ছিদাম হাসে ফিক করে। তারপর আবার বলতে শুরু করে— “এই গ্রামের পুবদিকের জঙ্গলে গেলে দেখতে পাবে শিবপাহাড়ি নামে এক পাহাড় আছে। পাণ্ডবরা বনবাসের সময় যখন কাম্যক বনে বাস করছিলেন তখন মাতা কুন্তী এই শিব পুজো করতেন, জানো! দুর্যোধনের বোন দুঃশলার স্বামী রাজা জয়দ্রথ গিয়েছিলেন দ্রৌপদীকে হরণ করতে। ভীমের হাতে অপমানিত হয়ে জয়দ্রথ তখন কঠোর তপস্যা শুরু করেন। সিদ্ধিনাথ শিব শেষ পর্যন্ত জয়দ্রথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন যে, কেউ তাঁকে কোনোদিনও যুদ্ধে হারাতে পারবে না।”
সায়ন বলে, “বাবা রে! তুই তো ইতিহাস ভূগোল সব গুলে খেয়েছিস দেখছি!”
একটু আনমনা হয়ে পড়ে ছিদাম, বলে, “আমাদের গ্রামের ওই নেপালদাদু মাঝেমধ্যেই পাড়ার ছেলেদের ডেকে গল্প শোনাতেন। আর বেঁচে নেই উনি।”
“তুই এই নেপালদাদুকে খুব ভালবাসিস না রে?”
ছিদাম বলে, “উনার পুরো নাম নেপালনাথ মুখোপাধ্যায়। খুব জ্ঞানী, পণ্ডিত লোক আমাদের গ্রামের। মলুটী ছিল উনার প্রাণ। উনার কাছেই তো আমরা মলুটী, মল্লনাথের এসব গল্প শুনে শুনে বড় হয়েছি গো।
‘বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথ রাঢ়ে চ তারকেশ্বর’
নেপালদাদুই শিখিয়েছিলেন মল্লেশ্বর শিবের এই মন্ত্র।”
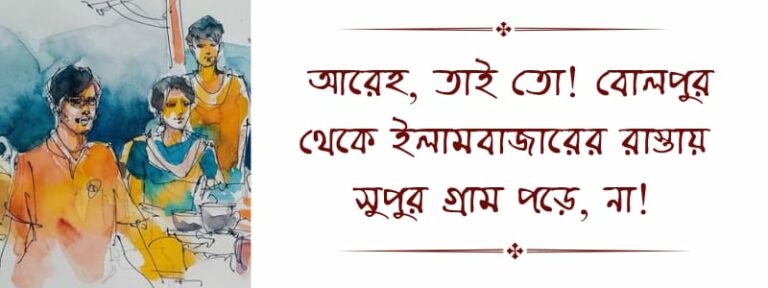
নেপালনাথ মুখোপাধ্যায়কে সীমাও খুঁজে পায় মুঠোফোনে। সায়নকে দেখিয়ে বলে, “এই দেখ, ঠিক বলেছে কিন্তু ছিদাম। ‘টেমপলস অফ ইন্ডিয়া’ নামে একটা ওয়েবসাইটে মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র বলে একটা পেজ আছে দেখলাম। সেখানে সব স্বয়ম্ভূ শিব মন্দিরের তালিকা আছে। সিদ্ধিনাথ নামে এই ‘ওঁ’ আকৃতির মহাদেবের কথাও রয়েছে সেখানে।”
“তবে একটা জিনিসে খটকা লাগল। জয়দ্রথ তো শোনা যায় সিন্ধুপ্রদেশের রাজা ছিলেন। তিনি বঙ্গের লাগোয়া ঝাড়খণ্ডী গ্রামে? অবাক লাগছে না?” ভুরু কুঁচকে বলে ওঠে সায়ন।
সীমা বলে, “কেন? দুঃশলা আর জয়দ্রথের ছেলের নাম তো সুরথ। সেই সুরথকেই আমরা আবার পাই বলিপুর বা বোলপুরের প্রভাবশালী রাজা রূপে।”
সায়ন বলল, “আরেহ, তাই তো! বোলপুর থেকে ইলামবাজারের রাস্তায় সুপুর গ্রাম পড়ে, না! যেখানে ছিল সুরথের রাজধানী। বাংলার প্রথম দুর্গাপুজো… তার সঙ্গে সুরথের নাম জড়িয়ে রয়েছে তো।”
“ওহ! কলকাতা থেকে আসার পথে সেই যে সুপুরের টেরাকোটার জোড়া শিবমন্দির দুটোর ছবি তুললাম!” সীমা বলে ওঠে।
সায়ন বলে, “হ্যাঁ। সেখানে বহুকাল আগে রাজত্ব করতেন যে রাজা তার নাম ছিল সুবাহু সিংহ। তার নাম থেকেই সুবাহুপুর হয়েছিল এই জনপদের নাম যা লোকমুখে আজ ‘সুপুর’। কিছুদিন আগেই পড়ছিলাম কোথায় যেন…”
“বেশ ইন্টারেস্টিং তো।” সীমা বলে ওঠে।

সায়ন বলে, “বলিরাজার থেকে বলিপুর বা এখনকার বোলপুর, সে গল্প আরও মজার, জানো!
সুরথ রাজা তো সুবাহুরই বংশধর। রাজ্যহীন হয়ে আত্মীয় পরিজন পরিত্যক্ত হয়ে আশ্রয় নেন এই সুপুরেই।”
সীমা বলে, “বাংলায় বসন্তকালের দুর্গা পুজো চালুর মূলে তো সুরথ। তারপর?”
“এখানকার গ্রাম্যদেবী শিবিক্ষাকে তুষ্ট করতেই সুরথ নাকি লক্ষাধিক বলি দিয়েছিলেন। সুপুরের শিবিক্ষা মন্দির থেকে ডাঙ্গালি কালীতলা অবধি বলি চলেছিল। অসংখ্য পশুর রক্তে নাকি সেদিন ভিজেছিল এই বলিপুর।”
“এই দেখ, এই দেখ…” হাতের মুঠোফোনে বীরভূমের সরকারি ওয়েবসাইটে এসব তথ্য খুলে সায়ন দেখাতে থাকে সীমাকে।
সীমা বলে, “ও তারপরই এই গোটা অঞ্চলের নাম হয়ে গেল বলিপুর! আর তা থেকেই আজকের এই বোলপুর!”
“বর্গি আক্রমণেও নাকি এই মন্দিরের তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। তার মূলে বোলপুরের সাহসী গ্রামবাসী।”
ছিদাম ওদের কথা শুনতে থাকে। ভালো লাগে তারও এসব জানতে।
কথাটা শেষ করতে না করতেই সায়ন ফেসবুকে স্টেট্যাস আপডেট দেয়, মল্লেশ্বর মন্দিরের একটা দারুণ টেরাকোটা প্যানেল ওয়ার্ক পোষ্ট করে, সঙ্গে লেখে ‘ফিলিং কিউরিয়াস আবাউট মহাভারত কানেকশন উইথ মল্লেশ্বর’।
সীমা বলে, “অমনি! ঝেড়ে দিলেন মশাই আমার থেকে! জ্ঞান নিয়ে বিতরণ করে বসলেন ফেসবুকে।”
“দেখিই না লোকজন কী বলে! কেউ তো আজকাল কিস্যু পড়ে না। জানে না। জানতে চায়ও না। যদি তবু কেউ কিছু জ্ঞান বিতরণ করে তাদের কমেন্টে।”
এবার কথা বলে ওঠে ছিদাম, “আমার কিন্তু জানতে আর শুনতে হেব্বি লাগে স্যার। জানো! আমাদের নেপাল দাদুর বইপত্র ঝেড়ে সারা নেটে ছড়িয়ে গেছে। কাগজে লেখালেখি হচ্ছে। ইন্টারনেটে ভরে গেছে মলুটীর কথা। মাঝখান থেকে দাদুই কিছু পায়নি, দুএকটা ছোট পুরস্কার ছাড়া। তবু এই মলুটীকে আঁকড়েই পড়ে রইল সারাজীবন।
অলংকরণ: শুভ্রনীল ঘোষ
ছবি সৌজন্য: Indiancolumbus
*পরের পর্ব প্রকাশ পাবে ১৯ এপ্রিল, ২০২৩
রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।


























One Response
ইতিহাসের পাতাগুলো খুব সুন্দর ভাবে লিখেছেন যা আমার মত ইতিহাসে পাতিহাঁস কে মুগ্ধ করে রাখল ।